‘সত্যার্থপ্রকাশ’ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতির এক আশ্চর্য অমর রচনা। এটি বৈদিক তত্ত্ব ও মহর্ষির অভিমতের এক বিশ্বকোষ। বেদ, স্মৃতি, দর্শন এবং অন্যান্য বিভিন্ন আর্য গ্রন্থের প্রমাণ ও গ্রন্থকারের যুক্তিতে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ-রত্ন বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের জন্য এক আলোকস্তম্ভ। ঋষি দয়ানন্দ বৈদ অনুসারী মধ্যকাল ও বর্তমান কালের বিকৃত মত–সমপ্রদায়গুলোর পর্যালোচনার পাশাপাশি অবৈদিক মত–সমপ্রদায়গুলোরও পর্যালোচনা আর্য পদ্ধতিতে নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বাক্য ও বচনের ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণের প্রচেষ্টা নানা আর্য পণ্ডিত সময়ে সময়ে করে আসছেন। স্বামী বেদানন্দ, পণ্ডিত উদয়বীর শাস্ত্রী ও পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক ঋষির বচনের ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ধারােতে স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতির নামও যুক্ত হয়েছে।
পূর্বাশ্রমে श्री লক্ষ্মীদত্ত दीक्षित নামে খ্যাত, ডি.এ.ভি. কলেজের সফল অধ্যক্ষ স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতি প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি আজীবন বৈদিক ধর্মের প্রচার–প্রসারে নিযুক্ত ছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। বহু বছর ধরে তিনি রামলাল কাপুর ট্রাস্টের প্রধান পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর লেখনী অবিরাম প্রবাহিত হয়েছে, যার ফলে সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজিতে প্রায় পঁয়ত্রিশটি উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত গ্রন্থ ‘সত্যার্থভাস্কর’-এ মহর্ষির বচনের বিশদ ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। তিনি যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে মহর্ষির মতামত ও নীতির সুদৃঢ় সমর্থন প্রদান করেছেন। বহু জটিল সমস্যার তিনি প্রশংসনীয় সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর সমস্ত গ্রন্থই আর্যসমাজের মানুষের আন্তরিক সমাদর পেয়েছে।
এই গ্রন্থ প্রথমবার স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতির অন্যান্য গ্রন্থের মতোই ইন্টারন্যাশনাল আর্যন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিক্রয় হতো রামলাল কাপুর ট্রাস্টের মাধ্যমে। পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। তাই স্বামীজি তাঁর সব গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার রামলাল কাপুর ট্রাস্টকে প্রদান করেছিলেন, ফলে এই গ্রন্থও উক্ত ট্রাস্টের দ্বারা পুনরায় প্রকাশ করা হচ্ছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, আর্য সমাজের মানুষ আগের মতোই আমাদের সহযোগিতা প্রদান করে যাবে।
প্রাককথন
বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের লোপ হয়ে সহস্র বছর কেটে গেছে। পুরাণিক হিন্দু ধর্মের রূপে তার অবশিষ্টাংশই সেখানে মিলত। যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা রাম ও কৃষ্ণ করতেন, তাকে ছেড়ে উপাসকরা রাম ও কৃষ্ণকেই উপাস্য মেনে তাঁদেরই ধূপ-নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা করতে শুরু করেছিল। গীতায় বলা হয়েছিল— ‘ইশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্টতি’ (গীতা০ ১৮/৬১), কিন্তু ভক্তজন তাঁকে নিজের হৃদয়-মন্দির থেকে সরিয়ে গলি-ঘুঁজির ইট-পাথরের মন্দিরে বন্দি করে ফেলেছিল। ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’—এমন ইচ্ছামতো ঘোষণা করে ঈশ্বর ও বেদ-এর নামে নিরীহ পশুদের হত্যা করে তথাকথিত ভক্তজন আনন্দ পেত। গুণ–কর্ম–স্বভাবের উপর নির্ভরশীল প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার স্থান নিয়েছিল জন্মভিত্তিক কলুষিত জাতিপ্রথা। দুধমুখো শিশুদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ফলত লক্ষ লক্ষ বাল্যবিধবা অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। পুরোহিতবর্গ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে অথবা সামাজিক দণ্ডের ভয় দেখিয়ে সতীর নামে জীবিতাবস্থায় চিতায় দগ্ধ হতে বাধ্য করত। ব্রাহ্মণবর্গ নানান পাখণ্ড রচনা করে জনতাকে লুটত। রোগকে ভূত–প্রেতের ক্রীড়া বলে একদিকে নিজের পকেট গরম করত, অন্যদিকে রোগীকে যথাযথ চিকিৎসার সুফল থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিত। জ্যোতিষের নামে ঠগবিদ্যা জোর গলায় চলছিল। তীর্থস্থানগুলো ব্যভিচারের আস্তানায় পরিণত হয়েছিল। ‘स्त्रीशूद्रौ गाधीयातामिति श्रुतेः’—এই মিথ্যা প্রচার করে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে নিয়মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল এবং কিছু লোক উপায়ের অভাবে নিরক্ষর রয়ে যেত। এইভাবে ভারত অশিক্ষিত-গাঁইয়া মানুষের দেশ হয়ে পড়েছিল।
এই দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয়দানকারী গ্রন্থগুলো রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসেবে উপস্থাপন করে। এতে সন্দেহ নেই যে সেই যুগে সামাজিক কু-প্রথা ও অন্ধবিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনে সমাজ-সংস্কারের পথ সুগম করা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮২৮ সালে সতীপ্রথার বিরোধী আইন প্রণীত হয়। তাঁরই প্রদেশের আর এক মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহকে বৈধতা দেওয়া আইন প্রবর্তন করান। মূলত রাজা রামমোহন রায় বৈদিক চিন্তাধারার প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ‘ব্রহ্মসমাজ’-এর ট্রাস্ট-ডিড ৮ জানুয়ারি ১৮৩০ সালে লিখিত হয়। তার অনুযায়ী ব্রহ্মসমাজের নিম্নোক্ত নীতিসমূহ নির্ধারিত হয়েছিল—
১. বেদ ও উপনিষদকে মান্য করা উচিত।
২. তৎসবিতে একেশ্বরবাদের প্রতিপাদন আছে।
৩. মূর্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় পরিত্যাজ্য।
বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীপ্রথা ইত্যাদি সবই বেদবিরুদ্ধ, তাই পরিত্যাজ্য। মূর্তিপূজার সম্পর্কেও তিনি লিখেছিলেন—
“If idolatry, as now practised by our countrymen and which the learned Brahmans so zealously support as conducive to morality, is not only universally rejected by the Shastrus, but must also be looked upon with great horror by common sense, as leading directly to immorality.” (Monotheistical System of the Vedas, p. 123)
অর্থাৎ—যে মূর্তিপূজা আজকাল আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এবং যাকে বিদ্বান ব্রাহ্মণরা সদাচারের সাধন বলাতে এত উৎসাহ দেখান, তা শুধু সকল শাস্ত্র দ্বারাই নিষিদ্ধ নয়, বরং সাধারণ বুদ্ধিতেও অত্যন্ত ভয়াবহ বলে গণ্য হওয়া উচিত, কারণ এর ফলে দুরাচার বৃদ্ধি পায়। এখান থেকে মহাদেব ও পার্বতীর মূর্তির ভয়াবহতার বাস্তবচিত্রের ইঙ্গিত করে রাজা রামমোহন রায় বলেছেন যে মূর্তিপূজা এবং পুরাণে প্রাপ্ত সেই সব কাহিনি, যাদের ভিত্তিতে মূর্তিপূজা প্রচলিত, সেগুলো থেকে সদাচার-শিক্ষার আশা করা বালুর ওপর প্রাচীর গড়ার মতো। অন্যত্র তিনি লিখেছেন—
"For, whenever, a Hindu purchases an idol from the market, or constructs one with his own hands, or has one made under his superintendence, it is his invariable practice to perform certain ceremonies, called Prana-pratishtha … by which he believes that its nature is changed from that of the mere materials of which it is formed and that it acquires not only life but also supernatural powers. Shortly afterwards, if the idol be of the masculine gender, he marries it to a feminine one, with no less pomp and magnificence than he celebrates the nuptials of his own children. The mysterious process is now complete and the god and goddess of their own making are esteemed the arbiters of his destiny."
(English Works of Raja Ram Mohan Rai by H. C. Sarkar, 1982, p. 72)
যখন কোনো হিন্দু বাজার থেকে মূর্তি কেনে, অথবা নিজের হাতে তৈরি করে, কিংবা নিজের তত্ত্বাবধানে কাউকে দিয়ে বানায়, তখন সে অবশ্যই তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করায়। এর অর্থ এই যে সে মনে করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার ফলে মূর্তির স্বভাব বদলে যায় এবং তাতে শুধু প্রাণই আসে না, বরং দেবত্বও আসে। যদি সেই মূর্তি পুংলিঙ্গ হয় তবে তার সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ মূর্তির বিবাহ দেওয়া হয়, ঠিক নিজের সন্তানের মতোই। এই রহস্যময় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে নিজেই তৈরি করা এই দেবী–দেবতা তার ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে।
মৌর্য যুগের পর পুষ্যমিত্রের সময় যে ধর্মের পোষণ করা হয়েছিল, ইতিহাসে তাকে ব্রাহ্মণধর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋষি দয়ানন্দ তাকে পুরাণিক ধর্ম বলেছেন (এখানে আমরা ধর্ম শব্দটি বর্তমান রূঢ় অর্থে ব্যবহার করছি)। এই ধর্ম তার নিজস্ব পরম্পরা অনুসারে সর্বদা রাজশক্তির আশ্রয় নিয়ে এসেছে। মধ্যযুগে এই শ্রেণি ইসলামের সাহায্যে নিজের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। এদের কারণেই সিন্ধি ভাষা দেবনাগরীর পরিবর্তে আরবি অক্ষরে লেখা হতে শুরু করে, কারণ এই শ্রেণি ‘স্বার্থসিদ্ধয়ে রাজ্যায় নমো নমঃ’ অথবা ‘যথা রাজা তথা প্রজা’-তে বিশ্বাসী ছিল। ইংরেজদের যুগে এই শ্রেণি চাকরি পাওয়ার জন্য ইংরেজি গ্রহণ করল। ভাষার সঙ্গে তার সাহিত্য, আর সাহিত্যের সঙ্গে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক তো আছেই, কালক্রমে তার সত্তাও তাতে প্রভাবিত না হয়ে থাকে না।
রাজা রামমোহন রায় প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁর চিন্তনে মৌলিকতা ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে যদি হিন্দুধর্মকে টিকে থাকতে হয় তবে তার বর্তমান রূপকে সংস্কার করতে হবে। না হিন্দুধর্মকে যেমন আছে তেমনই আঁকড়ে ধরে রাখলে চলবে, না সেটাকে ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেই কল্যাণ হবে। তাই তিনি মধ্যপন্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর ভারসাম্য হারাতে লাগলেন। নিজের ‘Autobiographical Sketch’-এ তিনি লিখেছেন—
"Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants."
অর্থাৎ যখন আমার জানা হলো যে তারা (ইংরেজরা) সাধারণত বেশি বুদ্ধিমান, বেশি ধীরস্থির এবং আচরণে সংযত, তখন তাদের প্রতি আমার পূর্বাগ্রহ চলে গেল এবং আমি তাদের পক্ষে ঝুঁকলাম। আমার বিশ্বাস হলো যে তাদের শাসন বিদেশি জুঅ হলেও ভারতবাসীর উন্নতির জন্য অবশ্যই উপকারী হবে।
রাজা রামমোহন রায়ের হীনম্মন্যতার সূচক এবং অত্যাচারী বিদেশি শাসকদের তোষামোদকারী এই বক্তব্য…ঋষি দয়ানন্দের নিম্নোক্ত বাক্যের তুলনায় এই কথন কতটা নীচ তা সয়ং সাখ্য—
“কেউ যতই করুক, কিন্তু যে স্বদেশীয় রাজ্য হয় সেটাই সর্বোপরি উত্তম, অথবা মত-ভেদ জনিত পক্ষপাতহীন, আপন-পরের প্রতি নিরপেক্ষ, প্রজার প্রতি মা-বাবার মতো কৃপা, ন্যায় এবং দয়ার সঙ্গে পরিচালিত হলেও বিদেশিদের রাজ্য সম্পূর্ণ সুখদায়ক হয় না।” (সত্যার্থপ্রকাশ, অষ্টম সমুল্লাস)
এতে স্পষ্ট যে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম-ধারণা (ব্রাহ্মসমাজ) বিশুদ্ধ ভারতীয় না হয়ে খ্রিস্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই বিষয়ে রোম্যা রোলাঁ-র (Romain Rolland) স্পষ্ট মত ছিল যে “রাজা রামমোহন রায় যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন, তা ছিল মার্টিন লুথার প্রবর্তিত প্রোটেস্ট্যান্ট একেশ্বরবাদ। তার সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টধর্মে লীন হয়ে যাওয়ার কারণে ভারতীয় সাধারণ জনগণের তার প্রতি বিশ্বাস আর অবশিষ্ট ছিল না।” (রোম্যা রোলাঁ—রামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃ. ১৫৫)
এই কারণেই রামমোহন সেই ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থার সমর্থন করেছিলেন, যা ম্যাকলে-র মতে ভারতীয়দের প্রবৃত্তি, সম্মতি, নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞায় ইংরেজ-খ্রিস্টান বানানোর একটি সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র ছিল (পি. ভি. কাণে—ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস, ভাগ ৫, পৃ. ৪১৬)। স্বয়ং ম্যাকলে লিখেছিলেন—
“We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, words and intellect.”
অর্থাৎ আমাদের উচিত এই দেশে এমন একটি শ্রেণি সৃষ্টি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, যারা আমাদের এবং আমাদের দ্বারা শাসিত কোটি কোটি ভারতীয়দের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতে পারবে। এই শ্রেণি রক্ত-মাংস ও রঙে ভারতীয় দেখালেও আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কথাবার্তা এবং মন-চেতনার দিক দিয়ে ইংরেজ হয়ে যাবে। এই প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাফল্যের বিবরণও ম্যাকলে-র ভাষাতেই পাওয়া যায়। ১৮৩৬ সালে নিজের চাচাকে লেখা এক চিঠিতে সে লিখেছিল—
“No Hindu, who has received English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy, but many profess themselves pure theists and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence.”
অর্থাৎ যে কোনো হিন্দু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে, সে তার ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ শুধু কৌশলবশত তাকে মান্য করে চলতে থাকে, অধিকাংশ কেবল একেশ্বরবাদী হয়ে যায় বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যদি আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্যকর হয়, তবে আজ থেকে ত্রিশ বছর পর বাংলার সম্মানিত পরিবারগুলোর মধ্যে একজনও মূর্তিপূজক অবশিষ্ট থাকবে না।
ম্যাকলে-র শিক্ষা-নীতির ওপর আধুনিক প্রেক্ষাপটে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন—
“The policy inaugurated by Macaulay is so careful as not to make us forget the force and vitality of Western culture, it has not helped us to love our own culture. In some cases, Macaulay's wish is fulfilled and we have educated Indians who are ‘more English than the English themselves’ to quote Macaulay's own words.”
এর মর্মার্থ এই যে ম্যাকলে-র শিক্ষা-নীতির অনুসারে শিক্ষিত ভারতীয়রা নিজেই ইংরেজদের চেয়েও বেশি ইংরেজ হয়ে গেছে।
রাজা রামমোহন রায় শুধু ম্যাকলে-র ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থার সমর্থনই করেননি, বরং ১৮২২ সালে নিজেই একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্টকে একটি চিঠি লিখে কলকাতায় বাংলার সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজকে অনাবশ্যক এবং ভারতীয়দের উন্নতির পথে বাধা বলে অভিহিত করেছিলেন (আর. এন. সামাধর—রাজা রামমোহন রায়, পৃ. ২৪–২৫)।
কেশবচন্দ্র সেন—রাজা রামমোহন রায়ের পর কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং নিজের বক্তৃতা-কুশলতার কারণে কেবল বাংলা নয়, সমগ্র দেশেই খ্যাতি অর্জন করেন। কেশববাবুর নিজের কোনো মৌলিক মতবাদ ছিল না। হিন্দুধর্মের স্বীকৃত মতগুলোকে অস্বীকার করার ফলে তাঁর দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কেশববাবু সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে রঞ্জিত ছিলেন এবং এই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে খ্রিস্টীয় সমাজের ভারতীয় সংস্করণে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজের হৃদয়ের অনুভূতিকে ৬ এপ্রিল ১৮৭৬ সালে কলকাতার টাউন হলে ‘ভারত জিজ্ঞাসা করছে—ঈশা কে?’ নামক বক্তৃতায় এ শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন—“আমার ঈশা, আমার মধুর ঈশা, আমার হৃদয়ের সর্বাধিক মূল্যবান হীরা, আমার আত্মার কণ্ঠহার যাকে আমি বিশ বছর ধরে আমার দগ্ধ হৃদয়ে ধারণ করেছি, ইত্যাদি” (সত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার—আর্যসমাজের ইতিহাস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৩)। ফরাসি মনীষী ও সাহিত্যিক রোম্যা রোলা লিখেছেন—“ঈশা তাঁর অন্তঃস্থলে স্পর্শ করেছিলেন। এখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঈশাকে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি তাকে বিশ্বের ধর্মীয় চেতনার সর্বোচ্চ ভাবনা বলে মনে করতেন। এতে কি আর কোনো বিষয় তাঁকে খ্রিস্টধর্ম থেকে পৃথক রাখতে পারত? কেশববাবু তখন উদিত শক্তিশালী জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধেই চলছিলেন।” (Romain Rolland : Prophets of New India)
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ সালে কেশববাবু আন্তর্জাতীয় বিবাহকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে একটি বিল উপস্থাপন করান। ১৬ মার্চ ১৮৭২ সালে এই বিলটি ‘Native Marriage Bill’ নামে পাস হয়। প্রথমে এর নাম রাখা হয়েছিল Brahmo Marriage Act অর্থাৎ ব্রাহ্মবিবাহ আইন। যারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন তারা এ বিলকে নিজেদের ওপর প্রযোজ্য করতে চাননি, তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। তাই কেশববাবুর সম্মতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল—“The term ‘Hindu’ does not include the Brahmos who deny the authority of the Vedas.” অর্থাৎ হিন্দু শব্দটি ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ তারা বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না (সত্যকেতু—আর্যসমাজের ইতিহাস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৮)। শুধু তাই নয়, তিনি ভারতের উপর ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এইসব প্রবণতার কারণেই তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লরেন্স তাঁকে ভারতীয় জনগণের উদ্ধারকর্তা বলে অভিহিত করে সম্মানিত করেছিলেন (ঐ, পৃ. ১৬৩)। এভাবে স্পষ্ট হয় যে, যদিও প্রারম্ভে ভারতের নবজাগরণের জন্য রাজা রামমোহন রায় প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন, তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি তাঁর এবং পরবর্তীতে কেশবচন্দ্র সেনের নীতির ফলে তারা ভারতীয় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।
রামকৃষ্ণ পরমহংস—সে যুগের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে তাঁর কোনো স্থান নেই। সমাজের প্রতি তাঁর কোনো বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তাঁর সমস্ত সময় কাটত কালীকে বিশ্বমাতা ও নিজের মাতারূপে মেনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর স্তব, উপাসনা ও কীর্তনে। তন্ত্রশক্তিতে পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিনী ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। প্রকৃত অর্থে তাঁর খ্যাতির কৃতিত্ব তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন ও আচরণের মাধ্যমে এ বক্তব্যকে অস্বীকার করেছিলেন যে, মূর্তিপূজা ঈশ্বরলাভের সিঁড়ি এবং সমাধিস্থাপনে সহায়ক ধ্যানের অভ্যাস একটি মাধ্যম। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ—উভয়েই শেষ শ্বাস পর্যন্ত প্রথম সিঁড়িতেই অবস্থান করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী (Vivekananda—A Biography by Swami Nikhilananda, প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা)-র লেখক লিখেছেন—
“১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট ভোররাতে একটি বাজনাধ্বনিময় কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় কালী-নাম তিনবার উচ্চারণ করেন এবং সমাধিস্থ হন, যেখান থেকে তাঁর মন আর কখনো ভৌতিক জগতে প্রত্যাবর্তন করেনি।” (পৃষ্ঠা ৬৬)
অর্থাৎ—মৃত্যুর দিন ভোরে একটা বেজে দুই মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনবার তাঁর প্রিয় কালী-नाम উচ্চারণ করেন এবং সেই সমাধিস্থ অবস্থায় প্রবেশ করেন, যেখান থেকে তিনি আর কখনো ভৌতিক জগতে ফিরে আসেননি।
इसी प्रकार স্বামী विवेकानन्द की मृत्यु का वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा है—
"On the supreme day he expressed his desire to worship Mother Kali at the Math and asked two of his disciples to procure all the necessary articles for the worship." (page 339).
অর্থাৎ—মৃত্যুর দিন স্বামী বিবেকানন্দ মঠে অবস্থিত কালী-মূর্তির পূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দুই শিষ্যকে পূজার সম্পূর্ণ সামগ্রী এনে দিতে বলেন।
উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে গুরু (শ্রীরামকৃষ্ণ) এবং শিষ্য (স্বামী বিবেকানন্দ)—উভয়েরই মৃত্যুর সময় কেবল কালী-রই স্মরণ হয়েছে, ভগবানের নয়। কিছু লোক বলেন, আমরা মূর্তিকে ঈশ্বর মনে করি না, আমরা তাকে কেবল মানসিক বিকাশের উপায় হিসেবে গ্রহণ করি। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের বক্তব্য—
"Hindus of the present age have not the least idea that it is the attributes of the Supreme King as figuratively represented by shapes corresponding to the nature of these attributes, they offer adoration and worship under the denomination of gods and goddesses. On the contrary, the slightest investigation will clearly satisfy every inquirer, that it makes a material part of their system to hold as articles of faith all those particular circumstances, which are essential to the belief in the independent existence of the objects of their idolatory as deities clothed with divine power."
(English Works of Raja Ram Mohan Rai by H. C. Sarkar, page 71)
অর্থ এই যে বর্তমান যুগের হিন্দুরা মোটেই জানে না যে যেসব দেব-দেবীর তারা পূজা করে, তারা পরব্রহ্মের গুণাবলির প্রতিনিধিরূপ। সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই বোঝা যাবে যে তারা এগুলোকে স্বাধীন সত্তা বলে মেনে নেয় এবং দেবশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বররূপেই তাদের পূজা করে।
স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলেন—
"Idolatory is the attempt of undeveloped minds to grasp spiritual truths." (Teachings of Swami Vivekananda, p. 142)
অর্থাৎ—মূর্তিপূজা অবিকশিত মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করার একটি সহায়ক মাধ্যম।
যদি মূর্তিপূজা অবিকশিত মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষের জন্য হয়, তবে যাদের সমগ্র জীবন মূর্তিপূজাতেই কেটেছে এবং যারা মূর্তিপূজা করতে-করতে ও কালী-নাম জপ করতে-করতে প্রाणত্যাগ করেছেন, তাদের কী বলা যায়?
আলবর নরেশ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার লিখেছেন—
"The Maharaja of Alwar ridiculed the worship of images which to him were nothing but figures of stone, clay or metal. The Swami tried in vain to explain to him that Hindus worshipped God alone, using images as symbols. The image was helpful for concentration, especially at the beginning of his spiritual life. The Maharaja was not convinced."
অর্থাৎ—আলবরের মহারাজা মূর্তিপূজাকে উপহাস করতেন; তাঁর কাছে মূর্তিগুলো কেবল পাথর, মাটি বা ধাতুর আকৃতি মাত্র ছিল। স্বামীজি তাঁকে বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করেছিলেন যে হিন্দুরা কেবল ঈশ্বরকেই পূজা করে, মূর্তিগুলোকে প্রতীকেরূপে ব্যবহার করে। আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনাকালে একাগ্রতা অর্জনে মূর্তি সহায়ক—কিন্তু মহারাজা তাতে বিশ্বাসী হননি।
কোনো বস্তুকে তার প্রকৃত রূপে দেখা জ্ঞানীর লক্ষণ। আলবর-নরেশ জ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি পাথরকে পাথর, মাটিকে মাটি বলেই মনে করতেন। গাঁথুনিকে গাঁথুনি বলা বিদ্যা; তাকে হালুয়া মনে করাই অবিদ্যা। হরিণ নিষ্কলুষ ভক্তিভরে, পূর্ণ বিশ্বাসে বালুকাকে জল ভেবে নেয়; কিন্তু তাতে সে জলের কাজ পায় না। সাধনের প্রয়োজন থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ সাধ্যের প্রাপ্তি না হয়; এবং প্রকৃত সাধন তাকে-ই বলা যায় যা সাধ্য লাভ করিয়ে দেয়।
যদি মূর্তিপূজা ঈশ্বর-প্রাপ্তিতে সহায়ক হতো তবে জীবনভর মূর্তিপূজা করা…শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শেষ সময়ে ঈশ্বরের স্মরণ থাকা উচিত ছিল, কালী–পূজার নয়, কিন্তু তা হয়নি।
বাস্তবে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিপূজার প্রতি অনুরাগ তাঁর নানাবিধ কুসংস্কারের ফল ছিল। এক স্থানে তিনি লিখেছেন— “যদি মূর্তিপূজায় নানা প্রকার কুৎসিত চিন্তাধারাও প্রবেশ করে থাকে, তবুও আমি তার নিন্দা করব না” (বিবেকানন্দচরিত, পৃ. ১৪৬)।
মূর্তিপূজার প্রসঙ্গ এলে স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তিবোধকে সরিয়ে রাখতেন—নিম্নলিখিত ঘটনাটি তা স্পষ্ট করে—
"When Miss Noble came to India in January 1898 to work for the education of India, he gave her the name of Sister Nivedita. At first he taught her how to worship Shiva and then made the whole ceremony culminate in an offering at the feet of Buddha."
(Vivekananda—A Biography by Swami Nikhilananda, p. 260)
শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের জন্য ভারতে আগত এক বিদেশিনীকে প্রথমে শিবের পূজা শেখানো, এবং পূজা শেষ হলে শিব–পূজার বিরোধী মহামতি বুদ্ধের পদে নৈবেদ্য অর্পণ করানো—এ কেমন বিচারবুদ্ধি?
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবীর বিষয়ে উক্ত জীবনীতে লেখা হয়েছে—
"One day in the Kali Temple of Calcutta a western lady shuddered at the sight of blood of goats sacrificed before the Deity and exclaimed—‘Why is there so much blood before the goddess?’ Quickly the Swami (Vivekananda) retorted—‘Why not a little blood to complete the picture?’" (Ibid., p. 261)
শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র সাধনা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। সমাজসেবা, দেশভক্তি, সমাজ–সংস্কার প্রভৃতি তিনি ভণ্ডামি বলে মনে করতেন। এতটাই নয়, দেশ বা সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের তিনি উপহাসও করতেন। তিনি যেমন ছিলেন মূর্তিপূজক, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত অন্ধবিশ্বাস, আচার–অনুষ্ঠান, চমৎকার প্রভৃতি বিষয়েও পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণভাবেই ভাবপ্রধান, যুক্তির সেখানে স্থান ছিল না।
বিবেকানন্দের ফরাসি জীবনীকার রোমাঁ রোলাঁর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণ এক মুসলমানের প্রভাবে নিজের দেবতাকে ভুলে আল্লাহর নাম জপতে শুরু করেন। এমনকি তিনি মুসলমানি পোশাক পরেন এবং গোমাংস ভক্ষণ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়ে যান। (ভবানীলাল ভারতী— মহর্ষি দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ, পৃ. ২১৬)।
এ কথাটি প্রমাণ করার জন্য যে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুসারীরা হিন্দু নন, তাঁদের উকিল কলকাতা হাইকোর্টে বিতর্কে বলেন—
"During his SADHANA of Islam Ram Krishna was on the verge of eating beef. According to Dr. S. C. Chatterji, during his practice of Islam Ram Krishna often read Quran."
"The practice of Islam or SADHANA took place under the guidance of Govind Ray, a convert to Islam. When the Sadhana was completed Ram Krishna saw a luminous figure appearing before him. The luminous figure is said to be that of Mohammad. Ram Krishna used to say Namaz three to five times a day in order to make it conform to the authentic five times of Islam."
—Indian Express, নয়া দিল্লি, ২০-৯-৯০
স্বামী বিবেকানন্দ—এখানে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ও ভারতবিরোধী এবং ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মপোষক কয়েকটি মতামত তাঁর নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। এই মতামতগুলির সংকলন আমরা কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত নিচের দুইটি গ্রন্থ থেকে করেছি—
Vivekananda—A Biography — Swami Nikhilananda Saraswati
Teachings of Swami Vivekananda
সহজতার জন্য বারবার বইয়ের নাম না লিখে আমরা উল্লেখিত ক্রমানুসারে শুধু । এবং II সংক্ষেপে লিখেছি। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা বা লেখায় পারস্পরিক বিরোধী ভাবের প্রাচুর্য রয়েছে। পদে-পদে পরস্পরবিরোধী কথার উদাহরণ পাওয়া যায়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে “Teachings of Swami Vivekananda”-এর সম্পাদক ভূমিকায় লিখেছেন—
“বিবেকানন্দ পৃথিবীর এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি আনুষ্ঠানিক সামঞ্জস্য নিয়ে কোনো চিন্তাই করতেন না। তিনি প্রায় সবসময়ই হঠাৎ করে বক্তৃতা দিতেন, মুহূর্তের পরিস্থিতি দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে, নির্দিষ্ট শ্রোতৃসমাজের অবস্থার কথা ভেবে কথা বলতেন, কোনো বিশেষ প্রশ্নের অভিপ্রায়ের প্রতিক্রিয়ায় কথা বলতেন। সেটাই ছিল তাঁর স্বভাব—আর তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতেন যদি আজকের কথা গতকালের কথার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতো।”
স্বামী বিবেকানন্দের মতামত
১.
“To the accusation from some Hindu that the Swami was eating forbidden food, he retorted—‘If the people of India want me to keep strictly to Hindu diet, please tell them to send me a cook and money enough to keep him.’ 1,129”
যখন কিছু লোক স্বামী বিবেকানন্দের গো-মাংস খাওয়া নিয়ে আপত্তি করল, তিনি বলেছিলেন—ভারতের মানুষ যদি চায় যে আমি হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ খাবার না খাই, তাহলে তাদের বলো আমাকে একজন রাঁধুনি পাঠাতে এবং তার বেতনের ব্যবস্থাও করতে।
কোনো নিরামিষভোজী মহান ব্যক্তি কোনোদিন এমন উদ্ভট দাবি করেননি।
২.
“Orthodox Brahmans regarded with abhorrence the habit of eating animal food. The Swami told them about the habit of beef eating by the Brahmans in Vedic times. (1, 260)”
অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা মাংশাহারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। স্বামীজি বলেছিলেন যে বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন।
৩.
এক সময় এমনও ছিল যে এই ভারতেই কোনো ব্রাহ্মণ মাংস না খেয়ে ব্রাহ্মণ থাকত না। তুমি বেদ পড়ো, তুমি দেখবে—যখন সন্ন্যাসী বা রাজা বাড়িতে আসত তখন কীভাবে ছাগল আর ষাঁড়ের মাথা ধড় থেকে আলাদা করা হতো। (স্বামী বিবেকানন্দের সাথে কথোপকথন—অনুবাদক: স্বামী ব্রহ্মস্বরূপানন্দ)
৪.
“He advocated animal food for the Hindus, if they were to cope at all with the rest of the world and find a place among the great nations. (1, 96)”
তিনি বলেছিলেন—যদি হিন্দুরা সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় এবং বৃহৎ জাতিগুলোর মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে চায়, তবে তাদের জন্য মাংসাশী হওয়া অপরিহার্য।
“So long as vegetable food is not made suitable for human system there is no alternative to meat eating. What we now want is an immense awakening of Rajasik shakti. So, I say, eat large quantities of flesh and meat. (II. 70)”
অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত শাকসবজি-ভিত্তিক খাদ্য মানুষ্যদেহের জন্য যথাযথ রূপে উপযুক্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত মাংসাহার ছাড়া বিকল্প নেই। এখন আমাদের প্রয়োজন প্রবল রজোগুণের জাগরণ। তাই আমি বলি—প্রচুর পরিমাণে মাংস খাও।
৬.
স্বামীজিকে এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন— “মাংস ও মাছ খাওয়া কি যথাযথ এবং প্রয়োজনীয়?” স্বামীজি উত্তর দিয়েছিলেন— “ভালো করে খাও ভাই, এতে যে পাপ হবে তা আমার হবে… বৈদিক ও মনুর ধর্মে মাছ ও মাংস খাওয়ার বিধান রয়েছে… ঘাসপাতা খেয়ে পেটের রোগে ভুগতে থাকা বাবাজিদের দলে দেশ ভরে গেছে… তাই এখন দেশের মানুষকে মাছ–মাংস খাইয়ে কর্মঠ করে তুলতে হবে।”— ‘বিবেকানন্দজিরে সঙ্গ মে’, পৃ. ২৬৭–২৭০
মাংসাহারের বিষয়ে এই ধরনের মত কেবল তারই হতে পারে, যে না বেদ পড়েছে, না মনুস্মৃতি, না ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানে, আর না দেহবিদ্যা বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান রাখে।
ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম
১.
"The vast majority of perverts to Islam and Christianity are perverts by the sword or descendents of those." (II.113) মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে খুব বড় একটি সংখ্যা সেই সব হিন্দুর, যাদের ধর্মান্তর হয়েছে তলোয়ারের জোরে, কিংবা যারা তাদের বংশধর।
২.
"The Mohammadon religion allows Mohammadons to kill all those who are not of their religion… ‘Kill the infidels if they do not accept Islam. They must be put to fire and sword.’" (II.189) অর্থাৎ ইসলাম তাদের হত্যা করতে অনুমতি দেয় যারা তাদের ধর্মের অনুসারী নয়। কোরআনে স্পষ্ট লেখা আছে “যদি কাফিররা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের হত্যা করো। কিংবা তাদের তলোয়ারে হত্যা করতে হবে অথবা আগুনে নিক্ষেপ করতে হবে।”
৩.
"The Mohammadons came upon the people of India always slaughtering and killing. Slaughtering and killing, they over-ran them." (II.151) বাস্তবে ইসলামের খলিফারা এক হাতে কোরআন আর অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে বলত “অথবা ইসলাম গ্রহণ করো, না হলে মৃত্যুকে বরণ করো।”
এত সব হওয়ার পরও স্বামীজি বলেন—
১.
"It is the followers of Islam and Islam alone who look upon and behave towards all mankind as their own soul." (I.254) কেবল ইসলাম অনুসারীরাই এমন মানুষ, যারা সমগ্র মানবজাতিকে নিজের আত্মার মতো মনে করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করে।
২.
"Without the help of Islam the theories of Vedant, however fine and wonderful they may be, are entirely valueless." (I.255) বেদান্তের তত্ত্ব যতই চমৎকার ও আশ্চর্য হোক না কেন, ইসলামের সাহায্য ছাড়া তার কোনো মূল্য নেই।
৩.
"The spirit of democracy and equality in Islam appealed to Narendra’s (Vivekananda’s) mind and he wanted to create a new India with Vedantic brain and Islamic body." (I.79)
ইসলামে গণতন্ত্র ও সাম্যের ভাবনায় নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি এমন এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন যার শরীর হবে ইসলামের এবং মস্তিষ্ক হবে বেদান্তের।
৪.
একদিকে তিনি ইসলামের বাহ্যিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও কথিত সার্বজনীনতার সমালোচনা করে বলেন—
“মুসলমানেরা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বড়াই করে, কিন্তু বাস্তব ভ্রাতৃত্ব থেকে কত দূরে! যারা মুসলমান নয় তারা ভ্রাতৃ-সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না; বরং তাদের গলা কাটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।”
— (ধর্মরহস্য, পৃ. ৪৩)
অন্যদিকে তিনি বলেন—
আমাদের মাতৃভূমির জন্য বিশ্বের দুটি মহান ধর্ম—হিন্দুধর্ম ও ইসলাম—এর সংযোগই একমাত্র কল্যাণকারী হতে পারে।
এর পরে আবার এক জায়গায় তিনি বলেন— “আমি মানবজাতিকে এমন স্থানে নিয়ে যেতে চাই, যেখানে না বেদ থাকবে, না বাইবেল, না কোরান।”
দেশপ্রেম
১. “কিছু লোক আছে, যাদের মস্তিষ্ক পশ্চিমের ভোগবিলাসী আদর্শে বিপথগামী হয়ে গেছে এবং যারা এই ভোগকে—পশ্চিমের এই অভিশাপকে—পুরোপুরি পান করেছে।” তবুও—
২. এপ্রিল ১৮৯৭-এ ভারতীয় এক সাময়িকীর মহিলা সম্পাদককে লেখা চিঠিতে স্বামীजी লিখেছিলেন— “আমার চিরকালই এই বিশ্বাস ছিল যে, পশ্চিমা দেশগুলির সাহায্য না পেলে আমরা উন্নতি করতে সক্ষম হব না।”
৩. যখন তাঁর আধ্যাত্মিক কন্যা এম. ই. নোবেল ভারতের আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন স্বামীজি ২৯ জুলাই ১৮৯৭-এ লিখলেন— “ভারত মহৎ নারী উৎপন্ন করতে পারে না। এ ধরনের নারী তাকে অন্যান্য দেশ থেকে ধার নিতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি তোমার কেল্টিক রক্ত তোমাকে সেই নারী করে তুলেছে, যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন।”
“আমেরিকার মহিলারা সৌন্দর্যে লক্ষ্মীর মতো এবং গুণে সরস্বতীর মতো—তাঁরা যেন স্বয়ং দেবী মূর্তিমান; তাঁদের পূজা করলে সত্যিই সব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। এখানে নারীদের দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত। অত্যন্ত আশ্চর্য নারীরা এরা।”
যে দেশ শাস্ত্রার্থযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ী জগদ্গুরু শংকরাচার্যকে পরাজিতকারী ভারতি দেবীকে জন্ম দিয়েছে, জনকের সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শাস্ত্রার্থের চ্যালেঞ্জ জানানো বাক্পটু গার্গীকে, কালিদাসের সমসাময়িক সারা দেশের পণ্ডিতদের পরাজিতকারী महारানি দুর্গাবতী ও ঝাঁসির মহারানী লক্ষ্মীবাঈকে, রাষ্ট্র রক্ষার জন্য একমাত্র পুত্রকে বলি দেওয়া পন্নাধায়কে, সদ্যবিবাহিতা অনুপম সুন্দরী স্বামীর প্রতি মোহে পতিকে বিপদের মুখে দেখে নিজ হাতে নিজের মস্তক কেটে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদায় নেওয়া হাড়া রানিকে, স্বতীত্ব রক্ষার জন্য জ্বলন্ত চিতায় ও কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগকারী পদ্মিনী প্রভৃতি বীরাঙ্গনাকে এবং লীলাবতীর মতো গণিতবিদদের জন্ম দিয়েছে—সে দেশের বিষয়ে বিবেকানন্দের ভারতবিরোধী উক্তি পড়ে এ-ই বলতে হয়— ঘর থেকে পা, অপর থেকে নাতা; এমন বউ যেন না দেন বিধাতা।
৪. “আমি যেমন ভারতের, তেমনি বিশ্বেরও। কোনো দেশেরই আমার ওপর বিশেষ অধিকার নেই। আমি কি ভারতের দাস?”
৫. ব্রিটিশ সরকারের সন্তুষ্টি বিবেচনায় রেখেই তিনি তাঁর সহযোগীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, “ভাষণ প্রস্তুত করার সময় এমন বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হোক, যাতে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ পায়।”
৬. তাঁর কাছে আমেরিকায় থাকা ভারতের তুলনায় বেশি পছন্দসই ছিল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল— “এখানে আমার খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের সব সুবিধাই রয়েছে। তবে আমি কেন অকৃতজ্ঞ ও মূর্খদের দেশে ফিরে যাব?”
৭. “ইংরেজি শাসনের গুণগান করার কারণেই প্রথমে ইংরেজরাই বিবেকানন্দকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল। এটি ছিল তাঁর রাজভক্তিরই পুরস্কার।”
ম্যাক্সমুলার
ম্যাক্সমুলার সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি লর্ড ম্যাকোলের প্রেরণায় সচেতনভাবেই ভারতীয় সাহিত্যকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর রোপণ করা বিষবৃক্ষের ফলই এই যে, আজকের শিক্ষিত সমাজ নিজস্ব সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে।
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ম্যাক্সমুলারের চেয়ে বড় দেশভক্ত আমাদের দেশে আর কেউ জন্মায়নি। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন—
“The Swami was deeply affected to see Maxmüller’s love for India. He wrote enthusiastically— ‘I wish I had a hundredth part of that love for my motherland. Endowed with an extraordinary and, at the same time, an intensely active mind, he has lived and moved in the world of Indian thought for fifty years or more.’”
ম্যাক্সমুলারের পাণ্ডিত্যের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এমনও বলেছিলেন— “কখনো কখনো আমার এমন ধারণা হয় যে স্বয়ং সায়ণাচার্য নিজেরই ভাষ্যের পুনরুদ্ধার করার জন্য ম্যাক্সমুলারের রূপে জন্ম নিয়েছেন।” (বিবেকানন্দের সংগে, পৃ. ৬১)
স্বামী বিবেকানন্দের ম্যাক্সমুলার-প্রশংসায় যুক্তি ও তর্কের সীমা পার হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বামীজির গুরু শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী ও উপদেশাবলীর ওপর একটি অত্যন্ত সুন্দর গ্রন্থ লিখেছিলেন— “Ramkrishna: His Life and Sayings.”
Maxmuller invited Vivekanand to lunch with him in Oxford on May 28, 1896. The Swami asked Maxmuller— “When are you coming to India? All men there would welcome one who has done so much to place the thought of their ancestors in a true light.” (I, 193)
ম্যাক্সমুলার স্বামী বিবেকানন্দকে ২০ মে ১৮৯৬ সালে ভোজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমুলারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— “আপনি ভারত কবে আসছেন? সেখানে লোকেরা সেই ব্যক্তিরই স্বাগতম জানাবে, যিনি তাদের পূর্বপুরুষদের ভাবনাকে তাদের যথার্থ রূপে উপস্থাপন করতে এত পরিশ্রম করেছেন।”
বাস্তবে, যদি স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থসমূহ ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত পড়েছিলেন, তবে কখনো এ ধরনের কথা বলার দুঃসাহস দেখাতেন না। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী স্থানে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।
বাস্তবে, যদি স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থসমূহ ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত পড়ে থাকতেন, তবে কখনও এ ধরনের কথা বলার সাহস দেখাতেন না। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী স্থানে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। এটি পড়ে বোঝা যাবে যে ম্যাক্সমুলার যা কিছু করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের খ্রিস্টান করে ভারতের দাসত্বের শৃঙ্খলকে দৃঢ় করা। ম্যাক্সমুলারের স্তুতি করে স্বামী বিবেকানন্দ জানি-অজানি নিজেকে এই পাপে অংশগ্রহণকারী বানিয়েছিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার
"Bhagwan Shri Ramkrishna incarnated himself in India."
भगवान् श्रीरामकृष्ण ভারতের মধ্যে অবতার নিয়েছিলেন।Two days before the death of R.K., Narendra was standing by the Master's bedside when a strange thought flashed into his mind. Was the Master truly an incarnation of God ? He said to himself that he would accept Shri R.K.'s divinity if the Master declared himself to be an incarnation. He stood looking intently at the Master's face. Slowly Shri R.K.'s lips parted and he said in a clear voice-"O my Narendra ! Are you still not convinced ? He who in the past was bom as Rama and Krishna, is now in this body as R.K." Thus R.K. put himself in the category of Rama and Krishna who are recognised by the Hindus as Avatars or incarnations of God." (1, 66-67) অর্থাৎ, রাম- কৃষ্ণের মৃত্যুর দুই দিন আগে নরেন্দ্র গুরুর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তার মনে একটি অদ্ভুত চিন্তা জেগে উঠল। গুরুজী কি সত্যিই ঈশ্বরের অবতার? তিনি নিজেকে বললেন, গুরুজী যদি নিজেকে অবতার হিসেবে ঘোষণা করেন, তবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি গভীরভাবে মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঠোঁট খুলল এবং পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন— "ওহ নরেন্দ্র! তুমি কি এখনও নিশ্চিত নয়? যিনি অতীতে রাম ও কৃষ্ণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এখন তিনি এই দেহে রয়েছেন রামকৃষ্ণ হিসেবে।" এভাবে রামকৃষ্ণ নিজেকে সেই রাম ও কৃষ্ণের শাখায় রেখেছিলেন, যাদের হিন্দুরা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। (I, 66-67)
"কৃষ্ণ ঈশ্বরের সকল অবতারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।" (II, 174)
৪ এপ্রিল ১৮৯৬-এ তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে লিখলেন যে রামকৃষ্ণ ঈশ্বর। মানুষ যদি তাকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করে, কোন ক্ষতি নেই।
"যদি আমি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখতাম, তবে আমি শাস্ত্র ও খ্রিস্টান ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতাম যে রামকৃষ্ণ পৃথিবীর সকল নবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (I, 193)
বুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "তিনি জীবিত মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (I, 269)
"সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে দেখা যায় না, যতক্ষণ না তিনি নবী, অবতার বা ঈশ্বরের প্রতিরূপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হন।" (II, 145-46)
২ আগস্ট ১৮৯৬-এ স্বামী বিবেকানন্দ আমমঠের গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি নিজে শিবের দর্শন লাভ করেন। অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি জানিয়েছেন, শুধু এটিই উল্লেখ করে যে তাকে আমমঠের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে যতক্ষণ না তিনি নিজ ইচ্ছায় মৃত্যুর পথে যান। কয়েক দিন ধরে তিনি শুধুই শিবের কথা বলতেন। তিনি বললেন— "মূর্তিটি নিজেই প্রভু।" (I, 271)
চঙ্গিজ খান ঈশ্বরাবতার
One day he spoke of Genghis Khan and declared that he was not a vulgar oppressor. He compared him to Napoleon and alexander, saying that they all wanted to unify the world and it was the same soul that had incarnated itself three times in the hope of bringing about human unity through political conquest. In the same way one soul might have come again and again as Krishna, Buddha and Christ to bring about unity of mankind through religion. (1, 266-67) অর্থাৎ—একদিন স্বামীজি চঙ্গিজ খানের বিষয়ে বলেছেন যে তিনি কোনো সন্ত্রাসী বা অত্যাচারী ছিলেন না। নেপোলিয়ন ও সিকন্দরের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন যে এরা সকলেই পৃথিবীকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। একই আত্মা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে মানবজাতিকে একতার সূত্রে বাঁধার উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রকাশ পেয়েছিল। আশায় তিনবার অবতার গ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে এক এবং অভিন্ন পরমাত্মা ধর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ঈসা রূপে এসেছে কি না—এই বিষয়ে কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র এটুকু যে বহুরুপী হলেও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পৃথিবীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি—এই পৃথিবীতে (স্বামী বিবেকানন্দের মতে) তাঁর নিজস্ব রূপই ছিল।
এভাবে আমরা দেখি যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা না যুক্তিনির্ভর এবং না কোনো সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যযুক্ত, না হিন্দুত্বের প্রতি কোনো নিষ্ঠা আছে, না ভারতীয়তার প্রতি কোনো আবেগ। যেমন তার গুরু আত্মকেন্দ্রিত ছিলেন, তেমনই বিবেকানন্দ গুরু-কেন্দ্রিত ছিলেন। এর ফলস্বরূপ, তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৮৬ সালে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সক্ষম হলো যে তাদের হিন্দু ধরা হবে না। তার যুক্তি ছিল, "হিন্দু সেই হয় যিনি বেদ মানেন। আমরা বেদ মানি না, আমাদের জন্য বেদ, বাইবেল, কুরআন সব সমান, তাই আমরা হিন্দু নই।"
সর সৈয়দ আহমদ খান – পাঞ্জাবের হিন্দুদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সর সৈয়দ বলেছিলেন—
"The word 'Hindu' that you have used for yourselves is, in my opinion, not correct because that is not in my view the name of a religion. Rather, every inhabitant of Hindustan can call himself a Hindu. I am, therefore sorry that you do not regard me as a Hindu, though I too am an inhabitant of Hindustan."
অর্থাৎ, আপনি আপনার জন্য ‘হিন্দু’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তা ঠিক নয়। হিন্দু শব্দ কোনো সম্প্রদায় বা ধর্মের পরিচায়ক নয়। হিন্দুস্তানে থাকা প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে হিন্দু বলতে পারে। আমাকে দুঃখ হচ্ছে যে আপনি আমাকে হিন্দু মনে করেন না, যদিও আমি হিন্দুস্তানের অধিবাসী।
আজ কে বিশ্বাস করবে যে এই শব্দগুলি কখনও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সর সৈয়দ আহমদ খানের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কয়েকদিন পরে সর সৈয়দ লিখেছিলেন—
"I object to every Congress, in every shape or form, whatsoever, which regards India as one nation."
অর্থাৎ, আমি কোনোভাবেই হিন্দুস্তানকে এক রাষ্ট্র হিসেবে মানতে প্রস্তুত নই। এই কথাগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে ১৬৪৭ সালে ভারত বিভাজনের জন্য দ্বি-রাষ্ট্র (Two Nation Theory) তত্ত্বের প্রবর্তক ছিলেন সর সৈয়দ আহমদ খান, নয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটীর মতো বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ হয়েছিল মুঃডান আংলো-ওরিয়েন্টাল (M.A.O. College) হিসেবে ১৮৭৫ সালে সর সৈয়দ আহমদ খানের দ্বারা।
১৮৮৩ সালে ব্যাঙ্ক (Heck) নামে একজন ইংরেজকে এই কলেজে প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ পর্যন্ত তিনি ওই পদে থাকেন। এই ১৬ বছরের মধ্যে সর সৈয়দ আহমদ খান ও তার কলেজ সম্পূর্ণভাবে মি. ব্যাঙ্কের প্রভাবের মধ্যে ছিল। ফলস্বরূপ, তারা উভয়ই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
ইংল্যান্ড থেকে ভারত যাত্রার আগে মি. ব্যাঙ্ক সেখানে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় ভারত জন্য প্রস্তাবিত সংসদীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন—
"The Muslims will be under the majority opinion of the Hindus, a thing which will be highly resisted by the Muslims and which, I am sure, they will not accept quietly."
অতএব, মুসলমানদের হিন্দুদের বিরোধে উসকানি দিয়ে, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই দেশে প্রবেশ করেছিলেন এবং যতদিন এখানে ছিলেন, এই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। এর তিন বছর পর, ১৮৮৮ সালে, মি. ব্যাঙ্কের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সর সৈয়দ Patriotic Association প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বিশ্বাস করানো যে ভারতের মুসলমানরা স্বরাজের জন্য চলমান আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে নেই।
সन् ১৮৬৫ সালে মি. বেক ইংল্যান্ডে একটি বক্তৃতা দেন, যার সারসংক্ষেপ আলিগড় কলেজের ম্যাগাজিনে এই কথাগুলিতে ছাপা হয়েছিল—
"A friendship between the English people and Muslims was possible but not between the Muslims and followers of other religiom."
অর্থাৎ ইংরেজদের সঙ্গে তো মুসলমানদের মিল হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো মতাবলম্বীর সঙ্গে নয়। এই ধরনের মানসিকতা থাকলে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবনা এবং দেশপ্রেমের ধারণা মুসলমানদের মধ্যে কীভাবে স্থায়ী হতে পারে?
সन् ১৮৬৮ সালে সর সৈয়দের এবং ১৮৬৬ সালে বেকের মৃত্যু হওয়ার পর বেকের উত্তরসূরি থিওডোর মরিসন বেকের কাজ চালিয়ে যান। তিনি মুসলিম ছাত্রদের ক্রমাগত উসকানি দিতেন যে ভারতে গণতন্ত্রের অর্থ হবে—সংখ্যায় কম মুসলমানদেরকে কাঠুরে, ঘাসকাটা শ্রমিক এবং পানি বহনকারী ঝিঁভার বানিয়ে দেওয়া।
মরিসনের পর কলেজের প্রিন্সিপাল পদে আর্চিবাল্ড নামে এক ইংরেজের নিয়োগ হয়। সেই সময় বঙ্গভঙ্গের কারণে মানুষের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ছিল। তা শান্ত করার জন্য ইংরেজ সরকার শাসনব্যবস্থায় কিছু সংস্কার করতে চাইছিল। এই বিষয়টির আভাস পাওয়া মাত্রই আর্চিবাল্ড তৎক্ষণাৎ শিমলায় পৌঁছে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে ১ অক্টোবর ১৯০৬ সালে সর আগাখানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। ব্রিটিশ সরকার ‘Divide and rule’ নীতির অধীনে আগেই এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় ভাইসরয়ের স্ত্রী লেডি মিন্টো-র উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে এক কর্মকর্তা লিখেছিলেন—
A big thing has happened today. A work of statesmenship that will affect India and Indian history for a long time. It is nothing less than the pulling out of 63 million people from joining the ranks of sedicious opposition."
এইভাবে ৬ কোটি মুসলমানকে জাতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে হিন্দু ও হিন্দুস্তানের উভয়েরই কট্টর বিরোধী বানানো হলো। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত মুসলমানরা ১৯২০ সালের পরে যা কিছু করেছে, তারই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারতের বিভাজন ঘটেছে।
এমনই ছিলেন আধুনিক ভারতের নির্মাতা ও সমাজসংশোধকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত সর সৈয়দ আহমদ খান। ইংরেজ কৃতঘ্ন প্রমাণিত হয়নি। মার্চ ১৯৪৭ সালে ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসার আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার কট্টর বিরোধী চার্চিলের সাথে দেখা করতে যান। ইংল্যান্ডের সহায়তা করার জন্য মুসলমানদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মরণ করে চার্চিল মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন—
"I am not going to tell you how to do it. But I will tell you one thing-whatever arrangements you make you must see that you don't harm a hair on the head of a single Muslim. They are the people who have been our friends and they are the people Hindus are now going to oppress. So you must take steps that they can't do it." (Indian Expeess Magazine. April 4. 1982)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন চার্চিলকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন এবং ভারতের বিভাজন এমনভাবে সম্পন্ন করেন যে মুসলমানরা ভারতভূমির একটি অংশ কেটে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন দেশ লাভ করে। এবং অবশিষ্ট ভারতে তাদের অধিকার আগের মতোই রয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আজও ঠিক তেমনি রয়েছে, যেমনটি ১৯৪৭ সালের আগে ছিল।
ইসাইধর্মের আক্রমণ—সন ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতের উপর ইংরেজদের শাসন ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান মি. মেঙ্গলস ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তার বক্তব্যে বলেছিলেন—
"Providence has entrusted the entensive empire of Hindustan to England in order that the banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Everyone must exert all his strengths that there will be no dilatoriness on any account in continuing in the country the grand work of making all Indians Christions."
অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছায় হিন্দুস্তানের বিশাল সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে দেওয়া হয়েছে যাতে খ্রিস্টের পতাকা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়ীভাবে লহরাতে পারে। প্রতিটি খ্রিস্টানকে অবশ্য কর্তব্য পালন করতে হবে যাতে সমস্ত ভারতীয়কে অবিলম্বে খ্রিস্টান করার মহান কাজে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে মনোনিবেশ করা যায়।
ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ (Mutiny 1857) শেষ হওয়ার দুই বছর পরে ইংল্যান্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টন ঘোষণা করেছিলেন—
"It is not only our duty but in our own interest to promote the diffusion of Christianity as far as possible throughout the length and breadth of India." (Christianity and Government of India by Mayhew, page 194)
অর্থাৎ এটি আমাদের কর্তব্যই নয়, বরং আমাদের স্বার্থও এইতে নিহিত যে ভারতের জায়গা জুড়ে ইসাইধর্মের যতটা সম্ভব বিস্তার ঘটুক।
বোম্বের গভর্নর লর্ড রি ১৮৭৬ সালে ইসাই মিশনারিদের একটি প্রতিনিধি দলের সামনে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে উপস্থাপন করে বলেছিলেন—
"They are doing in India more than all those civilians, soldiers, judges and governors your highness has met."
অর্থাৎ যত কাজ আপনার সৈন্য, বিচারক, গভর্নর এবং অন্যান্য কর্মকর্তা করছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ তারা (মিশনারিরা) করছেন।
বিদেশী শাসন এবং ইসাইধর্ম চোলি-দামনের মতো একে অপরের সাথে যুক্ত ছিল। আমাদের দাসত্বের শিকল আরও মজবুত করতে খ্রিস্টানরা ইংরেজদের সহযোগিতা করেছে। আগ্রাসক হিসেবে আসার আগে ইসাই মিশনারি পাঠানো হতো। মিশনারিদের মাধ্যমে মাঠ প্রস্তুত হওয়ার পর সেনারা অবতরণ করত। সেনাশক্তির দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠার পর সরকার দেশের খ্রিস্টানীকরণে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা প্রদান করত। মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে, মিশনারিদের করা সেবাকর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অসহায় মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের খ্রিস্টান বানানো। আজও কেরল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, আসাম প্রভৃতি স্থানে যেখানে খ্রিস্টানদের প্রভাব আছে, সেখানে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম জোরদার।
মুসলমান আগ্রাসক হিসেবে এই দেশে আসে এবং প্রায় সাত শতাব্দী শাসন চালায়। এটি ঠিক যে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেশের বাসিন্দা, কিন্তু তারা কখনও এই দেশে শাসন করেনি। এখানে শাসনকারী—গুলাম, তুঘলক, খেলজি, লোধি, মোগল প্রভৃতি—সব বিদেশী ছিলেন। তথাপি তাদের বিদেশী হওয়ার কারণে এই দেশের মুসলমানরা কখনও তাদের বিরোধিতা করেনি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এ কথার প্রমাণ দেয় যে মুসলমানদের এই মনোভাব আজও আগের মতোই রয়ে গেছে। সত্যি কথা হলো, সবচেয়ে कट्टर দেশপ্রেমিকও কলমা পড়লে দেশদ্রোহী হয়ে যায়।
সবচেয়ে বড় (জাতীয়তাবাদী ?) মুসলমানের হৃদয়ে বিদেশী আগ্রাসক মাহমুদ গজনভী, মুহাম্মদ গৌরী বা বাবরের প্রতি যে শ্রদ্ধা রয়েছে, তা মহারানা প্রতাপ, শিবাজি, রাম বা কৃষ্ণের জন্য নেই।
সন ১৯০১-এ জনসংখ্যার সভাপতিত্বকারী (Census Commissioner) মি. বর্ণ (Bem) লিখেছিলেন—
"Dayanand feared Islam and Christianity because he considered that the adoption and adaptation of any foreign creed would endanger the national feelings he wished to foster."
ঋষি দয়ানন্দ আশঙ্কা করতেন যে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মতো বিদেশী মত গ্রহণ করলে দেশের মানুষের জাতীয় অনুভূতিতে, যা তিনি জাগ্রত করতে চাইতেন, ক্ষতি হবে।
সন ১৯১১-এর জনসংখ্যার সভাপতিত্বকারী মি. ব্লান্ট লিখেছিলেন—
"The Arya Samaj doctrine and Arya Education alike sing the glories of ancient India and by so doing arouse a feeling of national pride in its disciples who are made to feel that their country's history is not a tale of humiliation." (Census Report of 1911, Vol. XV, Part I, Chap. IV, page 135)
অর্থাৎ আর্যসমাজের নীতি এবং শিক্ষা উভয়ই ভারতীয় প্রাচীন গৌরবের গান গায় এবং এভাবে তাদের অনুসারীদের মধ্যে জাতীয় গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমাদের দেশের ইতিহাস লাঞ্ছনার গল্প নয়।
ভারতের অস্তিত্বে আঘাত
এর বিরোধী মানসিকতায় ভারতীয়দের আচ্ছন্ন করে রাখার জন্য ইংরেজদের অভিযান চলছিল। লর্ড ম্যাকলে তাঁর বন্ধু মিস্টার রাউসকে লিখেছিলেন— “এখন আর শুধু নামকাওয়াস্তে নয়, আমাদের সত্যিই নবাব হতে হবে—আর সেটা কোনো আড়াল রেখে নয়, একেবারে খোলাখুলি।” (মিল্স কৃত ভারতীয় ইতিহাস, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৩২)। এই পরিকল্পনার অন্তর্গতভাবেই ১৮৬৬ সালে আর্থার এ. ম্যাকডোনাল্ড ‘সংস্কৃত সাহিত্যর ইতিহাস’ রচনা করেন। খ্রিস্টধর্মের প্রচারের মাধ্যমে ভারতের উদ্ধারের কথা বলার আগে এটাই প্রমাণ করা জরুরি ছিল যে ভারতের মানুষ আদিকাল থেকেই বর্বর ও অসভ্য। কারণ? যদি তাদের আগে থেকেই সভ্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে তাদের সভ্য করার দাবিই বা কীভাবে করা যাবে? ম্যাকডোনাল্ড রচিত গ্রন্থে যা লেখা হয়েছে তার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো—
“ইতিহাসপূর্ব কালে যেসব আর্যরা ভারত জয় করেছিল তারা নিজেরাও প্রাচীন কালে অন্যদের শিকার হতে হতে এসেছে (পৃ. ৪০৮); ভারতে ইতিহাসের অস্তিত্বই নেই। তারা কোনোদিন ইতিহাস লিখেইনি, কারণ কোনো ঐতিহাসিক কর্মই তারা কোনোদিন করেনি (পৃ. ১০–১১), ইরান ভারতকে মূল্যবান উপঢৌকন দিত (পৃ. ৪০৬)।”
এইভাবে ভারত চিরকাল পরাজিত হয়ে আসছে—এটাই হলো সেই ইতিহাসের সারসঙ্কলন, যা মিথ্যা জেনেও আমরা মানসিক দাসত্বের কারণে “আঙ্গলবাক্যং প্রমাণম্” বলে মেনে নিয়েছি।
বাস্তবে এই মতের প্রবর্তক ছিলেন ম্যাক্সমুলার। নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জোর দিয়ে বলেন যে পানিনির সময় পর্যন্ত ভারতীয়রা লেখা-পড়া পর্যন্ত জানত না। তাঁর গ্রন্থ ‘প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যর ইতিহাস’-এ তিনি নিজের পক্ষপাত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বৈদিক সভ্যতার এমন উঁচু শিখরে পৌঁছানো এক সমাজ লেখালেখির সঙ্গে অপরিচিত ছিল—এ কথা কল্পনা করাই অসম্ভব। বস্তুত, বেদগুলোর ভাষা, কাব্যরূপ, বিষয়বস্তু ও চিন্তার গভীরতা দেখে কে মানতে পারে যে নিরক্ষর লোকেরা এগুলোর রচয়িতা ছিল? ১৭৮৬ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের মঞ্চ থেকে দেওয়া বক্তৃতায় স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেছিলেন— “সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যতই হোক না কেন, তার গঠন প্রকৃতই বিস্ময়কর। তা গ্রিকের চেয়ে অধিক নির্ভুল, ল্যাটিনের চেয়ে অধিক সক্ষম এবং এদের যেকোনোটির তুলনায় আরও বেশি পরিশীলিত।” সংস্কৃত সম্বন্ধে উক্ত এই মতামতকে হঠাৎ আবেগজনিত উচ্ছ্বাস বলা যায় না। ভাষার বিকাশ শূন্যে হয় না। তা মানবসমাজের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, চিন্তা ও প্রত্যয়ের—তার অনুভূতি, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের, তার ভৌত প্রয়োজন, নৈতিক মূল্যবোধ, চেতনা এবং সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার যথার্থ প্রতিফলন। এটি একটি সর্বজনীন ও অখণ্ড নিয়ম। বৈদিক ভাষার এই সমৃদ্ধি প্রমাণ করে যে বৈদিক যুগের মানুষরা অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার নির্মাতা ছিলেন। তাদের স্রেফ পশুপালক যাযাবর হিসেবে উপস্থাপন করা সত্যের পরিপন্থী।
ম্যাক্সমুলারের মতে বেদকে শ্রুতি বলা হয়েছে, কারণ এর সংক্রমণ ও প্রসার শ্রুতি-পরম্পরায় ঘটেছে। এটি নাকি নির্দেশ করে যে বৈদিক যুগে লেখার প্রচলন ছিল না। কিন্তু তাঁর এই মতানুযায়ী তো শুধু বেদই নয়, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি পর্যন্ত এবং এমনকি পানিনির সময় পর্যন্তও লেখালেখির প্রচলন ছিল না। তাহলে এগুলোর সংক্রমণ ও প্রসারও কেবল শ্রুতি-পরম্পরায় হয়েছিল—এটাই তো প্রমাণিত হয়। তবে বেদের মতো এগুলোর নামও শ্রুতি কেন নয়? যদি ম্যাক্সমুলার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেন তবে ‘শ্রুতি’ শব্দের পেছনে অন্য কারণ দেখতে পেতেন। সত্য কথা হলো—যদি বৈদিক ভারত লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর এই বক্তব্য—প্রাচীন কালে ভারতীয়দের কোনো ইতিহাস ছিল না—আপনা থেকেই মিথ্যা হয়ে যায়। তখন তাঁর তৈরি করা ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্যতাই বা কোথায় থাকে? তাই তিনি এমন প্রতিটি প্রমাণকে অস্বীকার করে গেছেন, যেগুলো ওই যুগে লেখালেখির প্রচলনকে সমর্থন করতে পারত।
রেপসনের মতে— “পাণিনির যুগ-উদ্বর্তক গ্রন্থে বর্ণিত উচ্চ ও বিশুদ্ধ ভাষার তুলনায় বৈদিক বাঙ্গময়ের ভাষা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী। তবে খুব বেশি প্রাচীন হওয়া আবশ্যক নয়। সূত্রগ্রন্থগুলো, যা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলোর উত্তরবর্তী, তাতেও এমন এক স্বচ্ছন্দতা দেখা যায়, যা পাণিনির পূর্ণ প্রভাবের পর সহজে বোঝা যায় না।”
এই লেখায় এতটুকু সত্য আছে যে সূত্রগ্রন্থগুলি পানিনি-পূর্ববর্তী, কিন্তু রেপসন পানিনির কালের ঠিক ধারণা রাখেন না। তিনি পানিনিকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালের মনে করেন, অথচ পানিনির প্রকৃত সময় বিক্রমের প্রায় ২৬৫০ বছর পূর্বে। বহু সূত্রগ্রন্থ তাঁরও বহু বছর আগে রচিত। পানিনি নিজেই তাদের উল্লেখ করেন।
Jesperson : Language, its Nature, Origin and Development.
“The language also of the Vedic literature is definitely anterior, though not necessarily much anterior, to the classical speach as prescribed in the epoch-making work of Panini; even the Sutras which are undoubtedly later than the Brahmanas, show a freedom which is hardly conceivable after the period of the influence of Panini.” — Cambridge History of India, p. 113
এটি হল— ‘পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু’ (অষ্টা० ৪।৭।১০৫)—অর্থাৎ পাণিনির পূর্বে প্রাচীন এবং তাঁর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন – উভয় ধরনের সূত্রগ্রন্থ রচিত হয়ে গিয়েছিল। পৈডকীকল্প এবং আরুণপরাজী (আরুণ পারাশরী) প্রভৃতি নবীন সূত্রগ্রন্থ ছিল এবং আশ্মস্থ্যকল্প অপেক্ষাকৃত নবীন সূত্রগ্রন্থ ছিল, কিন্তু এগুলি সবই পাণিনির পূর্বকালের।
এর থেকেও বেশি, পাণিনির পরবর্তী সূত্র (৪।৩।১০৬)-এর মতে শৌনকের শিক্ষা, শৌনকের বृहদেবতা, শৌনকের প্রাতিসাখ্য ইত্যাদিও রচিত হয়ে গিয়েছিল। পাণিনির পূর্বে বহু ব্যাকরণকার হয়েছিলেন, যাদের স্মরণ পাণিনি করেছেন। এত অধিক ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনার পূর্বে অন্যান্য সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। তাতে চিকিৎসা, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। এত বিশাল সাহিত্য কেবল মৌখিকভাবে রচিত, প্রচারিত ও সংরক্ষিত ছিল—এই কথা সম্পূর্ণরূপে উপহাসযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি মহাভারত যুদ্ধের ৩০০ বছর পর পর্যন্ত অথবা বিক্রম থেকে ৩০০০ বছর পূর্বেই রচিত হয়ে গিয়েছিল, অতএব র্যাপসনের অন্যত্র (পৃ. ৬০) এই লেখা যে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সালে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল—এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।
সূত্র এবং প্রাচীন স্মৃতির ভাষা মহাভারতের সদৃশ। মহাভারত-সদৃশ ভাষা ইয়াস্কীয় নিরুক্ততেও আছে, অতএব যদি ইয়াস্ক ও সূত্রকার ঋষিরা পাণিনির পূর্বেকার হন, তবে মহাভারতও পাণিনির পূর্বেকার। মহাভারত (পুনা-সংস্করণ)-এ যদিও গবেষণার অবকাশ আছে, তথাপি তাতে পাণিনির পূর্বেকার এবং সূত্র-সদৃশ প্রয়োগ বেশি। মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত লেখার জন্য গণেশের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। গণেশ তাঁর সময়ের অশুলিপিতে লেখায় পারঙ্গম দক্ষ লেখক (stenographer) ছিলেন। তিনি কিছু নির্দিষ্ট শর্তে মহাভারত লেখা গ্রহণ করেছিলেন।
বেদ, ব্রাহ্মণ, দর্শন, উপনিষদ, ব্যাকরণ-গ্রন্থ ইত্যাদির বিভাগ করতে গিয়ে মণ্ডল, সূক্ত, কাণ্ড, অধ্যায়, প্রপাঠক, পাদ, খণ্ড প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো কেবল লিখিত গ্রন্থেরই বিভাগ-উপবিভাগ হতে পারে। অন্য কোনোভাবে এই নামগুলির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মৌখিক রূপে এক দিনের পাঠ বিভিন্ন শিক্ষক, পাঠশালা ও প্রজন্মে একইরকম হয়ে থাকা, এবং তাও যখন তাদের আকার ভিন্ন, লিখিত রচনার অভাবে অসম্ভব। শতপথ ব্রাহ্মণ ও কाठক সংহিতা ইত্যাদিতে বাণীকে লিপিবদ্ধ করার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের এক স্থানে কোষ বা পেটিকা থেকে বেদগ্রন্থ বের করে পাঠ করা এবং পরে তা সাবধানে আবার তাতে রেখে দেওয়ার উল্লেখ নিম্নলিখিত শব্দে পাওয়া যায়—
यस्मात् कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्न्तरव दध्म एनम् । — অথর্ব० ১৬।৭।২৩১
অর্থাৎ যেমনভাবে পেটি থেকে বেদের গ্রন্থ তোলা হয় এবং পড়া শেষ হলে আবার তাতেই রেখে দেওয়া হয়, তেমনভাবেই যাঁর নিকট থেকে আমরা বেদময় জ্ঞান লাভ করি, পুনরায় তাঁরই মধ্যে তাকে অবস্থিত পাই। কোষ অর্থাৎ পেটিকায় বৃহৎ আকৃতির গ্রন্থ সংরক্ষণ করার প্রাচীন প্রচলন ছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই পিটক ও কোষ বৃহৎ আকৃতির গ্রন্থের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। বেদের এই উক্তি কেবল লিখিত বা মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রেই অর্থবহ হতে পারে।
অথর্ববেদ (৭।৫০।৫)-এ ‘संलिखितम्’ শব্দ পাঠিত হয়েছে। ‘लिख’ শব্দের অর্থ— ‘অক্ষরের বিন্যাস’। সুতরাং ‘संलिखितम्’-এর অর্থ হলো ‘লেখা হয়েছে’ বা ‘লেখা-হওয়া’। ‘सम्’ উপসর্গ যুক্ত হলে এর অর্থ হয় ভালোভাবে লেখা বা শিলায় ইত্যাদিতে খোদাই করা থাকতেও পারে। এইভাবে বেদে লেখার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিও গুরুত্বপূর্ণ— ‘উত ত্বঃ পশ্যন্ম্ ন দদর্শ বাদম্ উত ত্বঃ শৃণ্যন্ম্ ন শৃণোত্যেনাম্’ (১০/৭১/৪) অর্থাৎ কেউ বাক্কে দেখতে থাকা সত্ত্বেও দেখে না এবং কেউ বাক্কে শুনতে থাকা সত্ত্বেও শোনে না। বাক্কে ‘দেখা’ এবং ‘শোনা’ আলাদা আলাদা ক্রিয়া। দেখা চোখের কাজ এবং শোনা কানের। বাক্ তখনই দেখা যেতে পারে যখন তা লিখিত রূপে থাকে।
পাণিনি ‘লোপ’-এর লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন— ‘অদর্শনং লোপঃ’ (অষ্টা. ১/১/৫৬)— যা কোনো বস্তু থেকে থেকে না থাকে, চোখে না পড়ে, তাকে ‘অদর্শন’ বলা হয়; অর্থাৎ বিদ্যমানের অদর্শনকেই লোপ-সংজ্ঞা বলা হয়। যা কোনোদিন দৃশ্যই ছিল না, তাকে ‘অদর্শন’ বলা যায় না। যদি ভাষা লিপি-রূপে না থেকে কেবল শ্রুতি-রূপেই থাকত, তবে ‘অদর্শন লোপঃ’-এর স্থলে ‘অশ্রবণ লোপঃ’ বলা হতো এবং ‘বর্ণবিনাশ’ না বলে ‘ধ্বনিবিনাশ’ বলা হতো।
পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান অনুযায়ী ব্রাহ্মী লিপির নমুনা মৌর্য যুগ থেকে পাওয়া গেছে বলা হয়, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে ওই লিপির আবিষ্কার সেই সময়েই হয়েছিল। যদি মৌর্য রাজাদের আদেশ খোদাই করার জন্যই প্রথম ওই লিপির ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে তার নাম ব্রাহ্মী কেন হলো? ‘ব্রহ্ম’ শব্দের প্রসঙ্গপ্রাপ্ত अर्थ হলো বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য যে লিপির ব্যবহার করা হয়েছে, তাকেই ব্রাহ্মী লিপি বলা যেতে পারে। দেবনাগরীরই প্রাচীন নাম ব্রাহ্মী, কারণ এর সর্বপ্রথম ব্যবহার ব্রহ্মাদেব করেছিলেন। লিপিজ্ঞান-সম্পর্কিত ইঙ্গিত ঋগ্বেদের ‘উত ত্যঃ পশ্যন্ন্ ন দদর্শ বাথম্’ (১০/৭১/৪) মন্ত্রে ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। শ্রবণের প্রতিপক্ষে বাক্-দর্শনই সম্ভব। এই ভিত্তিতেই ব্রহ্মা ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টি করেন। স্বামী দয়ানন্দের মতে, অক্ষর, কালি ইত্যাদি দিয়ে লেখার প্রথা লোকেরা ইক্ষ্বাকুর সময় প্রচলনে আনে, কারণ ইক্ষ্বাকুর সময়ে বেদ কণ্ঠস্থ রাখার প্রথার হ্রাস ঘটতে শুরু করেছিল। যে লিপিতে অক্ষর লেখা হতো, তার নাম ছিল দেবনাগরী।
পুরাণ-সাহিত্য এবং পরম্পরায় জীবাত্মাদের শুভাশুভ কর্মের হিসাব রাখার জন্য যমরাজের দপ্তরে চিত্রগুপ্তের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইরানেও—যেদিক থেকে আর্যদের ভারতে আসার সম্ভাবনা ধরা হয়—স্বর্গে কর্মের হিসাব রাখার বিষয়ক লেখাকে Hartsfield-এর মতে প্রাচীন ইরানিদের মধ্যে লেখার প্রचलনের প্রমাণ বলে গণ্য করা হয়েছে। আর্যরা ইরান থেকে ভারতে এসেছে ধরে নেওয়া হোক, বা ভারত থেকে ইরানে গেছে—দু’টি অবস্থাতেই ভারতীয় আর্যদের লেখন-কলা থেকে অনভিজ্ঞ ভাবার কোনো অর্থ হয় না।
ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, রাজতরঙ্গিণী, নেপাল-রাজবংশাবলি, কলিযুগ-রাজবৃত্তান্ত, অসংখ্য নাটক এবং চাম্পূগ্রন্থাদি সবই ইতিহাসের উপজীব্য। এগুলো ছাড়া কেবল অপূর্ণ শিলালিপি, মুদ্রা, মূর্তি এবং বিদেশি ভ্রমণবৃত্তান্তের ভরসায় Oxford-এর পণ্ডিতরাও তাদের ‘India’s History’ রচনা করতে পারতেন না। ভারতের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ महामहोপাধ্যায় ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (যাঁর শিক্ষা ইংল্যান্ডে হয়েছিল) লিখেছেন—
১. ন দর্শনম্ অদর্শনম্, নত্রতত্পুরুষঃ। যদ্ ভূত্বা ন ভবতি তদ্ অদর্শনম্ = অনুপলব্ধঃ, বর্ণনাশঃ তস্য লোপ ইতি সংজ্ঞা ভবতি। অর্থত্ প্রবক্ত্যাদর্শন লোপসংজ্ঞকং ভবতি।
২. Hartsfield – “Zoroast and His World”, 1947, p. 307
ভারতে ইতিহাস-লেখন
অলবেরুনি লিখেছিলেন— “দুর্ভাগ্যবশত হিন্দুরা ঘটনাবলির ঐতিহাসিক ক্রমের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয় না। তারা নিজেদের রাজাদের রাজ্যারোহণের কালক্রমকে উপেক্ষা করে।” প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার প্রফেসর ভাণ্ডারকর অলবেরুনির এই উক্তির প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে, অলবেরুনির এই বক্তব্য সেই সময়ের জন্য কিছুটা সত্য হতে পারে, যখন সে ভারতে এসেছিল এবং যখন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অধোগতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল; কিন্তু এ কথা বলা যে মধ্যযুগের পূর্বে ভারতীয়দের ইতিহাসবোধই ছিল না— তা বাস্তব তথ্যের পরিপন্থী হবে। ভারতীয়রা ইতিহাস লেখেইনি— এ কথা নিছক মিথ্যা। প্রাচীনকালে “ইতিহাস” এবং “পুরাণ”— উভয় শব্দ থেকেই ইতিহাসবোধ বোঝানো হত। অথর্ববেদ (১৫/৬/১১–১২)-এ লেখা আছে— মন্ত্র ১০-১২ মহর্ষিদয়ানন্দকৃত ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা বেদসংজ্ঞাবিচার পৃষ্ঠা ৮২ এ উদ্ধৃত রয়েছে
तमि॑तिहा॒सश्च॑पुरा॒णं च॒ गाथा॑श्च नाराशं॒सीश्चा॑नु॒व्यचलन् ॥
“তমিৎিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্যানুষ্ঠ্যচলন।”
इ॑तिहा॒सस्य॑ च॒वै स पु॑रा॒णस्य॑ च॒ गाथा॑नां च नाराशं॒सीनां॑ च प्रि॒यं धाम॑ भवति॒ य ए॒वं वेद॑॥
“ইতিহাসস্য চ বৈ স পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারাশংসীনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ।”
(সঃ) সেই [বিদ্বান্] পুরুষ (বৈ) নিশ্চিতরূপে (ইতিহাসস্য) ইতিহাসের (চ চ) এবং (পুরাণস্য) পুরাণের (চ) এবং (গাথানাম্) গাথা সমূহের (চ) এবং (নারাশংসীনাম্) নারাশংসীদের [বীর নরদের গুণকথার] (প্রিয়ম্) প্রিয় (ধাম) ধাম [ঘর] (ভবতি) হয়, (যঃ) যে [বিদ্বান্] (এবম্) এমন ব্যাপক [ব্রাত্য পরমাত্মাকে] (বেদ) জানে ॥১২॥
অমরকোষে ইতিহাসের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘পুরাবৃত্ত’ লেখা আছে।
ইতি–হ–আস = ঠিক এমনই ঘটেছিল। পুরা–বৃত্তম্ = যা পূর্বে ঘটেছে।
এইভাবে সাধারণত উভয় শব্দ থেকেই অতীত ঘটনার সংগ্রহকে ইতিহাস বা পুরাণ বলে গণ্য করা হয়। যাস্কের নিরুক্তে পাওয়া ‘ইত্যৈতিহাসিকাঃ’— অর্থাৎ “এভাবে ইতিহাস-মান্যকারীরা বলেন”— এই বাক্য থেকেও ঐ সময় ইতিহাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তবে ভারতীয় এবং অন্যান্য ইতিহাস-লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভারতের মানুষের মতে ইতিহাসের উদ্দেশ্য এই—
“ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তম্ ইতিহাসং প্রচক্ষতে।”
সৃষ্টি (সর্গ), প্রলয়-সৃষ্টি (প্রতিসর্গ), বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত— এই লক্ষণযুক্ত গ্রন্থকে “পুরাণ” বলা হয়। একইভাবে যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, গার্গী, ম্যৈত্রেয়ী ইত্যাদি কাহিনীর নাম “গাথা”। বংশাবলি প্রস্তুতকারীরা “পুরাবিদ্” নামে পরিচিত ছিলেন। কৌটিল্য (চাণক্য)-এর সময়ে ইতিহাসের গুরুত্ব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কৌটিল্য রাজাকে প্রতিদিন মধ্যাহ্ন-পরবর্তী সময়ে ইতিহাস শ্রবণ বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তাঁর মতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র— সবই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মশাস্ত্র (Law) এবং অর্থশাস্ত্র (Economics) একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কৌটিল্য এগুলিকে ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। প্রফেসর ভাণ্ডারকর বলেন— এটি কি বিস্ময়কর নয় যে, কৌটিল্য সেই সময়ে রাজপুত্র ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য এ বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলক করেছিল?
“উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমার ইউরোপীয় বন্ধুরা আমাকে বলতেন যে ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য Ramayana, Mahabharata এবং Puranas-কে হাত দিও না। তাদের লক্ষ্য ছিল কেবল মুদ্রা, শিলালিপি, বিদেশিদের ভ্রমণ-বিবরণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদির সাহায্যে ইতিহাস ও কালক্রম স্থির করা। কিন্তু এখন Mr. Pargiter এবং Mr. Jayaswal পুরাণ থেকেই কালক্রম আবিষ্কার করেছেন। Pargiter-এর শেষ কাজ পুরাণের গুরুত্ব প্রকাশ করে। অর্থাৎ আমাদের পুরাণসমূহের মতো উৎস এবং পরম্পরা, যেগুলো একসময়ে অবিশ্বাস্য বলে মনে করা হয়েছিল, তাদের গুরুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”
৯. Unfortunately the Hindus do not pay much attention to the historical order of things. They are very careless in relating the chronological succession of their Kings.
২. সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।
৩. ‘Journal of Bihar Oriental Studies’, গ্রন্থ ১৪, পৃ. ৩২৫–২৬
ভারতের ইতিহাস-সংক্রান্ত সংকলন
ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ (Indian History Congress) এর অ্যালাহাবাদে ১৬৩৮ সালে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সময় প্রফেসর ভাণ্ডারকর তাঁর সভাপতিত্বকালীন ভাষণে সেই সমস্ত ভারতীয় ইতিহাসবিদদের তীব্র নিন্দা করেছেন যারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে বারবার বলেন যে ভারতীয়দের ইতিহাস বোঝার ক্ষমতা ছিল না। একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে কলহণকে কেবল ভারতীয়রাই নয়, সার অরেল স্টেইন (Aurel Stein) প্রমুখ পাশ্চাত্য বিদ্বানরাও স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।
কলহণ তাঁর পূর্ববর্তী প্রায় এক ডজন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি থেকে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনায় সহায়তা নিয়েছেন। একইভাবে কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্র রচনায় সহায়ক পূর্ববর্তী বহু বিদ্বানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিদেশি বর্বর, অধর্মী ও বিধর্মী আক্রমণকারীরা আমাদের সরস্বতী-ভাণ্ডার (গ্রন্থাগারে) সংরক্ষিত হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করে ফেলেছে। একইভাবে এটি বলা মিথ্যা যে মুসলিম আগমনের আগে ভারতীয়রা লেখনসামগ্রী সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শুধু ভোজপত্র ও তালপত্রই নয়, তুলো দিয়ে তৈরি কাগজ এবং মসৃণ কাপড়ও লেখার জন্য ব্যবহার করত। স্বয়ং আলবেরুনির লেখায় জানা যায় যে বিজয়নগরের রাজাদের দরবারে মহিলা সচিব থাকতেন, যাঁদের কাজ ছিল রাজ্যে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা লিখে রাখা।
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
যখন পাশ্চাত্যরা প্রথমবার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন তাঁদের প্রবণতা ছিল সংস্কৃতকে আদিম ও মূল ভাষা মনে করা। জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ শ্লেগেল এবং ফরাসি বোপ প্রমুখেরও এই মনোভাবই ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁরা এই সত্যের ফলাফল বুঝতে পারল, তখন তাঁরা বিপরীত দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করল। ততদিনে প্রফেসর ম্যাক্সমুলার লর্ড ম্যাকলে দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই জন্যই যখন ফরাসি ব্যাকরণবিদ বোপ গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি শব্দের মূল সংস্কৃতকে দেখাতে শুরু করলেন, তখন ম্যাক্সমুলার প্রলাপ বকতে লাগলেন—“কোনো ভালো বিদ্বান কখনোই গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে হয়েছে ভাবতেই পারে না।” তিনি আরও লিখেছেন—“এখন আর কেউই সংস্কৃতকে গ্রীক, ল্যাটিন এবং অ্যাংলো-স্যাক্সনের মূল ভাষা মনে করার কল্পনা করতে পারে না।”
যে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি সহজেই বুঝবে যে এখানে ম্যাক্সমুলার ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের সঙ্গে অন্যায় করছেন। এর কারণ ছিল ম্যাকলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অধীনতা স্বীকার করার পর ভারতীয় ইতিহাসের বিরুদ্ধে রচিত ষড়যন্ত্রে যুক্ত হওয়া। ম্যাক্সমুলার পরিস্থিতির চাপে পড়ে ম্যাকলের দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং ভারতীয় ইতিহাসের বিরুদ্ধে রচিত ষড়যন্ত্রে তাঁর আত্মা বিলীন হয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। এই কথা তিনি ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫৫-তে ম্যাকলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভারাক্রান্ত মনে এই শব্দগুলোতে প্রকাশ করেছিলেন—
“I went back to Oxford a sadder but a wiser man.”
দুঃখী ছিলেন এজন্য যে, বিদ্বান হয়ে তিনি এক রাজনীতিবিদের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং জ্ঞানী ছিলেন এজন্য যে রাজনৈতিক বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন।
9 'No sound scholar can ever think of deriving any Greek or Latin words from Sanskrit.'
-Maxmueller : "Science of Language. Vol. 1. 4492.
? "No one supposes any longer that Sanskrit was the common source of Greek, Latin or Anglo-Saxon.'
-India, What can it teach us ?
3 "I went back to Oxford a sadder but a wiser man".
-Camp. "Hist, of India', Vol. VI, 1932
সুতরাং যাতে তিনি পৃথিবীর সুখ-সুবিধা ভোগ করতে করতে জীবিত থাকতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, তখন জার্মানিতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ম্যাক্সমুলার আর্থিক অভাবের মধ্যে জীবনযাপন করছিলেন। ম্যাকেলে তাকে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করেছিলেন, তখন ম্যাক্সমুলার দ্বিধা-সঙ্কটহীনভাবে এই দেশের সর্বনাশে লিপ্ত হয়েছিলেন।
ইংরেজরা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য বুঝতে পেরেছিল, এবং মুসলমানদের মতো সরাসরি তলোয়ার ব্যবহার না করে কূটনীতি প্রয়োগ করেছিল। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রশংসক ছিলেন, কারণ এটি পূর্বের বহু সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেছে। তারা জানতেন যে যুদ্ধে পরাজিত ভারতীয়রা সাংস্কৃতিকভাবে এখনও নিজেদেরকে ইংরেজদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে, তাই তারা এমন একটি জাল বুনেছিল যার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্য থেকেই তার বিরোধ সৃষ্টি হতে শুরু করে। ম্যাকেলের নির্দেশনায় তারা ইংরেজি শিক্ষার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছিল।
এই জালে ফাঁদে পড়াদের জন্য বড় বড় প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল। কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ. করা মেধাবী ছাত্রদের সর্বোচ্চ বৃত্তি দিয়ে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজে পাঠানো হত। সেখানে শিক্ষা সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্থানে প্রিন্সিপাল বা উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করা হত। লাহোরের অরিয়েন্টাল কলেজ এবং বারাণসীর কুইন্স কলেজে অক্সফোর্ডের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হত। এইভাবে ভারতীয়দের ধীরে ধীরে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের রঙে রঙানো শুরু হয়। তাদেরকে বোঝানো হত যে পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনায় তাদের নিজস্ব (ভারতীয়) সংস্কৃতি নীচের।
কালক্রমে দাস তার দাসত্বে আনন্দ অনুভব করতে শুরু করেছিল এবং এভাবে বিজয়ীর বিজয় সম্পন্ন হয়।
পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাদের প্ররোচিত ভারতীয় পণ্ডিতরা ওয়েদ, উপনিষদ ইত্যাদিতে এমন মন্তব্য চাপিয়ে দিলেন যে ভারতীয় নবীন প্রজন্মের মন পরিবর্তিত হলো। তাদের মধ্যে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি হীনতা জন্মালো। স্কুল ও কলেজে শেখানো হত যে ‘আর্য’ নামে অভিহিত এই দেশের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যা বিদেশী, যাতে তারা গর্ব করতে না পারে যে এই সুজলা-সুফলা-শ্যস্যশ্যামলা ভারতভূমি তাদের নিজস্ব।
ফলে নতুন প্রজন্মের মনে জন্ম নিল যে ভারতবর্ষের ধর্মশালায় যেমন আর্য, শক, হুন, মঙ্গোল, তুর্ক ও আফগান এসেছে, তেমনই ইংরেজরাও এসেছে এবং তাদেরও এই দেশে পূর্ববর্তীদের মতো অধিকার আছে। তাই তাদের সুবিধামত প্রমাণ সামনে আনা হয়েছে এবং প্রতিকূল প্রমাণ চাপা দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাগেস্থনিসের একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যা প্রায় ২৩শো বছর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে এসেছে বলে বলা হয় এবং বারবার প্রামাণিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।
ম্যাকব্রিন্ডলের সম্পাদিত Ancient India of Megasthanese পৃষ্ঠ ৩৪-এ উদ্ধৃত:
"It is said that India, being of enormous size when taken as a whole, is peopled by races both numerous and diverse, of which not even one was originally of foreign descent, but all were evidently indigenous; and moreover that India neither received a colony from abroad, nor sent out a colony to any other nation."
পর অধিকার করে নিয়েছিল। এই আর্য হিন্দু, পারসি, কাকেশীয়, গ্রীক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির পূর্বপুরুষ ছিলেন। ভারতের বাইরে কোনো স্থানে তাদের প্রাচীন বসতি ছিল।' যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আর্যদের এই অভিযান ম্যাগেস্থনিসের ভারত আগমনের প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ম্যাগেস্থনিস বলপ্রয়োগ করে বলেছেন যে ভারতের বাসিন্দারা সকলেই এখানে স্বদেশী। এটি স্পষ্ট করে যে প্রায় ২৩০০ বছর আগে বসবাসকারী ভারতীয় এবং তথাকথিত বিদেশীদের মধ্যে কেউই জানতো না যে আমরা আর্যজাতি হিসাবে বাইরে থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছি।
এখন মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে বলা শুরু হয়েছে যে এই দেশের মানুষদের মধ্যে যারা মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়েছে, তারা প্রধানত ছোট জাতি, अनुसূচিত জাতি, জনজাতি এবং গির্জন প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ, কারণ এই শ্রেণির মানুষই ভারতের প্রাথমিক-স্বদেশী। তাই হিন্দু থেকে মুসলমান বা খ্রিস্টান হওয়া মানুষই এই দেশের প্রকৃত মালিক। অন্যরা সবাই বিদেশী। ইংরেজ চলে গিয়েছে, কিন্তু ভারতের উপর প্রথম আক্রমণকারি আর্যদের আগে বেরিয়ে যেতে হতো।
৪ সেপ্টেম্বর ১৬৭৭-এ সংসদে সভাপতি দ্বারা মনোনীত ফরাসি এंथনি দাবি করেছিলেন যে সংবিধানের অষ্টম পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় ভাষার তালিকা থেকে সংস্কৃতকে বাদ দিতে হবে, কারণ এটি বিদেশী আগ্রাসী আর্যদের দ্বারা আনা বিদেশী ভাষা।
সন ১৬৭৮-এর শুরুতে ভারত তার প্রথম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করেছিল। এটি ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানী আর্যভট্ট-এর নামে নামকরণ করা হয়। এই উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৮-এ দ্রামুক (দ্রামুক মুনেত্র কষগম)-এর প্রতিনিধি লক্ষ্মণন রাষ্ট্রসভায় দাবি করেছিলেন যে ভারতীয় উপগ্রহের নাম 'আর্যভট্ট' রাখা উচিত ছিল না, কারণ এটি বিদেশী নাম।
কিছু বছর আগে, তামিলনাডুতে সেলেম নামক শহরে মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের আর্য হওয়ার কারণে তার মূর্তির গলায় জুতার মালা পরিয়ে এবং ঝাড়ু দিয়ে মারতে মারতে বাজারে শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। এভাবে আরও একবার তার সাহিত্যকে বিকৃত করে ভারতীয়দের মনে বিভিন্ন সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিরক্ত করে আত্মসম্মান থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাদের খ্রিস্টধর্মে প্ররোচিত করা হয়েছে।
এই ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ, পাশ্চাত্যরা ভাষাতত্ত্বের নাম করে একটি ইউরোপীয় ভাষার কল্পনা তৈরি করেছে, যাকে সংস্কৃতের মূল হিসেবে ধরা হয় এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার তুলনা করে তাদের বিপরীত যুক্তি উপস্থাপন করেছে।
১ এই প্রেক্ষিতে, দিল্লি থেকে প্রকাশিত Muslim India, ২৭ মার্চ, ১৬৮৫-এর সংখ্যায় প্রকাশিত এই বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয়:
"This land (India) belongs to those who are its original inhabitants and hence its rightful owners. It is they who built the Harappa and Mohenjodaro, the world's most ancient civilisation. Most of India's Muslims and Christians are converts from these sons of the soil, They are either Dalits or tribals. In all foreign invasions, it is these people who defended India. They (Aryans) don't belong to India and hence don't love India. They are foreigners, the enemy within. As Aryans, they are India's first foreigners. If Muslims and Christians are foreigners and must get out of India, as India's first foreigners, the Aryans are dutybound to get out first. Those who came first must leave first."
২
"Sanskrit should be deleted from the 8th schedule of the constitution because it is a foreign language brought to this country by foreign invaders. the Aryans." -Indian Express, 5.9.77
পরিণাম বের করে উল্টো গঙ্গা বয়ে দেওয়া শুরু করলো। তখন তারা ঘোষণা করলো যে ভাষার সাক্ষ্য অকাট্য, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয়ে বিশ্বস্ত।" জার্মান সংস্কৃতজ্ঞরা এখানে এমন অহংকার শুরু করেছিল যে তারা মনে করতো, বেদ অর্থ জার্মান ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে ভালোভাবে বোঝা যায়। এতটুকুই নয়, তারা জার্মানিকে ভাষাতত্ত্বের জন্মদাতা বলতেও শুরু করেছিল।" মিথ্যা ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্য-প্রব্রজনের কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। এ নামেই ইন্ডো-ইউরোপীয়ের কল্পনা করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে আর্যদের মূল নিবাস ইউরোপের কোনো দেশে বলা হয়েছে, যেখানে থেকে তারা ভারত সহ অন্যান্য দেশে বসতি স্থাপন করেছে।
সমগ্র বিশ্বের জানা আছে যে ভাষা এবং ব্যাকরণ নিয়ে যে অতুলনীয় অধ্যয়ন ভারতে হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়নি। ইন্দ্র থেকে পাণিনি পর্যন্ত শত শত মহান ভাষাবিদ এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং তারা তখনও যখন ইউরোপীয়রা প্রায় পড়াশোনা-লেখাপড়া জানতো না। কিন্তু রাজ্যাশ্রয়ের কারণে একজন জ্ঞানশীল, দুর্লভ দক্ষ সংস্কৃতজ্ঞকে একজন মহান পণ্ডিত হিসাবে উপস্থাপন করে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উৎকোচ করার জন্য তার বেদভাষ্য এবং তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি বহু গ্রন্থকে ভারতের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
ম্যাকালে দ্বারা ম্যাকসমূলারের হাতে জবরদস্তি ধরে দেওয়া কলম থেকে সৃষ্ট বেদের বিকৃত অর্থের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা আমরা নিজের শব্দে না বলে সরাসরি ম্যাকসমূলারের কথায় প্রমাণ করতে চাই। বেদের সম্পর্কে তার অনুভূতি প্রকাশ করে ম্যাকসমূলার লিখেছেন-
"বৈদিক সুক্তোং কি এক বড়ি সংখ্য্যা বিলকুলো বচ্ছকানি, নিকৃষ্ট, জটিল ঔর অত্যন্ত সাধারন হ্যায়।"
চন্দ্রনগরের প্রধান বিচারক, ফরাসি পণ্ডিত লুই জ্যাকোলিয়েট (Louis Jacolliot) সংবত ১৬২৬ (সন ১৮৬৬)-এ 'La Bible Dans Linde' (ভারতে বাইবেল) নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এক বছর পরে তার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতকে মানবতার কোল বলে উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে বিশ্বের সমস্ত চিন্তাধারা আর্যবিচার থেকে উদ্ভূত। ভারতের প্রশংসা পড়ে ম্যাকসমূলার হতবাক হয়ে যায়। গ্রন্থের সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন-
"জ্যাকালিয়ট অবশ্য ব্রাহ্মণোং কে বহকাভে মে আ গয়া হ্যায়।"
ম্যাকসমূলার এতটুকুই সন্তুষ্ট হননি। নিজের ক্ষোভ মেটাতে তিনি তার পুত্রকে লেখা একটি চিঠিতে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন-
"সংসার কি সব পুস্তকোং মে নতুন আহদনামা (বাইবেল অর্থাৎ New Testament) সর্বোত্তকৃষ্ট হ্যায়। ইসকে পশ্চাত কুরআন কে, জো এক প্রকর সে বাইবেল কা রূপান্তর হ্যায়, রাখ্খা জানা চায়ে। তত্পশ্চাত পুরানা আহদনামা (Old Testament), বৌদ্ধ ত্রিপিটিক, বেদ ঔর অবেস্তা হ্যায়।"
"The evidence of language is irreferable and it is the only evidense worth listening with regard to anti-historical periods."
-History of Sanskrit Literature, P. 1.3
"? The principles of German school are the only one which can ever guide us to an understanding of the Vedas, Germany is far more than any other country, the birth-place and home of the science of language."
-'Language' by W.D. Whitney
"$ 'A large number of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious, low and commonplace.'"
-Chips from a German Workshop. Ed. 1866, P. 27
"¥ 'The auther seems to have been taken in by the Brahmans in India.'"
যেমন আমরা বেদগুলো কণ্ঠস্থ করার জন্য দক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের ঋণী, তেমনই আমরা পাশ্চাত্য বিদ্বানদেরও ঋণী। ভারতীয় ব্রাহ্মণরা বেদগুলোকে ধ্বংস হতে বাঁচিয়েছিলেন, তেমনই পাশ্চাত্য বিদ্বানরা বেদগুলোকে কেবল ভারতেই সীমিত না রেখে, বিশ্বব্যাপী সম্পদে পরিণত করেছেন। ইউরোপীয় বিদ্বানদের প্রচেষ্টায় সারা বিশ্বে বেদগুলোর আলোচনা শুরু হয়, কিন্তু যেমন সায়ণাদি-এর দৃষ্টিভঙ্গি যজ্ঞমুখী ছিল এবং তাদের মতে বেদের প্রতিটি মন্ত্রের লক্ষ্য যজ্ঞের কোনো প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে মন্ত্রের নিয়োজন করা, তেমনই পাশ্চাত্য বিদ্বানদের লক্ষ্য বেদভাষ্য করে সেগুলোকে বিকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা। ম্যাক্সমুলারের ভাষ্যতে সায়ণ এবং ডারউইন উভয়ের ছায়া বিদ্যমান। ম্যাক্সমুলার বিকাশবাদকে সামনে রেখে সায়ণভাষ্যের অনুবাদ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের চিন্তাধারার মূলনীতি হলো বিকাশবাদের ধারণা। তাদের জন্য বিকাশবাদ প্রথম, এবং এর পর যা কিছু এসেছে তা বিকাশবাদের নীতির আলোকে দেখা হয়। বিকাশবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে তারা কোনো বিষয়ের সত্য বা মিথ্যা নির্ধারণ করে। এ ধরনের চিন্তাভাবনাকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না।
শ্রী অরবিন্দ ঘোষ পাশ্চাত্য বিদ্বানদের বেদভাষ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন—
"পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের মত হলো যে বেদ-এর ঋষি যখন অগ্নির উপাসনা করত, তখন তাতে চনের গুণও উল্লেখ করত যা অন্য কোনো দেবতার মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যখন সে বায়ুর উপাসনা করত, তখন বায়ুর মধ্যে সেই সমস্ত গুণ অন্তর্ভুক্ত করত যা অন্য কোনো দেবতার মধ্যে পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে সে এক দেবতার উপাসক নয়, বরং অনেক দেবতার প্রতি বিশ্বাসী, যা যুক্তিসঙ্গতও, যদি ধরা হয় যে একেশ্বরবাদের ধারণা মানুষের মস্তিষ্কে অনেক পরে এসেছে। যখন তাদের বলা হয় যে বেদে "এক সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য অগ্নি যম মাতরিশ্বানমাহু:"— এই মন্ত্র দ্বারা বলা হয়েছে যে ঈশ্বর এক এবং অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি সেই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম, তখন পাশ্চাত্য বিদ্বানরা বলে যে এই মন্ত্র পরে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে ম্যাক্সমুলার বহুদেবতাবাদ (Polytheism) এবং একেশ্বরবাদ (Monotheism)-এর একটি নতুন মত তৈরি করেছেন, যাকে তিনি হেনোথেইইজম (Henotheism) নামে অভিহিত করেছেন। হেনোথেইইজম-এর অর্থ হলো—যখন কোনো বিশেষ দেবতার উপাসনা করা হয়, তখন সেই দেবতার মধ্যে সব গুণ আরোপ করা হয় এবং এভাবে অন্য দেবতাদের সেই দেবতার তুলনায় নীচ মনে করা হয়।"
কিন্তু এই ধারণা কেবলমাত্র এই কারণে করা হয় যে, ম্যাক্সমুলার বিকাশবাদের বিপরীতে এটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় যে মানব-সংস্কৃতির প্রাথমিক সময়ে একেশ্বরবাদের মত উৎকৃষ্ট ধারণা মানুষের মস্তিষ্কে আসতে পারত। ম্যাক্সমুলার প্রমাণ দিতে পারেননি যে "एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" মন্ত্রটি বেদে পরে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই মন্ত্র বেদ-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি বিকাশবাদের স্বার্থে বদলানো যায় না।
{ 'Would you say that any one sacred book is superior to all others in the world 7 ... I say The New Testament. After that I should place the Koran, which, in its moral teachings, is hardly more than a later edition of the New Testament. Then would follow .... the Old Testament, the Buddhist Tripitaka ... The Veda and The Avesta.'
9 The Oxford English Dictionary defines Henotheism as the belief in a single God, without asserting that he is the only God; a stage between Polytheism and Monotheism. According to prof. Clayton, it dencies that each of the several divinities is regarded as the highest, the one which was worshipped and, therefore. treated as if he were the absolute being, independent and supreme for the worshipper.'- }
যদি খণ্ডিত হয়, তবে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের এ জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে নিজের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য নিজে বেদের অন্তঃসাক্ষী প্রমাণ হবে, অথবা রুডলফ, রায় এবং ম্যাক্সমূলার যা বলবেন তা প্রমাণ হবে। বেদের অর্থ যদি বেদ থেকে স্পষ্ট হয়, তবে সেই প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্থান থাকা উচিত। নিজেই বেদ বলে: 'একং সৎ বহুধা বদন্তি' তাকে অনেক নাম দিয়ে অভিহিত করা হয়। নিজে वेদে একেশ্বরবাদ এত স্পষ্ট বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ম্যাক্সমূলারের হীনোথীইজমকে ধরা যেতে পারে?
শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন:
"We are aware how modern scholars twist away from the evidence. This hymn, they say, was a late production; this lofty idea which it expresses with so clear a force rose up somehow in the mind or was borrowed by those ignorant fire-worshippers, sky-worshippers from their cultured and philosophical Dravadian enemies, But throughout the Veda we have confirmatory hymns and expressions. Agni or Indra or another is expressed hymned as one with all the other Gods. Agni contains all other divine powers within himself; the Maruts are described as all the Gods; the one deity is addressed by the names of others as well as his own, or, more commonly, he is given as Lord and King of the universe, attributes only appropriate to the Supreme Deity. Why should not the foundation of Vedic thought be natural monotheism rather than this new fangled monstrocity of henotheism ? Well, because primitive barbarians could not possibly have risen to such high conceptions, and if you allow them to have so risen, you imperil our theory of evolutionary stages of human development. Truth must hide itself, commonsense disappear from the field so that a theory should flourish. I ask, in this point, and it is the fundamental point, who deals most straightforwardly with the text, Dayanand or the western scholars ?"
শ্রী অরবিন্দের মতে, वेदের পাশ্চাত্য ভাষ্যকাররা ভাষ্য করতে করতে বিকাশবাদের পূর্বাগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে চলে। যদি वेদের অর্থ বিকাশবাদের নীতিকে সমর্থন না করে, তবে তারা অর্থকে বাঁকিয়ে মলিন করে নিজের অনুকূলে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। শ্রী অরবিন্দের মতে দয়ানন্দের ভাষ্য এই ধরনের বাঁকানো করে না। তারপরও, যাদু হলো যা শীর্ষে এসে বলে! যদিও পাশ্চাত্য ভাষ্যকাররা বিকাশবাদী পূর্বাগ্রহে আক্রান্ত, তবু वेদে এত উচ্চ স্তরের ভাব পাওয়া যায় যে তারা মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে সন্দেহে পড়ে যায় যে তাদের পূর্বাগ্রহ কি যথার্থ কিনা।
ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ খণ্ডে ম্যাক্সমূলার লিখেছেন:
"It is impossible for one scholar, it will probably be impossible for one generation of scholars to decipher the hymns of the Rigveda to a satisfactory conclusion."
অর্থাৎ, ম্যাক্সমূলারের মতে, একজন বৈদিক বিদ্বান বা এক প্রজন্মের বিদ্বানরাই ঋগ্বেদের ঋচাগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে না। ঋগ্বেদের সম্পর্কিত এই ধরণের ধারণা প্রকাশ করতে ম্যাক্সমূলার তখনই বাধ্য হয়েছিলেন যখন তিনি সেখানে এত উচ্চ স্তরের ভাব দেখেছিলেন।
ম্যাক্সমূলারের প্রধান শিষ্য ম্যাকডানল তার বই 'A Vedic Grammar for Students' এর ভূমিকাে লিখেছেন: ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের প্রথমে লেখা হয়েছে, তারপর নবম এবং শেষে দশম।" তাদের লেখার অর্থ হলো প্রথম ৮ এবং পরবর্তী ২ মণ্ডল লেখার সময় ভিন্ন, তবে 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' হলো প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্তের ৪৬তম মন্ত্র। তারপরও এটি প্রক্ষিপ্ত ধরা হয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি বিকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিট করে না।
মুকাবিলায় বিকাশবাদের দেয়ালগুলো যেন কেঁপে উঠতে লাগল। এমন পরিস্থিতিতে, वेদভাষ্য করে তাদের বিকাশবাদের খুঁন্টের সঙ্গে বাঁধা থাকা দুঃসাধ্য।
ধর্মান্তরণ এবং বেদার্থ
যদিও পাশ্চাত্য বিদ্বানরা বেদে অনেক পরিশ্রম করেছেন, তবুও তারা তাতে নিহিত জ্ঞানের গভীরতা খুঁজে পায়নি। সত্য পর্যন্ত পৌঁছাতে বিকাশবাদ ছাড়াও তাদের পূর্বাগ্রহ এবং স্বার্থও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় সমাজ ভারতকে খ্রিস্টান করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। ব্রিটেনের মানুষ মনে করত যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থায়ী করতে ভারতবাসীকে খ্রিস্টান ধর্মের ছাঁচে ঢালতে হবে। পাশ্চাত্য বিদ্বানরাও এই কাজে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাই তারা বেদের এমন ভাষ্য করেছেন, যা দেখার পর দেশবাসী তাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে হেয় চোখে দেখতে শুরু করল। বিদেশী বিদ্বানদের উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় জনতার মধ্যে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং সাহিত্য সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং ঘৃণা সৃষ্টি করা। এই দৃষ্টিতে, তাদের জন্য সায়ণ-ভাষ্য উপযোগী মনে হলো। তারা যে অনুবাদগুলো ইংরেজিতে করেছেন, সবই প্রায় সায়ণের ভিত্তিতে, এবং তারা वेদকে গবাদি পশুর গান, জঙ্গলের বাজে কথা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের জটিল উদ্ভিদ হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হল।
বেদের গবেষণা এবং অনুবাদকাজে নিজের অবদান বোঝাতে ম্যাক্সমূলার ১৮৬৬ সালে তার স্ত্রীকে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছেন:
“আমার এই সংস্করণ এবং বেদের অনুবাদ ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। এটি তাদের ধর্মের মূল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের দেখানো যে মূলটি কেমন, সেটাই গত তিন হাজার বছরে তার থেকে উদ্ভূত সবকিছুকে মূলসহ উচ্ছেদ করার একমাত্র পথ।”
১৮৬৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত সচিব ডিউক অফ আর্গাইলকে একটি চিঠিতে ম্যাক্সমুলার লিখেছিলেন—
“ভারতের প্রাচীন ধর্ম এখন প্রায় নষ্টপ্রায়। এখন যদি খ্রিস্টান ধর্ম তার স্থান না নেয়, তবে এর দোষ কার?”
খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ম্যাক্সমুলারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ই.বি. পুসে লিখেছিলেন— “ভারতকে খ্রিস্টান করার ক্ষেত্রে আপনার কাজ একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।”
এমনই ছিলেন ম্যাক্সমুলার। হিন্দুধর্মের প্রতি তার করা সেবায় মুগ্ধ হয়ে, ভারতের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— “ভারতের মানুষ সেই ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবে, যিনি তাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাভাবনাকে সঠিক রূপে উপস্থাপন করতে এত পরিশ্রম করেছেন।”
1 'This edition of mine and the translation of the Veda will, hereafter, tell to a great extent on the fate of India. It is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years.' -Life and letters of Frederick Maxmueller, Vol. 1 , Chap. XV. P. 34.
2. 'The ancient religion of India is doomed. Now, if Christianity does not step in, whose fault will it be ?' -Ibid. Chap. XVI. P. 378.
3. 'Your work will mark a new era in the efforts for the conversion of India.'
বস্তুত, তাদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসায় ম্যাক্সমুলার দ্বারা রচিত বইয়ের কারণে বিবেকানন্দ তার হাতে বিকল হয়ে পড়েছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো খ্রিস্টধর্মের রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের জন্য যীশু ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। তিনি যীশুর দেবত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন—“ঈশ্বর যীশু হয়ে জন্ম নিয়েছেন” (দেববাণী, পৃ. ৪০) “যীশু মসীহের মধ্যে অতিলৌকিক শক্তি ছিল। যীশু, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতারপুরুষরাই ধর্ম দিতে পারেন।” (দেববাণী, পৃ. ৪৬)। ‘ঈশদূত যীশু’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—এই মহাপুরুষ যীশুই বলেছেন—“কোনও ব্যক্তিই ঈশ্বরপুত্রের মাধ্যমে ছাড়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়নি এবং এই বক্তব্য শাব্দিকভাবে সত্য” (ঈশদূত যীশু, পৃ. ৩)। এক সংলাপের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—“যীশু ঈশ্বরঅবতার ছিলেন। মানুষ তাকে হত্যা করতে পারেনি। যাকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল তা কেবল তার ছায়ামাত্র ছিল।” (বিবেকানন্দ থেকে সংলাপ, পৃ. ১২০)। “যদি আমি যীশুর উপাসনা করি, তবে আমার জন্য সেই কাজ করার একমাত্র পদ্ধতি আছে—এবং তা হলো তাকে ঈশ্বররূপে আরাধনা করা।” (ঈশদূত যীশু, পৃ. ১৭)।
স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যয়ন গীতা ও উপনিষদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মূল বেদ তিনি পড়েননি এবং গুরুভক্তিতে তিনি এত অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে ম্যাক্সমুলারের চাতুর্য বোঝার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। তাই ‘ম্যাক্সমুলারবাক্যং প্রমাণং বাক্যং’ মেনে একইরূপ ইচ্ছানুযায়ী যীশুর পথে চোখ বন্ধ করে চলতে শুরু করেছিলেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে বিদেশী পণ্ডিতরা সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্য নিয়ে অনুকরণীয় পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু জাতিগত পক্ষপাত, রাজনৈতিক স্বার্থ এবং শাস্ত্র-বিষয়ে অজ্ঞানমুলক নানা বিভ্রান্তির কারণে তারা বৈদিক সাহিত্যকে তার প্রকৃত রূপে উপস্থাপন করতে পারেননি। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা এত পরিশ্রম করেছিলেন, তার ইঙ্গিত মোনিয়ার উইলিয়ামসের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকার এই শব্দগুলো থেকে পাওয়া যায়—“(অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে) বডেনপীঠের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল বডেন তার স্বীকৃতি-পত্রে (অগাস্ট ১৮১১) অত্যন্ত স্পষ্ট শব্দে লিখেছিলেন যে তার এই বিশাল দান-সম্পদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধর্মগ্রন্থগুলোর ইংরেজিতে অনুবাদ করা যাতে তার দেশবাসীরা ভারতীয়দের খ্রিস্টান করার কাজে এগিয়ে যেতে পারে।” কিছু সময় পরে একই মোনিয়ার উইলিয়ামস লিখেছিলেন—“যেদিন ব্রাহ্মণ-(বৈদিক)-ধর্মের দুর্গের প্রাচীর ক্রসের সৈন্যদের (খ্রিস্টান পাদরিদের) দ্বারা আক্রমণ করে ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই দিন হবে খ্রিস্টধর্মের সম্পূর্ণ ও অদ্বিতীয় জয়ের দিন।”
মোনিয়ার উইলিয়ামস বডেন পীঠের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই পীঠের প্রথম অধ্যাপক হোরেস হেমান উইলসন নিজে ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু তার দাতা কর্তৃক প্রেরিত কর্তব্যবোধের কারণে বাধ্য ছিলেন। তিনি একটি বই লিখেছিলেন—“Religious and Philosophical Systems of the Hindus”, এই বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—“এই বক্তৃতাগুলো জন মিয়ুর দুই শত পাউন্ড পুরস্কারের প্রার্থীকে সাহায্য করার জন্য।”
‘The founder (of the Boden Chair at Oxford) Col. Boden had stated most explicitly in his will (dated August 15, 1811) that the special object of his munificent bequest was to promote the translation of the scriptures into English to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion.’ - Sanskrit-English Dictionary by Monier Williams, 1899, Preface, P. IX.
“When the walls of the mighty fortress of Brahmanism are encircled, undermined and finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be signal and complete.” - Modern India and the Indians, Ed. 3, 1879, P. 261.
দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে। হিন্দুধর্মের খণ্ডন করার ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের লেখক এই পুরস্কারের অধিকারী হবেন।’’ একই জয়ান মিউর “The Oriental Studies” নামক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, এর প্রকাশকরা তার উপর লিখেছিলেন—“এই বই খ্রিস্টান পাদরিদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।”
পাদরি বাপ-দাদার সন্তান ম্যাকালে জন্ম থেকেই একজন খ্রিস্টান মিশনারি ছিলেন। তার প্রভাবের কারণে ম্যাক্সমুলারও (যিনি মূলত একজন বিদ্যাব্যসী ছিলেন) মিশনারি হয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাকালে কূটনীতিক ছিলেন, আর তার হাতে থাকা कठপুতলী ম্যাক্সমুলার কলমের অধিকারী ছিলেন। উভয়ের লক্ষ্য একটাই—খ্রিস্টধর্মের প্রচার করে ভারতে বিদেশী শাসনের ভিত্তি মজবুত করা।
বিদেশী শাসন এবং খ্রিস্টধর্ম চিরকাল একসাথে চলেছে। ভারতের দাসত্বের শৃঙ্খল মজবুত করতে খ্রিস্টান পাদরিরা ব্রিটিশ শাসকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের সমাপ্তির দুই বছর পর ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টন ঘোষণা করেছিলেন—“এটি শুধুমাত্র আমাদের কর্তব্যই নয়, বরং আমাদের স্বার্থও এটাই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার হোক।”
এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান মিসটার মেঙ্গলস পার্লামেন্টে বলেছিলেন—“প্রভুতার দ্বারা হিন্দুস্তানের বিশাল সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে যাতে যীশুমসীর পতাকা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লহরাতে পারে। প্রতিটি খ্রিস্টানের কর্তব্য হলো সমগ্র ভারতীয়দের অবিলম্বে খ্রিস্টান করার মহান কাজে সমস্ত শক্তি দিয়ে মনোনিবেশ করা।”
সन् ১৮৭৬ সালে বোম্বের গভর্নর জেনারেল লর্ড রি প্রিন্স অফ ওয়েলসের সামনে পাদরিদের শিষ্টমণ্ডল উপস্থাপন করে বলেছিলেন—“আপনার সৈন্য, বিচারক, গভর্নর এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের যে কাজ চলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি এই মিশনারিরা করছেন।”
লর্ড ম্যাকালে এবং তার সহযোগী ও ভারতীয় মনসপুত্ররা আজ পর্যন্ত যা করছেন, তার ফলাফল হিসেবে বিকৃত দেশের মানসিকতার উপর মন্তব্য করে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন "Naturally some of these are not behind the hostile foreign critic in their estimate of the history of Indian culture. They look upon India's cultural evolution as one dreary scene of discord, folly and superstition. They are eager to imitate the material achievements of Western States, and tear up the roots of ancient civilisation, so as to make room for the novelties imported from the West. One of their number recently declared that if India is to thrive and flourish, England must be her "spiritual mother" and Greece ber 'spiritual grandmother"." অর্থাৎ— "প্রকৃতপক্ষে, এদের মধ্যে কিছু শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী সমালোচকের তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে যথেষ্ট নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। তারা ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশকে একটি একঘেয়ে বিবাদ, মূর্খতা ও কুসংস্কারের দৃশ্য হিসেবে মানেন। তারা পশ্চিমা রাষ্ট্রের ভৌত অর্জন অনুকরণের আগ্রহী, এবং প্রাচীন সভ্যতার মূল চিরা তুলে ফেলে পশ্চিম থেকে আনা নতুনত্বের জন্য স্থান তৈরি করতে চায়। সম্প্রতি এদের মধ্যে একজন ঘোষণা করেছেন যে, যদি ভারত সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তবে ইংল্যান্ড তার ‘আত্মিক মা’ এবং গ্রীস তার ‘আত্মিক ঠাকুমা’ হতে হবে।"
আচার্যরা প্রাচীন ঋষি পরম্পরার অনুসরণ করে যেখানে বেদকে পবিত্র, অপৌরুষেয় ও ঈশ্বরীয় জ্ঞান মনে করেছিলেন, সেখানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এগুলোকে প্রায়শই মানব-পুস্তকাগারের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে মানলেও, এগুলোকে পবিত্র দিব্য জ্ঞান ও বিভিন্ন বিদ্যার ভাণ্ডার নয়, বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ হিসেবে দেখেন, যেখান থেকে প্রাচীন অসভ্য প্রায় জঙ্গলি মানুষের চিন্তা-ধারা এবং রীতি-নীতি বোঝা যায়।
ম্যাগেস্থনিসের বিশ্বস্ততা
যখন সার উইলিয়াম জোন্স, হেনরি টন্স, কোলব্রুক, শ্ল্যাগেল, হাম্বল্ট এবং শপেনহাওয়ারর মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্য পশ্চিমে পৌঁছল, তখন মানুষের আগ্রহ ছিল ভারত থেকে আসা প্রতিটি সাহিত্যিক গ্রন্থকে অতিপ্রাচীন যুগের হিসেবে মানার। কিছু মানুষের কাছে ভারতের উৎকর্ষের এই ধারণা বিরক্তিকর মনে হতে শুরু করল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এ.এইচ. সেসের লেখায়—
"কিন্তু যেখানে মানুষ সম্পর্কিত, তার ইতিহাস এখনও পর্যন্ত বাইবেলের প্রান্তে লেখা তারিখ পর্যন্ত সীমিত ছিল। মানুষের অধিকালের আবির্ভাবের এই প্রাচীন ধারণা আজও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এবং তথাকথিত সূক্ষ্ম ইতিহাসজ্ঞরা প্রাচীন ইতিহাসের তারিখকে ছোট করার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই প্রজন্মের জন্য যারা বিশ্বাস করত যে মানুষের সৃষ্টি প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর বা এর কাছাকাছি সময়ে হয়েছে, তাদের জন্য ধারণা যে মানুষ এক লাখ বছর আগে থেকে আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ছিল।"
পাশ্চাত্য লেখকরা বুদ্ধের পূর্বের ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মানেন না, বরং তা প্রাগৈতিহাসিক যুগ মনে করেন। যে একক ভিত্তি-তারিখ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭) তাদের দ্বারা ভারতীয় সময়সূচীর পুরো কাঠামো গড়ে উঠেছে, তা হলো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও গ্রিক আগ্রাসী আলেকজান্ডারের তথাকথিত সমকালীনতার গল্প। এটি ম্যাগেস্থনিস দ্বারা লেখা বলে ধরা হয়, কিন্তু যখন নিজেই ম্যাগেস্থনিসের ভারতে আগমন বিতর্কিত, তখন তার ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়সূচী কীভাবে প্রামাণিক হতে পারে? যদি ম্যাগেস্থনিস ভারতে এসে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে থাকতেন এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালীন হতেন, তাহলে কীভাবে তিনি নন্দ এবং বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিবিদ চাণক্যের উল্লেখ না করতেন? কিন্তু তিনি তাদের কোনো নামও উল্লেখ করেননি। এতটুকুই যথেষ্ট যে ম্যাগেস্থনিস…
"But as far as man was concerned, his history was still limited by the dates in the margin of our Bibles. Even today the old idea of his recent appearance still prevails and the so-called critical historians still occupy themselves in endeavouring to reduce the dates of his early history.... To a generation which had been brought up to believe that 4000 B.C. or thereabout the world was being created, the idea that man himself went back to 1,00,000 years ago was both inconceivable and incredible." - Antiquity of Civilised Man, Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 60, July-December, 1930.
1 These lectures were written to help candidates for a prize of £ 200 given by John Muir, the well-known old Hailebury man and great Sanskrit scholar, for the best refutation of the Hindu Religious System. -Eminent Orientalists, Madras P. 72.
2.The publishers of John Muir's book 'The Oriental Studies' admit that this book will prove most serviceable to the Christian Missionaries. -Ghosh and Bros. 61 Sankaritollah, Calcutta, 1878.
3. It is not only our duty; but in our own interest to promote the diffusion of Christianity, as far as possible, throughout the length and b cadth of India. - Christianity and Government of India, Mathew, P. 194.
4 Providence has entrusted the extensive empere of India to England so that the banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Everyone must exert all his strength that there may be no dilatoriness on any account in continuing in the country of the grand work of making all Indians Christians .*
5 "They are doing in India more than all those civilians, soldiers, judges and governors your highness has met."
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও আলেকজান্ডারের সমকালীনতা সম্পর্কিত গল্প, যার ভিত্তি রাখার জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়, সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরপর এর ভিত্তিতে নির্ধারিত অন্যান্য সমস্ত সময়সূচী স্বয়ংক্রিয়ভাবে খণ্ডিত হয়ে যায়। ভারতীয় সূত্র অনুযায়ী বুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, আদিতে শঙ্করাচার্য ইত্যাদির কাল প্রচলিত সময় থেকে প্রায় ১২০০ বছর পিছিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, ম্যাগেস্থনিস দ্বারা লেখা বলে পরিচিত গ্রন্থ ‘ইন্ডিকা’ আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। তার নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতের ইতিহাস লেখা হয়েছে। ভি. আর. রামচন্দ্রন ‘A Peep into Historical Past’ (১৮৬২) এবং রামচন্দ্র দীক্ষিত ‘Mauryan Polity’-তে বলেছেন যে, তৎকালীন সমাজ ও সামরিক রচনার বর্ণনা যা চাণক্য তার অর্থশাস্ত্রে করেছেন, তা ম্যাগেস্ঠনিসের বর্ণনার (Classical Accounts of India-1860) সঙ্গে মিল খায় না। প্রফেসর কিথও এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
যেখানে পুরাণে শক, যবন, পারসি, হুনদের আক্রমণের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে আলেকজান্ডারের কোনো উল্লেখ নেই। প্লিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, ম্যাগেস্ঠনিসের বর্ণনা পরস্পরবিরোধী এবং অবিশ্বাস্য। ডঃ খানবাখও বলেছেন, এতে সন্দেহ আছে যে ম্যাগেস্ঠনিস একবারও পলিবোথায় গিয়েছিলেন কি না। স্ট্রেবো স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, ভারতের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অধিকাংশ গ্রিক লেখক মিথ্যাবাদী ছিলেন, কিন্তু এই ধরনের লেখকদের ওপর অক্সফোর্ডের পণ্ডিতরা তাদের ভারতীয় ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং ভারতীয়রাও সেই ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা করেছেন।
আজকাল পশ্চিমা লেখকরা নতুন তথ্য পাওয়া মাত্র তার ওপর বিবেচনা করে পূর্বাগ্রহ সংশোধন করতে শুরু করেছেন, কিন্তু যেসব দিনে ইংরেজি শাসনের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল, তখন এই অবস্থা ছিল না। সমস্ত লেখা পূর্বাগ্রহের ওপরই করা হত। সম্প্রসারক ইউরোপীয়দের ভারতীয়দের সামনে উপস্থাপন করার জন্য একজন আদর্শ বীরের মূর্তি গড়া প্রয়োজন ছিল। এজন্য তারা আলেকজান্ডারের মূর্তিকে যথাযথ মনে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গ্রিক লেখকদের মূল গ্রন্থ ধ্বংস হয়ে গেছে। পরবর্তী সাহিত্য থেকে তাদের উদ্ধৃতিগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। ডঃ খানবাখ কর্তৃক জার্মান ভাষায় উপস্থাপিত এই সংকলন ‘ইন্ডিকা’ নামে পরিচিত। ১৮৭৭ সালে ম্যাকক্রিন্ডল ‘Ancient India after accounts of Magasthanese and Aryan’ নামে এর ইংরেজি রূপান্তর করেছেন। এরই সম্প্রসারণ এবং কল্পিত মানচিত্র তৈরি করে ভিনসেন্ট স্মিথ ‘Oxford History of India’-তে এটি ব্যবহার করেছেন এবং আমরা আমাদের গৌরবময় মহাপুরুষদের যথোপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে তাদের অনুকরণ করেছি, কিন্তু কালের পরিক্রমায় নিজেই পাশ্চাত্য লেখকরাই এই গ্রিক লেখকদের অবিশ্বাস্য ঘোষণা করতে শুরু করেছেন।
‘আলেকজান্ডার এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমকালীন ছিলেন’—উইলিয়াম জোন্স এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রফেসর এম. ট্রায়ার তার ‘কলহাণকৃত রাজতারঙ্গিনী’-এর প্রস্তাবনায় এই বিষয়ে প্রতিউত্তর দেন। এই বিষয় নিয়ে তিনি ম্যাক্সমুলারকেও চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু ম্যাক্সমুলার তার মত উল্লেখ না করে নিজের ‘History of Sanskrit Literature’-এ উইলিয়াম জোন্সের সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন— “ভারতের ইতিহাসকে গ্রিসের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করা এবং সময়সূচী ঠিক করা একমাত্র উপায়। কিছু পদ্ধতি বিশেষত মি. ট্রায়ারের রাজতারঙ্গিনী-এ করা আপত্তিগুলোর সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং গ্রিসের স্যান্ড্রাকোটসকে এক ধরা নিয়ে কোন আপত্তি নেই।” গ্রিসের আলেকজান্ডার এবং ভারতের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালীনতা সম্পর্কিত উইলিয়াম জোন্সের মত পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।
বেদের অবস্থান
ভারতে অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভারতীয় প্রথাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বেদ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার। এগুলোকে ধর্মের মূল বলা হয়েছে— ‘বেদোऽখিল ধরমমূলম’। আস্থিকতা এবং নাস্তিকতার মানদণ্ডও বেদের নিন্দা ও স্তুতি-র ওপর নির্ভরশীল—‘নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ’। অর্থাৎ, যার বেদ নিন্দা করা হয় না, সে আস্থিক। বেদ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। পরোক্ষভাবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত লৌকিক সাহিত্য ও বিভিন্ন বিদ্যায়ও এরা বহুভাবে অন্তর্ভুক্ত। বেদের গুরুত্বের কারণে সমস্ত ধর্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায় তাদের মূল বেদেই খুঁজে পেতে চেষ্টা করে এসেছে।
আজকাল পৃথিবী যতই উন্নতি করেছে, তবু মানুষের সমস্যার সমাধান যেমন বেদের মধ্যে আছে, তেমন অন্যত্র বিরল। মানুষের জীবনের জন্য যা কিছু ব্যবহারযোগ্য, তার সবকিছুর নির্দেশনা বেদের মধ্যে রয়েছে। বেদে আচৈতন্যের সঙ্গে পরলোকীয় জ্ঞান, ভৌত জ্ঞান সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং ভোগের সঙ্গে মুক্তির বর্ণনা আছে। যদি বেদ মানুষের জন্য এতটা উপযোগী না হত, তবে ব্রাহ্মণরা প্রাণ দিয়ে তার রক্ষা করতেন না, দক্ষিণ ভারতের মানুষরা বেদ মুখস্থ করা জীবনলক্ষ্য বানাতেন না। আজও অনেক বেদপাঠী এর যুগ-যুগান্তের শ্রবণ ও মৌখিক পরম্পরা পালন করছেন। তাদের মুখে বেদ আজও সেই রূপে সংরক্ষিত আছে যেভাবে কখনো আদিঋষিরা উচ্চারণ করেছিলেন। বিশ্বের এই অনন্য বিস্ময় দেখে এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আবেগময় হয়ে বলেছেন, যদি বেদের সমস্ত মুদ্রিত কপি বিলীন হয়ে যায়, তবুও ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে তা পুনরায় প্রাপ্ত করা সম্ভব।
বেদের মহত্ত্বকে ভারত স্বীকার করেছে এবং তার রক্ষার জন্য বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বেদমন্ত্রের সংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা আজকের গণিতের ভাষায় Permutation and Combination হিসেবে বলা যেতে পারে। বেদমন্ত্র স্মরণ রাখা এবং এতে একটি অক্ষরও, বা মাত্রাও, লোপ বা বিপর্যয় না ঘটে, তার জন্য তা ১৩ভাবে মুখস্থ করা হতো—এগুলোকে সংহিতা পাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, পুষ্পমালাপাঠ, ক্রমমালাপাঠ, শিখাপাঠ, রেখাপাঠ, দণ্ডপাঠ, রথপাঠ, ধ্বজপাঠ, ঘনপাঠ এবং ত্রিপদঘনপাঠ বলা হয়। এই পাঠের নিয়মাবলী ‘বিকৃতিভল্লী’ নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করে ম্যাক্সমুলার তার গ্রন্থ ‘Origin of Religion’-এ পৃষ্ঠা ১৩১-এ লিখেছেন—
"The texts of the Vedas have been handed down to us with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word or even an uncertain aspect in the whole of Rigveda."
যদি ব্রাহ্মণরা বেদ মুখস্থ করে নিজেরা সংরক্ষণ না করতেন, মুসলিম শাসনের পর বেদ বেঁচে থাকত না। এমন অবস্থায়, যদিও পণ্ডিতদের কাছে বেদের অর্থের জ্ঞান না থাকত, তারা বেদ মুখস্থ করে যা রক্ষা করেছেন, তার জন্য পুরো মানবজাতি তাদের ঋণী থাকবে। প্রশ্ন উঠে, এটি কি শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস ছিল? নাকি এর পেছনে কোনো গভীর চিন্তাভাবনা ছিল?
শুধু অন্ধবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিশ্বাস দীর্ঘ সময় ধরে টিকতে পারে না। চিন্তাশীল মানুষ কোনো না কোনো সময়ে এর পরীক্ষা করতে চাইবে, এবং যখন তার মনে হবে বিশ্বাস কেবল অন্ধবিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল, তখন তা গ্রহণ করতে সে অনিচ্ছুক হবে। আশ্চর্যজনক যে ভারতের চিন্তাশীল মানুষ—সাংখ্য, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের রচয়িতারা—এটি কখনো অনুভব করেননি। এর অর্থ, অতিপ্রাচীনকালীন প্রজন্মের কাছে বেদের অর্থ সুস্পষ্ট ছিল এবং এজন্য তারা বেদের মহত্ত্বের বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। পরম্পরার ভিত্তিতে একে অপরকে বেদের অর্থ শেখানোর প্রথা বিলীন হলে ধীরে ধীরে বেদের জ্ঞানের স্পষ্টতা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল।
এইভাবে বেদার্থ বা বেদভাষ্যের পরম্পরা শুরু হয় যখন মানুষ মৌখিক উপদেশের মাধ্যমে বেদার্থ বোঝার ক্ষেত্রে অক্ষমতা অনুভব করতে থাকে। বেদার্থ করার গুরুজনরা বেদকে তাদের-নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন এবং সেই অনুযায়ী অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্যই প্রাচীন প্রামাণিক আচার্যরাও বেদমন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করেছেন।
বৈদিক ভাবধারায় যজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের প্রাধান্য বাড়ার কারণে বেদমন্ত্রের ব্যবহার মূলত যজ্ঞে সীমিত হয়ে গেছে। যজ্ঞের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বেদের আধ্যাত্মিক এবং আধ্যৌভৌত অর্থ गौণ হয়ে গেছে এবং যাজিক প্রক্রিয়ায় তাদের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। বেদমন্ত্রের কেবল অধিযাজিক অর্থ প্রদানের সরাসরি আঘাত পড়েছে আধিদৈবিক প্রক্রিয়ায়। প্রাচীনকালে আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার অনুযায়ী যে বৈজ্ঞানিক অর্থ বেদে করা হত, তা ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। ফলস্বরূপ, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রতিপাদক মন্ত্র চারণ-ভাটদের স্তোত্রে পরিণত হয়েছে এবং এভাবে বেদের সর্বজ্ঞাত্মকতা নষ্ট হয়েছে।
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বেদার্থকারীরা ভাষ্যকাররা যাজিকতাবাদের কেন্দ্রে আবদ্ধ থেকেছেন। সায়ণের যুগ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, আধ্যাত্মিক উপাদান স্পষ্ট নির্দেশকারী মন্ত্রকেও জোর করে যাজিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হত। যজুর্বেদের ২৩তম অধ্যায়ের রাজধর্মের ব্যাখ্যা প্রদানকারী মন্ত্রগুলোকে মাহিঘর এমন অসভ্য অর্থে ব্যাখ্যা করেছে যে, আমরা সভ্য বিশ্বের সামনে লজ্জিত হয়ে দাঁড়াই।
প্রকৃতপক্ষে মাহিঘরের অর্থ এতটাই কুৎসিত যে কামশাস্ত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রकरणেও এমন অশ্লীল ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। এমন অর্থ মন্ত্রকে বিকৃত করেও করা সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় মাহিঘরের অর্থ তখনই গৃহীত হতে পারে যদি আমাদের উদ্দেশ্যই বেদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হয়। মাহিঘরের অর্থ পড়ে চার্বাকদের মন্তব্য—
त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्तभण्डनिशाचराः
जर्फरी-तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्।।
अश्वस्थास्य शिश्न तु पत्नीग्राहां प्रकीर्तितम्।
भण्डेस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यं जातं प्रकीर्तितम्।
मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्।।
মাহিধরের অর্থ তাই ত্যাগযোগ্য নয়, কারণ এটি অশ্লীল তাই নয়, বরং কারণ এটি মন্ত্রের প্রকৃত অর্থই নয়। শতপথব্রাহ্মণে এমন অর্থ পাওয়া যায়, তবে সেখানে অন্যান্য স্থানে মন্ত্রের অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজ্য অর্থও পাওয়া যায়। এটি নির্দেশ করে যে, মাংসভক্ষণ, মদ্যপান, পশুবলি, গোপনন্দ্রিয়পূজা ইত্যাদি আসুরিক প্রবণতাকে ব্রাহ্মণাদির গ্রন্থে প্রক্ষেপ করা হয়েছে এবং বেদ বলে আখ্যায়িত করে নিজের বিশ্বাসের বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে।
প্রশ্ন উঠে, বেদ কি সত্যিই এই ধরনের কুকৃত্যের প্রশংসা করে? যদি উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তবে বুদ্ধের মতো মহাত্মার কণ্ঠে আমরা বলব যে আমরা এমন বেদকে মানি না। কিন্তু তাতে ত্রুটি বেদের নয়; ত্রুটি সেই চশমার, যার মাধ্যমে সবকিছু কালো-কালো দেখা যায়।
লর্ড ম্যাকালে তার মিশনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। লোকমান্য তিলক-এর মতো দেশভক্তের কলমে তিনি লিখিয়েছেন যে, ভারতের বসবাসকারী আর্য (হিন্দু) দেশের স্বদেশী নয়, বরং আগ্রাসী হিসেবে বাইরে থেকে এসে বসবাস করেছেন। নিজের দেশে আমরা পরদেশী হয়ে রয়েছি। বাবু উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তার বই ‘মানবেরাদি জন্মভূমি’-এ লিখেছেন—
"তিলক মহাশয় (আর্যদের মূল স্থান সম্পর্কে) সংশোধন করার জন্য গত বছর আমরা তার বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি সরলভাবে বললেন—‘আমার মূল বেদ অধ্যয়ন নেই। আমরা সাহেবদের অনুবাদ পড়েছি।’"
অর্থাৎ, তারা মূল বেদ পড়েননি, শুধু বিদেশীদের অনুবাদ পড়েছেন। সায়ণ ও তার অনুসারী ম্যাক্সমুলারের দূষিত বেদার্থ সবাইকে এমন অন্ধকারে রেখেছিল যে, আজও তা খোলা হয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতির পোষক কনহাইয়ালাল মানিকলাল মুনশি তার বই ‘লোপামুদ্রা’-তে ঋগ্বেদের ভিত্তিতে লিখেছেন—আর্যদের ভাষায় এখনও জঙ্গলি অবস্থার স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। মাংসও খাওয়া হতো, এবং গরুর মাংসও। 'অতিথিগ্ব' ছিল গরুর মাংস খাওয়ানোর মহিমান্বিত উপাধি। ঋষিরা সোমরস পান করে মাতাল থাকতেন এবং লোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করতেন। সাধারণ মানুষও মদ্যপান করে মাতাল হতো। তারা জুয়া খেলত। ঋষিরা যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজারকে বিনাশ করতেন। তারা সুন্দরী নারীদের আকৃষ্ট করার জন্য মন্ত্র রচনা করতেন। কুমারী থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান অধম বলে মনে হতো না। অনেক ঋষির পিতার পরিচয় অজানা ছিল। আর্যরা নেকড়ের মতো লোভী ছিল। বিকৃত বা অশ্লীলতার কোনো ধারণা ছিল না। আত্মার কোনো ধারণা ছিল না। ঈশ্বরের কোনো কল্পনা, নাম বা বিশ্বাস ছিল না। নিজস্ব দেশের কোনো ধারণা ছিল না। দস্যুরা ভারতের শিবলিঙ্গ পূজক প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন।
যখন আমরা চিঠি লিখে তাদের কাছে ঋগ্বেদের সেই মন্ত্র উদ্ধৃত করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম, যাদের ভিত্তিতে তারা এই সমস্ত লিখেছে, তারা একইভাবে উত্তর দিয়েছেন, যেমন লোকমান্য তিলক করেছিলেন। তারা আমাদের নামে ২ ফেব্রুয়ারি ১৬৫০ তারিখে চিঠি পাঠিয়েছেন—
"I believe the Vedas to have been composed by human beings in the very early stage of our culture and my attempt in this book has been to create an atmosphere which I find in the Vedas its translated by western scholars and as given in Dr. Keith's Vedic Index. I have accepted their views of life and conditions of those times."
অর্থাৎ—“আমি বেদকে বিশ্বাস করি যে আমাদের সংস্কৃতির প্রারম্ভিক পর্যায়ে মানুষ দ্বারা রচিত হয়েছে। আমার এই বইয়ে আর্যদের সম্পর্কে যা কিছু লিখেছি, তার ভিত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের, বিশেষ করে ডঃ কিথের দ্বারা করা বেদের অনুবাদ। আমি সেই সময়ের মানুষের জীবনধারা এবং অবস্থার বিষয়ে তাদের মত গ্রহণ করেছি।"
রায়ণ এবং অনুসারী পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতদের নৃকথা-প্রক্রিয়া অগ্রাহ্য করে, সাধারণ সংস্কৃতভিত্তিক বেদার্থ করার এই কুপরিণতি দেখা দেয় যে, সমস্ত সত্য বিদ্যার গ্রন্থ বেদ কেবল কিসসে-কাহিনির সংকলনে পরিণত হয়ে যায়। এপর্যন্ত, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, শাখা, শ্রোতসূত্রসহ বহু সংস্কৃত গ্রন্থকেও বেদ মনে করে, সময়ে সময়ে যে প্রক্ষেপণ ঘটেছে তা সব বেদের মস্তকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এভাবে আমাদের মস্তিষ্কের ভূ-খণ্ডে বেদের প্রতি অবিশ্বাসের পাথুরে প্রাচীর তৈরি হয়েছে।
ঋষি দয়ানন্দের আবির্ভাব
এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দয়ানন্দের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ভারতীয় পুনর্জাগরণের (Renaissance) পুরোধা ছিলেন। ফ্রান্সের মহান লেখক রোমা রোলা লিখেছেন—
"This man with the nature of a lion is one of those, whom Europe is too apt to forget when she judges India, but whom she will probably be forced to remember to her cost; for he was that rare combination, a thinker of action with a genius for leadership. He was a hero with the athletic strength of a Hercules who thundered against all forms of thought other than his own, the only true one. He was so successful that in five years Northern India was completely changed. He possessed unrivalled knowledge of Sanskrit and the Vedas. Never since Shankara had such a prophet of Vedism appeared. Dayanand was not a man to come in an understanding with religious philosophers imbued with western ideas."
অর্থাৎ—“এই সিংহ প্রকৃতির মানুষটি এমন একজন, যাকে ইউরোপ প্রায় ভুলে যায় যখন সে ভারতকে বিচার করে, কিন্তু একদিন ইউরোপকে তার ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হতে হবে; কারণ তিনি ছিলেন কার্যনির্বাহী চিন্তাবিদ এবং নেতৃত্বের জন্য অদ্বিতীয় প্রতিভার বিরল সংমিশ্রণ। তিনি শারীরিক বলের দিক থেকে হারকুলিসের মতো ছিলেন, যিনি সত্যের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের চিন্তার বিরুদ্ধে বজ্রধ্বনি করতেন। পাঁচ বছরে উত্তর ভারত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। সংস্কৃত এবং বেদের জ্ঞান তার চেয়ে কম কেউ জানে না। শঙ্করের পর দয়ানন্দের মতো বেদের প্রকৃত প্রচারক আর কেউ হয়নি। পাশ্চাত্য চিন্তায় প্রভাবিত কোনো ধর্মীয় বা দার্শনিক ধারার সঙ্গে তিনি কখনো সমঝোতা করেননি।”
ঋষি দয়ানন্দের বেদভাষ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে শ্রী অরবিন্দ ১৬১৬ সালে লিখেছেন—
"In the matter of Vedic interpretation, I am convinced that whatever may be the final complete interpretation, Dayanand will be honoured as the first discoverer of the right clues. Amidst the chaos and obscurity of old ignorance and age-long misunderstanding, his was the eye of direct vision that pierced to the truth and fastened on to that which was essential. He has found the keys of the doors that time had closed and rent asunder the seals of the imprisoned fountains."
অর্থাৎ— “বৈদিক ব্যাখ্যার বিষয়ে আমার বিশ্বাস, যে কোনো চূড়ান্ত সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হোক, ঋষি দয়ানন্দকে সর্বদা সঠিক সংকেতের প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে সম্মান করা হবে। পুরনো অজ্ঞতা এবং দীর্ঘকালীন ভুল বোঝাবুঝির বিশৃঙ্খলা ও অস্পষ্টতার মধ্যে তার ছিল সরাসরি দৃষ্টির চোখ, যা সত্যকে উপলব্ধি করে তা যা অপরিহার্য তা নির্ধারণ করেছে। সময় যেসব দ্বার বন্ধ করে রেখেছিল, তার চাবি সে খুঁজে পেয়েছে এবং বন্ধ জলাধারের সীল ভেঙে ফেলেছে।”
ম্যাক্সমুলারের হৃদয় পরিবর্তন
নিজের আর্থিক দুরাবস্থার কারণে ম্যাক্সমুলারকে তার আত্মার চুক্তি স্বীকার করতে হয়েছে এবং লর্ড মেকালে’র দাসত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। অক্সফোর্ডে তার প্রাথমিক বছরগুলিতে, তার জন্য প্রয়োজন ছিল তার অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করা। তাই সেই সময়ে যা কিছু লিখেছেন, তা সেই পরিস্থিতির ফলাফল ছিল। এই আত্মসমর্পণের কারণে তার মন তাকে কাঁটাকাটি করেছে। সুতরাং, যখনই সে এই অবস্থার বাইরে আসার সুযোগ পেয়েছে, তখনই তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এবং ভিতরের কথাগুলো বাইরে আসতে শুরু করেছে।
এই ভিতরের কথা কী ছিল? ম্যাক্সমুলার লিখেছেন—
"Of the Rigveda, the most ancient of Sanskrit books, two editions are now coming out in monthly numbers. The one published at Bombay by what may be called the liberal party; the other at Prayag (Allahabad) by Dayanand Saraswati, the representative of Indian orthodoxy. The former gives a paraphrase in Sanskrit and Marathi and English translation, the latter a full explanation in Sanskrit followed by a vernacular (Hindi) commentary. These books are published by subscription and the list of subscribers among the natives of India is very considerable."
— India: What can it teach us
ম্যাক্সমুলার ছিল স্বামী দয়ানন্দ দ্বারা প্রয়াগ থেকে মাসিকভাবে প্রকাশিত ঋগ্বেদভাষ্যের নিয়মিত গ্রাহক এবং তার নাম গ্রাহকের তালিকায় মুখপৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছিল। স্বামীজিকৃত ঋগ্বেদভাষ্য পড়ে ম্যাক্সমুলারের চোখ খুলে যায় এবং তার চিন্তা পরিবর্তিত হতে থাকে।
১৮৮২ সালে কেমব্রিজে ম্যাক্সমুলারের কিছু বক্তৃতা হয়, যা ১৮৮৩ সালে India: What can it teach us নামে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতায় স্বামী দয়ানন্দ, বেদ এবং ভারতের সম্পর্কে ম্যাক্সমুলারের মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। কখনো স্বামী দয়ানন্দের সম্পর্কে তার পূর্ববর্তী মন্তব্য ছিল—
"He (Dayananda) actually published a commentary in Sanskrit on Rigveda. But in all his writings there is nothing which could be quoted as original, beyond his somewhat strange interpretations of words and whole passages of Vedas." — Maxmueller: A Real Mahatma, P. 8
অর্থাৎ, স্বামী দয়ানন্দ ঋগ্বেদের ভাষ্য করেছেন, কিন্তু তার সমগ্র সাহিত্যিক রচনায় এমন কিছু নেই যা মৌলিক বলা যায়, শুধু এটি যে তিনি বেদের শব্দ ও বাক্যের কিছু অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেছেন।
ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা পড়ার পর ম্যাক্সমুলার এই মহান গ্রন্থকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করেছেন এবং স্বামী দয়ানন্দ ও তার কৃতির প্রশংসা করেছেন—
"We may divide the whole of Sanskrit literature beginning with the Rigveda and ending with Dayanand's Introduction to his commentary of the Rigveda, into two parts."
— India: What can it teach us, P. 102
এইভাবে ম্যাক্সমুলার যেখানে সংস্কৃত সাহিত্যের এক ধ্রুবে ঋগ্বেদকে স্থাপন করেছেন, সেখানে অন্য ধ্রুবে স্বামী দয়ানন্দের ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
১৮৬৬ সালে ম্যাক্সমুলার লিখেছেন—
"A large number of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious, low and commonplace."
— Chips from a German Workshop, Ed. 1866, P. 27
অর্থাৎ, অনেক বেদীয় সুক্ত অত্যন্ত শৈশবজাত, জটিল, নিকৃষ্ট এবং সাধারণ। এতে একে অপরের সঙ্গে সঙ্গতি নেই, এবং সঠিক অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেদ ধর্মীয় বিশ্বাসের সংকলন মাত্র। যা অধিকাংশের বোধগম্য নয়। মানবজাতি যে আশ্চর্য দিয়ে শিশুর মতো জগতকে দেখে, তার ছায়া মন্ত্রগুলিতেও বিদ্যমান।
সেই একই ম্যাক্সমুলার ১৮৮২ সালে লিখেছিলেন—
"বেদের ভাষা যেমন, তাতে জীবনদর্শন যেমন এবং ধর্মের দর্শন যেমন, তা থেকে যে দৃশ্যপট দেখা যায়, তা বছরের দ্বারা মাপা সম্ভব নয়। বেদে যে অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে, তা আমাদের ইউরোপীয়দের জন্য ১৬শ শতকে আধুনিক মনে হয়। তার চেয়েও প্রাচীন কোনো সাহিত্যকর্মের নাম আমরা শুনিনি। মানব চিন্তাধারার ইতিহাস সম্পর্কে যে তথ্য বেদ থেকে পাওয়া যায়, তা বেদ আবিষ্কারের আগে আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল।"— আমরা ভারত থেকে কী শিখতে পারি, পৃ. ১৩০
১৮৬৮ সালে ম্যাক্সমুলার তার পুত্রকে লেখা চিঠিতে বেদকে অবমূল্যায়ন করে এই অবমাননাকর শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন—
"Would you say that any one sacred book is superior to all others in the world?.... I say, the New Testament. After that I should place the Koran which, in its moral teachings is hardly more than a later edition of the New Testament, Then would follow..... The Old Testament, the Buddhist Tripitaka... The Veda and the Avesta."
অর্থাৎ, পৃথিবীর সব গ্রন্থের মধ্যে নতুন আহদনামা (The Bible বা New Testament) সর্বোত্তম। এর পরে কোরান, যা এক প্রকারে বাইবেলের রূপান্তর, রাখা যেতে পারে। তারপরে পুরাতন আহদনামা (Old Testament), বৌদ্ধ ত্রিপিটক, বেদ এবং অ্যাভেস্টা।
পরবর্তীতে ১৮৮৩ সালে ম্যাক্সমুলার এইভাবে বেদের প্রশংসা করেছেন—
"যদি কেউ মানবজাতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চায়, বা এভাবে বলতে পারেন, যদি কেউ আর্য-জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চায়, তবে তার জন্য বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের কোনো সাহিত্য বৈদিক সাহিত্যের তুলনায় স্থির হতে পারে না।"— আমরা ভারত থেকে কী শিখি, পৃ. ১২৪
"মানুষ বেদের গুরুত্ব কমানোর অনেক চেষ্টা করেছে, তবে এর গুরুত্ব আজও যেমন ছিল, তেমনই আছে। আজও ধর্মীয়, সামাজিক বা দার্শনিক বিতর্কে বেদকেই চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।"
— ওই পৃ. ২২৭
স্বামী দয়ানন্দ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং যাস্কের নৃকথার ভিত্তিতে বেদের ছন্দকে চিহ্নিত করার বক্তৃতাকে প্রামাণিক মনে করতেন, যেখানে ম্যাক্সমুলাররা প্রায়শই সাধারণ সংস্কৃতভিত্তিক বেদভাষ্য করছিলেন। ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা অধ্যয়নের পর তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় এবং তিনি লিখেছিলেন—
"বাস্তবে বেদগুলোকে বোঝার জন্য বৈদিক পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি। অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। ঈসার জন্মের ৪০০ বছর পূর্বে যাস্ক নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অনুসরণ করেই আমরা বেদগুলো ঠিকভাবে বুঝতে পারি।"— আমরা ভারত থেকে কী শিখি, পৃ. ১৫০
পাশ্চাত্য মত অনুযায়ী, বৈদিক আর্যরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করতেন। ম্যাক্সমুলারও এটি বিশ্বাস করতেন, কারণ তিনি বিবর্তনের বিপরীতে মেনে নেবেন না যে মানব সংস্কৃতির প্রারম্ভিক সময়ে একেশ্বরবাদ মত উচ্চতর ধারণা মানুষের মস্তিষ্কে আসতে পারে।
পরবর্তীতে তার এই মত পরিবর্তিত হয় এবং তিনি লিখেছেন—
"There are hymns in the Rigveda that assert the unity of the Divine. Thus it is said—'That which is one, sages name it in various ways. They call it Agni, Yama, Matarishwa.'"
— "এক সদ্বিপ্রা বহুধা বন্তি, অগ্নি বর্ম মাতরিশ্বানমাহু:'"— India: What can it teach us, পৃ. ১২৮
"শ্রাদ্ধ" শব্দের ম্যাক্সমুলার দ্বারা করা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে স্বামী দয়ানন্দের এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি মান্য করার ফল।
"শ্রাদ্ধ" শব্দটি অর্থবহ। এই শব্দটি সম্পর্কিত সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য হলো—এই শব্দটি না বেদে পাওয়া যায়, না ব্রাহ্মণগ্রন্থে। তাই এটি বলা যায় যে, এই শব্দটি পরে প্রচলিত হয়েছে। শ্রাদ্ধ শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'শ্রদ্ধয়া যত্কৃতমিতি শ্রাদ্ধ' বা 'শ্রদ্ধার্থমিদং শ্রাদ্ধ'—এই পরিস্থিতিতে যারা শ্রাদ্ধ শব্দটিকে শুধু সাপিণ্ড-তিলোদকদান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ধরে নেন, তারা ভুল করেন।
— ওই পৃ. ২১৬
পাশ্চাত্য এবং তাদের অনুসারী ভারতীয় পণ্ডিতদের মত ছিল যে ভারতের মূল অধিবাসী ছিলেন ড্রাভিড, দাস এবং দস্যু নামে পরিচিত লোকেরা। পরে আর্যরা এই দেশে আক্রমণ করে, দেশটির আদিবাসীদের পরাজিত করে জোরপূর্বক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর বিপরীতে স্বামী দয়ানন্দের ধারণা ছিল যে, আর্যই এই দেশের মূল অধিবাসী। তার সংস্পর্শে আসার পর ম্যাক্সমুলারের মত পাল্টে যায় এবং পরোক্ষভাবে সে ঘোষণা করে যে—
"We have all come from the East—all that we value most has come to us from the East and by going to the East everybody ought to feel that he is going to his 'old home' full of memories, if only we can read them."
— India, পৃ. ২১
অর্থাৎ, এটি নিশ্চিত যে আমরা সবাই পূর্ব থেকে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের যা কিছু মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ, সবই পূর্ব থেকে এসেছে। এই অবস্থায় যখনই আমরা পূর্বের দিকে যাই, তখন আমাদের ভাবা উচিত যে, পুরনো স্মৃতিসমূহকে ধারণ করে আমরা আমাদের পুরনো বাড়ির দিকে যাচ্ছি।
১৮৬৮ সালে তার স্ত্রীকে লেখা ম্যাক্সমুলারের চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, ম্যাক্সমুলার ভারতীয়তার সর্বনাশের পরিকল্পনা করছিল। একই ম্যাক্সমুলার ভারতীয় প্রশাসনিক সেবায় (I.C.S. = Indian Civil Service) নিয়োগপ্রাপ্ত যুবকদের ইংল্যান্ড থেকে পাঠানোর সময় ভারত পরিচয় দিতে বলেছিল—
"আপনি আপনার বিশেষ অধ্যয়নের জন্য যেকোনো শাখা গ্রহণ করুন—ভাষা, ধর্ম, দর্শন, আইন, প্রথা, প্রাথমিক শিল্প বা বিজ্ঞান—প্রতিটি বিষয়ের অধ্যয়নের জন্য ভারতই সর্বাধিক উপযুক্ত। আপনি পছন্দ করুন বা না করুন, প্রকৃত সত্য হল যে মানব ইতিহাসের অমূল্য এবং নির্দেশক তথ্য শুধুমাত্র ভারতভূমিতে সংরক্ষিত, কেবলমাত্র ভারতভূমিতে।"
বাস্তবিকভাবে, বেদসংক্রান্ত সমস্ত অনর্থের মূল হলো মধ্যযুগীয় আচার্য, বিশেষ করে সায়ণের বেদার্থ-সম্পর্কিত ধারণা। যদি এই বিদেশি পণ্ডিতদের কাছে সায়ণের চেয়ে বেদের উৎকৃষ্ট ভাষ্য পৌঁছাত, তবে বেদের এই দুরবস্থা সম্ভবত হতো না। গত পাঁচ হাজার বছরে বহু আচার্য এসেছেন, কিন্তু বেদের প্রকৃত রূপটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কেউ ছিলেন না।
বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বেদ সম্পর্কিত প্রচলিত বিভ্রান্তি দূর করতে স্বামী দয়ানন্দ স্বাধীনভাবে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে বেদভাষ্য রচনা করেছিলেন এবং বেদের গভীরার্থ প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি সময়ের পূর্বেই স্বর্লোক চলে গিয়েছিলেন। তাই বেদের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা কেবল নির্দেশমূলক। যদি তিনি দীর্ঘ সময় বাঁচতেন এবং চারটি বেদের ভাষ্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হতেন, তবে তিনি বেদের ‘সর্বজ্ঞনময়ত্ব’ এবং ‘সর্ব বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি’—এই মনুর প্রতিপাদ্য সত্য প্রমাণ করতে সফল হতেন।
তার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে ছিল বেদ। এজন্য চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী, সংবৎ ১৯৩২ অনুযায়ী ১০ এপ্রিল ১৮৭৫ সালে যখন স্বামী দয়ানন্দ আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন—
"আর্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে, বেদের নির্ধারিত ধর্মতত্ত্ব প্রতিটি সভাসদকে মান্য করানো এবং তার প্রচার দেশ-প্রদেশে যথাশক্তি করা।"
প্রতিষ্ঠার সময়ই আর্যসমাজের ‘প্রথম নিয়ম’ নির্ধারিত হয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে, বেদ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি এবং সর্বশেষে বিশ্বে শান্তি ও সুসমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিশ্বাস ও সংকল্প নিয়ে তিনি বেদের বিরুদ্ধ মনতত্ত্ব এবং সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের নির্মূলের জন্য প্রচার শুরু করেছিলেন।
সত্যার্থপ্রকাশের রচনা
স্বামীজি তাঁর নীতি প্রচারের জন্য বাক্য ও লেখনী উভয়ই ব্যবহার করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি ১৮৬৭ সালে হারদ্বার কুম্ভ উপলক্ষে ‘পাখণ্ড-খণ্ডন’ নামে একটি ছোট্ট বই মুদ্রণ করিয়েছিলেন, যা তিনি ব্যাপকভাবে বিতরণ করেছিলেন। এর পরে ১৮৬৬ সালে কাশীর পণ্ডিতদের সঙ্গে হওয়া শাস্ত্রার্থের সম্পূর্ণ বিবরণ সংস্কৃত ও হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। তা থেকে স্বামীজির মতবাদ প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য মিলেছিল। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি ‘অদ্বৈতমত-খণ্ডন’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা ১৮৭০ সালে সেখানে প্রকাশিত হয়। হুগলীতে পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের সঙ্গে হওয়া শাস্ত্রার্থও ১৮৭৩ সালে কাশী থেকে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।
১৮৭৪ সালে স্বামীজি গ্রন্থ রচনায় বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন, যার ফলে পরবর্তী দুই-তিন বছরে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—সত্যার্থপ্রকাশ।
সত্যার্থপ্রকাশের রচনার প্রেরণাস্রোত ছিলেন রাজা জয়কৃষ্ণদাস। তিনি মুরাদাবাদের বাসিন্দা ‘রাণায়নী’ শাখার সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি স্বামীজির উপদেশে প্রভাবিত হয়ে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। সেই সময় কলেক্টর, জজ ইত্যাদি উচ্চপদে সাধারণত ইংরেজদেরই নিয়োগ দেওয়া হতো। তাই রাজা জয়কৃষ্ণদাসের ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাওয়া একটি বড় সাফল্য ছিল। তিনি সময়ে সময়ে স্বামীজির সঙ্গে মিলিত হতেন।
যেষ্ঠ মাস, সম্বৎ ১৬৩১ (মে ১৮৭৪) সালে স্বামীজি কাশী আগমনকালে রাজা জয়কৃষ্ণদাস সেখানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। একদিন যখন তিনি স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন তিনি প্রস্তাব দেন—
“ভগবান! আপনার উপদেশামৃত থেকে যারা লাভবান হতে পারে, তারা কেবল আপনার বক্তৃতা শুনতে পারা ব্যক্তিরা। সকলেই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত হতে পারে না, এবং আপনি নিজে সর্বত্র উপস্থিত হতে পারবেন না। অতএব যদি আপনার মতবাদ লিখিতভাবে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বহু মানুষ লাভবান হতে পারবে। এইভাবে আপনার উপদেশ স্থায়ী হবে এবং ভবিষ্যতের লোকরাও উপকৃত হবে।”
এই প্রস্তাবের সঙ্গে রাজা সমস্ত ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করেন। ‘নেকি ওর পুছ পুছ’—স্বামীজিকে প্রস্তাবটি পছন্দ হয় এবং তিনি তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। রাজা গ্রন্থ লিখানোর জন্য চন্দ্রশেখর নামের একজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতকে নিয়োগ দেন।
স্বামীজির বিশ্বাস ছিল— “প্রক্ষিমক্রিয়মানস্য কালঃ পিপতি তদ্রসম্” তিনি যেই কাজটি উপকারী মনে করতেন, তা শুরু করতে দেরি করতেন না। সেই অনুযায়ী আষাঢ় বদি ১৩, সম্বৎ ১৬৩২ (১২ জুন ১৮৭৪), শুক্রবারে সত্যার্থপ্রকাশ লিখানোর কাজ শুরু হয়। স্বামীজি বলতেন এবং পণ্ডিত চন্দ্রশেখর লিখতেন।
সমগ্র সত্যার্থপ্রকাশের রচনায় প্রায় দেড় মাস সময় লেগেছিল। ৫০০ পাতার এই গ্রন্থ ১৮৭৫ সালে স্টার প্রেস, বারাণসী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতে ১২টি সমুল্লাস ছিল। ঈসাই ও মুসলিম মতবাদের সম্পর্কিত ১৩'তম এবং ১৪'তম সমুল্লাস, যা বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে রয়েছে, তা প্রাথমিক সংস্করণে ছিল না। সংশোধিত ও সম্প্রসারিত সত্যার্থপ্রকাশ যদিও ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়, তবুও তার মুদ্রণ স্বামীজির জীবদ্দশায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণটি আজকের দিনেও আর্যসমাজের কাছে বৈধ, যেখানে ১৪টি সমুল্লাস এবং ‘স্বমন্তব্যামন্তব্য’ শিরোনামের মাধ্যমে স্বামীজির অভিমত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রথম সংস্করণে ১৩-১৪তম সমুল্লাস
অনেক ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে বর্তমান ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এ যে ১৩তম এবং ১৪তম সমুল্লাস উপলব্ধ আছে, সেগুলো প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়নি, তাই এগুলো স্বামীজীর লেখা নয়। এগুলো আর্য সমাজের লোকেরা স্বামীজীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত সংস্করণে নিজেরা যোগ করে দিয়েছে। এই আক্ষেপের সমাধানের জন্য আমরা এখানে প্রথম সংস্করণের দশম সমুল্লাসের পৃষ্ঠা ৩০৭-এর ফটোকপি-ব্লক ছাপছি, যেখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে স্বামীজি ১৩তম এবং ১৪তম সমুল্লাস লিখতে চেয়েছিলেন। এই ফটোকপি আমরা আমাদের নিজস্ব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রথম সংস্করণের দুর্লভ প্রতি থেকে করিয়েছি। বলা যেতে পারে— ‘লিখতে চেয়েছিলেন’ থেকে এটা কীভাবে প্রমাণিত হলো যে ‘লিখেছিলেন’? এমন লোকদের জন্য স্বামীজীর সেই চিঠি প্রমাণ, যা তিনি মাঘ বদি ২, সম্বৎ ১৮৩১ (২৩ জানুয়ারি ১৮৭৫) তারিখে স্টার প্রেস, কাশীর লালা হরবংশলালকে লিখেছিলেন। সেই পত্রের এই বিষয়ক অংশ এইরূপ—
“আগে মুরাদাবাদে কোরানের খণ্ডনের অধ্যায় গবেষণা করার জন্য গিয়েছিলাম, তো গবেষণা করে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে কি না? যদি না এসে থাকে, তবে রাজা জয়কৃষ্ণদাসজিকে চিঠি লিখুন, দ্রুত ছাপার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং বাইবেলের অধ্যায়ও সব গবেষণা করে ছাপিয়ে দিন।” (পত্র-ব্যবহার, পৃ. ২২)
এই পত্র থেকে কোরান এবং বাইবেল—উভয়েরই খণ্ডন-মণ্ডন স্বামীজীর জীবিত অবস্থায় ছাপা হওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে নিশ্চিত হয়ে যায় যে কোনো কারণে সেগুলো ছাপা হতে পারেনি। এরই সমর্থন মেলে সংশোধিত ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এর ভূমিকায় স্বামীজীর নিজেই লিখিত এই কথাগুলোতে—
“কিন্তু শেষের দুই সমুল্লাস এবং পরবর্তী স্বসিদ্ধান্ত (স্বমন্তব্য-অমন্তব্যপ্রকাশ) কোনো কারণে প্রথমে ছাপা যেতে পারেনি, এখন এগুলোও ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।”
প্রথম সংস্করণের হস্তলিখিত প্রতি রাজা জয়কৃষ্ণদাসজীর পৌত্র রাজা জ্বালাপ্রসাদজীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে তার ফটোকপি করিয়ে নেওয়া হয়েছে, যা পরোপকারিণী সভা, আজমেরে সংরক্ষিত আছে। তাতে ১৩তম সমুল্লাসে কোরান মতের এবং ১৪তম সমুল্লাসে খ্রিস্টিয় মতের সমালোচনা আছে।
উপলব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে সংশোধিত ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এর সমগ্র পাণ্ডুলিপি ঋষি তাঁর নির্গমনকাল থেকে প্রায় ১৪ মাস পূর্বে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন এবং তার প্রেস-কপি বানিয়ে প্রেসে পাঠানোও শুরু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু বৈদিক যন্ত্রালয়ের ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতার কারণে ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ তাঁর জীবদ্দশায় ছাপা হয়ে প্রকাশিত হতে পারেনি। এই কারণেই বিরোধীরা এ কথা বলার সুযোগ পেয়েছে যে संवत् ১৬৪০-এর ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ আসল নয়, স্বামীজীর মৃত্যুর পর আর্য সমাজের লোকেরা তা তৈরি করে তাঁর নামে ছাপিয়ে দিয়েছে।
ঋষি-রচিত গ্রন্থে অশুদ্ধি
স্বামী দয়ানন্দ ১৮৬০ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত গুরু বিরজানন্দজীর কাছে থেকে বিদ্যাধ্যয়ন করেছিলেন। এই তিন বছরে তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। স্বামীজি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—“পরে যখন তাঁর (গুরুবর) সঙ্গে পরিচয় হলো, তখন ‘তিন বছরে ব্যাকরণ আসে’—এমন কথা বলাতে আমি তাঁর কাছেই পড়ার সংকল্প করেছিলাম।” অষ্টাধ্যায়ী ও মহাভাষ্যের অতিরিক্ত তিনি আর কোন কোন গ্রন্থের অধ্যয়ন করেছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এতটাই নিশ্চিত যে দণ্ডীজি থেকে তিনি সেই দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি সত্য–অসত্যের বিচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু গুরুবরের কাছ থেকে চাবি পেলেও তালা খুলতে অনেক সময় লেগেছিল। আত্মকথা অনুযায়ী—“বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত করে আমি দুই বছর পর্যন্ত আগ্রায় ছিলাম।” আগ্রা থেকে তিনি জয়পুরে যান। সেখানে তিনি শৈব–বৈষ্ণব বিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—“সেখানে (জয়পুরে) আমি প্রথমে বৈষ্ণবমতের খণ্ডন করে শৈবমতের প্রতিষ্ঠা করি। জয়পুরের মহারাজা রামসিংহ শৈবমত গ্রহণ করেন। এর ফলে শৈবমতের এমন প্রসার ঘটে যে সহস্র সহস্র রুদ্রাক্ষের মালা আমি নিজের হাতে দিয়েছি। এখানে শৈবমত এত দৃঢ় হয়েছিল যে হাতি–ঘোড়া প্রভৃতির গলায়ও রুদ্রাক্ষের মালা পড়ে গিয়েছিল।” জয়পুরে স্বামীজি অক্টোবর ১৮৬৬ পর্যন্ত ছিলেন। ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদা ১৬২৩ বিক্রমী (১ মার্চ অথবা পণ্ডিত লেখারামের মতে ১২ মার্চ, ১৮৬৭) তারিখে স্বামীজি হরিদ্বার পৌঁছান। তখন হরিদ্বারে কুম্ভের মহামেলা বসেছিল। সেখানে পৌঁছে তিনি সপ্তসরোবর নামক স্থানে নিজের ডেরা ফেলেন এবং ‘পাখণ্ড–খণ্ডনী’ পতাকা ওড়িয়ে মূর্তিপূজা, অবতারবাদ, ভাগবতাদি পুরাণ, জলস্থানের তীর্থনাম, কণ্ঠি, তিলক ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক চিহ্নের খণ্ডন শুরু করে দেন।
এই প্রসঙ্গ বিস্তারের উদ্দেশ্য হলো এ কথা জানানো যে ১৮৬৩ সালে গুরুবরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় থেকে অক্টোবর ১৮৬৬-তে জয়পুর ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত কাল ছিল নিজের মত ও নীতিসমূহ ক্রমশ নির্ধারণ করার সময়। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের এই ছিল ভূমিকা। তখন পর্যন্ত তিনি নানাবিধ বিষয়ের জটিল প্রশ্নের সমাধান খুঁজতেই ব্যস্ত ছিলেন। প্রথমবার আমরা দয়ানন্দকে হরিদ্বারে ‘পাখণ্ড–খণ্ডনী’র নীচে, গুরুবর প্রদত্ত স্নেহনাম ‘কুলকর’ বা ‘কালজিহ্ব’কে যথার্থ প্রমাণ করতে দেখছি। ‘কুলকর’-এর অর্থ হলো খুঁটি—যে নিজ অবস্থানে খুঁটির মতো অচঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে, সে-ই ‘কুলকর’। সময় এলে দয়ানন্দ শাস্ত্রার্থ–সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে এই নামকে সম্পূর্ণভাবে যথার্থ প্রমাণ করেছিলেন। অসত্যের খণ্ডনে যার জিহ্বা কালের মতো হয়ে উঠত—এমন দয়ানন্দ সত্যই ছিলেন ‘কালজিহ্ব’।
১৮৮৩ সালে ঋষি দয়ানন্দের দেহাবসান ঘটে। এইভাবে ঋষির কার্যকাল ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত মোট ১৬ বছর স্থায়ী হয়। এই সময়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলোর সংখ্যা কে গুনতে পারে? পৌরাণিক, জৈন, বেদান্তী, খ্রিস্টান, মুসলিম এবং তাদের নানান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ জানানো বহু মানুষ—আর সেই সব আঘাত একা সয়ে যেতেন একমাত্র দयानন্দ। প্রায়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি হত; আবার এমন সুযোগও আসত, যখন অভিমন্যুর মতো একা দয়ানন্দের উপর এক সঙ্গে সাত–সাতজন (অথবা আরও বেশি) মহারথী ঝাঁপিয়ে পড়ত। ১৮৬৬ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কাশী–শাস্ত্রার্থে এমনটিই ঘটেছিল। তখন যাত্রার জন্য আজকের মতো সুবিধা ছিল না। তবু তিনি দক্ষিণ ব্যতীত সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লিখিত পত্রের সংখ্যাও হাজারে পৌঁছয়। যেখানে যেতেন বা থাকতেন, বিপুলসংখ্যক লোক তাঁর কাছে এসে নিজের সংশয়ের সমাধান করত। তবুও তিনি ছোট–বড় মিলিয়ে প্রায় ৩২টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; কিন্তু এসব ব্যস্ততার কারণে তিনি নিজ হাতে বেশি লিখতে পারেননি, না প্রেস–কপিগুলো পরীক্ষা করতে পেরেছেন, আর না-ই বা প্রুফ দেখার সুযোগ পেয়েছেন।
মুন্সি বখ্তাবর সিংহের নামে শ্রাবণ শুক্লা ১৩, বুধবার, संवत् १६३७ (১৮ আগস্ট, ১৮৮০) তারিখে পাঠানো একটি পত্রে স্বামীজি লিখেছিলেন—“যে ‘সংস্কৃতবাক্য-প্রবোধ’ বইটি ছাপা হয়েছে, তা বহু স্থানে ‘সংস্কৃতবাক্য-প্রবোধ’-এ অশুদ্ধও ছাপা হয়েছে। এই অশুদ্ধির তিনটি কারণ আছে। একটি—তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়া, আমার চিত্ত সুস্থ না থাকা। দ্বিতীয়ত—ভীমসেনের অধীনে শোধন হওয়া এবং আমার না দেখা, না প্রুফ পরীক্ষা করা। তৃতীয়ত—ছাপাখানায় কোনো কম্পোজিটর বুদ্ধিমান না থাকা।” (ঋষি দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৬৮০, ভাগ ১, পৃ. ৩৮৭–৮৮)
‘সত্যার্থপ্রকাশ’ স্বামীজি পণ্ডিতদের বলে লিখিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের লেখা হাতে নিয়ে দেখবার অবসরই বা কোথায় ছিল তাঁর? যেমন লেখা হয়েছে, তেমনই প্রেসে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামীজির বিবশতার সুযোগ নিয়ে লেখক পণ্ডিতরা তাতে এমন এমন বিষয়ের সংযোজন করে দিয়েছিলেন, যা স্বামীজির মন্তব্যের বিপরীত ছিল; কিন্তু এ কথা জানা গেল ছাপা বেরোনোর পরেই। দ্বিতীয় সংস্করণে মহর্ষি যে ভুলগুলোর সংশোধন করেছিলেন, তা মহর্ষির নয়, লেখক পণ্ডিতদেরই ছিল—এ কথা নিজেই রাজা জয়কৃষ্ণদাসের এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়—
“সত্যার্থপ্রকাশ’-এ স্বামীজির যে মত লেখা হয়েছিল, পরে যা পরিবর্তিত হলো, তার জন্য স্বামীজি এতটা দায়ী নন। স্বামীজির সেই সময় প্রুফ দেখার অবকাশ ছিল না। শুরুতে স্বামীজি সকল মানুষকেই ভালো ভেবে তাঁদের ওপর বিশ্বাস করে নিতেন। হতে পারে যে লেখক বা মুদ্রকের দ্বারা এসব মত ‘सत्यार्थप्रकाश’-এ ছাপা হয়ে গেছে।” ঐ কথাগুলো স্বামীজির অভিমত নয়—এই মর্মের একটি বিজ্ঞাপন ‘ঋগ্বেদ’ এবং ‘যজুর্বেদ-ভাষ্য’-এর অঙ্ক ১ এবং ২–এর মুখপৃষ্ঠায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিজ্ঞাপন থেকে সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এর প্রথম সংস্করণে লেখক ও পরীক্ষকদের ভুলের কারণে এমন বহু কথা ছাপা পড়েছিল, যা ঋষির বিপরীত ছিল।
স্বামীজির ভাষা বিচার করার সময় শুধু এটুকুই মনে রাখা যথেষ্ট নয় যে হিন্দি তাঁর মাতৃভাষা ছিল না; এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর কাছে এমন অবকাশও ছিল না যে কোথাও বসে সুস্থির চিত্তে গ্রন্থের রচনা করবেন। তিনি নিরন্তর গতিশীল ছিলেন এবং তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তাঁর সহকর্মীরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করতেন না—
১. ভীমসেন এখন ভাষা খুব ঢিলা বানায়। তাকে শিক্ষা দিয়ে দিও যে ভাষা তৈরি করতে ঢিলেমি যেন না হয়।
২. আমরা ভীমসেনের শোধিত বই দেখেছি, তাতে খুব ভুল বের হয়। এতে বোঝা যায় যে সে বড় গাফিল।
৩. আর এখন সে ভাষাও ভালো বানায় না, যেমন আগে বানাত। সে প্রতিদিনই অধঃপতিত হচ্ছে। কখনো গ্রাম্য ভাষা লিখে দেয় এবং ‘চ’-এর অর্থ ‘আর’ করা উচিত, সেটাকেও ‘ও’-র অর্থে করে দেয়। (পত্র ও বিজ্ঞাপন পৃ. ৩১৭, ৩৩৪, ৪৫৫)
এ থেকে স্পষ্ট যে স্বামীজি আরও সুস্পষ্ট এবং পরিমার্জিত ভাষা চাইতেন। কিন্তু এই কাজের জন্য শান্ত পরিবেশ ও সময় দরকার, আর তাঁর জীবনে দুটিরই অভাব ছিল।
গ্রন্থগুলোর মুদ্রণাদি কর্মে ঋষি দয়ানন্দকে কী ধরনের লোকের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে, তা তাঁর পত্র-ব্যবহার থেকেই স্পষ্ট। এমন অবস্থায় লেখা ও মুদ্রণে সাধারণ ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। স্বামীজির সারাজীবনে একমাত্র মুন্সি সমর্থদাসই এমন ব্যক্তি মিলেছিলেন, যিনি ঋষিভক্ত হওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত এবং ঋষির কাজের মাহাত্ম্য উপলব্ধিকারী ছিলেন। তাঁর সময়ে ঋষির যে গ্রন্থগুলো ছাপা হয়, তাতে তিনি বড় সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এর প্রথম সংস্করণে এমন কথা আছে, যা সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণে নেই। সেগুলোই সেগুলি, এবং তাদের মধ্যে কিছু কথা তো এমনও আছে, যেগুলো আমরা বড় গর্বের সঙ্গে উদ্ধৃত করে এসেছি। সেসবের কারণে মহর্ষিরও গৌরব বেড়েছে এবং আর্যসমাজেরও। সেগুলো কেন বাদ দেওয়া হয়েছে, তা বিদ্বানদের দ্বারা অনুসন্ধানযোগ্য। নিদর্শনস্বরূপ তাদের মধ্য থেকে কিছু এখানে দেওয়া হচ্ছে—
১. বিবাহে অনেক অর্থের নাশ করা অনুচিতই বটে, কারণ সে অর্থ নিছকই নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে অনেক রাষ্ট্র নষ্ট হয়ে গেছে এবং বৈশ্য লোকদের তো বিবাহে অতি অধিক অর্থব্যয়ের কারণে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়। তাই অর্থের নাশ কখনোই করা উচিত নয়। (সমুল্লাস ৪, পৃ. ১১০)
২. এ কথাটিও অবশ্যই জানা উচিত যে দেশ-দেশান্তরে বিবাহ হওয়া যথোচিত, কারণ পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হলে প্রীতি হবে এবং দেশ-দেশান্তরের ব্যবহারেরও পরিচয় জানা যাবে, বলাদি গুণও সমতুল্য হবে এবং আহার-ব্যবহারও এক হবে। এতে মানুষের বড় সুখ হবে। যেমন পূর্ব–দক্ষিণ দেশের কন্যা এবং পশ্চিম–উত্তর দেশের পুরুষদের সঙ্গে যখন বিবাহ হবে, এবং পশ্চিম–উত্তর দেশের মানুষের কন্যা এবং পূর্ব ও দক্ষিণে বসবাসকারী পুরুষদের সঙ্গে যখন বিবাহ হবে, তখন বল, বুদ্ধি, পরাক্রমাদি তুল্য গুণ হয়ে যাবে। পত্রের মাধ্যমে এবং আসা–যাওয়ার দ্বারা পারস্পরিক প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং পরস্পরের গুণ-গ্রহণ হবে এবং সব দেশের আচরণ সব দেশের মানুষের জানা হবে, আর পারস্পরিক বিরোধ যা আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। এতে মানুষের বড় আনন্দ হবে। (সমু. ৪, পৃ. ১৩৬–৪০)
৩. যেমন ঈশ্বর কোনো এক দেশের নন, বরং সব দেশের, তেমনি সংস্কৃতও কোনো এক দেশের নয়। তবে এমন জানা যায় যে আর্যাবর্ত দেশে আগে প্রবৃত্তি বেশি ছিল। সব ঋষি–মুনি এবং রাজারা আর্যাবর্তদেশবাসী লোকেরা পরম্পরায় সংস্কৃত পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন। সব দেশভাষার মূল সংস্কৃতই, কারণ সংস্কৃত যখন বিকৃত হয় তখন তাকে অপরভ্রংশ বলা হয়। (সমু. ৭, পৃ. ২৪৬–৫০)
৪. মুসলমানের ভাষা শিখতে বা কোনো দেশের ভাষা শিখতে কিছু দোষ হয় না, বরং কিছু গুণই হয়। ‘অপশব্দজ্ঞানপূর্বকে শব্দজ্ঞানেই ধর্ম’—এটি ব্যাকরণ মহাভাষ্যের বচন। এর অভিপ্রায় এই যে অপশব্দজ্ঞান অবশ্যই করা উচিত, অর্থাৎ সব দেশ–দেশান্তরের ভাষা শেখা উচিত, কারণ সেগুলো শেখার দ্বারা বহু ব্যবহারের খবর জানা যায় বলে উপকার হয় এবং সংস্কৃত শব্দের জ্ঞানও তাদের যথার্থভাবে বোধ হয়। যত দেশের ভাষা জানা যায়, ততই মানুষের অধিক জ্ঞান হয়, কারণ সংস্কৃতের শব্দ বিকৃত হয়ে-ই সব দেশভাষা হয়েছে। মহাভারতে লেখা আছে যে যুধিষ্ঠির ও বিদুরাদি বহু দেশের ভাষা জানতেন। তাই যখন যুধিষ্ঠিরাদিরা লক্ষাগৃহের দিকে গেলেন, তখন বিদুরজি যুধিষ্ঠিরজিকে ম্লেচ্ছ ভাষায় বোঝালেন এবং যুধিষ্ঠিরজি ম্লেচ্ছ ভাষায়ই জবাব দিলেন—তিনি যথাযথ তা বুঝে নিলেন।
মহাভারতে লেখা আছে—
“প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞমিদং বচঃ।
প্রাজ্ঞং প্রাজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোऽব্রবীত্॥”—আদিপর্ব ১৪৪, ২০
তদ্বত্ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে দেশ–দেশান্তর ও দ্বীপ–দ্বীপান্তরের রাজা এবং প্রজাগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। যারা দেশ–দেশান্তরের ভাষা জানতেন না, তাঁদের ব্যবহারেরই বা সিদ্ধি হতো কীভাবে? এতে কী বোঝা গেল—দেশ–দেশান্তরের ভাষা জানায় কোনো দোষ নেই, বরং বড় উপকারই হয়। (সমু. ১১, পৃ. ৩২৭)
৫. নোন ও পৌন রুটিতে যে কর আরোপ করা হয়, তা আমার কাছে ভালো বলে মনে হয় না, কারণ নুন ছাড়া দরিদ্রেরও নির্বাহ হয় না; নুন সবারই প্রয়োজনীয় এবং যারা মজুরি–মেহনতের দ্বারা কোনো মতে নির্বাহ করে, তাদের উপরে এই নুনের কর দণ্ডতুল্য হয়ে থাকে। এতে দরিদ্রদের কষ্ট পৌঁছে। তাই এমন হওয়া উচিত যে মদ, আফিম, গাঁজা, ভাঙ—এসবের উপর দ্বিগুণ–চতুর্গুণ কর আরোপিত হোক—তাই ভালো কথা, কারণ নেশাদিকের ছাড়া-ছুটি হওয়াই ভালো এবং যা মদাদি একেবারেই ছুটে যায় তো মানুষের বড় ভাগ্য, কারণ নেশা দ্বারা কারো কোনো উপকার হয় না। তাই এগুলোর ওপরই কর চাপানো উচিত এবং লবণাদির ওপর নয়। পৌন রুটির কর দ্বারা গরিব মানুষের খুব কষ্ট হয়, কারণ গরিব লোক কোথাও থেকে ঘাস কেটে নিয়ে আসে বা কাঠের বোঝা—এগুলোর ওপর পয়সার কর লাগলে অবশ্যই কষ্ট হয়। তাই পৌন রুটির যে কর আরোপ করা হয়, সেটিও আমাদের বোধে ভালো নয়। (সমু. ১১, পৃ. ৩৮৬৪–৮৫)
৬. সরকার কাগজ (স্ট্যাম্প) বিক্রি করে এবং অনেক কাগজে অর্থ অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে দরিদ্র মানুষদের খুব কষ্ট পৌঁছায়। তাই এ কাজ রাজার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে গরিব লোকেরা দুঃখ পেয়ে বসে থাকে। কচেহরিতে অর্থ ছাড়া কোনো কাজই হয় না। তাই কাগজের উপরে যে খুব বেশি অর্থ লাগে তা আমার কাছে ভালো বলে মনে হয় না। এটিকে ছেড়ে দিলে প্রজাদের আনন্দ হয়। (সমু. ১১, পৃ. ৩৮৭)
৭. বার্ষিক উৎসবাদি থেকে মেলা করা—এতেও আমাদের কাছে কোনো মহাশ্রেয় গুণ বোধ হয় না, কারণ এতে মানুষের বুদ্ধি বহির্মুখী হয়ে যায় এবং অর্থও অত্যন্ত ব্যয় হয়। (সমু. ১১, পৃ. ৩৬৫)
৮. শুধু ইংরেজি পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা—এটাও তাদের ভালো কথা নয়, বরং সব প্রকারের বই পড়া উচিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বেদাদি সত্য সনাতন সংস্কৃত গ্রন্থগুলো পড়বে না, ততক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর, ধর্ম, অধর্ম, করণীয় এবং অকরণীয় বিষয়গুলোকে জানবে না। তাই সব পুরুষার্থের জন্য বেদাদিকেই পড়া উচিত। (সমু. ১১, পৃ. ৩৬৫)
শেষের উভয় উদ্ধৃতি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনার প্রসঙ্গের; কিন্তু উপর থেকে বর্তমান আর্যসমাজকে লক্ষ্য করেই যেন লেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে। ঋষি ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। যার আশঙ্কা করেছিলেন আজ তাই ঘটছে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, আর্য-মহাসম্মেলন, গ্রন্থ-উন্মোচন, উদ্বোধন, সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান ইত্যাদির আড়ালে আর্যসমাজের প্রচারের নামে যে উৎসবগুলো হচ্ছে, সেগুলো কেবল কিছু ব্যক্তির আত্মপ্রচার ও শক্তিপ্রদর্শনের নিমিত্ত হয়ে পড়েছে। ফলত তালির গর্জন, স্লোগানের কোলাহল, পণ্ডালের সাজসজ্জা ও বিদ্যুতের ঝলকানিতে বাইরে থেকে সবল বলে মনে হওয়া আর্যসমাজ ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে। যেসব দোষ দূর করার জন্য আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেগুলোই আজ আর্যসমাজে প্রবেশ করে নিজেকে নিরাপদ মনে করছে এবং অন্তর্যামীভাবে আর্যসমাজকে খেয়ে ফেলছে। এখন সময় ‘কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্’ কর্মসূচিকে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ‘কৃণ্বন্তো স্বযমার্যম্’ গ্রহণ করার।
১৮৩৪–৩৫ সালের প্রায় সময়ে ভারতে ইংরেজ সরকারের সামনে এই প্রশ্ন দেখা দিল যে এখানে কীরূপ শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। লর্ড মেকলে এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনের কথা বলে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—
“We must do our best to form a class of persons who may be Indian in blood and colour but English in taste, opinions, words and intellect.”
অর্থাৎ—আমরা এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরির পূর্ণ চেষ্টা করব যারা রক্ত-মাংস ও রঙে যদিও ভারতীয় বলে মনে হবে, কিন্তু আচরণ–বিবেচনা, রীতি–নীতি, কথাবার্তা এবং মন–মস্তিষ্কে ইংরেজ হয়ে যাবে। আজ কি আমরা আর্যসমাজের তরফ থেকে দयानন্দের নামে চলা Dayanand English Medium Co-educational Public Schools-এর মাধ্যমে এমনই একটি শ্রেণী তৈরি করছি না, যারা সত্যিই ঠিক তাই, যেমনটি মেকলে চাইছিল? স্যুট পরা, টাই লাগানো ছেলে, স্কার্ট-পরা, চুলকাটা মেয়েরা—যারা নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা বোধ করে, নমস্তের বদলে “গুড মার্নিং” বলে, হিন্দির তুলনায় ইংরেজি সিনেমা দেখতে বেশি পছন্দ করে, অমলেট খেয়ে নাশতা করে—Nationality-র ঘরে “ভারতীয়” লেখা দেখে তবেই তাদের ভারতীয় হওয়ার ধারণা করা যায়। অন্যথায় তারা Tuesday-কে চেনে, মঙ্গলবারকে নয়। এর ভিত্তি সেই দিনেই পড়েছিল যেদিন ‘দয়ানন্দ’ ও ‘বৈদিক’-এর মাঝে ‘অ্যাংলো’ নিজের আসন পেতেছিল। ডি.এ.ভি. কলেজ প্রতিষ্ঠাকারী ত্রিমূর্তি (মহাত্মা হনুরাম, লালা লাজপত রায় এবং পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যালঙ্কার)–এর মধ্যে একজন লালা লাজপত রায় তাঁর গ্রন্থ ‘স্বামী দयानন্দ এবং আর্যসমাজের বর্তমান অবস্থা’-তে লিখেছেন— “সারা স্কিমের দুর্বলতা এখানেই ছিল যে কলেজের নাম ‘অ্যাংলো-বৈদিক’ রাখা হয়েছিল এবং ‘বৈদিক’-এর উপর ‘অ্যাংলো’-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই দুর্বলতার কারণেই সরকারী ও মিশন কলেজ এবং দয়ানন্দ কলেজের মধ্যে খুব অল্পই পার্থক্য রইল। আমাদের দল সবসময় বৈদিক-এর উপর অ্যাংলো-কেই অগ্রাধিকার দিতে থাকল।”
সত্যার্থপ্রকাশ হিন্দিতে
মূর্তিপূজার বিষয় নিয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ ও কাশীর পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত শাস্ত্রার্থ ১৬ নভেম্বর ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মূর্তিপূজার সমর্থনে সমবেত মণ্ডলীতে নিম্নলিখিত বিদ্বানগণ উপস্থিত ছিলেন—
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, পণ্ডিত শিবসহায়, পণ্ডিত মাধবাচার্য, পণ্ডিত বামনাচার্য, পণ্ডিত দেবদত্ত শর্মা, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কবাচস্পতি, পণ্ডিত চন্দ্রসিংহ ত্রিপাঠী, পণ্ডিত রাধেমোহন তর্কবাগীশ, পণ্ডিত দুর্গাদত্ত, পণ্ডিত বস্তীরাম দ্বিবেদী, পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ শিরোমণি, পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, পণ্ডিত ঘনশ্যাম, পণ্ডিত ঠাকুরদত্ত, পণ্ডিত হরিদত্ত দুবে, পণ্ডিত মৈরোদত্ত, পণ্ডিত শ্রীধর শুক্ল, পণ্ডিত বিশ্বনাথ ম্যাথিল, পণ্ডিত নবীননারায়ণ তর্কালংকার, পণ্ডিত মদনমোহন শিরোমণি, পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত মায়াকৃষ্ণ বেদান্তী, পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত ধনীরাম, পণ্ডিত দেবঘর, পণ্ডিত নরসিংহ শাস্ত্রী, পণ্ডিত যবাহরদাস উদাসী, পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন, পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ শ্রৌত্রিয়, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, পণ্ডিত রামশাস্ত্রী, পণ্ডিত শালিগ্রাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত ঢুন্ডিরাজ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামস্বামী মিশ্র, পণ্ডিত ভরতদ্বাজ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী, প্রমদাদাস মিত্র।
উপর্যুক্ত বিদ্বানদের অতিরিক্ত কাশীর অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও শাস্ত্রার্থস্থলে বসার জন্য যথোচিত স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন—
কাশীনরেশ মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ সিংহ, কাশীনরেশের ভাই রাজকুমার বীরেশ্বরনারায়ণ সিংহ শর্মা, বাবু ফতহনারায়ণ সিংহ শর্মা, ঐশ্বর্যনারায়ণসিংহ শর্মা, তেজসিংহ বর্মা, রঈস মৈনপুরী, রায় কৃষ্ণদেবশরণসিংহ, চৌধারি গুরুদত্তসিংহ শর্মা, হাজারি যदুনন্দন নাগল, ভারতেন্দু বাবু হরিশচন্দ্র গুপ্ত, বাবু গোকুলচন্দ্র গুপ্ত (ভারতেন্দুর ভাই)।
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও বালশাস্ত্রীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা স্বয়ং স্বামীজিও করতেন। জামানত স্বামীজির বিরুদ্ধেই ছিল। সভাপতি কাশীনরেশ যেমন মূর্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি নিজের নগরের পণ্ডিতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকা-ও স্বাভাবিক ছিল। তবু নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলি যা লিখেছে তা নিঃসন্দেহে চিন্তনীয়। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ (১৭ জানুয়ারি ১৮৭০) শাস্ত্রার্থের বিবরণ প্রদান করে লিখেছিল—
“Finding it impossible to overcome the great man by regular discussion, the Pandits resorted to the adoption of a sinister end to subserve their purpose. The host of the Pandits headed by the Maharaja himself clapped their hands signifying the defeat of the great pandit in the religious warfare. Though mortified greatly at the unmanly conduct of the Maharaja, Dayanand Swami has not lost courage. Though alone, he stands undaunted in the midst of a host of opponents. He has the shield of truth to protect him. He has issued a circular calling on the Pandits of Benaras to show which part of the Vedas sanctions idol worship. But no one has ventured to make his appearance.”
অর্থাৎ যখন কাশীর পণ্ডিতরা নিশ্চয় জেনে গেলেন যে তাঁরা শাস্ত্রার্থে স্বামী দয়ানন্দকে পরাজিত করতে পারবেন না, তখন তাঁরা নীচ অস্ত্রের আশ্রয় নিলেন এবং মহারাজার নেতৃত্বে তালি বাজিয়ে নিজেদের বিজয়ের প্রদর্শন করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবহারে দুঃখ পেলেও দয়ানন্দ সাহস হারাননি। নিজের রক্ষার্থে সত্যের কবচ ধারণ করে তিনি শত্রুসেনার মধ্যে নির্ভীকভাবে অবিচল দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বারংবার পণ্ডিতদের চ্যালেঞ্জ করেছেন—বেদ থেকে মূর্তিপূজার প্রতিপাদক একটি মাত্র মন্ত্র দেখাতে; কিন্তু কোনো কেউই সামনে আসার সাহস করেনি।
‘পাইওনিয়র’ (১৫ জানুয়ারি ১৮৭০) লিখেছিল—
“The Swami maintained that the Vedas did not inculcate idolatory and the Pandits could not produce at the time, nor have they produced since a single passage from the Vedas that could dislodge the Swami from his position. The answers of the Pandits were all evasive. They made a ‘tamasha’ of it. How can one, in the face of these facts, boldly assert that the Swami got the worst of the fight?”
অর্থাৎ মূর্তিপূজা বেদবিহিত কি না—কাশীর শাস্ত্রার্থের এটাই ছিল মূল বিষয়; কিন্তু কাশীর পণ্ডিতরা এর উত্তর না তখন দিতে পেরেছেন, না পরে আজ পর্যন্ত দিতে পেরেছেন। তাঁরা শাস্ত্রার্থকে ‘তামাশা’ বানিয়ে দিলেন। এমন অবস্থায় কে বলতে পারে যে স্বামীজি পণ্ডিতদের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন?
কিন্তু জাদু তা-ই, যা মাথার ওপর চড়ে কথা বলে। জয়-পরাজয় আপেক্ষিক শব্দ। এতটুকু সবাই জানে যে এই প্রসঙ্গের পর স্বামীজির খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর জীবনীকার দেবেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ বছর গবেষণার পর প্রমাণ-পর-প্রমাণ দিয়ে এ-তথ্যেরই সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন—
“কাশী-শাস্ত্রার্থের পর স্বামীজি প্রয়াগ, মির্জাপুর ইত্যাদি হয়ে আবার বানারস এলেন। এ বার কাশী-নরেশ আগ্রহভরে তাঁকে নিজের রাজমহলে আমন্ত্রণ করলেন এবং সিংহাসনে আসীন করে শাস্ত্রার্থকালের নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।”
এই শাস্ত্রার্থের সময় কলকাতার সুপরিচিত ব্যারিস্টার শ্রী চন্দ্রশেখর সেন তখন কাশীতেই ছিলেন। তিনি স্বামীজির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এমনই নিমন্ত্রণ কুম্ভমেলার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা এবং ব্রাহ্মসমাজের জ্যেষ্ঠ নেতা) পূর্বেও জানিয়েছিলেন। তিনি স্বামীজির প্রখর প্রতিভাকে চিনে নিয়েছিলেন। তাই কলকাতায় তাঁর আগমনের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করা হচ্ছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজি কলকাতায় পৌঁছালেন। তাঁর আগমনের সংবাদ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৭২-এর ‘ইন্ডিয়ান মিরর’-এ এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—“The redoutable Hindu iconoclast, Pandit Dayanand Saraswati, who recently discomfited the learned Pundits at Benares in an open theological encounter, and has otherwise made himself famous throughout Northern India, has come down to Calcutta, and is now staying in the suburban garden house of Rajah Joundra Mohan Tagore at Nynan. He has issued notices in Sanskrit, Hindi, Bengali and English inviting inquirers and others to come and discuss the theological subjects with him.”
“মূর্তিপূজার মহাশত্রু পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি অল্পদিন পূর্বে কাশীর পণ্ডিতদের শাস্ত্রার্থে পরাজিত করে ভারতের উত্তরাঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি এখন কলকাতায় এসে রাজা যతిেন্দ্র মোহন ঠাকুরের নগরের নিকট নৈনান উদ্যান (প্রমোদ কানন)-এ অবস্থান করছেন এবং জিজ্ঞাসু ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছেন।”
স্বামী দয়ানন্দের মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি এবং অধ্যয়নের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু তিনি তো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অবিদ্যার অন্ধকার দূর করতে এবং ভণ্ডামি, দম্ভ ও মিথ্যা আড়ম্বরের উপর আঘাত হানতে বেরিয়েছিলেন। তাই তাঁকে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতে হতো। প্রথমে তিনি সংস্কৃতেই বলতেন। এর কারণ তাঁরই কথায় এ ছিল— “ভারতে নানান ভাষা বলা হয়। তখন আমি কোন ভাষায় বলব? সংস্কৃত সমস্ত ভারতীয় ভাষার মূল, অতএব সংস্কৃতেই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত।” কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বলার ফলে তাঁর প্রচারের পরিধি বিদ্বৎসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।
সে সময় কলকাতায় একের পর এক অসাধারণ বিদ্বান, সাধক ও মহাত্মা বাস করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, মহেশচন্দ্র তর্করত্ন, তারাচন্দ তর্কবাচস্পতি—অসংখ্য নামের মধ্যে এ কেবল কয়েকটি। কলকাতার জনসাধারণের উপর তাঁর কী প্রভাব পড়েছিল, তার বিবরণ শ্রী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ ‘মহাত্মা দয়ানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী’-তে এভাবে করেছেন—
“কেশববাবুর বাড়িতে যেদিন আমি প্রথম দয়ানন্দের বক্তৃতা শুনলাম, সেদিন একটি কথাই আমি অনুভব করলাম। আমি জানতাম না যে সংস্কৃতে এমন মধুর ও রসপূর্ণ বক্তৃতা হতে পারে। তিনি এমন সহজ সংস্কৃত বলতে লাগলেন যে সংস্কৃতভাষায় যে ব্যক্তি মহামূর্খ, সেও অনায়াসে তাঁর কথা বুঝে ফেলতে পারে। আর একটি বিষয়ে আমি আশ্চর্য হলাম। ইংরেজি ভাষা থেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখে ধর্ম ও সমাজের বিষয়ে এমন উদার চিন্তা আমি আগে কখনো শুনিনি।”
প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাণী ও ব্যাখ্যা শুনে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে যেত। তারা বিশ্বাসই করতে পারত না যে এক কোপীন-কমণ্ডলুযুক্ত সন্ন্যাসী, যিনি ইংরেজি একেবারেই জানেন না, সমাজ ও ধর্মের বিষয়ে এভাবে পরিমার্জিত, উৎকৃষ্ট ও উচ্চ চিন্তার ধারক হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণ আসে। বেয়ারিলিতে মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষণ হচ্ছিল। পুলিশ–কর্তা হিসাবে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থার ভার স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (তখন মুন্সীরাম)–এর পিতা লালা নানকচন্দের উপর ছিল। তিনি স্বামীজির বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি চাইলেন তাঁর পুত্র যেন স্বামীজির বক্তৃতা শোনে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একদিন তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সফল হলেন। ভাষণ শুনে ফিরে আসার পর তরুণ মুন্সীরাম অপ্রতিবন্ধে বলে উঠল—“Oh! He reasons so well without the knowledge of English.” এ ছিল লর্ড ম্যাকাওলের শিক্ষানীতির ফল যে ইংরেজি না জানা ভারতীয়দের অশিক্ষিত ও গোঁয়ার বলে গণ্য করা হতো।
মথুরার প্রজ্ঞাচক্ষু দণ্ডী স্বামী বিরজানন্দের পর বাংলার মনীষীরা স্বামী দয়ানন্দের শক্তিকে চিনতে পারলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো সংস্কারকদের মনে বারবার এই চিন্তা উদ্ভাসিত হচ্ছিল যে স্বামীর সরাসরি জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানারূপ কুসংস্কার, অনাচার এবং অন্ধবিশ্বাসে আক্রান্ত জাতির উদ্ধার স্বামী দয়ানন্দ ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। তাই একদিন কথায় কথায় তাঁরা স্বামীজিকে বলেছিলেন— “যদি আপনি জনতার মধ্যে গিয়ে প্রচলিত দেশী ভাষায় আপনার ভাবনা তাঁদের সামনে তুলে ধরেন, তবে নিঃসন্দেহে দেশের বড় উপকার হবে। সাধারণত অনুবাদের সময় অনুবাদক আপনার মতামতকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করেন। এতে আপনার প্রতি অন্যায় ঘটে। সুতরাং আপনাকে মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি জনতার সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং তা কেবল প্রচলিত দেশী ভাষায়ই সম্ভব।”
সত্যের অনুসন্ধানী ও প্রচারক দয়ানন্দ সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই প্রচলিত দেশী ভাষা ছিল হিন্দি, যাকে তিনি ‘আর্যভাষা’ নাম দিয়েছিলেন। এই নাম দেওয়ার মূল কারণ তিনি পূণেতে দেওয়া তাঁর অষ্টম বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন—
“মানুষ–সৃষ্টির উৎপত্তির পর কিছু কাল অতিবাহিত হলে আর্য ও দস্যু—এ দুটি বিভেদ সৃষ্টি হয়—‘বিজানীহার্যাঁন যে ভ দস্যবঃ’ (ঋক্ ১।৫১।৫১৮)। এইভাবে আদিসৃষ্টিতে মাত্র দুই জাতিই ছিল—আর্য ও দস্যু। আর্য অর্থাৎ সুজ্ঞ, বিদ্বান মানুষ এবং দস্যু অর্থাৎ দুষ্ট।”
এর যৌক্তিকতা নিয়ে এখানে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এতটুকু স্পষ্ট যে বহু কারণে এই নাম গৃহীত হতে পারেনি এবং আর্যভাষার জন্য ‘হিন্দি’ নামটিই প্রচলিত হয়ে গেল। প্রচলিত হয়ে গেলে কোনো শব্দের প্রাচীন অর্থ অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে থাকে মাত্র। হিন্দি দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা ছিল। স্বামীজি হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। হিন্দিতে তাঁর প্রথম বক্তৃতা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কাশীতে হয়। বক্তৃতা অবশ্য হিন্দিতেই হয়েছিল, কিন্তু সংস্কৃত বলার অভ্যাস এবং হিন্দির অনভ্যাসের কারণে বাক্য পর বাক্য তিনি সংস্কৃতেই বলে গেলেন।
হিন্দিতে বক্তৃতা দেওয়ার ফল হলো এই যে সাধারণ মানুষ অধিক সংখ্যায় বক্তৃতা শুনতে আসতে লাগল, কিন্তু পণ্ডিতদের সংখ্যা কমতে শুরু করল। স্বামীজি ভাষাকে ভাবের আদান–প্রদানের মাধ্যম মনে করতেন। যত বেশি মানুষের কাছে নিজের কথা পৌঁছে দেওয়া যায়—এই উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দিকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি সংস্কৃত বলতেন, তখন সেটিও এত সহজ হত যে সংস্কৃতের সাধারণ জ্ঞান থাকা ব্যক্তিরাও তা বুঝতে পারতেন। দুরূহ সংস্কৃতকে তিনি ‘কাকভাষা’ বলতেন। স্বামীজির সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে আর্যসমাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনিজী ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আজমেরে অনুষ্ঠিত ঋষি–নির্বাণ অর্ধশতবার্ষিকীর উপলক্ষে স্বামীজিকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরজী মীমাংসককে বলেছিলেন যে একদিন কাশীর এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বামীজিকে বলেছিলেন—যখন আপনাকে সংস্কৃত বলতে আসে না (তার দৃষ্টিতে স্বামীজির সহজ ও প্রসাদগুণযুক্ত সংস্কৃত, সংস্কৃত ছিল না), তখন এখানে কাশীতে এসে ঝামেলা কেন পাকাচ্ছেন? এ সময় স্বামীজি শান্ত ও সহজ ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে আমি তো সেই সংস্কৃতই বলি, যা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখেছেন। যদি সেটি সংস্কৃত না হয়, তবে আমি মেনে নিই যে আমাকে সংস্কৃত আসে না, কিন্তু আপনি বলুন আপনার সংস্কৃতটি কোনটি?
এ সময় সেই নৈয়ায়িক বললেন যে আমি আপনার সঙ্গে নব্যন্যায়ে শাস্ত্রার্থ করব। যদি নব্যন্যায়ের ভাষায় শাস্ত্রার্থ করতে না পারেন, তবে নিজের পরাজয় স্বীকার করুন। এর পর স্বামীজি ‘তথাস্তু’ বলে শাস্ত্রার্থ করতে সম্মত হলেন। পণ্ডিত আর্যমুনিজী জানিয়েছিলেন যে সে সময় আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। আমারও বিশ্বাস ছিল যে স্বামী দয়ানন্দ নব্যন্যায়ের ভাষায় শাস্ত্রার্থ করতে পারবেন না। কিন্তু আমাকে (আর্যমুনিকে) আশ্চর্য হতে হল, কারণ স্বামীজি অল্প সময়ের মধ্যেই নব্যন্যায়ের ভাষায় সেই নৈয়ায়িকের ছেড়ে–ছাড়ে বাধ্য করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীজি শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনারা কি আমাদের কথোপকথন বুঝতে পেরেছেন?” শ্রোতারা না বলায় স্বামীজি বললেন, যেমন দুই কাকের লড়াই হলে কেউ তাদের ভাষা বোঝে না, নব্যন্যায়ের ভাষাও সেই রকম। তাই আমি একে কাকভাষা বলি। আমি পাণ্ডিত্য–প্রদর্শনের জন্য নয়, মানুষ যেন আমার কথা বুঝতে পারে—এই উদ্দেশ্যে সহজ সংস্কৃতই ব্যবহার করি।
কলকাতায় আসার আগে স্বামী দয়ানন্দ হিন্দির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না। গুজরাট ছেড়ে যাওয়ার পর তিনি অধিকাংশ সময় হিন্দিভাষী প্রদেশেই প্রচার করেছিলেন। সে সময় কথ্য বা চলতি হিন্দির বহু কাজচলাউ শব্দ তিনি শিখেছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যে ধরনের পরিশীলিত ভাষার প্রয়োজন, তাতে তখনও তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তার সূত্রপাত তো কাশীতে তাঁর প্রথম বক্তৃতার সঙ্গেই হয়। যে হিন্দিতে তিনি বক্তৃতা দিতেন, সেই হিন্দিই তিনি ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এর রচনায় ব্যবহার করেছিলেন।
সত্যার্থপ্রকাশের হিন্দি
যেমন আমরা আগে লিখে এসেছি, সত্যার্থপ্রকাশ-এর প্রথম সংস্করণের রচনার কাজ ১২ জুন ১৮৭৪ সালে আরম্ভ হয়েছিল। তখন পর্যন্ত স্বামীজি হিন্দি ভাষার উপর পুরো অধিকার অর্জন করতে পারেননি। তাই তাতে অজান্তেই ভাষা ও ভাব—উভয় দিক থেকেই বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। অনুশীলনের ফলে তাঁর মধ্যে পরিশোধন আসে। সেই কারণে ১৮৮২ সালে রচিত এবং ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত সত্যার্থপ্রকাশ-এর দ্বিতীয় সংস্করণকেই প্রামাণিক ধরা হয়।
স্বামীজির মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি এবং অধ্যয়নের ভাষা সংস্কৃত; ফলে তাঁর হিন্দির ওপর উভয়েরই প্রভাব ছিল। তিনি সংস্কৃতের তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি করতেন, তদ্ভব শব্দের কম। স্বামীজি পুরাণে, পুনরণি, পুরশ্চরণ, পাষণ্ড, নৈরোগ্য ইত্যাদি শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও তিনি সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুযায়ী করতেন। এ-কারণেই তাঁর হিন্দিতে আত্মা, আয়ু, সন্তান, বিজয় ইত্যাদি শব্দ পুল্লিংগ, দেবতা স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃতে নপুংসকলিঙ্গ বলে ধরা শব্দগুলোকেও তিনি হিন্দিতে পুল্লিংগের মতো ব্যবহার করেছেন, যেমন— “কোনোও দ্বিতীয় বস্তু ছিল না”, “এক প্রাচীন পুস্তক যা বিক্রমের সংবত ১৮৭২-এর লেখা ছিল”, “না পড়ে সংস্কৃত কীভাবে আসতে পারে”, “এ আগুনের সামর্থ্য”—ইত্যাদি।
গুজরাটি হওয়ার ফলে তার বহু শব্দ তাঁর ভাষায় হুবহু চলে এসেছে, যেমন— উন্দর, সসা, কুম্ভার, জমণে (ডানে)। সংস্কারবিধি-র জাতকর্ম-সংস্কারে স্বামীজি লিখেছেন— “এরপর ঘি ও মধু দু’টিকে বরোবর মিশিয়ে … শিশুর জিহ্বায় ‘ওঁ’ লিখে …।” আয়ুর্বেদের মতে ঘি ও মধু সমান পরিমাণে মিশে বিষে পরিণত হয়, কিন্তু গুজরাটিতে বরোবর শব্দের অর্থ “সমান মাত্রায়” নয়, “উচিত মাত্রায়”। “আপন সব মিলকে”—এই বাক্যগঠনও গুজরাটির প্রভাব-প্রসূত।
প্রয়োজনে, বিশেষত ইসলামের খণ্ডনের প্রসঙ্গে তিনি মজহব, ফেরেশতা, খরচ, সারকশি, বহিশ্ত, হুকুম, ইনসাফ, কেয়ামত ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রারম্ভিক রচনায় জবলौं, হোवै, রহৈ, বিবেচনা, প্রকাশনা—এরকম নামধাতুর ব্যবহার, এবং রাখতা হুঁ-এর স্থানে ঘরতা হুঁ—এর ব্যবহার, তৎসহ খুব করে হারা প্রত্যয়ের প্রয়োগ ব্রজভাষার প্রভাবের দিকেই ইঙ্গিত করে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের খণ্ডন করার জন্য স্বামীজির প্রয়োজন হয়েছিল শক্তিশালী ভাষার। এমন ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও কথ্য-রীতির প্রচুর ব্যবহার থাকে। নিজের বক্তৃতাগুলোকে প্রভাবশালী করে তোলার জন্য স্বামীজি সেগুলোর ভরপুর ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ—
“যখন সংবত ১৬১৪ সালের বছরে তোপের মারায় মন্দির, মূর্তিগুলো ইংরেজরা উড়িয়ে দিয়েছিল, তখন মূর্তি কোথায় গেল? মূর্তি তো একটা মাছির পা-ও ভাঙতে পারেনি। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ হতো, তবে এদের গুঁড়িয়ে দিত এবং এরা ছুটোছুটি করত।”
“ধিক্কার পোপ এবং পোপ-নির্মিত এই মহা অসম্ভব লীলাকে, যিনি জগৎকে ভ্রমে রেখেছেন! ভেবো তো, এই মহামিথ্যা কথাগুলো ওই অন্ধ পোপ ও ভিতরের ফাটা চোখওয়ালা তাদের শিষ্যরা শোনে এবং মানে!”
রস সৃষ্টির জন্য তিনি দৃষ্টান্ত-কথারও প্রচুর ব্যবহার করতেন। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ব্যবহারভানু-তে এমন বহু গল্প পাওয়া যায়। নিজের রচনা ও বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে যে শক্তিশালী শৈলীর জন্ম তিনি দিয়েছিলেন, তাতে মুগ্ধ হয়ে বীর বিনায়ক দামোদর সাওয়রকর লিখেছিলেন— “যে সহজ হিন্দিতে ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থপ্রকাশ রচনা করেছেন, সেই সহজ হিন্দিই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হোক।” (স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দি সেবা, পৃ. ৬৬)
স্বামী দয়ানন্দ মূলত প্রখর চিন্তক ও মননশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ গদ্যের রূপ প্রকাশ পেয়েছে ইতিবৃত্তাত্মক শৈলীতে, যা তিনি সত্যার্থপ্রকাশ-এর পূর্বার্ধে (প্রথম দশ সমুল্লাসে) প্রায়শই নিজের মতবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। বিষয়ের অনুরূপ তাঁর গভীর, গম্ভীর এবং অর্থবহ ভাষার दर्शन আমরা তাঁর ঋগ্বেদাদি ভাষ্য-ভূমিকা-তে পাই।
শ্রী বিষ্ণুপ্রভাকরের কথায়— “তাঁর (স্বামীজির) হাস্য–ব্যঙ্গপ্রধান শৈলী কোথাও অত্যন্ত কঠোর, তো কোথাও সহজ হাস্য-রসের প্রাচুর্যে মন-প্রাণকে আন্দোলিত করে তোলে। শ্রাদ্ধ-তর্পণের খণ্ডন করতে গিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ তরবারির মতো অন্তর চিরে চলে যায়।” মৃত প্রাণীদের নিতে যমদূত পৃথিবীতে আসে—এই কথার উপহাস উড়িয়ে তিনি লিখেছেন—
“যখন জঙ্গলে আগুন লাগে তখন সঙ্গে-সঙ্গে পিপীলিকা প্রভৃতি জীবের দেহ ছুটে যায়। তাদের ধরতে যদি যমের অসংখ্য গণ আসে, তবে সেখানে অন্ধকার হয়ে যাওয়া উচিত; আর যখন তারা পরস্পর জীবদের ধরতে দৌড়াবে তখন কখনো তাদের দেহে ঠোক্কর লাগবে; তখন যেমন পাহাড়ের বিশাল শিখর ভেঙে পৃথিবীতে পড়ে, তেমনি তাদের বড় বড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গরুড় পুরাণ পাঠ ও পাঠ শুনতে-থাকা লোকদের উঠোনে পড়ে যাবে, তখন তারা চাপা পড়ে মরবে, না বাড়ির দরজা বা রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে—তবে তারা কীভাবে বেরোবে ও চলতে পারবে? শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ড-প্রদান সেই মৃত প্রাণীদের কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু মৃতদের প্রতিনিধি পোপজির উদর ও হাতে পৌঁছায়। বৈতরণী পার হতে গরু যায় না, আবার প্রাণী কার লেজ ধরে পার হবে? আর হাত তো এখানেই জ্বালিয়ে বা কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে লেজ কীভাবে ধরবে?”
এরই সঙ্গে সম্পর্কিত আর-একটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ। আক্রমণ এখানে-ও আছে, কিন্তু স্বামীজি এতে হাস্যের পরশ দিয়ে এমনভাবে উপস্থিত করেন যে শ্রোতা হেসে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না—
“মথুরা তিন লোকের থেকে আলাদা তো নয়, কিন্তু সেখানে তিনটি জীব এমন লীলা-কর্তা আছে, যাদের জন্য জল, স্থল ও আকাশ—কোনো ক্ষেত্রেই কারো সুখ পাওয়া কঠিন। এক—চৌবেজি; কেউ স্নান করতে গেলে নিজের বলে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে থেকে বকতে থাকে—‘আনো ভাঙ আর লাড্ডু, খাব-খাওয়াব, যজমানের জয়জয়কার করাব।’ দ্বিতীয়—জলের কচ্ছপ; এরা কেটে খেয়েই ফেলে, যাদের জন্য ঘাটে স্নান করাও কঠিন। তৃতীয়—আকাশের ওপরে লালমুখো বানর; পাগড়ি, টুপি, গয়না এবং জুতো পর্যন্ত ছাড়ে না—কেটে খায়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে মারে, আর এই তিনজনই পোপ এবং পোপজির চেলাদের পূজ্য।”
কাশী-প্রবাসে স্বামীজির দেখা হয়েছিল ভর্তৃহেন্ডু বাবু হরিশচন্দ্রের সঙ্গে। ১৮৬৬ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কাশী-শাস্ত্রার্থে ভর্তৃহেন্ডু উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিনি স্বামীজির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দশ বছর পরে যখন তিনি স্বামীজিকে একজন সত্যিকারের দেশভক্ত, প্রখর সমাজসংস্কারক এবং হিন্দির প্রবল পক্ষপাতী রূপে চিনলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলো। দ্বিতীয়বার যখন স্বামীজি কাশীতে এলেন, তখন স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে আসা কাশীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ভর্তৃহেন্ডুজি সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে দেখা গেলেন। পরবর্তীতে তিনি স্বামীজির বাসভবনে এসে খণ্ডন–মণ্ডন নিয়ে আলোচনা করেন। ভর্তৃহেন্ডুজির সাহিত্যে স্বামীজির ভাবনার প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়। ভর্তৃহেন্ডুর ভারত-দুর্দশা, বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি এবং প্রেমযোগিনী নাটকে প্রথাগত ধর্ম এবং ভণ্ডামির তীব্র সমালোচনা পড়তে পড়তে দয়ানন্দকে তাঁর অনুপ্রেরণাসূত্র বলে মনে হয়। একটি কথা খুব কম লোক জানেন—ভর্তৃহেন্ডু হরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটক অন্ধের নগরি বিষয়গত দৃষ্টিতে তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। স্বামীজি এই কাহিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নাটক লেখার দু’ বছর পূর্বেই। নিজের গ্রন্থ ব্যবহারভানু-তে আদর্শ রাজার রূপকে হিসেবে এই কাহিনি নিজের ভাষায় লিখেছেন। নাটকটির প্রকাশ সম্বৎ ১৯৩০ (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ)-এ হয়েছিল, অথচ ব্যবহারভানু-র প্রকাশ সংবত ১৯৩৬ (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)-এই হয়ে গিয়েছিল। ভর্তৃহেন্ডু নাটক শেষ করেন সেখানে, যেখানে লোকেরা রাজাকে টিকটিকিতে দাঁড় করিয়ে দেয়; কিন্তু স্বামীজি তাকে ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর তার ছোট ভাই সুনীতিকে সিংহাসনে বসিয়ে তার সুশাসনের বর্ণনা করেন—
“আর যখন যে দেশের প্রাণীদের সৌভাগ্যের উদয় হতে থাকে, তখন সুনীতি-সদৃশ ধর্মপরায়ণ, বিদ্বান, পুত্রের মতো প্রজাপালক রাজাসহ সভা এবং ধর্মপরায়ণ পুরুষার্থী পিতার মতো রাজসম্পর্কে প্রেমাসক্ত মঙ্গলকারিণী প্রজা থাকে।”
স্বামীজির রসবোধ প্রায়শই ব্যঙ্গপ্রধান এবং শিক্ষামূলক ছিল। রাজার বেগুনের প্রশংসা করার সময় দরবারিদের প্রশংসা করা এবং রাজার বেগুনের দোষ বলার সময় দরবারিদের তার নিন্দা করা—এই কাহিনি পরে পণ্ডিত রাধেশ্যাম কথক তাঁর একটি নাটকে ব্যবহার করেছিলেন। ভর্তৃহেন্ডুজির অতিরিক্ত তাঁর প্রভাববলয়ের অন্যান্য বহু সদস্যও স্বামীজির ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। বলা হয় যে প্রতাপনারায়ণ মিশ্র কিছু সময়ের জন্য আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ভজন—“পিতু মাতু সাহাযক স্বামী সখা …”—এই কালেই রচিত। ভর্তৃহেন্ডুজি সম্পাদিত কবিবচনসুধা এবং হরিশচন্দ্র ম্যাগাজিন-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবীনচন্দ্র রায়, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রমুখের সঙ্গে স্বামীজির নামও লেখা হতো। মতবাদগত দিক থেকে স্বামীজির সঙ্গে পুরোপুরি একমত না হলেও ভর্তৃহেন্ডুজি স্বামীজির অদ্বৈত মত খণ্ডন গ্রন্থটি কবিবচনসুধা-য় দুই সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজির বিজ্ঞাপনও তাতে প্রকাশ পেত। স্বামীজির আত্মকথা খড়িবলী হিন্দিতে প্রথম আত্মজীবনী বলে মানা হয়।
প্রচলিত অর্থে স্বামী দয়ানন্দকে সাহিত্যিক বলা যায় না। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা—ইত্যাদি সাহিত্যের কোনো শাখায় প্রত্যক্ষভাবে স্বামীজির কোনো অবদান নেই; কিন্তু তাঁর প্রভাব সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। ভর্তৃহেন্ডু ও দ্বিবেদী যুগের সমস্ত রচনায় দয়ানন্দ আচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। রামধারি সিংহ দিনকরের মতে, এ-কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে— “রীতিকালের ঠিক পরবর্তী সময়ে হিন্দিভাষী অঞ্চলে যে সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক ঘটনা ঘটেছিল, তা হলো স্বামী দয়ানন্দের পবিত্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই সময়ের কবিরা শৃঙ্গার-কবিতা লিখতে বসে অনুভব করতেন যেন স্বামী দয়ানন্দ পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছেন। এই ভয়ের কারণে ছায়াবাদী কবিরাও রমণী-উপমার পরিবর্তে ‘জুঁইয়ের কুঁড়ি’ অথবা ‘বিহঙ্গিনী’র আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ভাবের প্রকাশ করতে লাগলেন।”
পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের সহপাঠী প্রেমচন্দের প্রারম্ভিক সাহিত্য দয়ানন্দ এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের চিন্তাধারার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের অধীন হয়েছিল। জয়শঙ্কর প্রসাদ এবং ম্যাথিলীশরণ গুপ্ত তাঁদের সাহিত্যে যত্রতত্র বহুস্থানে যে অতীতের গৌরবগাথা গেয়েছেন, তার মূলেও দয়ানন্দ কর্তৃক ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এ বর্ণিত প্রাচীন আর্যাবর্তের গৌরবগাঁথার বিস্তার রয়েছে এবংদিনকর-এর মতে তো ‘সাকেত’-এর রাম দয়ানন্দের ‘কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্’-এর নারা উচ্চারণ করেন। বিতর্কের জন্য পদ্য উপযুক্ত মাধ্যম নয়। তার জন্য সহজ, স্বাভাবিক, শক্তিশালী এবং লোকপ্রচলিত ভাষার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং গুজরাটি হয়েও স্বামীজীর ভাষায় শক্তিও আছে এবং স্বাভাবিকতাও আছে। তা যেমন হাসায় এবং গুঁদগুঁদ করে, তেমনই সংগ্রামের জন্য ললকারও দেয়।
ডা. রামমनोহর লোহিয়া একবার হিন্দির বিখ্যাত লেখক শ্রী বিষ্ণুপ্রভাকরকে বলেছিলেন—“কোনো দেশে মধ্যপ্রদেশের শাসন হয়, সীমান্ত প্রদেশের নয়। ভারতের মধ্যপ্রদেশগুলোর ভাষা হিন্দি, সেটিই এই দেশের রাজভাষা হবে।” ঋষি দয়ানন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে এই কথাটিই একশো বছর পূর্বে বুঝে নিয়েছিলেন এবং দয়ানন্দের নেত্র সেই দিন দেখতে চেয়েছিল যখন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এবং আटक থেকে কটক পর্যন্ত নাগরী অক্ষরের প্রচার হবে। “আমি আর্যাবর্তজুড়ে ভাষার ঐক্য সম্পাদন করার জন্যই আমার সমগ্র গ্রন্থ আর্যভাষায় লিখে প্রকাশ করেছি।” এই অনুরাগের সঙ্গেই তিনি ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এ লিখেছিলেন—“যখন পাঁচ-পাঁচ বছরের ছেলে-মেয়ে হয় তখন দেবনাগরী অক্ষরের অভ্যাস করাও, অন্য দেশীয় ভাষাগুলোরও।” ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা (বেদানাং নিত্যত্ববিচার:)–এ তিনি লিখেছেন—“যে কেউ কোনো দেশভাষা পড়ে, তারই সেই দেশভাষার সংস্কার হয়।” তাই তিনি অন্য দেশীয় ভাষার আগে দেবনাগরী অক্ষরের অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছেন।
অর্থাৎ সংঘের এই কর্তব্য হবে যে সে হিন্দি ভাষার প্রসার বাড়াবে, তার বিকাশ করবে, যাতে তা ভারতের সামাসিক সংস্কৃতির সব উপাদানের অভিব্যক্তির মাধ্যম হতে পারে এবং তার স্বকীয়তায় হস্তক্ষেপ না করে হিন্দুস্থানি এবং অষ্টম তফসিলে নির্দিষ্ট ভারতের অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত রূপ, শৈলী এবং পদসমূহ আত্মসাৎ করে এবং যেখানে প্রয়োজন বা কাম্য সেখানে তার শব্দভাণ্ডারের জন্য প্রধানত সংস্কৃত থেকে এবং গৌণত অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে তার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ধারাগুলোর সংযোজন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে হয়েছিল, কিন্তু এটি সেই আন্দোলনের ফল ছিল, যার সূচনা ঋষি দয়ানন্দ করেছিলেন ১৮৮২ সালে সরকারের নিযুক্ত হান্টার কমিশনের কাছে হিন্দির পক্ষ সমর্থনে স্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি পাঠিয়ে। হিন্দির প্রসঙ্গে এই কথা বোঝা দরকার যে, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াসে তিনি কোনো পূর্বাগ্রহ বা পক্ষপাতের অনুভূতি থেকে প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে যাননি। এর বিপরীতে, রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন অনুভব করতে করতেই তিনি হিন্দি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে সংস্কৃত দেবভাষা হয়েও বর্তমানে জনভাষা হওয়ার সামর্থ্য রাখে না। ভাষার প্রতিটি শব্দের একটি পটভূমি থাকে। তা সেই দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে গড়ে ওঠে। ভাষা বদলে গেলে সেই বিশেষ সংস্কৃতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। সংস্কৃতি সমাজের আত্মা। তা নষ্ট হয়ে গেলে সমাজ বেঁচে থাকে না।
স্বামীজি ইংরেজি বা কোনো ভাষা পড়া–পড়ানোর বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তিনি জানতেন যে ইংরেজি বিদেশি শাসকদের ভাষা এবং তাঁর দুঃখ ছিল এই যে ইংরেজি ক্রমে লোকের মাতৃভাষা হয়ে উঠছে। তাই তিনি দেশ জুড়ে আর্যসমাজগুলোকে আদেশ দিলেন যে তারা ভাষানির্ধারণের জন্য গঠিত হান্টার কমিশনের কাছে বিপুল সংখ্যায় স্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি পাঠাক। আর্যসমাজের ফতেহগড়ের স্তম্ভ বাবু দুর্গাদাসজীকে ১৭ আগস্ট ১৮৮২ তারিখে লেখা নিজের পত্রে স্বামীজি লিখেছিলেন—“এই কাজ একজনের করার নয়, আর সুযোগ হারালে সেই সুযোগ ফিরে পাওয়া দুর্লভ। যদি এই কাজ সিদ্ধ হয়, তবে আশা করি প্রধান সংস্কারের ভিত্তি স্থাপিত হবে।” স্বামীজির প্রচেষ্টায় দেশের কোণ–কোণ থেকে হিন্দিকে রাজভাষার পদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল। কানপুর থেকে পাঠানো মেমোরিয়াল থেকে জানা যায় যে প্রায় দুই লাখ মানুষের স্বাক্ষরে যুক্ত দুই শত মেমোরিয়াল হান্টার কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আর্যসমাজ মীরাটের পক্ষ থেকে ২০৪২৬/৮ আকারের ১৬ পৃষ্ঠার মেমোরিয়ালে হিন্দির ব্যবহার এবং দেবনাগরী লিপিতে শিক্ষা দেওয়ার দাবি যুক্তিসম্মত ভিত্তিতে করা হয়েছিল। একইভাবে কানপুরের বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে স্যার এল. ফ্রেন্ড কানিংস, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও अवध অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল, তাতে ভাষা কমিশনের সভাপতি হান্টার এবং সদস্য জাস্টিস মাহমুদ কর্তৃক হিন্দির পক্ষে উপস্থাপিত মতের উল্লেখ করে হিন্দিকে রাজভাষা করার জন্য এভাবে নিবেদন করা হয়েছিল যে, “যখন শিক্ষাকমিশন এলাহাবাদে মেও হল-এ অধিবেশন করছিল, তখন প্রেসিডেন্ট ডা. হান্টার সাহেবকে বলতে হয়েছিল যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দির বড় চাহিদা আছে। তখনই জাস্টিস মাহমুদ সাহেবও বলেছিলেন—‘যদিও আমি মুসলমান, কিন্তু এখানে লোকজনের মত প্রকাশ করছি—সবাই চায় যে হিন্দিই সর্বত্র প্রচলিত হোক এবং উর্দু, যা টেড়েমেড়ে লেখা হয়, আমার মতে না থাকাই ভালো।’”
আমরা এখানে আর্যসমাজ মীরাট এবং কানপুরের বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পাঠানো দুটি স্মারকলিপি উদ্ধৃত করছি। এই স্মারকলিপিগুলো পণ্ডিত ভাগবদন্তজী সম্পাদিত ‘ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র এবং বিজ্ঞাপন’ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে পৃষ্ঠা ১৬০ থেকে ১৭৪ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। আর্যভাষাকে সরকারি কাজে প্রচলিত করার জন্য ঋষি দয়ানন্দের প্রেরণায় পাঠানো…ঋষি দয়ানন্দের প্রেরণায় আর্যভাষাকে রাষ্ট্রকার্যে প্রবৃত্ত করার জন্য নানা স্থান থেকে রাজঅধিকারীদের কাছে দুই শত মেমোরিয়াল পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমরা একটি মেমোরিয়াল এবং একটি নিবেদনপত্রের প্রতিলিপি নীচে দিচ্ছি, যাতে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে রাষ্ট্রকার্যে আর্যভাষা হিন্দিকে প্রচলিত করার ক্ষেত্রে আর্যসমাজ এবং তার প্রবর্তক (সে সময়ে, যখন এ দিকে কারও মনোযোগও যায়নি) কত মহান কাজ করেছিলেন। আজ হিন্দির ইতিহাসে আর্যসমাজ এবং তার প্রবর্তকের হিন্দি-প্রচারের কাজের উল্লেখ মাত্র তিন–চারটি পংক্তি লিখে শেষ করে দেওয়া হয়। আমাদের মতে এর প্রধান কারণ আর্যবিদ্বানদের এই ক্ষেত্রে (ইতিহাস-লেখন) উদাসীন থাকাই, নইলে কোনো হিন্দির ইতিহাস-লেখক এমন সাহস দেখাতে পারতেন না। ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যে বহু খণ্ডে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা থেকে প্রকাশিত ‘হিন্দির বৃহৎ ইতিহাস’-এ ঋষি দয়ানন্দ কর্তৃক করা হিন্দি ভাষার প্রচারের বিষয়ে কিছুই লেখা হয়নি।
আর্যসমাজ মীরাট কর্তৃক প্রেরিত মেমোরিয়াল
(মুখপত্র)
ও৩ম্
মেমোরিয়াল
অর্থাৎ নাগরী প্রচারক নিবেদন-পত্র
শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাতিবিজ্ঞ মহামান্যবর এডুকেশনাল কমিশনের প্রধানাধ্যক্ষক শ্রীরামান ডক্টর হান্টার সাহেবের সেবা-সমীপে অতিশয় বিনয়পূর্বক প্রার্থনা।
১. পরবর্তী কানপুর থেকে প্রেরিত নিবেদন-পত্রের তৃতীয় প্যারাগ্রাফ থেকে প্রকাশ পায় যে দুই-শো মেমোরিয়াল শিক্ষা-কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছিল।
২. এই মেমোরিয়াল ২০/২৬ আট-পেজি আকারের ১৬ পৃষ্ঠায় লিথোতে ছাপা হয়েছে।
যদিও আজ পর্যন্ত যত দেবনাগরী-প্রচারক প্রार्थনাপত্র অর্থাৎ মেমোরিয়াল আপনার সেবায় পাঠানো হয়েছে, সম্ভব যে তাদের তুলনায় এই নিবেদন-পত্রটি খুবই তুচ্ছ হবে; কিন্তু न्यायাধীশ মহাশয়দের জন্য সামান্য ইঙ্গিতমাত্রই অনেক হয়, তাই আশা করা যায় যে এই ছোট্ট নিবেদন-পত্রটির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া হবে এবং বিবেচনার সঙ্গে যথার্থ ও প্রজাহিত সম্মতি প্রদান করা হবে।
প্রশ্ন—যে দেশে যে ভাষার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়, তা কি সেখানে সকল লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযোগী?
উত্তর—যে দেশে যে ভাষার দ্বারা সেখানে লোকদের শিক্ষা দেওয়া হবে, তা সেখানে লোকদের প্রাকৃত ও স্বাভাবিক ভাষা হওয়া উচিত; অর্থাৎ সকল নারী-পুরুষ যেন ভেতরে-বাইরে, রাত্রিদিন বিনা চিন্তাভাবনায় সেই ভাষাই বলতে ও চলতে পারে। কারণ সেই ভাষার কেবল অক্ষর-অভ্যাস হয়ে গেলে কী শিশু ও যুবা সকল নারী-পুরুষ দ্রুত শব্দ বার করতে ও পড়তে পারবে। এর কারণ এই যে, বোলচাল তো সেই-ই, যা মা-বাবা, ভাই-বান্ধব ও সঙ্গীদের থেকে শুনে-শুনে বলা হয়েছে; কেবল অক্ষর শেখা এবং তাদের জোড়-তাড়ে শ্রম করাই বাকি থাকবে। কিন্তু সেই মাতৃভাষা যেন শুধুমাত্র কথাবার্তা ও লেখালেখির নির্বাহমাত্রই না হয়, বরং তাতে সামনে অগ্রসর হওয়া এবং বিদ্বান হওয়ার জন্য কাব্য ও বিদ্যার বিস্তৃত পথও থাকুক। এখন থাকে অক্ষর—সে মাতৃভাষার অক্ষর এমন হওয়া উচিত যা সহজলভ্য হয় এবং যাতে সব ধরনের শব্দ লেখা যায় এবং পড়তে গিয়ে যেরকম লেখা আছে হুবহু তেমনই আসে এবং এক জনের লেখা অন্য জন নির্ভুল ও শুদ্ধভাবে পড়ে নিতে পারে।
এখন এই বিবেচনা করা যে, এই দেশের প্রাকৃত ভাষা কোনটি—যদিও এই আর্যাবর্তে বাঙালি, গুজরাটি, মরাঠি প্রভৃতি বহু ভাষা ক্রমে বঙ্গ, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রাদি দেশে বলা হয়, কিন্তু আমাদের পশ্চিমোত্তর দেশে প্রধান নাগরী ভাষা, যাকে এখন লোকেরা হিন্দি বলতে আরম্ভ করেছে,ই প্রচলিত ও কথ্য। এবং এটিকে বাদ দিয়ে অবধ, পাঞ্জাব ও মারওয়ারাদি প্রদেশেও এই ভাষাই কোনো কোনো শব্দের উলটপালট ও উঁচুনিচু স্বরের ভেদে বলা হয়, এবং এই কারণে এক জনের বোলচাল আরেক জন ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে। এবং এই মাতৃভাষা এমন সুগম যে কয়েক প্রদেশ অতিক্রমের পরবর্তী প্রদেশের লোকেরাও বাঙালি, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভাষা না পড়েও, না শিখেও বুঝে নেয় এবং কেবল মেলামেশার দ্বারা স্পষ্ট করে বলতে শুরু করে। এ হলো এর সুগমতা-সরলতার অল্প-স্বল্প বর্ণনা, এখন এর পূর্ণতার ব্যাখ্যা শুনুন—এতে কী সুন্দর সুন্দর কাব্য সরল-সোজা কথাবার্তার ভাষায় রয়েছে, যে বড় বড় প্রসিদ্ধ ভাষার কবিতাও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। একটু সুর, তুলসী, কেশব ও বিহারী প্রভৃতি কবিদের কবিতার দিকে লক্ষ্য করুন—কী আশ্চর্য অলংকার এবং গূঢ় অভিপ্রায় এই ভাষায় বাঁধা ও সমন্বিত হয়েছে। গদ্যও এই ললিত ভাষার অত্যন্ত রসময়। প্রেমসাগর, রাজনীতি, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখলেই তার উৎকৃষ্টতা ও উচ্চতা ভালোমতো প্রমাণিত হয়।
গণিত, ভূগোল, ইতিহাস এবং চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং প্রতিদিন রচিত হতে থাকে। সুতরাং এই প্রাকৃত ভাষা সম্পূর্ণরূপে সবার পড়া ও লেখার উপযুক্ত।
এখন থাকে সেই অক্ষর কোনগুলি, যাতে এই ভাষা ও অন্য ভাষার শব্দের পূর্ণাঙ্গ নির্বাহ হতে পারে এবং সেগুলি যথাযথভাবে লেখা-পড়া যায় এবং লেখক-পাঠক কোথাও থেমে বা আটকে না যায়।
এই অনুপম ও অতুলনীয় অক্ষরগুলি সংস্কৃত ভাষার, যা পৃথিবীমাত্রের সমস্ত অক্ষরের চেয়ে উত্তম ও সুন্দর। তাদের মধ্যে প্রধানত এই বিষয়টি আছে যে প্রতিটি অক্ষরের আকৃতি পৃথক ও স্বতন্ত্র। পড়া-লেখায় বিভ্রান্তি কখনোই ঘটে না এবং এমন সরল ও সহজ যে দুই-চার দিনের অভ্যাসেই আয়ত্ত হয়ে যায়। যদিও সংস্কৃত ভাষায় তেষট্টি অক্ষর আছে, তন্মধ্যে বাইশটি স্বর, তেত্রিশটি ব্যঞ্জন, চারটি অযোগবাহ এবং চারটি “যম” আছে; কিন্তু আমাদের প্রাকৃত নাগরী ভাষায় অধিকাংশে বারো স্বর, তেত্রিশ ব্যঞ্জন, দুই অযোগবাহ বিসর্গ ও অনুস্বার এবং এক “যম” সানুনাসিক অর্থাৎ মোট আটচল্লিশটি অক্ষরই কাজ দেয় এবং এই অক্ষরগুলির দ্বারা এই ভাষা ও অন্যান্য ভাষার শব্দের যথোচিত নির্বাহ সম্ভব। এবং এই মনোরম অক্ষরগুলির সর্বোচ্চ গুণ এই যে, এগুলিকে কমবেশি করে কিছু-কে-কিছু বানানো যায় না।
১. বর্ণগুলোর এই বিবরণটি বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষার অনুযায়ী করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সানুনাসিক ‘অনুনাসিক’ কোনো স্বতন্ত্র বর্ণ নয়, বরং তা স্বরের একটি বিশেষ উচ্চারণমাত্র। একে সূচিত করার জন্য স্বরের উপরে “ঁ” এর মতো চিহ্ন দেওয়া হয়, যা কোনো স্বতন্ত্র বর্ণের চিহ্ন নয়। ‘যম’ স্বতন্ত্র বর্ণ।
মুসলমানদের এই দেশে আসা এবং ওঠাবসার ফলে আরবি–ফারসি ভাষার যে শব্দগুলি নাগরীভাষার সঙ্গে মিশে গেছে, সেইকেই লোকেরা উর্দু বলতে শুরু করেছে। কিন্তু এই উর্দু প্রধানত দিল্লি, লখনউ প্রভৃতি দুই-চারটি বড় বড় নগরে, যেখানে পূর্বে বাদশাহরা বাস করতেন, সেখানে বলা হয়। সেখানেও ফারসি-পড়া-লেখা জানা লোকেরাই মূলত বলেন; বাকিরা সকল নারী-পুরুষ নিজেদের মাতৃভাষাই বলেন। আমাদের ভাষায় পারস্পরিক মিলন-যোগসূত্রে যদি কোনো আরবি–ফারসি কিংবা ইংরেজি শব্দ এসে পড়ে এবং সকলের মধ্যে প্রচার পায়, তবে তা বলা ও লেখা এমন কোনো দোষের বিষয় নয় যাতে কোনো ক্ষতি ঘটে। কিন্তু হ্যাঁ, দোষ এবং ক্ষতির কথা হল এই যে, লোকদের মনে এই ধারণা প্রবেশ করছে যে ফারসি হলো আয়না; তা না পড়ে লিখে মানুষের কথাবার্তা ও চরিত্র নাকি শুদ্ধ ও সংবরিত হয় না। তাই তারা ফারসি পড়তে-পড়তে তাদের লেখায় খাঁটি আরবি–ফারসি শব্দ গুচ্ছগুচ্ছ করে ঢোকায় এবং যতটা সম্ভব নিজের ভাষার সরল-সোজা শব্দের পরিবর্তে আরবি–ফারসির বাঁকা-টুংকা শব্দ খুঁজে এনে বলে ও লেখে। এমনকি ইযাফত ও তর্কীব ইত্যাদিও আরবি–ফারসিরই প্রয়োগ করে।
এই ফারসির নাম নিয়ে ঋণখোরেরা নিজেদের কথা-বার্তায় বড় বড় লুগতই আরবি–ফারসির বলে থাকে, যেগুলো সাধারণ মানুষ বোঝে না এবং বহুবার বলে ওঠে—“তোমার এই ফারসি তো আমাদের বুঝে আসে না, দেশি ভাষায় বললে বুঝি।” কিন্তু তাদের লেখা জুলেখা, বাহার-দানিশ ও মাঘোরামের চেয়ে কম হয় না—যার বোঝা তো দূরের কথা, অন্যরা আনন্দও পায় না। তারপর বলুন তো, এই নামমাত্র উর্দু, যা প্রকৃতপক্ষে ফারসির ঘোমটা টেনে আছে, মানুষ তাকে কীভাবে সহজ ও সুগম দেখতে পারে? কখনোই না।
ভেবে দেখুন, মানুষের সারা জীবন যদি শুধু উর্দুর জন্য ফারসি পড়তে পড়তেই কেটে যায়, তবে পরে আর কী করবে? আর সেই ফারসিটাই বা কেমন—যাতে উপর উপর এবং মুখ দ্যাখা কথাবার্তা তৈরি করা, চাটুকারিতা, তোষামোদি এবং রসাল কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নেই।
এর ফল এখানে যে সব মানুষের উপর পড়েছে, তা অবশ্যই বিচক্ষণ মানুষ জানেন। হয়তো এই উর্দু, যার ফলে বড় ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে, যদি সরকারি দফতরে লেখা-পড়া না হতো তবে কখনো প্রচার পেত না এবং যেমন আজ চাকরির লোভে মানুষ পড়ে, তেমনভাবে নামও নিত না। তাতেও উর্দু জানা লোকেরা নাগরী জানা লোকদের তুলনায় একেবারে সওয়া (শতভাগের এক-চতুর্থাংশও নয়) অংশ নয়। এর কারণ একই—খাঁটি কথ্যভাষা এবং অক্ষরের সহজতা। এই উর্দু ভাষার দফতরগুলোতে প্রচার হওয়ায় বড় মারাত্মক ক্ষতি এই যে, সাধারণ মানুষ তাদের মামলা-মোকদ্দমার লেখাপড়া শুনে গঙ্গা–বধিরের মতো মুখ চেয়ে থাকে; অনেক চেষ্টা করে কান পাতলেও বোঝে না। যেখানে কোনো পড়াশোনা জানা ব্যক্তি কোনো কারণবশত বা উদ্দেশ্যে নিজের মাথা ঘামিয়ে শত শত উদাহরণ দেয়, তখন গিয়ে উল্টো-সিধে অর্থ কিছুটা বুঝলে বোঝে, নইলে নয়—অবশেষে যেমন কেউ বলেছে তেমনই মেনে নেয়। যারা পক্ষপাতিত্ব কাজে না লাগান, সেই সব উকিল, মুখতিয়ার এ ব্যাপারের সাক্ষ্য দিতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে যখন কোনো সরকারি কাগজ বা চিঠিপত্র যায়, তখন অসহায় তারা তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যদি ভাগ্যক্রমে ফারসি জানা কেউ পাওয়া যায় তো পাওয়া যায়, না হলে মুসলমানদের এই দেশে আগমন এবং ওঠাবসার ফলে আরবি–ফারসির যে শব্দগুলি নাগরীভাষার সঙ্গে মিশে গেছে, সেটিকেই লোকেরা উর্দু বলে ডাকে। কিন্তু এই উর্দু প্রধানত দিল্লি, লখনউ প্রভৃতি দুই-চারটি বড় নগরে বলা হয়, যেখানে পূর্বে বাদশাহরা বাস করতেন। সেখানে যদিও ফারসি-পড়া-লেখা জানা লোকেরা কথাবার্তা চালায়, বাকি সবাই নিজের মাতৃভাষায় কথা বলে। আমাদের ভাষায় পারস্পরিক সংযোগে যদি কোনো আরবি–ফারসি বা ইংরেজি শব্দ এসে যায় এবং সকলের মধ্যে প্রচার পায়, তবে তা বলা বা লেখা কোনো ক্ষতির বিষয় নয়। কিন্তু ক্ষতির বিষয় হল—লোকদের মনে ধারণা প্রবেশ করছে যে ফারসি জানা ছাড়া মানুষের কথাবার্তা ও চরিত্র উন্নত হয় না। তাই তারা ফারসি পড়তে পড়তে লেখায় খাঁটি আরবি–ফারসি শব্দ ঢুকায় এবং যেখানে সম্ভব, নিজের ভাষার সরল শব্দের পরিবর্তে বাঁকা-টুংকা আরবি–ফারসি শব্দ ব্যবহার করে। এমনকি ইযাফত ও তর্কীব ইত্যাদিও আরবি–ফারসিই ব্যবহার করে।
ফারসির নাম নিয়ে ঋণখোরেরা নিজেদের কথাবার্তায় বড় বড় লুগত ব্যবহার করে, যা সাধারণ মানুষ বোঝে না এবং বলে—“তোমার এই ফারসি আমাদের বোঝা যায় না।” তবে তাদের লেখা জুলেখা, বাহার-দানিশ ও माधোরামের তুলনায় কম নয়; বোঝাও কঠিন, আনন্দও কম। এই নামমাত্র উর্দু, যা প্রকৃতপক্ষে ফারসির ঘোমটা টেনে রেখেছে, মানুষ কীভাবে সহজ ও সুলভ মনে করতে পারে? কখনোই না।
মানুষ যদি সারা জীবন শুধু উর্দুর জন্য ফারসি পড়তে কাটায়, তাহলে পরে আর কী করবে? এবং সেই ফারসিই এমন, যেখানে উপরের দিকে ও মুখ দেখানো কথাবার্তা, চাটুকারিতা, তোষামোদি ও রসিক কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নেই।
এর ফলে এখানে যে মানুষদের ক্ষতি হয়েছে, তা বিচক্ষণ লোকেরা জানেন। হয়তো এই উর্দু, যার কারণে বড় ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে, যদি সরকারি দফতরে লেখা-পড়া না হতো, তবে কখনো প্রচার পেত না। যেমন আজ চাকরির লোভে মানুষ পড়ে, তেমনভাবে নামও নিত না। তবুও উর্দু জানা লোকেরা নাগরী জানা লোকদের তুলনায় একেবারে সামান্য। কারণ—খাঁটি কথ্যভাষা এবং অক্ষরের সহজতা।
এই উর্দু ভাষার সরকারি প্রচারের ফলে বড় ক্ষতি হল—সাধারণ মানুষ মামলা-মোকদ্দমার লেখাপড়া শুনে গঙ্গা-বধিরের মতো মুখ চেয়ে থাকে; কান দিলেও বোঝে না। যেখানে পড়াশোনা জানা কেউ কোনো কারণে বা উদ্দেশ্যে মাথা ঘামিয়ে শত শত উদাহরণ দেয়, তখন কেবল কিছুটা অর্থ বোঝে, না বোঝে নয়। অবশেষে যেমন কেউ বলেছে তেমনই মেনে নেয়। যারা পক্ষপাত কাজে ব্যবহার করে না, সেই সব উকিল-মুখতিয়ার এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারে। সাধারণ মানুষের কাছে যখন কোনো সরকারি কাগজ বা চিঠি পৌঁছায়, তারা অসহায় হয়ে তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভাগ্যক্রমে ফারসি জানা কেউ যদি পাওয়া যায়, তবে পাওয়া যায়; না হলে—যত্নের পরও যখন কোনো শব্দ পড়তে যায় না, তখন তাদের স্থলে ‘ও’ বা ‘ক’ বলে দেওয়া হয়। এই অক্ষরগুলিতে যখন ফারসিরই এমন দুরবস্থা, তাহলে অন্য ভাষার কথা কী—যা লেখা পর্যন্ত আসে না। যদিও ফারসিপ্রেমীরা এখানে কথ্য ভাষার জন্য ‘টে, ডাল, ডে’ নামক নতুন অক্ষর উদ্ভাবন করেছেন, তবুও এখানকার ভাষার যথাযথ কার্যকারিতা সম্ভব হয়নি। তাই তারা বহু স্থানীয় কথার শব্দ নিজেদের মতো করে বানিয়েছে, যেমন—ব্রাহ্মণকে ‘বিরহমন’ এবং দক্ষিণকে ‘দকন’ বলা। শেষ পর্যন্ত এই লিখিত খতগুলোতে শুধু সেই শব্দই দেখা যায় যা মুখে চড়ে থাকে, এবং যেগুলি প্রায়ই একইভাবে লেখা হয়, দ্বিধায় ফেলে। যেখানে অন্য ভাষার শব্দ আসে এবং মুখ থেকে কিছুটা কিছুটা উচ্চারিত হয়, যেমন—নাম, গ্রাম, স্থান, সেগুলো কখনো সঠিকভাবে পড়া যায় না।
ফারসি অক্ষর ও তাদের লিখনশৈলীর এই দুর্বলতার কারণে এই দেশের মানুষের বড় ক্ষতি হয়েছে। প্রতিনিয়ত নতুন জাল তৈরি হয়, মানুষ দিনরাত প্রতারণার শিকার হয়। অল্প অল্প লিখতে-পড়তে সাহায্যের জন্য ছটফট করে বেড়ায়। নাম উঠানো ও কলম ধরানোর জন্য প্রতিনিয়ত হিড়িক পড়ে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের নিয়ম হল—যখন শিশুর বয়স পাঁচ-সাত বছর, তখন তাকে প্রথমে মাতৃভাষা শেখানো হয়, এবং যখন সে এতে পারদর্শী হয়ে যায় ও গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যা শিখেছে, তখন তার রুচি অনুযায়ী অন্য ভাষা ও বিদ্যা শেখানো হয়।
এখানে কিছুদিন ধরেই এক অদ্ভুত চলন শুরু হয়েছে—শিশু যতক্ষণ মা-বাবার কোলে খেলছে ও তুতলাচ্ছে, ততক্ষণ মাতৃভাষা শেখে; যখন পড়াশোনার যোগ্য হয়, তখনই মোল্লা ও মিয়াদের কাছে তুলে দেওয়া হয়। আর সেই গান যে—
"কারিমা বাবখসায় বর হাল মা। কি হস্তম আসীরে কমদে হাওয়া।"
গানটি কেবল জিহ্বা ভাঙা এবং গলা ফাটানোর জন্যই হয়, কারণ সেই অবস্থায় অন্য ভাষা শেখা বা তার বোঝা সম্ভব নয়। ফলে শিশুর মন শিথিল ও মন্দ হয়ে নীচু অবস্থায় থাকে। নিজের ভাষার মতো কিছু শেখার সুযোগ হয় না, অন্য ভাষা শিখলেও মারমুখীভাবে। শেষমেষ দুটি ভাষার সারমর্ম এতটুকুই থাকে—
"অয় আকরিম বযশীশ কর উপরে হাল আমাদের কে।
কি হুঁ আমি কায়দি হাওয়া এবং হাভিস কা।"
এটাই মুন্সিদের সমগ্র জীবনব্যাপী শ্রমের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, যা তারা আদালত ও দফতরে ছড়িয়ে রেখেছে। এতো করেই তারা নিজেদের বড় মনে করে এবং মনে করে জ্ঞান হয়েছে, আর ফারসিতে অহংকারভরে পড়ে—
"কলম গোয়দ কি মন শাহে জেহানম। কলম কশ রা বদৌলত মে রসানম।"
কৌতুক হল—ছোট ছেলেরা বুকের ওপর হাত রাখে, রসিক ছড়া পড়ে এবং ঠান্ডা শ্বাস নেয়, নিজেকে সাজাতে ও ওরশ তৈরি করতে যৌনকর্মীকে ছাড়িয়ে দেয়। ভাবার বিষয়—যে ভাষার এমন খারাপ বৈশিষ্ট্য, তা কি শিক্ষাদানের বা প্রচারের যোগ্য? কখনোই না।
নিঃসন্দেহে, এমন ভাষা যার এমন কষ্টকর বৈশিষ্ট্য এবং খাঁটি দুর্বলতা আছে, মানুষ কেন তা পড়ে ও শেখায়? এর সমাধান হল—নাহি সরকারি কাজকর্মে ব্যবহৃত হয়, না মানুষ তা গ্রহণ করে। হয়তো মনে না হয়, তবে দেখুন, যারা তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করতে চায়, তারা সবাই নাগরী পড়ায়। আর কেউ যদি বলে, “আপনি তো উর্দু-ফারসি জানেন, মেয়েদের কেন শেখান না?”—তাহলে তারা বলবে, “তাদের কোন চাকরি করার দরকার নেই।” তারা জানে, উর্দু-ফারসি পড়ে ছেলেদের যা হয়েছে, মেয়েদের কী হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা করতে চাই না, তাদের জন্যই তা করতে হয়। এটি প্রমাণ করে, উর্দু ও ফারসি শুধু তারা শেখে ও শেখায়, যাদের আদালত ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক থাকে। বাকিরা প্রথমে নিজেদের মাতৃভাষা শেখে।
এই দেশে হাজারো চাটশালা ও পাঠশালা আছে, যেখানে লাখো ছেলে নাগরী পড়ে। যদি মাতৃভাষায় আগ্রহ না থাকত, তাহলে কে পড়ত? এই লেখার উদ্দেশ্য নয় যে মাতৃভাষা ছাড়া কেউ কিছু পড়বে না, বরং মূল লক্ষ্য—প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের প্রধান নাগরীতে হোক, এরপর যাঁর যা রুচি, সেই অনুযায়ী সংস্কৃত, ইংরেজি ও আরবি ইত্যাদি শেখানো হোক। এবং যতক্ষণ নিজের ভাষায় পারদর্শী না হয়, ততক্ষণ অন্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। এই নিয়ম ছাড়া যত ক্ষতি হয়েছে, তার সাক্ষী প্রায় ফারসি ও ইংরেজি ভাষাভিত্তিক কথাবার্তা ও অনুবাদই। হ্যাঁ, এর বাস্তবায়ন সম্ভব, যদি সরকারি দফতরে নাগরীর প্রচার হয়। শেষ পর্যন্ত, নাগরী ভাষা ও তার অক্ষর থেকে জনগণ যে সুবিধা পায়, তা সকলেই জানে। বিদেশিরাও তা প্রশংসা করে এবং পড়ার জন্য উৎসাহী। এমনকি ইংল্যান্ডের কমিশনাররা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উর্দুর স্থলে নাগরীকে প্রয়োজনীয় ও প্রধান ঘোষণা করেছেন। তাই আশা করা যায়, আমাদের প্রার্থনাও অবশ্য সফল হবে।
আলমিতি
আর্যসমাজ মেরঠের একজন সভাসদ লিখেছেন। মিতি—মাঘ বদি ১২ রবিবার, সম্বত্ ১৬৩৬ বিক্রম.
‘নিবেদন-পত্র’
অশেষগুণসম্পন্ন মহামান্য মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত সার আলফ্রেড কামিন্স, সি, বি, সি, আই, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ ও অবধের লেফটিন্যান্ট গভর্নর মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু।
সাবিনয় নিবেদনমিদান—
আমরা রইস প্রার্থীরা জেলা কানপুরের পক্ষ থেকে আপনার কাছে বিনয় করি যে, আমাদের দীন দুর্দশার প্রতি দয়া করে মনোযোগ দিন! ন্যায্যশীল সরকারের ইচ্ছা যে, প্রজাকে কোনোভাবে কষ্ট না হোক। আমাদেরকে বোকা না বানানো এবং আমাদের সাধারণ ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই ন্যায্যশীল সরকারের এবং ইংরেজ সরকারের মত। আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি যখন সরকার থেকে শিক্ষা-কমিশনের বসার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এটি ভেবে যে, এখন আমাদের দীন দশার প্রতি শিক্ষা কমিশন যথাযথভাবে আপনার কাছে মত প্রকাশ করবে।
কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের সম্পর্কে, অর্থাৎ আমরা যারা আপনার প্রার্থীরা, আমাদের ডাকের প্রতি কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এখানে হিন্দি-উর্দুর স্থলে, অর্থাৎ দেওনাগরী অক্ষরের ফারসি অক্ষরের স্থলে, সব সরকারী দফতরে হওয়া, সেটিই আমাদের ডাক ছিল। যে সব অসুবিধা উর্দু চালু থাকার কারণে হয়, তা বর্ণনা করার জন্য আপনার সামনে, যেটি আপনি নিজেই ভালোভাবে জানেন, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আমাদেরকে উর্দু থেকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। এজন্য আমরা আপনার কাছে, যিনি আমাদের পিতার সমান, সংক্ষেপে বলছি—
১. এই নিবেদনপত্র নীল রঙের ফুলস্কেপ কাগজে ৪ পৃষ্ঠায় গ্রেট টাইপে মুদ্রিত।
(১) ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসপ্যাচে এই বিষয়টি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষকে তাদের নিজের কথ্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। উর্দু, যা আজও উত্তর হিন্দুস্তানে শিক্ষাদানে ব্যবহার হয়, তা মানুষের কথ্য ভাষা নয়। আমাদের মাতৃভাষা এবং দেশীয় ভাষা, যা আমাদের ঘরে-বাড়িতে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে নিয়মিত ব্যবহার করে, তা হলো হিন্দি, কিন্তু উর্দু নয়। আমাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা হিন্দিতেই হওয়া উচিত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা ছড়াতে পারে।
(২) হিন্দি, অর্থাৎ আমাদের কথ্য ভাষা, যা দেওনাগরী অক্ষরে লেখা হয়, তা বাঙালি, গুজরাটি, মারাঠি ভাষার মতো সংস্কৃতের একটি শাখা। কিন্তু বাঙাল, গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রে প্রত্যেক ভাষা সরকারি দফতরে প্রচলিত এবং সাধারণ মানুষকে এ ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, এখানে ও দফতরে লিখা-পড়া হিন্দিতেই হোক।
(৩) শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় যে, হিন্দির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চাওয়া মানুষের সংখ্যা বেশি, কারণ দুই লাখ মানুষের অনুমানের ভিত্তিতে দুই শতাধিক মেমোরিয়াল এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-কমিশনের কাছে পৌঁছেছে। উর্দু সাধারণ মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হয় কারণ দেশের দফতরে উর্দু লেখা-পড়া হয় এবং উর্দুর প্রচার শুরু হয়েছিল তখন থেকেই যখন এটি দফতরের ভাষা হিসেবে স্থির করা হয়।
(৪) হিন্দিতে অনেক সহজ শব্দ রয়েছে যা সকলেই বুঝতে পারে এবং দেওনাগরী অক্ষরে লেখা হয়। উর্দুতে অর্ধেকের বেশি শব্দ আরবি ও ফারসির, যা সকলের বোঝার বাইরে। কেবল ফারসি এবং আরবি জানেন এমন মানুষই বোঝেন, এবং এগুলো ফারসি-আরবি অক্ষরে লেখা হয়।
(৫) মুসলমান শাসনের আগে এখানে দেওনাগরী অক্ষরেই কাজ করা হতো।
(৬) যদিও মুসলমান শাসক ও ইংরেজ সরকার উর্দুকে দফতরের ভাষা বানিয়ে পাঠশালা স্থাপন করে এবং এর প্রচারের বড় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে, তবুও সাধারণ মানুষ এটিকে গ্রহণ করেনি এবং করতে চায় না। কেবল বড় শহরে কিছু মানুষ উর্দু বললেও, বাকি সব হিন্দু-মুসলিম গ্রাম ও kasba-তে হিন্দি কথ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো সরকারি কাগজ উর্দুতে তাদের কাছে পৌঁছায়, তখন তা পড়াতে গ্রাম-গ্রাম ঘুরে বেড়াতে হয়। হিন্দিতে এই কষ্ট কখনো হয় না, কারণ প্রতি গ্রামে কমপক্ষে একজন দুজন মানুষ হিন্দি পড়াশোনা জানে।
(৭) শিক্ষা সংক্রান্ত ডিরেক্টরের রিপোর্ট এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত বই থেকে স্পষ্ট হয় যে, এখনও লাখ লাখ হিন্দু, মুসলমান, সহস্রাধিক খ্রিস্টান হিন্দি পড়ে। বড় শহরে উর্দু পড়ে কেবল তারা যারা আদালতে চাকরি করতে চায় বা যাদের কাজ আদালতের সঙ্গে যুক্ত।
(৮) খ্রিস্টানদের বই দেওনাগরী অক্ষরে উপদেশ দেওয়ার জন্য তৈরি। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, হিন্দি জানেন এমন মানুষ অনেক।
(৯) প্রেসিডেন্ট শিক্ষা কমিশন, শ্রীমান হান্টার সাহেব, লাহোরে বক্তৃতায় বলেছেন যে, মেমোরিয়ালগুলি অধিকাংশ হিন্দির জন্য দেওয়া হয়েছে এবং বিপরীতে খুব কম। যারা হিন্দির জন্য দিয়েছে...যারা মেমোরিয়াল দিয়েছে, তারা সাধারণ মানুষ; এবং যারা উর্দুর জন্য দিয়েছে, তারা সরকারি কর্মচারী। যাদেরকে সরকার আমলা ক্লাস বলে। এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, আমরা সকলেই হিন্দি চাই।
(১০) মফসসিলের যে তহসিলি ও হালকা-বন্দি স্কুল রয়েছে, সেখানে অধিকাংশ হিন্দিতেই পড়ানো এবং লেখা হয়। এ বিষয়ে ইন্সপেক্টর ও স্কুল ডিরেক্টরের কাছে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, এবং সাধারণ স্কুলেও অধিকাংশ শিক্ষা হিন্দিতেই দেওয়া হয়। তাই আমরা প্রার্থনা করি, যদি সরকার দফতরে হিন্দি চালু করার নির্দেশ দেয়, তবে বড় উপকার হবে; নইলে যে অর্থ এই মাদরাসায় খরচ হয়, তা ব্যর্থ যাবে।
(১১) সরকার চায় যে, তার শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। সরকার চায় প্রজারা সবাই পড়াশোনা জানুক, গ্রামের সাধারণ মানুষও আদালতের কাগজ পড়তে পারে যেমন এখন আদালতের লোক পড়ে। তাই সরকারের এই উদ্দেশ্য হিন্দিকে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বানিয়ে, ইংরেজির সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নির্ধারণে সফল হতে পারে। সাধারণ শিক্ষা উর্দুর মাধ্যমে কখনো ছড়াতে পারবে না।
(১২) দফতরে ফারসি ও আরবি অক্ষরের স্থানে দেওনাগরী অক্ষর বসানোর যতটা প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, তার একটি বড় কারণ হল, যখন দফতরে দেওনাগরী প্রচলিত হবে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ার এক কারণ হবে। দফতরে দেওনাগরী অক্ষরের প্রচার সহজে করা সম্ভব। সেই একই কর্মকর্তা, সেই অনুমোদন, সেই কর্মচারী হিন্দিতে লেখা কিছু শিখতে ছয় মাস সময় পেলে শিখতে পারবে, কারণ দেওনাগরী অক্ষর সহজ এবং দ্রুত আয়ত্ত করা যায়।
(১৩) আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, সেন্ট্রাল প্রোভিনসেস অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার যেখানে সম্প্রতি হিন্দি চালু হয়েছে, এবং জেলা ত্রাই ও রাজ্য রিভাঁ-তে হিন্দির প্রচার করা হয়েছে, সেসব রিপোর্ট সংক্ষেপে দেখুন।
(১৪) দেওনাগরী অক্ষর এত সহজ যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান তিন দিনেই ৪৮ অক্ষর এবং ১২ মাত্রা শিখে লিখতে-পড়তে সক্ষম, এবং ছয় মাসে এমন অভ্যাস করা যায় যা এখন আদালতের লোকেরা উর্দু অক্ষর শেখার জন্য ছয় বছর ব্যয় করেন।
(১৫) সব হিন্দু-মুসলমান নিজেদের খাতা দেওনাগরীতেই লিখে এবং তার আদল-বদলও এই অক্ষরে করে।
(১৬) পটওয়ারীর কাগজও অধিকাংশ দেওনাগরী অক্ষরে লেখা হয়।
(১৭) উর্দু অক্ষরে বড় বড় ত্রুটি রয়েছে। আলাদা আলাদা অক্ষরের উচ্চারণ মিলিয়ে শব্দ বানালে তা ভ্রান্ত হয়। লেখা আলাদা যায় এবং পড়া আলাদা যায়। একটি বিন্দু ছাড়া বা যোগ দিলে অর্থ উল্টো হয়ে যায়। উর্দুতে জাল খুব সহজে তৈরি হয় এবং সরকার কিছু ব্যবস্থা নিতে পারে না। তাই আমরা প্রার্থনা করি, মূলটাই কেটে ফেলুন যাতে উদ্ভিদ অর্থাৎ উর্দু আর না থাকে, তখন জাল হবে না এবং সরকার বড় উপকার পাবে। উর্দু অক্ষরের অনেকের উচ্চারণ একই, কিন্তু রূপ ভিন্ন।
(১৮) উর্দু অক্ষরে তিনটি মাত্রা এবং ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। দেওনাগরী অক্ষরে ১২টি মাত্রা এবং ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, মাত্রাগুলিতে তিনটি প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। এ কারণেই আরবি, তুর্কি, ইংরেজি কোনো ভাষার শব্দ যেমন উচ্চারিত হয়, ঠিক তেমনই দেওনাগরীতে লেখা হয় এবং ঠিক তেমনই পড়া হয়। উর্দুতে একটি শব্দ বহুভাবে পড়া যায়। আমরা প্রার্থনা করি, মানচিত্র দেখুন, যেখানে সামান্যভাবে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে উর্দু বহু রূপে লেখা ও পড়া যায়।
| # | মূল শব্দ | উর্দুতে পড়ার বিভিন্ন রূপ (বাংলা বর্ণে উচ্চারণ) |
|---|---|---|
| 1 | নিরঞ্জন | নিরজ্জন, বিরহমন |
| 2 | পিয়ারেলাল | পিয়ারেলাল, বিহারীলাল |
| 3 | বচ্চন | থম্মন, ভম্মন, বচ্চন |
| 4 | সাহেব দরিয়া পার হবে | কাসবী মজুদ রেহে, কিশ্তি মজুদ রেহে |
| 5 | নাওয়াত সাফেদ | বানাত সেফেদ |
| 6 | মুরৈথা | মুড়না, মুরনিয়া, মুরন্থা, মুরন্তিয়া, মুরটা, মুহনা, মরহটা |
| 7 | আলুবুখারা | আলুবুখারা, উল্লু বিচারা |
| 8 | ভেনি নে মারা | নাভি নে মারা, তেনে মারা |
| 9 | পার্বতী | পার্বতী, সালাদনী |
| 10 | তামসুক | তামসুক, নামক, তামক |
| 11 | হোলি ফুকওয়া দো | হোলি ফিকওয়া দো |
| 12 | এক সাহেব 'ছতামরা' | 'জমরাহী ডাঙ্কা' পড়তেন, 'পট্টি ডাঙ্কা' কে |
| 13 | আরও খুগৌর | চুকর ঘণ্ট, কুহনহ' কে |
(১৬) যখন শিক্ষা কমিশন আলাহাবাদ মেয়োহলে বসেছিল, তখন প্রেসিডেন্ট অনেরিবিল ডাক্তার হন্টার সাহেবকে বলতে হয়েছিল যে হিন্দির প্রতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বড় চাহিদা রয়েছে।
(২০) একই সময় অনেরিবিল জাস্টিস সাইয়্যদ মাহমুদও বলেছেন যে, যদিও আমি মুসলমান, তবে এখানকার মানুষের মতামত প্রকাশ করি—তারা সকলেই চায় যে হিন্দি সব জায়গায় প্রচলিত হোক এবং উর্দু, যা বাঁকা-টুংকা লেখা হয়, আমার মতামতে থাকা উচিত নয়।
(২১) আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে হিন্দি চালুর জন্য কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেশনস জাজদের মতামত নেওয়া হোক।
(২২) শিক্ষা কমিশনের সামনে প্রায় ৪০ জন পাঞ্জাব থেকে শিক্ষা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি পুরুষ উর্দুর স্থানে হিন্দি প্রচলিত করার জন্য জোর দিয়েছিলেন; বিশেষ করে পাঞ্জাবের লর্ড পাদরি এই বিষয়ে ভালোভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।
(২৩) এখন আমরা আপনার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা করছি যে, আপনি উপরোক্ত লিখিত বিষয়সমূহ এবং শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করার সময় হিন্দির প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন এবং হিন্দি ও দেওনাগরী…আক্ষরগুলো কচেরিতে ব্যবহারের অনুমতি দিন এবং আমরা সকলেই আপনার প্রজা আপনার চিরঞ্জীবী হওয়ার বিনয় করি।
-: 0 :-
স্বামীজি তখনকার রাজাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন যাতে তারা নিজেদের রাজ্যের কাজ হিন্দিতে পরিচালনা করেন। সেই অনুযায়ী উদয়পুরের মহারাজা দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দিকে রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সরকারি অফিসের নামগুলি সংস্কৃত শৈলীতে রাখা হয়েছিল, যেমন—মহদ্রাজ সভা, শৈলকান্তার সম্পর্কিনী সভা, নিজ সৈন্য সভা, শিল্পসভা ইত্যাদি। মেওয়াড় রাজ্যের রাজপত্র (গ্যাজেট) ‘সজ্জনকীর্তিসুধাকর’ নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তিনি জোধপুর নরেশকে চিঠি লিখেছিলেন যে রাজকুমারদের প্রথমে হিন্দি (দেবনাগরী), তারপর সংস্কৃত এবং পরবর্তীতে (যদি সময় হয়) ইংরেজি পড়ানো হোক। ১২ আগস্ট ১৮৮৩ সালে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কর্নেল প্রতাপসিংহ একদিন আবেদন শুনতে শুনতে উর্দুতে লেখা ৫০–৬০টি আবেদন চিড়িয়ে ফেলেন। সেই দিন থেকেই রাজ্যের সমস্ত কাজ হিন্দিতে শুরু হয়।
হিন্দি দেশীয় একতার জন্য অপরিহার্য মনে করে তিনি জীবনশেষ পর্যন্ত এর প্রচার ও প্রসারের জন্য পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি শ্রী শ্যামজি কৃষ্ণবর্মাকে বেদভাষ্যের ডাক পার্সেলে দেবনাগরী লিপিতে ঠিকানা লেখার প্রেরণা দেন। মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত সমাজসংশোধক শ্রী গোপাল হরিদেশমুখকে আর্যভাষার প্রচারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রেরণা দেন। তাদের থেকে প্রেরণা পেয়ে কর্নেল অলকাট হিন্দি পড়া শুরু করেন।
একজন সজ্জন যখন তাদের গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিলেন, তখন তিনি লিখেছিলেন—“যাঁরা সত্যিই আমার ভাবনা জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা এই আর্যভাষা শেখাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করবেন। অনুবাদ তো বিদেশীদের জন্য হয়।” ম্যাডাম ব্লাভতস্কিকে স্বামীজি লিখেছিলেন—“আমার উদ্দেশ্য আপনাকে অনুবাদ থেকে বিরত রাখা নয়, কারণ ইংরেজি অনুবাদ ছাড়া ইউরোপীয় জাতিগণ সত্যের আলো পেতে সক্ষম নয়। কিন্তু ভারতের আর্যজনতা যদি আমার ভাষ্য ইংরেজিতে প্রকাশিত হলে সংস্কৃত এবং হিন্দি অধ্যয়ন ত্যাগ করবে। আমার বেদভাষ্য বোঝার জন্য সংস্কৃত ও হিন্দি অধ্যয়ন, যা আমার প্রধান লক্ষ্য, নষ্ট হয়ে যাবে।”
স্বামীজির কোনো ভাষার প্রতি দ্বেষ বা বিরোধ ছিল না, কিন্তু তিনি বলতেন, “যে এই দেশে জন্মেছে এবং এর ভাষা শিখতে পারছে না, তার থেকে আর কী আশা করা যায়?” তাই তিনি আর্যভাষা (হিন্দি) শেখাকে প্রতিটি আর্যসমাজীর জন্য বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছিলেন।
হিন্দির যে রূপের প্রচার ও প্রসার স্বামীজি চাইতেন, তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ‘সত্যার্থপ্রকাশ’-এ পাওয়া যায়—
“যা সত্য, তাকে সত্য এবং যা মিথ্যা, তাকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করা সত্যার্থের আলো মনে করা হয়। সে সত্য বলে না যে, যেখানে সত্য সেখানে মিথ্যা এবং যেখানে মিথ্যা সেখানে সত্যের আলো দেখায়, কিন্তু যা পদার্থ যেমন আছে, তাই বলা, লেখা এবং মানা সত্য বলা হয়।”
দেবনাগরী লিপির উৎকৃষ্টতা
স্বামী দয়ানন্দ আর্যভাষা হিন্দির উৎকৃষ্টতা এবং দেবনাগরী লিপির বৈজ্ঞানিকতার প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন। নাগরী লিপির পরিপূর্ণতা তিনি কীভাবে প্রমাণ করেছেন, তা সম্পর্কিত একটি ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। একজন প্রসিদ্ধ মৌলভি এবং একজন প্রসিদ্ধ পাদ্রি তাদের-নিজ নিজ লিপির উৎকৃষ্টতা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন যে তিনটির মধ্যে যে লিপি উৎকৃষ্ট, সেটিই গ্রহণযোগ্য হবে, বাকি দুইটির পরিত্যাগ করা হবে। উৎকৃষ্টতা কিভাবে নির্ধারণ হবে, তা জন্য এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, প্রত্যেকে তার নিজের ভাষার সবচেয়ে কঠিন বাক্যগুলো বলবে এবং যেই লিপিতে সঠিকভাবে লেখা সম্ভব হবে, সেই লিপিই উৎকৃষ্ট হবে। স্বামীজি যেসব বাক্য আরবি বা ইংরেজিতে শুনেছেন, তিনি সেগুলো দেবনাগরীতে তেমনই লিখে ফেলেছিলেন, কিন্তু স্বামীজি যে শব্দগুলো বলেছিলেন, সেগুলো আরবি বা রোমান লিপিতে লেখা যায়নি। স্বামীজি যে শব্দগুলো বলেছিলেন, সেগুলো পাণিনির প্রত্যাহার সূত্রের একটি ‘অমণ্ণনম্’ ছিল। এর জন্য দেবনাগরী ছাড়া অন্য কোনো লিপিতে অক্ষর নেই। (সরস্বতী, অক্টোবর ১৬৩৬, পণ্ডিত ধর্মদেব শাস্ত্রীর প্রবন্ধ ‘রোমান লিপির মোহ’)।
স্বদেশী
দেশে তৈরি বস্তুসমূহের প্রতি স্বামীজির কতটা প্রেম ছিল, তা তার এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়—
“আমরা এবং আপনাদের জন্য উপযুক্ত যে, যে দেশের পদার্থ থেকে আমাদের শরীর তৈরি, তা আজও রক্ষা হয়। ভবিষ্যতেও সেই দেশের উন্নতি, তন, মন, ধন—সব মিলিয়ে প্রেমের সঙ্গে করাই উচিত।”
ভাষা, ভাব, অলংকার, পরিধান—সবই পরাধীন মানুষের পরিচয়।
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ঋষি দয়ানন্দ গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। শুধু চিন্তা করাই নয়, নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে দেশের শিল্পায়নের জন্য বিদেশের সঙ্গে পত্রচারিতাও করেছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি তার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেননি। স্বামীজি এই বিষয়টি গভীর দুঃখের সঙ্গে অনুভব করতেন যে বিদেশি পণ্যের ব্যবহারে দেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সত্যার্থপ্রকাশে তিনি লিখেছেন—
“যখন বিদেশি দেশের মধ্যে ব্যবসা করবে, তখন দারিদ্র্য এবং দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছু হবে না।”
এটি সেই সময়ের কথা যখন “ভারতের অধিবাসীরা সাধারণত মানচেস্টারে তৈরি কটন কাপড় পরত। শিশুরা ইংলিশ এবং ফরাসি খেলনা দিয়ে খেলত, মূর্শি (লেখাপড়ার শিক্ষক) বিদেশি কাগজ লেখার কাজে ব্যবহার করত। ভারতীয়রা বিদেশি গ্লাস দিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসি ব্র্যান্ডি পান করত।”
এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তখনকার ভারতীয়দের সমগ্র মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে বিদেশি রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিল এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারকে ফ্যাশন বা আধুনিকতার বিপরীতে ধরা হতো।
এই পরিস্থিতিতে স্বামী দয়ানন্দ বিদেশি পণ্য ও জীবনযাত্রার বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য গ্রহণের প্রেরণা দিয়ে বলেছিলেন—
“এতটুকু দিয়ে বুঝে নাও যে, ইউরোপীয়রা তাদের দেশের জুতোর যত মর্যাদা এবং মান দেয়, অন্য দেশে বসবাসকারীরা তা দেয় না। তাদের দেশের তৈরি জুতো অফিস ও কচেরিতে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই দেশী জুতো নয়। দেখো, কয়েকশ বছর আগে ইউরোপীয়রা এই দেশে এলো এবং আজও তারা মোটা কাপড় ইত্যাদি পরছে যেমন তারা স্বদেশে পরত, কিন্তু তারা তাদের দেশের রীতি ত্যাগ করেনি, আর তোমাদের অনেকেই তাদের অনুকরণ করেছে। তাই তোমরা নির্বোধ এবং তারা বুদ্ধিমান মনে হয়। অনুকরণ করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।” (স.প্র.)
সংস্কারবিধি
স্বামীজি বিবাহ-সংস্কারের প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ স্বদেশী (হাতে কাটা, হাতে বোনা) পোশাক ব্যবহারকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। ‘অন্যান্য দেশের মানুষকেও ততটা মর্যাদা দেওয়া হয় না যতটা নিজের দেশের তৈরি জুতোর’—এটি যারা লিখেছেন, তাদের হৃদয়ে বিদেশি শাসন ও বিদেশি পণ্যের ব্যবহার প্রতি কতটা ঘৃণা ছিল তা স্পষ্ট।
ছাওলি নিবাসী ঠাকুর ঊধোসিংকে বিদেশি পোশাকে দেখে মহর্ষিজি বলেছিলেন—
“তুমি কি এই বিদেশি কাপড় পরিধান করে তোমার পিতার চেয়ে বেশি সংস্কৃত হয়ে গেছ? নিজের দেশের পোশাক গ্রহণ করাই সৌন্দর্য।”
বাস্তবিকভাবে, স্বামীজির আচরণ, জীবনযাপন, পোশাক, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়—সবই স্বদেশী রঙে রঙিন ছিল। তার অন্তর এবং বাহ্যিক সবই স্বদেশী রঙে রঙে রঙা ছিল। স্বামীজি তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজকে সমালোচনা করে লিখেছেন—
“এই মানুষদের মধ্যে স্বদেশভক্তি খুবই কম। অনেক নিয়ম তারা খ্রিস্টানদের আচরণ থেকে গ্রহণ করেছে। খাদ্যাভ্যাস, বিবাহ ইত্যাদির নিয়মও পরিবর্তন করেছে। নিজের দেশের প্রশংসা বা পূর্বপুরুষদের গুণগান করা তো দূরের কথা, বরং তার বদলে ভরপুর নিন্দা করে।”
মহর্ষির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। যোধপুর রাজ্যের কর্মচারী, কর্মকর্তারা এবং অভিজাত সমাজের মানুষ মারওয়াড়ে খাদি কাপড় ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কর্নেল প্রতাপসিংহ আদেশ জারি করে রাজকর্মচারীদের জন্য খাদি পরিধান বাধ্যতামূলক করলেন। স্বামী দয়ানন্দের শিক্ষার এই ফলাফল ছিল যে, ইংরেজি সংবাদপত্র ‘স্টেটসম্যান’-এর ১৪ আগস্ট ১৮৭৬-এর রিপোর্ট অনুযায়ী—
“পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা লাহোরে প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সব সদস্য সমাজ-মন্দিরে একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বিদেশি পোশাক ব্যবহার করা হবে না এবং কেবলমাত্র নিজের দেশে তৈরি পোশাক ব্যবহার করা হবে।”
শ্রী দত্তাত্রেয় ডাবলে তাঁর গ্রন্থ ‘The Arya Samaj’-এর পৃ. ১৩৭-এ লিখেছেন—
“এই কারণেই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে স্বামী দয়ানন্দের চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ‘স্বামী দয়ানন্দ তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাধারা দ্বারা হাতে তৈরি পোশাক ও অন্যান্য স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের যে ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন, তা পঞ্চাশ বছর পরে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার আন্দোলনের একটি প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।’”
গো ও ভারতীয় সংস্কৃতি
ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদিকাল থেকেই গরুর প্রতি যতটা শ্রদ্ধা ছিল, তার সমান মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা। জন্মদাত্রী মা, গোমাতা এবং ভারত মাতার তিনিই সমানভাবে ভক্তি, সেবা ও রক্ষার যোগ্য। ভারতে গরু অর্থনীতির একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও বিবেচিত হয়।
সত্যার্থপ্রকাশ হলো বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সজ্জিত গ্রন্থ। এর একটি বিষয় হলো গরু। কিন্তু এই বিষয়কে তিনি ‘গোকরুণানিধি’ নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে রচনা করেছিলেন, যা এই বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। দয়ানন্দ সত্যিই দয়াসাগর ছিলেন।
একবার উদয়পুরে দশহরীর সময়ে চড়ানো পশুবলির ক্ষেত্রে দয়ানন্দ দ্রবীভূত হৃদয় নিয়ে মহারানা সাজ্জন সিংহের কাছে প্রশ্ন করলেন— “আপনি রাজা, বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত। আমি এই নির্বোধ প্রাণীদের আইনজীবি হয়ে আপনার সামনে অভিযোগ উপস্থাপন করতে এসেছি। বলুন, তাদের অপরাধ কী যে দেবতার নামে তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে?”
মহারানা দীর্ঘকাল ধরে চলা এই প্রথা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন।
‘গোকরুণানিধি’-তে স্বামীজি লিখেছেন— “হে পরমেশ্বর! তুমি কেন এই পশুদের প্রতি, যারা নিরপরাধ মারা যায়, দয়া করো না? তাদের প্রতি কি তোমার প্রেম নেই? তাদের জন্য কি তোমার বিচারসভা বন্ধ হয়ে গেছে? কেন তাদের কষ্ট মুক্ত করতে মনোযোগ দাও না? কেন তাদের আহ্বান শোনো না?”
এখানে প্রকাশভাবে ঈশ্বরের বিচারব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। উপরন্তু ক্রূরতা, অত্যাচার এবং পক্ষপাতের অভিযোগ আনা হচ্ছে। ঈশ্বরকে বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্নদের রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এটি সমস্ত করছেন সেই ব্যক্তি, যার মুখ থেকে সবচেয়ে বড় আপত্তি আসলেও কোনো আহ প্রকাশ হয়নি। যার ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায়ে এত অটল বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর সময়ও তিনি বলেছেন “হে দয়াময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তুমি সুন্দর খেলাটি করেছ”—এই ভাবেই দয়ানন্দের হৃদয়ে গোহত্যার কারণে যে কষ্টদায়ক যন্ত্রণার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, সে প্রকাশ পেয়েছে। দয়ানন্দের মতে, অনৈতিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মনে ভয়, সন্দেহ ও লজ্জার ভাব জন্মায়। একই স্মরণে তিনি তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন—
“হে প্রভু! কেন তুমি এই মাংসভক্ষণকারীদের আত্মায় করুণার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছ না, যাতে নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি দোষ দূর হয়ে তারা এই খারাপ কাজ থেকে বাঁচতে পারে।”
যিনি বিদেশি শাসকদের দ্বারা প্রতিরক্ষার জন্য প্রণীত ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই দয়ানন্দ গোমাতার প্রাণ রক্ষার জন্য দ্বারস্থ হতে কোনও দ্বিধা অনুভব করেননি। কখনও তিনি আজমীরে মেজর এ.জি. ডেভিডসন কমিশনারের কাছে পৌঁছাতেন, কখনও কর্নেল বুকের কাছে গোবধ বন্ধের জন্য আবেদন করতেন। বুক তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে দয়ানন্দকে এই বিষয়ে ভাইসরায়ের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।
এ প্রসঙ্গে, স্বামীজি ১৮৭৩ সালে ফাররুখাবাদে উত্তর প্রদেশের (তৎকালীন সংযুক্ত প্রদেশ) লেফটিন্যান্ট গভর্নার মি. মেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—
“যদি আপনি লন্ডনে ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হন, তাহলে আপনি কি গোবধ বন্ধ করার চেষ্টা করবেন?”
স্বামীজি তাঁর গ্রন্থগুলির ইংরেজি অনুবাদ করার অনুমতি দেননি। কিন্তু ‘গোকরুণানিধি’-র ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে বিদেশে পাঠানোর প্রচেষ্টা করা এবং সময়ে সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা করা, দয়ানন্দের গবাদি পশুদের প্রতি করুণা ও প্রেমের গভীর প্রকাশ।
স্বামী দয়ানন্দ তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে দুটি বিষয়কে সর্বজনীন আন্দোলনের বিষয় করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালিয়েছিলেন। হিন্দিকে রাজভাষা করার জন্য মতসংগ্রহের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। গোরক্ষার্থে জনমত সংগ্রহের জন্য তিনি দুই কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, এই স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যীয় রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনের মাধ্যমে পৌঁছানো। এই আবেদনের বৈধতা সম্পর্কেও তিনি উচ্চস্তরের বহু আইনজীবীর পরামর্শ নিয়েছিলেন। (দেখুন—ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র ও বিজ্ঞাপন, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৪৬, ৪৬০-৬১, এবং খণ্ড ২, পৃ. ৫৩৭, ৫৫৮, ৭৫৬)।
বোম্বেই থেকে আর্যসমাজ, দানাপুরের মন্ত্রীকে ১২ মার্চ ১৮৮২ তারিখে প্রেরিত এ সংক্রান্ত পত্রে তিনি লিখেছেন—
“আমি আপনাদের, পরোপকারপ্রিয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের, গো, মহিষ এবং বলের হত্যা প্রতিরোধের জন্য দুইটি পত্র প্রেরণ করছি—একটি সংশোধন করার জন্য, অন্যটি যার অনুযায়ী সংশোধন করা হবে। এটিকে স্নেহ ও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করুন, যাতে মহাশয়দের কীর্তি এই জগতে চিরকাল বিরাজমান থাকে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে যে, দুই কোটিরও বেশি রাজা, মহারাজা এবং প্রধান মহাশয়দের সংশোধন করে আর্যাভর্তীয় সম্মানিত গভর্নর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের কাছে আবেদন জানিয়ে উল্লিখিত গরু ও অন্যান্য পশুর হত্যাকে রোধ করা হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের আনন্দের সঙ্গে এই মহোন্নত কাজটি শীঘ্রই সম্পন্ন করবেন। আরও পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, যেখানে যেখানে উপযুক্ত মনে করবেন, সেখানে সেখানে পাঠিয়ে সংশোধন করুন। পুনরায় নিচে লিখিত স্থানে রেজিস্ট্রি করে প্রেরণ করুন।”
স্বামীজি এই উদ্দেশ্যের পত্র বহু স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। মহারানি ভিক্টোরিয়াকে প্রেরণীয় আবেদনের খসড়া এখানে সংযুক্ত করা হলো।
সঠিক করার পত্র
ও৩ম
এই পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে কি, যে সুখলাভে আনন্দিত এবং দুঃখপ্রাপ্তিতে অপ্রসন্ন না হয়? যেমন অন্যের করণীয় কল্যাণে নিজেই আনন্দিত হয়, তেমনি পরোপকারে সুখী হওয়া উচিত। কি এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ভূগোলবিদ্যায় ছিল, আছে বা থাকবে, যে পরোপকারমূলক ধর্ম ও পরহানিস্বরূপ অধর্ম ব্যতীত ধর্ম ও অধর্মের সিদ্ধি করতে পারবে? ধন্য তারা, যারা নিজেদের দেহ, মন ও অর্থ দিয়ে বিশ্বের অধিক উপকার সাধন করে। নিন্দনীয় তারা, যারা নিজের অজ্ঞতা ও স্বার্থবশত দেহ, মন ও অর্থ দিয়ে বিশ্বের ক্ষতি করে বড় উপকারের বিনাশ ঘটায়।
সৃষ্টিক্রম অনুযায়ী নিখুঁতভাবে এটি নিশ্চিত হয় যে, ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা পূর্ণ উপকারের জন্যই। সামান্য লাভে মহাহানি করা অর্থহীন। বিশ্বে জীবনের দুইটি মূল—একটি খাদ্য এবং দ্বিতীয় পানীয়। এই ভাবনায় আর্য্যবর শিরোমণি রাজা, মহারাজা ও প্রজাজন মহোপকারক গরু ইত্যাদিকে কখনও হত্যা করেননি এবং অন্যকে হত্যার অনুমতি দেননি। এখনো এই গরু, ষাঁড়, মহিষকে হত্যা বা মৃত্যুর জন্য প্রেরণ করতে চান না, কারণ খাদ্য ও পানীয়ের আধিক্য এদের মাধ্যমেই সম্ভব। এ থেকে সকলের জীবন সুখময় হতে পারে।
যত ক্ষতি রাজা ও প্রজার হয় এদের হত্যা ও মৃত্যুর মাধ্যমে, অন্য কোন কর্মে তত হয় না। এর সিদ্ধান্ত ‘গোকরুণানিধি’ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ—একটি গরুর হত্যার মাধ্যমে ৪,২০,০০০ (চার লক্ষ বিশ হাজার) মানুষের সুখের ক্ষতি ঘটে।
সেজন্য আমরা সকলেই স্বপ্রজার হিতৈষিণী শ্রীমতি রাজরাজেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার ন্যায়-প্রণালীর কাছে অনুরোধ করছি, যে অন্যান্যায়রূপ বড় উপকারী গরু ইত্যাদির হত্যা বন্ধ করা হোক, যাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হতে পারি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, বিদ্যা, ধর্ম, প্রজা-হিত-প্রিয় শ্রীমতি রাজরাজেশ্বরী কুইন, সংসদ সভা এবং সর্বোপরি আর্যাভর্তের সম্মানিত গভর্নর জেনারেল সাহেব বাহাদুর উক্ত ক্ষতিকর গরু, ষাঁড় এবং মহিষের হত্যা উদ্দীপ্ত ও আনন্দসহকারে শীঘ্রই বন্ধ করবেন এবং আমাদের সকলকে পরম আনন্দিত করবেন।
দেখুন, উক্ত গরু ইত্যাদির হত্যার ফলে দুধ, ঘি এবং কৃষকদের কত ক্ষতি হয়েছে, যা রাজা ও প্রজার জন্য বড় ক্ষতি হয়েছে এবং প্রতিদিন বাড়ছে। পক্ষপাত ছেড়ে কেউ দেখলে, তিনি বুঝবেন—পরোপকারই ধর্ম এবং পরহানি অধর্ম।
বিদ্যার এই ফল ও নীতি কি নয় যে, যার যার অধিক উপকার, তাকে পালন ও বৃদ্ধি করা উচিত, কখনও নাশ নয়। পরমদয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, সর্বান্তুপর্যায়ী, সর্বশক্তিমান পরমাত্মা যেন এই সমস্ত উপকারী কাজ করার ক্ষেত্রে একমত হন।
হস্তাক্ষর
বিজ্ঞাপনপত্রমিদম
সকল আর্যপুরুষদের জানানো হলো, যে পত্রের ওপর (ও৩ম) এবং নিচে (হস্তাক্ষর) এই বক্তব্য লেখা আছে, সেটিই সঠিক করার পত্র। এতে সঠিক করার নিয়ম হলো—যার স্বরাজ্য ও দেশে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মানুষের সংখ্যা রয়েছে, সেই সংখ্যার উল্লেখ করে, অর্থাৎ শত, হাজার, লাখ বা কোটি মানুষের পক্ষ থেকে “আমি … নামা পুরুষ সঠিক করি” এইভাবে এক সম্মানিত প্রধান পুরুষের হস্তাক্ষরের মাধ্যমে সমস্ত সাধারণ আর্যপুরুষের স্বাক্ষর গণ্য হবে।
যদি মুসলমান বা খ্রিস্টানরা এই মহোপকারমূলক বিষয় সম্পর্কে দৃঢ়তা ও আনন্দের সঙ্গে স্বাক্ষর করতে ইচ্ছুক হন, তাঁরা করতে পারেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আপনারা পরম উদার মহাত্মার প্রচেষ্টা, উৎসাহ এবং প্রীতির মাধ্যমে এই সর্বোপকারক মহাপুণ্যকীর্তিপ্রদায়ক কাজ যথাযথভাবে সফল করবেন।
১. এর পূর্ণ বিবরণ ‘গোকরুণানিধি’ (রা.লা. ক. ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত দয়ানন্দীয় লঘুগ্রন্থ-সংগ্রহ, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮) এবং ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ সমু. ১০ (অ.স. শতাব্দী সংখ্যা ৩, পৃ. ৪১৫-৪১৬) এ দেখুন। উভয় গ্রন্থে সংখ্যায় কিছু ভিন্নতা আছে।
২. সঠিক করা পত্রের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনও বহু স্থানে প্রেরিত হয়েছিল।
চৈত্র কৃষ্ণ ১, সং. ১৬৩৬, অনুসারে ১৪ মার্চ ১৮৮২, মুম্বাই
দয়ানন্দ সরস্বতী
এই হস্তাক্ষর অভিযানটিতে স্বামীজী প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেন। শাহপুরাধীশ স্যার নাহারসিংহের মাধ্যমে ৪০,০০০, ফররুখাবাদের গোপালরাও হরির মাধ্যমে ৭২০০০, কাটিলার ঠাকুরানি সাহিবা দ্বারা ৬০,৩০৮, এটার জালিমসিংহ রূপধনী ও তার ভাগ্নে গুলাবসিংহের মাধ্যমে ১০,০০০, বোম্বে’র সেবক লালকৃষ্ণদাসের মাধ্যমে ১৫,৩২০, বাবু কৃপারামজি দ্বারা ৫০,০০০ (মোট ২,৭৭,৬২৮) হস্তাক্ষরযুক্ত পত্র প্রাপ্ত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত স্বামীজীর মৃত্যুর কারণে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
ফররুখাবাদের আর্যসমাজের বড় গুরুত্বপূর্ণ অবদান মহর্ষির সকল কার্যক্রমে ছিল। সরকারের কাছে প্রেরণকৃত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের পাশাপাশি এই কাজে অর্থ সংগ্রহেও তারা যথাযথ উৎসাহ প্রদর্শন করেছিল। মহর্ষির অনুপ্রেরণায় ২৬ জানুয়ারি, সন ১৮৮১-এ আর্যসমাজের অন্তরঙ্গ সভা গোরক্ষা কার্যক্রমে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সভার মত ছিল, যদি এক বছরে ২০০টি গরুকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করে ক্রয় করা যায় এবং তাদের পালন-পরিচর্যার যথাযথ ব্যবস্থা করা যায়, তবে এই কাজের বার্ষিক খরচ হবে ৬,৫০০ রুপি। অন্তরঙ্গ সভা তাদের বাজেটে এই বার্ষিক ব্যয় অনুমোদন করে।
মহারানা সাজ্জনসিংহ গবাদি পশুর হত্যা বন্ধ করার বিষয়ে জোধপুরের মহারাজা জসবন্তসিংহকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তার উত্তরে জোধপুর-নরেশ লিখেছিলেন:
“মহার প্রজা ১৪,৬১,১৫৬ হিন্দু এবং ১,৩৭,১১৬ মুসলিম বা তিনটি পশু (গরু, ষাঁড় এবং মহিষ) হত্যা না করার ব্যবস্থায় খুশি এবং আমি এ বিষয়ে রাজি।”
সং. ১৬৩৬, পোষ্য বাদি ৫
হস্তাক্ষর- রাজরাজেশ্বরী মহারাজাধিরাজ জসবন্ত সিংহ
মারওয়ার, জোধপুর
এই চিঠি ঠাকুর জগদীশ সিংহ গেহলোট তাঁর ‘রাজপুতানা ইতিহাস’ খণ্ড ১, পৃ. ২৮৭-এ উদ্ধৃত করেছেন। সং. ১৬৩৬, পোষ্য বাদি ৫ ছিল শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ১৮৮২। এই সময়ে মহর্ষিজী উদয়পুরে ছিলেন। জয়পুর রাজ্যেও গোরক্ষা এবং পশুর রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। দানাপুরের খ্রিস্টান জনস সাহেব স্বামীজীর যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে ভবিষ্যতে গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগের শপথ নেন।
আর্যসমাজের নয়, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে রিওয়াড়ীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এর কারণ সেখানে গরুশালাটি, যা মহর্ষির অনুপ্রেরণায় রাও যুধিষ্ঠির সিংহ (রাও বীরেন্দ্র সিংহের পিতামহ) ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্ভবত আধুনিক যুগে এটি ভারতের প্রথম গরুশালা ছিল, যা জনসাধারণের কল্যাণের দৃষ্টিতে স্থাপিত হয়েছিল।
১. এখানে সং. ১৬৩৮ প্রয়োজন। চৈত্র শুক্ল ১ থেকে নতুন সং. শুরু হয়। ফররুখাবাদের ইতিহাস নামক গ্রন্থে পৃ. ২০০-এও সং. ১৯৩৮ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ইংরেজি তারিখ ২৪-৩-১৪৬৮২ দেওয়া আছে, যা অসম্পূর্ণ। ১৪ মার্চ দেওয়া উচিত।
সমাজে নারীর স্থান
ফ্রান্সের মনীষী রোমঁ রোলাঁ অনুসারে, "আর্যসমাজ সব মানুষের এবং দেশের প্রতি ন্যায় ও স্ত্রী-পুরুষের সমতার নীতিকে স্বীকার করে। এটি জন্মনাজাতির বিরুদ্ধে। স্বামী দয়ানন্দের চেয়ে বড় কঠিনভাবে হারিজনের হিতরক্ষক অন্য কেউ খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারীদের দয়নীয় অবস্থার থেকে উদ্ধারের এবং সমান অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দয়ানন্দ মহান উদারতা দেখিয়েছেন।"
দয়ানন্দ নারীর প্রতি কেবল ভোগ্য হিসেবে না দেখে, তাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান সক্ষম ঘোষণা করে একটি বিপ্লবী চেতনা জন্ম দিয়েছেন। নারী-উত্তরণের দিকে মহর্ষির এই সংकल्पনা তার চিন্তার উচ্চতর ভাবনার প্রমাণ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারীরাও পুরুষদের সমান শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত হোন, যাতে তারা রাজকাজ এবং ন্যায়-প্রশাসন ইত্যাদিতে পুরুষদের থেকে পিছিয়ে না থাকে।
ন্যায়কাজে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন- "রাজাদের স্ত্রীদের উচিত যে সব নারীর জন্য ন্যায় এবং ভাল শিক্ষা প্রদান করা এবং নারীদের ন্যায় ইত্যাদি পুরুষরা না করুন, কারণ পুরুষদের সামনে নারী লজ্জিত ও ভয়মুক্ত হয়ে কথা বলতে পারে না।" (যজুর্মাষ্য ১০১২৬)
স্বামীজীর মতে রানি রাজাকে বলেছিলেন- "যেমন আপনি পুরুষদের বিচারক, তেমনি আমি নারীদের বিচারক। আমি আপনার থেকে কম নই।" (ঋগ্বাষ্য ১৩১২৬৭৭)
ন্যায়-প্রশাসনের মতো কঠিন কাজে নারীর অংশগ্রহণের ঘোষণা তখনকার ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা ছিল, যা স্বাধীন ভারত সংবিধানের মাধ্যমে স্বীকৃতি পেয়েছে।
ঋষি দয়ানন্দ ন্যায়িক প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্ভাব্য কুপ্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাই উদয়পুরনরেশ মহারানা সাজ্জনসিংহকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন- "নারীর সাক্ষ্যে নারীদের থেকে জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নিন, তবে নারীরা যদি রয়, তাহলে যথাযথ ব্যবস্থায় রাখুন, যাতে সেখানে অন্য কোনো দূরবর্তী নারী পরিবর্তে উত্তর না দেয়। যদি সামনে থাকে, কেউ তার দিকে দৃষ্টি না রাখুক, হাস্য বা ভয় দেখাক না।" (ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র ও বিজ্ঞাপন, সং. ৩, খণ্ড ২, পৃ. ৬২৬)
সত্যার্থপ্রকাশ
"আধার পরমঃ ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এন্ড চ।" - মনু ১।১০৮
শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতিতে নির্দিষ্ট আচরণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তবে 'শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতি রেভ'—শ্রুতি ও স্মৃতিতে পরস্পরের বিরোধ থাকলে শ্রুতির প্রমাণ্যতা থাকবে। শ্রুতিতে চিরন্তন ধর্মের প্রতিপাদন, স্মৃতিতে দেশ ও কালের বিশেষ পরিস্থিতিতে अपेक्षित ধর্ম নির্দেশিত হয়। বেদ ঈশ্বরীয় জ্ঞান হওয়ায় স্বয়ংপ্রমাণ, স্মৃতিগ্রন্থ মানুষের উক্তি হওয়ায় পরোপ্রমাণ। তাই মনু বলেন- 'ধর্ম জিজ্ঞাসামানান প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ'। অন্য কথায়, স্মৃতির প্রমাণ্যতা সেই পর্যন্ত, যতদূর তা বেদের বিরুদ্ধে নয়।
আরবরা যখন সিন্ধুকে অধীন করে হিন্দুদের জোরপূর্বক মুসলিম বানাতে, তাদের নারীদের অপহরণ এবং সহিংসতা চালাতে শুরু করে, তখন একটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়। সমাধানের জন্য দেবল মুনি একটি স্মৃতি তৈরি করেছিলেন, যাতে জোরপূর্বক মুসলিম করা ব্যক্তিদের শুদ্ধ করে আবার হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।
সন ১৯৪৬-এ পাকিস্তানের প্রাপ্তির জন্য মুসলিম লীগ-এর নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত নোয়াখালি অঞ্চলে হাজার হাজার হিন্দুকে জোরপূর্বক মুসলিম করা হয় এবং হাজার হাজারকে তলোয়ারের ঘাটে হত্যা করা হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম হওয়া হিন্দুদের পুনঃপ্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (সমগ্র ভারতের হিন্দু মহাসভা-এর তখনকার সভাপতি) একটি সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় सनাতনধর্মের প্রতিনিধিত্ব স্বামী করপাত্রিজী করছেন এবং আর্যসমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন এই পংক্তির লেখক পণ্ডিত লক্ষ্মীদত্ত দীক্ষিত।
স্বামী করপাত্রিজী বলেন যে, হিন্দুধর্মে পুনঃপ্রবেশের ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী এক পাউ গোবর খেতে হবে। এ বিষয়ে ডঃ মুখার্জী একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, নোয়াখালিতে জোরপূর্বক মুসলিম করা একটি বৃদ্ধা মহিলাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তোমাকে কীভাবে মুসলিম করা হলো?” তিনি আমাকে জানান যে, আমাকে এবং আমার মত অন্য বোনদের এইভাবে মুসলিম করা হয়েছিল যে দুই মৌলভি পাগড়ির এক এক প্রান্ত ধরেছিল এবং তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে আমাদের পাগড়ি ধরে রাখতে বলেছিল। ভয়ে আমরা পাগড়ি হাতে নিয়েছিলাম। মৌলভিরা কালিমা পাঠ করে আমাদের মুসলিম ধরা হলো, কিন্তু যখন তারা কালিমা পাঠ করছিল, আমি মনে মনে রাম-রাম করছিলাম।
ডঃ মুখার্জী আমাকে বললেন, “বলো, সেই বৃদ্ধা কোথায় মুসলিম হলো, যাতে আমি তাকে আবার হিন্দু হতে এক পাউ গোবর খেতে বলি?” আমি বলেছিলাম, যে কেউ বলে “আমি হিন্দু”, তাকে হিন্দু ধরতে হবে। তার জন্য কোনো শুদ্ধি-সংস্কারের প্রয়োজন নেই। ডঃ মুখার্জী আমার দেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে সারাদেশে ঘোষণা করলেন। এটি ছিল স্মার্ত ধর্ম।
মনুস্মৃতি ইত্যাদির মতো সত্যার্থপ্রকাশও ঋষি দয়ানন্দ দ্বারা রচিত একটি স্মৃতি।
ঋষি দয়ানন্দের প্রাদুর্ভাবের সময় দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা কল্পনা করে হৃদয় কাঁপে। ব্যক্তিদের ধর্ম-কর্ম এবং সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার উপর পণ্ডিত, পুরোহিত ও পঞ্চদের একাধিপত্য ছিল। রাজারা তাদের মাধ্যমে প্রজার ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন সবাই মিলে ভোলি-ভালি অশিক্ষিত জনগণকে লুটতে ষড়যন্ত্র করছে। এই অবস্থা কেবল আমাদের দেশেরই ছিল না; পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে, কোনো না কোনোভাবে, সারাবিশ্বই এই দুরবস্থার শিকার ছিল। ইউরোপে পোপ, তুর্কিতে খলিফা, এবং অন্যান্য দেশে ধর্মগুরুদের প্রভাব বলবৎ ছিল। রাজাদের চেয়ে শক্তি তাদের হাতে ছিল।
জন্মের ঘটনাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হতো যে মানুষের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের কোনো মূল্য ছিল না। মানুষের মধ্যে জন্মগত জাতি, ছোঁয়া-ছাত, ধর্ম-কর্মের কঠোর পার্থক্য তৈরি করা হয়েছিল। ধর্মের নামে মন্দির, রাস্তা ও গলিতে রক্তের নদী বয়ে যেত। ঈর্ষা, দ্বেষ, বিরোধ, বৈমন্স্য ও ধ্বংসের সৃষ্টি ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিল। উন্নতি ও মুক্তির সাধক ধর্ম বিভিন্নভাবে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
ঈশ্বরের যত নাম পাওয়া যেত, তত দেবদেবীর কল্পনা করা হতো, আর কত ধর্ম, মঠ ও সম্প্রদায় এই দেশে জন্ম নিচ্ছিল যেন কুকুরমূত্র বা বর্ষার ব্যাঙের মতো। সত্যার্থপ্রকাশ-এর উত্তরার্ধের ভূমিকায় ঋষি তাদের সংখ্যা এক হাজারের বেশি উল্লেখ করেছেন।
জেনীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, হাতির পায়ের নিচে পিষিত হওয়ার ভয় থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য জেন মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। জেনীরা শিখিয়েছিল যে, গঙ্গা বা কাশী থেকে কিছুই মক্কা নয় এবং গিরনারের, পালিতানার ও আবুর মতো তীর্থস্থান মুক্তি দেবে।
পুরাণসমূহের পর্যালোচনা করে ঋষি লিখেছেন- "শিবপুরাণে শৈবরা শিবকে পরমেশ্বর ধরে বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা, গণেশকে দাস বানায়। বৈষ্ণবরা বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে পরমাত্মা ধরে শিবকে বিষ্ণুর দাস, দেবী ভাগবতে দেবীকে পরমেশ্বরী ও শিব, বিষ্ণু ইত্যাদিকে তার কর্মী বানায়। গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর ও সকলকে তার দাস বানায়। শিবপুরাণে শিব থেকে, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু থেকে, দেবীপুৰাণে দেবী থেকে, বায়ুপুৰাণে বায়ু থেকে সৃষ্টি ও প্রলয় বিবেচিত হয়। এখন ভাবুন, এসবের মধ্যে পারস্পরিক একমত, একতা, মিল বা সদ্ভাব থাকবে নাকি পারস্পরিক দ্বেষ, বিরোধ, মতভেদ ও ঝগড়া?"
ঋষি বলেন, "যদি এমন ছলকাণ্ড না চলত, তবে আর্যাবর্ত দেশের এই দুঃশ্চল অবস্থা কেন হতো?" ঋষি প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের একশটি নামের ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে আর্যাবর্তে প্রচলিত মত-মতান্তরের আরাধ্য দেবদের একরূপতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। পুরাণ ও পৌরাণিক গ্রন্থের অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, কিভাবে পরমাত্মার প্রতিটি নামকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন মত সৃষ্টি করা হয়েছে। শৈবরা শিবকে, বৈষ্ণবরা বিষ্ণুকে প্রভৃতি একই পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নামকে নিয়ে নানা সম্প্রদায় চালু করেছে। ঋষি লিখেছেন, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের বিভিন্ন নাম।
“এই নামগুলোর অর্থ যেভাবে প্রথম সমুল্লাসে করা হয়েছে, সেই সাতার্থ না জানায় শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি মানুষ একে অপরের নিন্দা করেন। মন্দমতি লোকেরা তাদের বুদ্ধি প্রসারিত করে ভাবেন না যে বিষ্ণু, রুদ্র, শিব প্রভৃতি একই সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বরের বিভিন্ন গুণ-কর্ম-স্বভাবযুক্ত হওয়ায় সেগুলি তার প্রকাশক।”
সম্পূর্ণ জগতের উৎপাদক হওয়ায় ব্রহ্মা, রক্ষক হওয়ায় বিষ্ণু, সংহারক হওয়ায় রুদ্র, নিয়ামক হওয়ায় যম প্রভৃতি একই পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত। এই বিষয়টি না বুঝে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকরা প্রতিটি নামকে কেন্দ্র করে ভক্তি শুরু করেছে। এই ভেদ বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা পারস্পরিক নিন্দা, বিরোধ ও দ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে পরিবারের কলহের কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের বৈর্য দূর করতে মহর্ষি প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের একশটি নামের ব্যাখ্যা করেছেন।
স্বামীজীর খণ্ডনাত্মক লেখার উদ্দেশ্য বোঝার জন্য প্রাথমিক ভূমিকা এবং ১১ থেকে ১৪তম সমুল্লাসের ভূমিকা-অভিযান পড়া প্রয়োজন। হয়তো কেউ পুরোপুরি সহমত না হতে পারে এবং কারো কাছে ভাষা কঠোর মনে হতে পারে, তবে তাদের ভাবনার প্রশংসা না করলে এটি অসম্পূর্ণ থাকবে।
একাদশ সমুল্লাসের অভ্যূমিকায় ঋষি লিখেছেন, “এই সব মতবাদের, তাদের শিষ্য এবং অন্যান্যদের একে অপরের সত্য-অসত্য বিচার করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম না করতে হোক, এজন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পরে সবাই নিজেদের বোঝাপড়া অনুযায়ী সত্য মত গ্রহণ করবে এবং অসত্যকে ত্যাগ করবে।”
তারপর তিনি লিখেছেন, “আমার এই কর্মকে যদি কেউ উপকার মনে না করে, তবুও বিরোধ করবেন না, কারণ আমার উদ্দেশ্য কারও ক্ষতি বা বিরোধ করার নয়, বরং সত্য-অসত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানো।”
মানবজন্মের উদ্দেশ্য হলো সত্য-অসত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানো, বিতর্ক বা বিরোধ সৃষ্টির জন্য নয়। …… যদি আমরা সব মানুষ এবং বিশেষ জ্ঞানের লোকেরা ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করে সত্য-অসত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং সত্য গ্রহণ ও অসত্য ত্যাগ করি, তবে আমাদের জন্য এটি অসম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত যে, এই জ্ঞানের লোকদের বিরোধই সবাইকে বিরোধের জালে ফেঁসে রাখছে। যদি তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে না ফেঁসে, সবাইকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়, তবে সকলেই ঐক্যমত হবে।”
এইভাবে দ্বাদশ সমুল্লাসের অনুভূমিকায় তিনি লিখেছেন—‘যা যা জৈনদের মত-বিষয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তা-তা তাদের গ্রন্থানুসারে লেখা হয়েছে। এতে জৈনদের খারাপ মনে করা উচিত নয়, কারণ যা কিছু আমরা তাদের মত সম্পর্কে লিখেছি, তা শুধুমাত্র সত্য-অসত্যের সিদ্ধান্তের জন্য, বিরোধ বা ক্ষতি করার জন্য নয়। এই লেখা যখন জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্যরা দেখবে, তখন সবাইকে সত্য-অসত্যের সিদ্ধান্তে চিন্তা এবং লেখা করার সময় এবং বোধ থাকবে। যতক্ষণ পক্ষপাতী ও প্রতিপক্ষ মিলে প্রীতি সহ বিতর্ক বা লেখা না করে, ততক্ষণ সত্য-অসত্যের সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। যখন জ্ঞানের মধ্যে সত্য-অসত্যের নির্ধারণ হয় না, তখন অজ্ঞদের অজ্ঞান অন্ধকারে পড়ে প্রচুর দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষয়ের অর্থে বন্ধুত্ত্বপূর্ণভাবে বিতর্ক ও লেখা করা আমাদের মানবজাতির প্রধান কাজ। যদি এটি না হয়, তবে মানুষের উন্নতি কখনও সম্ভব নয়।’
তেরোতম সমুল্লাসের অভ্যূমিকায় একই আশয় প্রকাশ করতে ঋষি লিখেছেন— “এই লেখা শুধুমাত্র সত্যের বৃদ্ধি এবং অসত্যের হ্রাসের জন্য লেখা হয়েছে, কারও দুঃখ দেওয়া বা ক্ষতি করা বা মিথ্যা দোষারোপ করার জন্য নয়।”
চৌদ্দতম সমুল্লাসে ইসলামের সমালোচনা করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম একতার দৃষ্টিতে এটি যথেষ্ট আপত্তিকর মনে হয়েছে। ১৯৪২ সালে সিন্ধের মুসলিম লীগ সরকার সত্যার্থপ্রকাশের চৌদ্দতম সমুল্লাস পড়া, ছাপা, বিক্রি, রাখা ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সার্বদেশিক আর্যপ্রতিনিধি সভা এবং সিন্ধ সরকার মধ্যে চিঠিপত্র চলছিল। যখন কোনও ফল পাওয়া যায়নি, তখন ২১-২২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে আর্য-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমগ্র ভারতের স্তরে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শান্তিপূর্ণ সমাধান আনতে একবার পুনরায় সিন্ধের প্রধানমন্ত্রী (এখন মুখ্যমন্ত্রী) সার গুলাম হুসাইন হিদায়াতুল্লাহর সাথে চিঠিপত্র চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সার্বদেশিক সভা সত্যাগ্রহের ঘোষণা দেয়।
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা-প্রধান মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজীর নেতৃত্বে পাঁচ সত্যাগ্রহীর প্রথম দল করাচিতে পৌঁছায়। এই দলে ছিলেন—
১। লা. খুশহালচন্দ আনন্দ (শ্রী আনন্দ স্বামী) – পঞ্জাব
২। শ্রী স্বামী অভেদানন্দ সরস্বতী – বিহার
৩। রাজগুরু শ্রী ধুরেন্দ্র শাস্ত্রী (স্বামী ধ্রুবানন্দ সরস্বতী) – উত্তর প্রদেশ
৪। কুংবর চন্দকরণ শারদা – রাজস্থান
৫। পণ্ডিত লক্ষ্মীদত্ত দীক্ষিত – দিল্লি
দল পৌঁছাতেই সিন্ধ সরকার অস্ত্র সমর্পণ করে এবং মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজী সফলভাবে সত্যাগ্রহের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
চৌদ্দতম সমুল্লাসের অনুভূমিকায় ঋষি লিখেছেন— “না অন্য কোনও মতের উপর, না এই মতের উপর মিথ্যা খারাপ বা ভালো প্রদানের উদ্দেশ্য রয়েছে, তবে যা ভালো তা ভালো এবং যা খারাপ তা খারাপ সবার জানা হোক। কেউ কারও উপর মিথ্যা চালাতে পারবে না এবং না সত্যকে রোধ করতে পারবে; সত্য-অসত্য প্রকাশিত হলেও ইচ্ছুক হলে কেউ মেনে নিক বা না নিক, কারও উপর জোর করা হয় না। এই লেখা হঠ, দুরাগ্রহ, ঈর্ষা, দ্বেষ, বিতর্ক এবং বিরোধ কমানোর জন্য করা হয়েছে, বাড়ানোর জন্য নয়, কারণ একে অপরকে ক্ষতি না করে পরস্পরের উপকার করা আমাদের প্রধান কাজ।”
এই সমুল্লাসের শেষে স্বামীজী লিখেছেন— “পরমাত্মা সমস্ত মানুষের প্রতি করুণাময় হোক, যেন সবাই প্রেমে, মিলনে এবং একে অপরের সুখের উন্নতিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন আমি আমার বা অন্যদের মত-মতান্তরের দোষ পক্ষপাতমুক্তভাবে প্রকাশ করি, তেমনই যদি সব জ্ঞানী করি, তবে কি কঠিন হবে যে পরস্পরের বিরোধ দূর হয়ে মিলন ঘটবে এবং আনন্দে ঐক্যমত হয়ে সত্য অর্জন সম্ভব হবে।”
সত্যার্থপ্রকাশের শেষ প্রকরণ 'স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশ'-এ ঋষি লিখেছেন— “আমি আমার মন্তব্য সেইজন্যই জানি যে, যা তিন কাল ধরে সকলের জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। আমার কোনো নতুন কল্পনা বা মতান্তর চালানোর সামান্যও উদ্দেশ্য নেই, তবে যা সত্য, তা গ্রহণ ও মান্য করা এবং যা অসত্য, তা ত্যাগ ও পরিত্যাগ করানো লক্ষ্য। যদি আমি পক্ষপাতী হতাম, তবে আর্যাবর্তে প্রচলিত মতগুলির মধ্যে একটি সম্পর্কে অনড় হতাম, তবে যা যা আর্যাবর্ত বা অন্যান্য দেশে অধর্মযুক্ত চলনচলতি আছে, তা আমি গ্রহণ করি না এবং যা ধর্মযুক্ত তা ত্যাগ করি না, কারণ এমন কাজ করা মানব-ধর্মের পরিপন্থী।” এই সমস্ত উদ্ধৃতি পড়ার পরে মহর্ষির বিরুদ্ধে পক্ষপাত বা অসহিষ্ণুতার অভিযোগ করা সম্পূর্ণ অন্যায় হবে।
ভারতে দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিতে খণ্ডন-মণ্ডন সর্বদা চলতে এসেছে। সমন্বয়বাদ নামে আজকাল বলা হয় ‘নিজ নিজ জায়গায় সবই সঠিক’, যা আধুনিকতা বা ভদ্রমন্যতার পরিচয় হিসেবে গণ্য হয়। অধিক বুদ্ধিমানদের মধ্যে শোনা যায়—সমালোচনা ঠিক আছে, কিন্তু খণ্ডন করা উচিত নয়। এভাবে বলার সময় তাদের মনে ‘সমালোচনা’ ইংরেজি criticism-এর এবং ‘খণ্ডন’ ইংরেজি condemnation-এর অর্থ ধারণ করে। এটি হয় কারণ তারা সমালোচনা ও খণ্ডন শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝে না।
‘রামালোচনা’ শব্দ সম্+আ উপসর্গসহ ‘লুচ’ ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ কোনো বস্তুকে সবভাবে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা। মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণে আমরা সেই বস্তুর রূপ-রঙ, গুণ-কর্ম-স্বভাব এবং গুণ-দোষের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ক্ষতি-লাভ বিবেচনা করি। তখনই আমাদের সেই বস্তুর পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জিত হয়। কৃষক বা মালী তার ক্ষেত বা বাগানে জন্মানো ঘাসপাত ও উদ্ভিদকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখেন। অপকারী বা ক্ষতিকারক ঘাসপাতকে তিনি বের করে দেন এবং উপকারী উদ্ভিদকে সেচ-সার দিয়ে পুষ্ট করেন।
একইভাবে সমাজের কল্যাণকামী মহাপুরুষ সমাজে বিদ্যমান ত্রুটি, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করে সমাজের উন্নয়নে সহায়ক চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার করেন। এটাই খণ্ডন-মণ্ডনের প্রকৃত রূপ। শরীরকে ক্ষতি পৌছে দেওয়া অঙ্গ কেটে ফেলা এবং সুস্থ অঙ্গ পুনঃপ্রতিস্থাপন করা শরীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খণ্ডন-মণ্ডন। সমাজকে সুস্থ ও শক্তিশালী করার জন্য মিথ্যা বিশ্বাস দূর করা আবশ্যক। দयानন্দের খণ্ডনের মূল উদ্দেশ্য এটিই ছিল।
ঋষির দূরদর্শিতা
মহর্ষি কতটা বিনয়ী ও দূরদর্শী ছিলেন, তা প্রমাণ করার জন্য আমরা ‘ঋষি দयानন্দ সরস্বতীর চিঠি ও বিজ্ঞাপন’-এর উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যা আর্শ সাহিত্য ও মহর্ষির গ্রন্থের গবেষকদের মতামত প্রতিফলিত করে—
“ঋষি দयानন্দের জীবনচরিত, তার গ্রন্থ, চিঠি ও বিজ্ঞাপনে ঋষি দयानন্দের দূরদৃষ্টি উদাহরণের সঙ্গে পূর্ণ। এমন একটি প্রসঙ্গ আমরা এখানে উপস্থাপন করছি। মুম্বই আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠার আগে এক ঘটনা ‘মুম্বই আর্যসমাজের ইতিহাস’-এ পৃ. ৮-এ উল্লেখ আছে—
‘শাস্ত্রার্থে জীবনজি-কে পরাজিত করার পর তার অবস্থানে তিনি মুম্বইয়ে সম্ভাব্য গৃহস্থ্য হয়ে ধর্মীয় আলোচনা চালিয়ে মুম্বইয়ে আর্যসমাজ স্থাপন করার জন্য স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এরপর তিনি সকলকে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন।’”
“ভাই, আমাদের কোনো স্বাধীন মত নেই। আমি তো বেদের অধীনে আছি এবং আমাদের ভারতবর্ষে পঁচিশ কোটি আর্য আছে। অনেক কথায় কিছু-কিছুতে ভিন্নতা রয়েছে। তাই তা বিবেচনা করলে আপনারই অব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি সন্ন্যাসী এবং আমার কর্তব্য হল যে, আপনারা যাদের অন্ন খাই, তাদের বিনিময়ে যা সত্য বুঝি, তা নির্ভীকভাবে উপদেশ করা। আমি কোনো খ্যাতির লোভী নই। কেউ আমার স্তুতি করুক বা নিন্দা করুক, আমি আমার কর্তব্য অনুযায়ী অর্থবোধ করাই। কেউ চাইলে মেনে নিক বা না নিক, এতে আমার কোনো ক্ষতি-লাভ নেই।”
তখন এক ভাই বললেন, “আমরা যদি সমাজ প্রতিষ্ঠা করি, এতে কি কোনো জনসাধারণের ক্ষতি হবে?”
এর জবাবে স্বামীজী বললেন— “আপনি যদি সমাজের মাধ্যমে পারপার্থক্য করে পরোপকার করতে পারেন, তবে সমাজ করুন। এতে আমার কোনো নিষেধ নেই। তবে এতে যথাযথ ব্যবস্থা না রাখলে ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খলা হবে। আমি শুধু যেমন অন্যদের উপদেশ দিই, আপনাদেরও তাই করব এবং এটুকু লক্ষ্য রাখবেন যে, আমার কোনো স্বাধীন মত নেই এবং আমি সর্বজ্ঞও নই। তাই যদি আমার কোনো ভুল ভবিষ্যতে পাওয়া যায়, যুক্তিপূর্ণ ভাবে পরীক্ষা করে তা সংশোধন করুন। যদি তা না করেন, তবে এটি নতুন একটি মত হয়ে যাবে এবং এভাবেই ‘বাবাবাক্যং প্রমাণম্’ বলে ভারতবর্ষে নানা ধরনের মতান্তর প্রচলিত হয়ে, ভেতরে ভেতরে দুরুগ্রহের ফলে ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পুত্ররা নানা রকমের ক্ষতি ভোগ করবে এবং ভারতবর্ষ দুঃখজনক অবস্থায় পড়বে। এতে একটি মত আরও বৃদ্ধি পাবে। আমার অভিপ্রায় হল, এই ভারতবর্ষে নানা ধরনের মতান্তর প্রচলিত থাকলেও তারা সব বেদকে মানে। সুতরাং বেদ-শাস্ত্রের সমুদ্রের মধ্যে এই সমস্ত নদী-নৌকা পুনরায় মিলিয়ে দেওয়ার ফলে ধর্মে একতা সৃষ্টি হবে এবং ধর্মের একতার মাধ্যমে জাগতিক ও ব্যবহারিক উন্নতি হবে। এতে কৌশল, কলা, দক্ষতা সবই উন্নত হবে এবং মানবজীবন সফল হবে, শেষে নিজের ধর্ম-শক্তি দ্বারা অর্থ, কাম এবং মুক্তি অর্জিত সম্ভব।”
ঋষি দয়ানন্দের উপরোক্ত কথন থেকে স্পষ্ট যে, তিনি আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে খুবই দ্বিধান্বিত ছিলেন। মতান্তরের ইতিহাস যা তাঁর সামনে ছিল, তা মনে রেখে তাঁর উদ্বেগ ছিল যে, নাকি আর্যসমাজও তার পিছনে, তাঁর নামে একটি সম্প্রদায় হয়ে যেতে পারে।— ‘ঋষি দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন’, সং. ৩, ভাগ ২, পৃ. ৮।
বস্তুত, মনুস্মৃতির প্রবক্তা মনুর পরে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক, এবং জাগতিক ও পরলোকীয় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্র ধর্মের প্রচারক দয়ানন্দ ছাড়া আর কোনো আচার্য বা ঋষি হননি। ঋষি দয়ানন্দ সরাসরি বেদের ভিত্তিতে কথা বলতেন। বেদের পরে মানবকৃত গ্রন্থে তিনি মনুর প্রমাণ্যতা স্বীকার করতেন। মনুস্মৃতির পরে এই গৌরব সত্যার্থপ্রকাশে প্রাপ্ত।
শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংশকের মতে, “ঋষি দয়ানন্দের লেখাগুলি বোঝার জন্য এটি লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঋষি দয়ানন্দের শৈলীতে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। যেমন মহর্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বহু স্থানে প্রা়ঢ়িবাদ দ্বারা সমাধান দেওয়া হয়েছে, তেমনি ঋষির গ্রন্থেও কিছু স্থানে প্রা়ঢ়িবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সমাধান সাময়িক, সুতরাং তা নীতি হিসেবে গণ্য করা যায় না। প্রা়ঢ়িবাদকে ঋষি দয়ানন্দ বিশেষ অবস্থায় গ্রহণ করতে অসঙ্গত মনে করেননি। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য সম্পর্কিত তাঁর লেখা ‘যদি শঙ্করাচার্য জৈনদের খণ্ডনের জন্য সেই (অদ্বৈত) মত গ্রহণ করে থাকে, তবে তা কিছু ভালো’ কথাটি মনোযোগের দাবি রাখে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দয়ানন্দের কোন লেখা নীতিগত এবং কোনটি প্রা়ঢ়িবাদ অনুযায়ী লেখা, তা আলাদা করা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রা়ঢ়িবাদ অনুযায়ী দেওয়া সমাধানকে নীতি মনে করলে অনেক স্থানে বেদাদি শাস্ত্রের (এবং কোথাও কোথাও তাঁর নিজের লেখা-ও) সঙ্গে বিরোধ হবে।”
সত্যার্থপ্রকাশের প্রথম সংস্করণ (সংবত ১৬৩২ বিক্রমী) এর কপিতে সত্যার্থপ্রকাশের রচনা সম্পর্কিত শ্লোক একটি পত্রে লেখা রয়েছে, যা এই রূপে রয়েছে—
এই ধরনের শ্লোক গ্রন্থকার ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা, সংস্কারবিধি, আর্যাভিবিনয় ইত্যাদির প্রারম্ভেও লিখেছেন। একই পরম্পরায় সত্যার্থপ্রকাশের আদিতে লিখিত উক্ত শ্লোক প্রথম সংস্করণে ভুলবশত ছাপা হয়নি। এই কারণে সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে এবং পরে প্রকাশিত সংস্করণেও ছাপা হয়নি। স্বল্পতম পার্থক্যে প্রথম শ্লোক ‘সংস্কারবিধি’ এবং ‘আর্যাভিবিনয়’ এর প্রারম্ভে এবং তৃতীয় শ্লোক ‘আর্যাভিবিনয়’ এর প্রারম্ভে পাওয়া যায়।
ও৩ঃম্ সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ
ভূমিকা
যখন আমি এই গ্রন্থ ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ রচনা করেছিলাম, তখন এবং তার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় বলার, পাঠ্যপাঠন করার সময় এবং জন্মভূমি হওয়ায় গুজরাতি ভাষা ব্যবহার করার কারণে আমার এই ভাষার বিশেষ জ্ঞান ছিল না, ফলে ভাষা কিছুটা অসংগত হয়ে গিয়েছিল। এখন ভাষা বলার ও লেখার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই এই গ্রন্থকে ভাষা-ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ করে দ্বিতীয়বার মুদ্রণ করানো হয়েছে। কোথাও কোথাও শব্দ-প্রয়োগ বা বাক্য-গঠনের পার্থক্য হয়েছে, এটি করা উচিত ছিল, কারণ এর পার্থক্য না করলে ভাষার ধারাবাহিকতা ঠিক করা কঠিন হত, তবে অর্থে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, বরং বিশেষ কিছু লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, যা প্রথম মুদ্রণে কোথাও কোথাও ভুল ছিল, তা বাদ দিয়ে, শোধন করে ঠিকঠাক করা হয়েছে।
এই গ্রন্থটি ১৪টি সমুল্লাস, অর্থাৎ চৌদ্দটি বিভাগে রচিত। এর মধ্যে ১০টি সমুল্লাস পূর্বার্ধে এবং ৪টি উত্তরার্ধে রয়েছে, তবে শেষের দুটি সমুল্লাস এবং পরবর্তী স্ব-সিদ্ধান্ত কোনো কারণে প্রথমে মুদ্রিত হয়নি, এখন সেগুলোও মুদ্রিত হয়েছে।
(১) প্রথম সমুল্লাসে ঈশ্বরের ওম্কাদারি নামের ব্যাখ্যা।
(২) দ্বিতীয় সমুল্লাসে সন্তানদের শিক্ষা।
(৩) তৃতীয় সমুল্লাসে ব্রহ্মচার্য, পাঠ্যপাঠন ব্যবস্থাপনা, সত্য-অসত্য গ্রন্থের নাম এবং পড়া-শেখার পদ্ধতি।
(৪) চতুর্থ সমুল্লাসে বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের আচরণ।
(৫) পঞ্চম সমুল্লাসে বনপ্রস্থান এবং সন্ন্যাসাশ্রমের পদ্ধতি।
(৬) ষষ্ঠ সমুল্লাসে রাজধর্ম।
(৭) সপ্তম সমুল্লাসে বিদেশী বিষয়।
(৮) অষ্টম সমুল্লাসে জগতের উৎত্তি, অবস্থান এবং প্রলয়।
(৯) নবম সমুল্লাসে বিদ্যা-অবিদ্যা, বন্ধন এবং মোক্ষের ব্যাখ্যা।
(১০) দশম সমুল্লাসে আচরণ-অনৈতিকতা এবং খাদ্য-অখাদ্য বিষয়।
(১১) একাদশ সমুল্লাসে আর্যাবর্তীয় মতমতান্তুরের খণ্ডন-মণ্ডন বিষয়।
(১২) দ্বাদশ সমুল্লাসে চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈনমতের বিষয়।
(১৩) ত্রয়োদশ সমুল্লাসে ঈসাই-মতের বিষয়।
(১৪) চৌদ্দতম সমুল্লাসে মুসলমানদের মতের বিষয়।
এবং চৌদ্দ সমুল্লাসের শেষে আর্যদের সাতন বেদবিধিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে, যা আমি যথাযথভাবে মানি। এই গ্রন্থ রচনার আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সত্যের প্রকৃত অর্থকে উদ্ভাসিত করা। অর্থাৎ যা সত্য, তাকে সত্যই বলা, এবং যা অসত্য, তাকে অসত্যই প্রতিষ্ঠিত করা — একেই আমি সত্যার্থের প্রকাশ বলে মনে করি। সেই কথা সত্য বলা যায় না, যেখানে সত্যের স্থানে অসত্য এবং অসত্যের স্থানে সত্য প্রতিপন্ন করা হয়। বরং যে বস্তু যেমন, তাকে তেমনই বলা, লেখা এবং তেমনই গ্রহণ করাকেই ‘সত্য’ বলা হয়।
___________________________________________________________________________________
সত্যার্থপ্রকাশ এর প্রথম সংস্করণের লেখার সূচনা আষাঢ় বদি ১৩, সং. ১৬৩১ অনুযায়ী ১২ জুন ১৮৭৪, শুক্রবারে হয়েছিল এবং পণ্ডিত ভাগবদত্তজি অনুযায়ী এই সমস্ত লেখা সং. ১৬৩১-এর মধ্য বা সেপ্টেম্বর ১৮৭৪-এ লেখা হয়েছে।
"এই গ্রন্থের ভাষা ব্যাকরণানুসারে ঠিকঠাক করা হয়েছে।" এই শব্দগুলি থেকে স্পষ্ট যে, গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণকে সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বলেননি। তবে "যা প্রথম মুদ্রণে কোথাও কোথাও ভুল ছিল, তা বাদ দিয়ে শোধন করে ঠিক করা হয়েছে" এবং "প্রত্যেকটি বিশেষ লেখা হয়েছে" এই শব্দগুলি থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম সংস্করণে কিছু বাদ ছিল, যা দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে।
নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য গ্রন্থকার তার ঋগ্বেদভাষ্য এবং যজুর্বেদভাষ্য এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, যা শ্রাবণ এবং ভাদ্রপদ সং. ১৬৩৫-এ মুদ্রিত হয়েছে, তাদের মুখপৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন মুদ্রণ করেছিলেন—
"সবাইকে জানা যাক যে, যে বিষয়গুলো বেদ এবং তাদের অনুযায়ী, আমি তা মানি, বিপরীত বিষয়গুলো না। তাই যা কিছু আমার বানানো ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ এবং ‘সংস্কারবিধি’ প্রভৃতি গ্রন্থে, গৃহ্যসূত্র বা মনুস্মৃতি প্রভৃতি বই থেকে অনেক বাক্য লেখা হয়েছে, তার মধ্যে বেদার্থের সাথে মিল থাকা বিষয়গুলোকে প্রমাণ স্বরূপ এবং বিপরীতকে অপ্রমাণ মানি। যা কিছু বেদার্থ থেকে উদ্ভূত, সেগুলোকে প্রমাণ স্বরূপ মানি, কারণ বেদ ঈশ্বর-বাণী হওয়ায় আমার কাছে সম্পূর্ণ মান্য। এবং যা কিছু ব্রহ্মা থেকে জৈমিনি মুনি পর্যন্ত মহাত্মারা বেদানুকূলভাবে রচনা করেছেন, তা আমি সাক্ষী সমান প্রমাণ হিসেবে মানি।"
এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ছিল একসাথে সকল বিভ্রান্তি দূর করা।
চৌদ্দ সমুল্লাস—প্রথম সংস্করণটি রাজা জয়কৃষ্ণদাস (মুরাদাবাদ) মুদ্রণ করেছিলেন। এরা ব্রিটিশদের রাজদরবারের আশ্রয়দাতা এবং তাঁদের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা উপাধিটিও তিনি ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অন্যদিকে রাজাজির মুসলমানদের (সির সাইয়্যদ আহমद খান প্রমুখ) সঙ্গেও বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তিনি এই লোকদের অসন্তুষ্ট করতে পারেননি। এই কারণেই প্রথম সংস্করণে ১৩তম এবং ১৪তম সমূল্লাস ছাপা হয়নি। রাজাজির পরিবারে প্রথম সংস্করণের হাতেলিখা কপি সংরক্ষিত আছে। তাতে এই দুটি সমূল্লাস বর্তমান রয়েছে। পরোপকারিণী সভার স্বর্গীয় মন্ত্রী দেওয়ান বহাদুর হবিবিলাস শারদা রাজাজির উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে প্রথম সংস্করণের হাতেলিখা কপি সংগ্রহ করে তার ফটোকপি করিয়ে নিয়েছিলেন। এই ফটো কপি পরোপকারিণী সভার সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু তাতে (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে) ১৩তম সমূল্লাস ইসলাম সম্পর্কিত এবং ১৪তম খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত।
প্রয়োজন— সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের প্রণয়নে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানবজাতিকে সত্য–অসত্যের বিচার করে সত্যকে গ্রহণ এবং অসত্যকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম করে তোলা। তিনি অন্যত্র লিখেছেন—
“এই মতগুলোর অল্প অল্প ত্রুটি প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলি দেখে মানুষ সত্য–অসত্যের সিদ্ধান্ত করতে পারে এবং সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের ত্যাগ করতে ও করাতে সক্ষম হয়।”
“এই সব মতবাদীদের, তাঁদের শিষ্যদের এবং অন্য সকলকে পারস্পরিক সত্য–অসত্যের বিচার করতে অধিক কষ্ট না হয়, এই জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এতে যে যে স্থানে সত্য মতের প্রতিষ্ঠা এবং অসত্যের খণ্ডন লিখিত হয়েছে, তা সকলকে জানানোই উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এতে যেমন আমার বুদ্ধি, যতটুকু বিদ্যা এবং এই চারটি মতের (পুরাণী, জৈনী, কিরাণী এবং কুরাণী) মূল গ্রন্থসমূহ দেখার দ্বারা যে জ্ঞান হয়েছে, তা সকলের সামনে নিবেদন করাকে আমি শ্রেয় মনে করেছি; কারণ লুপ্ত বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করা সহজ নয়। পক্ষপাত ত্যাগ করে এটি দেখলে সত্য–অসত্য সকলেরই জানা হয়ে যাবে। পরে নিজের নিজের বিবেচনা অনুসারে সত্য মত গ্রহণ করা এবং অসত্য মত ত্যাগ করা সহজ হবে।” — অনুভূমিকা ১
“এই লেখাটি যখন জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য লোক দেখবে, তখন সকলেরই সত্য–অসত্য বিষয়ক চিন্তা ও লেখালেখির সুযোগ ও জ্ঞান হবে।” — অনুভূমিকা ২
তুলনামূলক অধ্যয়ন— সকল মতবাদ ও সম্প্রদায়ের তুলনামূলক অধ্যয়ন না করলে সত্য–অসত্যের সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এখানে–সেখানে বিভিন্ন মতের প্রতীক বা প্রতিনিধিদের বাদী–প্রতিবাদীর রূপে উপস্থিত করে তাঁদের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে সত্যার্থকে জানাতে ও জানাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য—
“যখন পর্যন্ত বাদী–প্রতিবাদী হয়ে সৌহার্দ্যসহকারে বিতর্ক বা রচনা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য–অসত্যের সিদ্ধান্ত হতে পারে না।” — অনুভূমিকা ২
“এই লেখার উদ্দেশ্য এই যে, সকল মানুষের জন্য দেখা, শোনা, লেখা ইত্যাদি করা সহজ হবে। … সকল মানুষের উচিত যে সকলের মত–সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি দেখে বুঝে কিছু সম্মতি ও অসম্মতি প্রদান করা বা লেখা; না পারলে অন্তত শোনা—কারণ যেমন পড়লে পণ্ডিত হওয়া যায়, তেমনি শুনলেও বহুश्रুত হওয়া যায়। যদি শ্রোতা অন্যকে বোঝাতে না-ও পারে, তবুও নিজে তো বুঝেই যায়। যদি এক মতের লোক অন্য মতের বিষয়ে জানে আর অন্যরা না জানে, তবে যথার্থ সংলাপ সম্ভব নয়; কিন্তু অজ্ঞ লোক কোনো ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেন এমন না হয়, তাই এই গ্রন্থে প্রচলিত সব মতের বিষয় সামান্য করে লেখা হয়েছে। এতেই অবশিষ্ট বিষয়গুলোর সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে সেগুলো সত্য না মিথ্যা। যে যে বিষয় সর্বসম্মত সত্য, সেগুলো তো সবার মধ্যেই একরূপ। বিবাদ হয় মিথ্যা বিষয়গুলোতে। অথবা একটি সত্য এবং অপরটি মিথ্যা হলেও কিছুটা বিতর্ক চলেই। যদি বাদী–প্রতিবাদী সত্য–অসত্য নির্ণয়ের জন্য বিতর্ক করেন, তবে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।” — অনুভূমিকা ৩
___________________________________________________________________________________
যে মানুষ পক্ষপাতদুষ্ট হয়, সে নিজের অসত্যকেও সত্য এবং অন্য বিরোধী মতাবলম্বীর সত্যকেও অসত্য প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকে। তাই সে সত্য মত লাভ করতে পারে না। এই কারণেই বিদ্বান আপ্তব্যক্তিদের প্রধান কাজ হলো উপদেশ বা লেখার মাধ্যমে সকল মানুষের সামনে সত্য–অসত্যের স্বরূপ উপস্থাপিত করে দেওয়া। পরে তারা নিজেরাই নিজের কল্যাণ–অকল্যাণ বুঝে সত্যার্থকে গ্রহণ এবং মিথ্যার্থ কে পরিত্যাগ করে সর্বদা আনন্দে থাকবেন।
মানুষের আত্মা সত্য–অসত্যের জ্ঞানী, তবুও নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, হঠ, দূরাগ্রহ এবং অবিদ্যা প্রভৃতি দোষের কারণে সত্যকে ছেড়ে অসত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু এই গ্রন্থে এমন কোনো বিষয় রাখা হয়নি, এবং কারও মনকে দুঃখ দেওয়া বা কারও ক্ষতি সাধন করাই উদ্দেশ্য নয়; বরং যার দ্বারা মানবজাতির উন্নতি ও উপকার হয়, সত্য–অসত্যকে মানুষ বুঝে সত্যকে গ্রহণ এবং অসত্যকে পরিত্যাগ করে—কারণ সত্যোপদেশ ব্যতীত মানবজাতির উন্নতির অন্য কোনো কারণ নেই।
___________________________________________________________________________________
“এই লেখাটি একমাত্র মানুষের উন্নতি এবং সত্য–অসত্যের সিদ্ধান্তের জন্য; অর্থাৎ সব মতের বিষয়ে অল্প অল্প জ্ঞান হোক, এতে মানুষে মানুষে পরস্পর ভাববিনিময়ের সুযোগ পাবে এবং একে অপরের দোষের খণ্ডন করে গুণের গ্রহণ করবে। কোনো অন্য মতের উপর, না এ মতের উপর অকারণে নিন্দা বা প্রশংসা চাপিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য নয়; বরং যা কল্যাণকর তাই কল্যাণকর, আর যা দোষ তাই দোষ—এগুলো সবই সকলের জানা থাকুক। কেউ যেন কাউকে মিথ্যা বলে চালাতে না পারে এবং কেউ যেন সত্যকে থামাতে না পারে, এবং সত্য–অসত্য বিষয় প্রকাশিত করার পরও যার ইচ্ছা সে মানুক বা না মানুক—কাউকের ওপর কোনো জবরদস্তি করা হয় না। আর এই-ই ভদ্রলোকেদের রীতি যে, নিজের কিংবা পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে গুণ জেনে—গুণের গ্রহণ এবং দোষের পরিত্যাগ করবেন, এবং একগুঁয়েদের একগুঁয়েমি ও দূরাগ্রহ কমান–কমাতে সহায়তা করবেন।” সত্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থার কারণেই গ্রন্থকার তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের নিয়মগুলিতে তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। আর্যসমাজের চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়ম ক্রমান্বয়ে এইরূপ—
৪—সত্যকে গ্রহণ করা এবং অসত্যকে ত্যাগ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।
৫—সব কাজ ধর্মানুসারে, অর্থাৎ সত্য ও অসত্যকে বিবেচনা করে করা উচিত।
ঈশ্বর ও বেদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, সীমাহীন শ্রদ্ধা এবং গভীর আস্থার মূলে গ্রন্থকারের এই ধারণাই ছিল যে ঈশ্বর “সমস্ত সত্য বিদ্যার আদিমূল” (নিয়ম ১), এবং বেদ “সমস্ত সত্য বিদ্যার গ্রন্থ”। পরিশোধন—সত্যকে সর্বোপরি মান্য করার কারণে গ্রন্থকার কখনও তাঁর বক্তব্যকে “অন্তিম সিদ্ধান্ত” রূপে উপস্থাপন করেননি। লেখন বা মুদ্রণে অসাবধানতার ফলে কোনো ভুলের ইঙ্গিত পাওয়া গেলে ‘যেমন সেখানে সত্য হবে তেমনই করার’ জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মুন্সি বখ্তাবরসিংহের নামে প্রেরিত তাঁর এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— “যে সংস্কৃত বাক্যপ্রবোধ গ্রন্থ ছাপানো হয়েছে, তার বহু স্থানে রচনাটি অশুদ্ধ, এবং কিছু স্থানে সংস্কৃতবাক্যপ্রবোধে অশুদ্ধই ছাপা হয়েছে। এই অশুদ্ধির তিনটি কারণ আছে। এক, শীঘ্র প্রস্তুত করা; আমার চিত্ত সুস্থ না থাকা। দুই, ভীমসেনের অধীনে শোধন হওয়া এবং আমার না দেখা, না প্রুফ দেখা। তিন, ছাপাখানায় কোনো দক্ষ কম্পোজিটর না থাকা।”—মুন্সি বখ্তাবরসিংহের নামে গ্রন্থকারের পত্র, শ্রাবণ শুক্লা ১৩, বুধবার, সম্বৎ ১৬৩৭ (১৮ আগস্ট ১৮৮০)—ঋষি দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন, তৃতীয় সংস্করণ ১৬৮০, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩০৭–৮৮।
ধর্মীয় ঐক্য—গ্রন্থকারের বিশ্বাস ছিল যে “বিভিন্ন মতের বিদ্বানদের বিরোধই সকলকে বিরোধ-জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। যদি এরা নিজেদের উদ্দেশ্যে আবদ্ধ না থেকে সকলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান, তবে এখনই ঐকমত্য হয়ে যাবে।” —অনুভূমিকা ১।
সন ১৮৫৭–এর স্মৃতি এখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু তার ফলে যে স্বাভাবিক ঐক্য ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। জনগণের মধ্যে হতাশা-জনিত অকর্মণ্যতার ভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল, যেন ১৮৫৭–এর পরাজয়ের পর তারা নিজেদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। তার অবস্থা ছিল সেই রূপবতী বিধবার মতো, যার জীবনসঙ্গী চলে গেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের কারণে বহু লোলুপ ও কামুক ব্যক্তি তার ওপর অত্যাচার করছে। এমন অবস্থায় দুঃখ ও যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে কাউকেই প্রতিরোধ করতে না পেরে সে নিজেরেকে তাদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে পড়ে।
কিন্তু যেখানে অন্যায় ও অত্যাচার থাকে, সেখানে তার প্রতিবাদীও জন্ম নেয়। দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসন্তোষের ফলস্বরূপ এখানে-ওখানে বিদ্রোহের অঙ্কুর ফুটে উঠছিল। বাংলায় রাজা রামমোহন রায়ের পরম্পরায় ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ওজস্বী বক্তা বাবু কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন। বম্বেতে প্রার্থনাসমাজের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এবং রায়বাহাদুর ভোলানাথ সারাভাই প্রভৃতি সংস্কারক ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়্যদ আহমদ খাঁ নতুন প্রাণসঞ্চার করছিলেন। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভারতের নবনির্মাণ দৃশ্যমান হচ্ছিল, কিন্তু अखণ্ড ভারতের ঐক্য তখনও খণ্ড খণ্ডই ছিল। এই দিকে প্রচেষ্টা অবশ্য হচ্ছিল। স্বামী দয়ানন্দ দেশে-বিদেশে উদীয়মান এই শক্তিগুলিকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর মনে হল যেন একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটছে। তাঁর মেধা শুধু ভেদ দেখেই কাটাছেঁড়া করার মতো ছিল না। তিনি দোষগুলো দূর করে অবশিষ্ট গুণের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইতেন। তিনি চাইতেন দেশব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মনেতাদের এক মঞ্চে এনে এমন প্রেরণা দিতে, যাতে তাদের চিন্তাধারায় ঐক্য সৃষ্টি হয় এবং তারা সবাই মিলে সংস্কারের পথে এগিয়ে যান। তিনি উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ‘যেখানে ইচ্ছা সেখানে উপায়’—তিনি উপায় পেয়ে গেলেন।
জানুয়ারি ১৮৭৭ সালে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটন ভারতসম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার উপलক্ষে দিল্লিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের আয়োজন করেছিলেন। মনে হয়েছিল যেন সেই দরবার ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শক্তির এক প্রদর্শন। এই দরবারে রাজবংশ ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রধান ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ভারতের সুপরিচিত তাত্ত্বিক ও সমাজসংস্কারক মহাপুরুষরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। “সন্তন কাহা সীকরী সো কাজ”—তবু স্বামী দয়ানন্দও সেখানে পৌঁছেছিলেন। সবাই আসার কারণ আলাদা ছিল। স্বামী দয়ানন্দ এসেছিলেন এই ভাবনা নিয়ে যে সেখানে সমবেত সামাজিক নেতারা একত্রে চলার কোনো পথ নির্ধারণ করবেন। তাঁর ধারণা ছিল যে দেশের সমস্ত রাজারা সেখানে একত্র হবেন এবং যদি তারা তাঁর কথা শোনেন তবে খুব শীঘ্রই দেশে একতা প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর দরবারের সুযোগে রাজাদের নিজের নিজের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার ফুরসত থাকলে তারা কি করে এমন এক সন্ন্যাসীর কথা শুনতেন, যিনি তখন সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী এবং চরম নাস্তিক রূপে খ্যাত ছিলেন। এজন্য এ দিকে তিনি সফল হতে পারেননি।
স্বামী দয়ানন্দের দরবারে আসার দ্বিতীয় কারণ ছিল ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত সংস্কারকদের সঙ্গে পরামর্শ করা। তাই দরবারে উপস্থিত সমস্ত সংস্কারক নেতাদের তিনি তার বাসস্থানে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আজকের যুগে এই ধরনের ঐক্য-সম্মেলনের আয়োজন সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু তখন এ রকম আয়োজন ছিল এক অভিনব বিষয়। একে ভারতের প্রথম ঐক্য-সম্মেলন বলা যেতে পারে। তাতে ভারতের সকল প্রধান সংস্কারকরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান মিরর (Indian Mirror) তার ১৪ জানুয়ারি ১৮৭৭ সংখ্যায় লিখেছিল— “আমরা শুনেছি দিল্লিতে একটি পপুলার মিটিং হয়েছে। পণ্ডিত দयानন্দ সরস্বতীর বাসভবনে একটি কনফারেন্স এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে ভারতের বর্তমান সংস্কারকদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। আমাদের মন্ত্রী শ্রী কেশবচন্দ্র সেনও তাতে উপস্থিত ছিলেন। যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সংস্কারকদের মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক সত্য ও বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে সন্দেহ নেই যে বহুল ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর ফল জন্মাবে। আমরা এর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করি।”
এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—ব্রাহ্মসমাজের শ্রী কেশবচন্দ্র সেন, লাহোরের সুপরিচিত ব্রাহ্মসমাজ নেতা শ্রী নবীনচন্দ্র রায়, মুসলমানদের সর্বাধিক সম্মানিত নেতা স্যার সাইয়্যদ আহমদ খাঁ, রায়বাহাদুর শ্রী গোপালরাও হরিদেশমুখ, পূনা; খ্যাতনামা বেদান্তী মুন্সি কানহাইয়ালাল অলখধারী, লুধিয়ানা; মুন্সি ইন্দ্রমণি, মুরাদাবাদ; বাবু হরিশ্চন্দ্র চিন্তামণি, বোম্বাই এবং পণ্ডিত মনফুল। স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে রাজা জয়কৃষ্ণদাস সি. আই. ই. সহ বহু প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তবে তারা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন কি না, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এই সভার পূর্ণ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না, তবে এ কথা নিশ্চিত যে সেখানে বড় স্পষ্টতা ও উদারতার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন যে যদি আমরা সবাই একমত হয়ে এক পদ্ধতিতে দেশের সংস্কারের কাজে এগোই তবে দেশ দ্রুত উন্নত হতে পারে। দেশের ঐক্য ও সংস্কার প্রসঙ্গে সবাই একমত ছিলেন। দেশের জনমতও তাঁদের সঙ্গে ছিল। ইন্ডিয়ান মিরর–এর মন্তব্য আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। লাহোরের বিরাদেরে হিন্দ এ বিষয়ে লিখেছিল—
“আমরা পরম আনন্দের সঙ্গে এই কথা জানাই যে দিল্লি দরবারের উপলক্ষে হিন্দুস্তানের খ্যাতনামা ও যোগ্য সংস্কারকগণ পণ্ডিত দयानন্দ সরস্বতীর বাসভবনে একটি বিশেষ সভা এই উদ্দেশ্যে আয়োজন করেছিলেন যে আসলে আমাদের পার্থক্য ধর্ম থেকে নয়, মূল লক্ষ্য এক। উত্তম হবে যদি ভবিষ্যতে আলাদা আলাদা কাজ না করে সবাই একত্র হয়ে জাতির সংস্কারে নিযুক্ত হই এবং আমাদের মধ্যে যদি কোনো মতভেদ থাকে তবে তা পারস্পরিক বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে সমাধান করি।” —বিরাদেরে হিন্দ, লাহোর, জানুয়ারি ১৮৭৭
এতসব হওয়ার পরও সভাটি একমত হতে পারেনি। এর অসাফল্য সম্পর্কে এই সভারই একজন সদস্য বাবু নবীনচন্দ্র রায় আট বছর পরে তাঁর পত্র জ্ঞানপ্রদীপ-এ লিখেছিলেন—
“তারপর দ্বিতীয়বার আমাদের স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দিল্লিতে কায়সার-ই-হিন্দের দরবারে। সেখানে তিনি আমাদের, বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং শ্রী হরিশ্চন্দ্র চিন্তামণিকে আমন্ত্রণ করে প্রস্তাব করেছিলেন যে আমরা আলাদা আলাদা ধর্মোপদেশ না করে ঐক্যের সঙ্গে কাজ করলে বেশি ফল হবে; কিন্তু মূল বিশ্বাসে আমাদের তাঁদের সঙ্গে মতভেদ ছিল। তাই যেমন তিনি চেয়েছিলেন, ঐক্য গড়ে ওঠেনি।” —জ্ঞানপ্রদীপ, ভাগ ৪, নং ৩১–৩২, জানুয়ারি ১৮৮৫।
স্বামী দয়ানন্দের বিশ্বাস ছিল যে, দেশের অভ্যুদয় ও মানুষের কল্যাণ ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতদিন না সমগ্র দেশে এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই এক ধর্ম কেবল বৈদিক ধর্মই হতে পারে। ব্রাহ্মসমাজী এবং মুসলমানরা বেদকে নির্ভ্রান্ত ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণের স্পষ্ট উল্লেখ বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীতে পাওয়া যায়।
“বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন আবার দিল্লিতে স্বামী দयानন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি বলেন যে বহু বিষয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে একমত, কিন্তু একটি কথা তিনি বুঝতে পারেন না—বেদের আশ্রয় না নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা কীভাবে দেওয়া সম্ভব?”
— পি. এস. বসু রচিত Life and Words of Keshav Chandra Sen, পৃষ্ঠা ৩২
এইভাবে এই সম্মেলনের জাহাজ এসে বেদের অপৌরুষেয়তা ও নির্দোষতার প্রশ্নে আছড়ে পড়ে। এই কথার সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যায় যে, একবার বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বামীজিকে বলেছিলেন—আপনি যদি বেদের কথা না বলে এই কথা বলেন যে আপনি যা বলছেন তা ঈশ্বরের বার্তা, তবে মানুষ সহজেই আপনার কথা মেনে নেবে এবং ঐক্যের প্রয়াসে আপনি সাফল্য লাভ করবেন। স্বামীজি তা গ্রহণ করেননি। হজরত মুহাম্মদ বা ঈসামসীহের মতো তিনি নিজেকে খোদার পয়গম্বর কীভাবে মানতে পারতেন?
স্যার সैयদ আহমদ খাঁ স্বামীজিকে শুধু সম্মানই করতেন না, বরং এও মানতেন যে স্বামীজি যেভাবে বেদের অর্থ করেন, সেটাই সঠিক। শুধু তাই নয়, স্বামীজির অর্থব্যাখ্যার নীতির ভিত্তিতেই তিনি কোরআনের অর্থ ব্যাখ্যার ওপর জোর দিয়েছিলেন।
তিন বছর পরে, ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে, স্বামীজি আগ্রার সেন্ট পিটার্স চার্চের বিশপ মহাশয়কে বলেন যে, যদি আমরা, আপনি এবং অন্যান্য ধর্মের নেতারা কেবল সেই কথাগুলিরই প্রচার করি, যেগুলি সকলেই মানে, তবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তখন আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে কেবল নাস্তিকরাই থেকে যাবে। এটি ছিল তাঁর শেষ প্রয়াস; কারণ তিন বছর পরে, ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রয়াস ব্যর্থ হলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে তিনি আন্তরিকভাবে ভারতের ঐক্যে বিশ্বাস রাখতেন এবং এর জন্য ধর্মীয় নেতাদের পারস্পরিক মতভেদ দূর করাকে তিনি অপরিহার্য মনে করতেন।
স্বামীজি যখন ঐক্যের প্রচেষ্টায় ক্রমশ ব্যর্থ হতে থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মত বেদ ও বৈদিক ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে এবং বেদের বিরোধী বলে যা কিছু তিনি মনে করেছেন, তার তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তবু তাঁর সমালোচনায় কোথাও বিদ্বেষের লেশমাত্রও ছিল না। বাবু হরিশচন্দ্র চিন্তামণিকে তিনি বলেছিলেন—
“আমার উদ্দেশ্য সকলকে এমন প্রয়াসে একত্র করা, যেমন যুক্ত হাত। আমি কোল থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত একজাতীয়তার চেতনা জাগাতে চাই। আমার খণ্ডন হিতের জন্য।”
— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত জীবনচরিত
তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলেই তাঁর সদ্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি গির্জায় গিয়ে বাইবেলের খণ্ডন করেছেন এবং যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, কোরআনেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন; তবু বহু প্রাজ্ঞ খ্রিস্টান ও মুসলমান তাঁর ভক্ত ছিলেন। লাহোরে তাঁর প্রচারের কেন্দ্র যখন ড. রহিম খাঁর কোঠি হয়েছিল, তখন বম্বেতে আর্যসমাজ মন্দির নির্মাণে এক মুসলমান উদারতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। স্বামীজির মহানতা সকলেই স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর বিরোধীরাও (যাদের মধ্যে কাশী ও মহারাষ্ট্রের …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
এই গ্রন্থে যে-যে স্থানে ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধান বা মুদ্রণের সময় থেকে থেকে রয়ে গিয়ে থাকে, তা জানা-বুঝে যেমনটি সত্য হবে তেমনই সংশোধন করে দেওয়া হবে; আর কেউ পক্ষপাতবশত অন্যভাবে সন্দেহ বা খণ্ডন-মণ্ডন করবে, তার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। হ্যাঁ, যিনি সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণচিন্তক হয়ে কিছু জানাবেন, তা সত্য বলে বিবেচিত হলে তাঁর মত গ্রহণ করা হবে।
যদিও আজকাল প্রত্যেক মতের মধ্যে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি আছেন, তবুও তারা যদি পক্ষপাত ত্যাগ করে ‘সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত’—অর্থাৎ যেসব বিষয় সকলের অনুকূল ও সর্বত্র সত্য সেগুলির গ্রহণ, এবং যে বিষয়গুলি পরস্পরের বিরোধী সেগুলির পরিত্যাগ করে—প্রীতি সহকারে আচরণ করেন ও করান, তাহলে বিশ্বের সম্পূর্ণ কল্যাণ হবে; কারণ বিদ্বানদের বিরোধ থেকেই অবিদ্বানদের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি পেয়ে বহুবিধ দুঃখের বৃদ্ধি এবং সুখের হানি ঘটে। এই ক্ষতিটিই, যা স্বার্থপর মানুষের প্রিয়, সকল মানুষকে দুঃখসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে।
এদের মধ্যে যারা কোনো লোকহিতকে লক্ষ্য করে প্রবৃত্ত হন, তাদের সঙ্গে স্বার্থপর লোকেরা বিরোধ করতে উদ্যত হয়ে নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু ‘সত্যমেব জয়েৎ নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ’, অর্থাৎ সদা সত্যেরই জয় এবং অসত্যের পরাজয়, এবং সত্যের দ্বারাই বিদ্বানদের পথ প্রসারিত হয়—এই দৃঢ় বিশ্বাসকে আশ্রয় করে আচার্যরা পরোপকারকর্মে উদাসীন না হয়ে কোনোদিনই সত্যার্থের প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন না।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন—তাঁরাও শুধু যে স্বামীজির বিদ্বত্তা স্বীকার করতেন তাই নয়, এ কথাও মানতেন যে স্বামীজি যা বলতেন, সেটাই সঠিক; কিন্তু যুগের বিরোধিতা করে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সাহস তাঁদের ছিল না।
তবে তাহলে তাঁকে ভুলভাবে কেন বোঝা হল? আসলে কোনো ব্যক্তি ও তাঁর চিন্তাধারাকে বুঝতে হলে তাকে বারবার, প্রতিটি দিক থেকে দেখা প্রয়োজন। তখনই তার এমন এক রূপ ধরা পড়ে, যা একেবারেই নতুন বলে মনে হয়। যে এভাবে দেখবে, সে দयानন্দের বাহ্যিক রূক্ষতার আড়ালে প্রেমে পরিপূর্ণ কোমল ও উদার হৃদয়ের দর্শন পাবে। টলস্টয় ছিলেন পরম আস্তিক এবং ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন পরম নাস্তিক; তবু টলস্টয়ের প্রতি নিজের হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে গোর্কি যে কথাগুলি লিখেছেন, সেগুলি কত গভীর ও সত্য—
“নাস্তিক হয়েও আমি কোনো অজানা প্রেরণায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, কিন্তু ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাঁকে দেখেছিলাম এবং দেখে মনে হয়েছিল—এই মানুষটি তো যেন পরমাত্মার মতো।”
দयानন্দের প্রসঙ্গেও ঠিক এমন কথাই বলতে আমার কলম অস্থির হয়ে উঠছে।
এ কথা বলা যেতে পারে যে, যদি স্বামী দয়ানন্দের লক্ষ্য একটি সর্বসম্মত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে, তবে তাঁর বেদের উপর এত জোর দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু তাঁর এই অবস্থান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ছিল। বেদ যে সর্বপ্রাচীন, তা নিঃসন্দেহ। তার মহিমাও বিশ্ব স্বীকৃত। প্রশ্ন উঠতে পারে—এ কি কেবল অন্ধবিশ্বাস, না এর পেছনে রয়েছে গভীর চিন্তাভাবনা? নিছক অন্ধবিশ্বাসের উপর কোনো ধারণা অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকতে পারে না। চিন্তাশীল মানুষ কোনো না কোনো সময় তার পরীক্ষা করবেই; আর যখন সে উপলব্ধি করবে যে তার বিশ্বাস ফাঁপা অন্ধবিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তখন তা গ্রহণ করতে তার অসহায় বোধ হবে। বেদের ক্ষেত্রে এমন অনুভূতি কখনও দেখা দেয়নি। বেদের প্রাচীনতা মাথায় রাখলে এ কথা মানতে অসুবিধা হয় না যে, বেদে প্রতিপাদিত মূলধারাই পরবর্তীকালে নানা সম্প্রদায় ও মতের রূপ নিয়ে বিভক্ত হয়েছে। জাস্টিস গঙ্গাপ্রসাদের রচিত Fountain Head of Religions গ্রন্থে এই ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এর একটি বড় সুবিধা ছিল—হিন্দুদের সব সম্প্রদায়েরই বেদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় তাঁদের এক মঞ্চে আনা তুলনামূলক সহজ ছিল। অন্যান্য মত-মতান্তরও কিছু না কিছু মাত্রায় বেদের প্রতি আস্থাশীল।
বেদ সর্বপ্রাচীন হওয়ায় কোনো ধর্মেরই বৈদিক ধর্মের চেয়ে প্রাচীন বা সমকালীন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বর্তমানে পৃথিবীতে বহু মত প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। তাই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে সেগুলি সকলই সাম্প্রদায়িক। এর বিপরীতে, বেদের যুগে অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব না থাকায় বেদ এবং সেই সূত্রে বৈদিক ধর্ম মানবধর্ম রূপে অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্বমান্য—এ কথা যুক্তিসিদ্ধ। বিতর্কের জন্য ন্যূনতম দু’টির প্রয়োজন হয়। বহু বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়াও বিতর্কের বিষয় হতে পারে; কিন্তু যখন কেবল একটি মাত্র থাকে, তখন তার নির্বাচন স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বসম্মত হয়। এইভাবে সকল মত-মতান্তরের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য যৌথ ধর্ম হিসেবে বৈদিক ধর্মের প্রতি স্বামী দয়ানন্দের জোর দেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী ছিল।
এই ধরনেরই একটি সভার আয়োজন স্বামী দয়ানন্দের গুরু দণ্ডী স্বামী বিরজানন্দজি ১৮৬১ সালের শুরুতে করতে চেয়েছিলেন। সে সময় দেশীয় রাজ্যগুলির রাজাদের এক দরবার আগ্রায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল……, যেখানে বহু রাজা-মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জয়পুরের রাজা রামসিংহ প্রধান ছিলেন। দণ্ডীজি তাঁদের সামনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, একটি সর্বজনীন সভার আয়োজন করা হোক, যেখানে দেশজুড়ে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁরা এই বিষয়ে বিচার করবেন যে, কোন কোন গ্রন্থকে সত্য–অসত্য এবং ধর্ম–অধর্মের সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাজা জয়সিংহ এই সর্বজনীন সভার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে এই সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ষোলো বছর পরে গুরুবর বিরজানন্দের শিষ্য স্বামী দयानন্দ একই ধরনের প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও সফল হতে পারেননি। হা হন্ত!
“যদগ্রে বিষমিব”—গীতা ১৮.৩৭-এর এই সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে’মৃতোপমম্
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্
অর্থ—যা আরম্ভে বিষের মতো প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃতের সদৃশ, যা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে উৎপন্ন হয়, সেই (আধ্যাত্মিক) সুখ সাত্ত্বিক বলে কথিত। এর আশয় এই যে, যখন বুদ্ধি অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন মানুষ সত্য ও পরম সুখের অনুভব করে। এখানে এই বচন উদ্ধৃত করার মাধ্যমে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় পাঠকদের কাছে এই কথাটি স্পষ্ট করা বলেই প্রতীয়মান হয় যে, এই গ্রন্থে তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা আপাতদৃষ্টিতে কঠোর বা তিক্ত মনে হতে পারে; কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে তা সর্বজনহিতকর প্রমাণিত হবে। ইনজেকশনের সূচের মতো এর বিঁধুনি থেকে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় এটি হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবমাত্রের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক রোগসমূহকে প্রশমিত করার সর্বোত্তম ঔষধ হিসেবে প্রমাণিত হোক—এই পবিত্র অভিপ্রায় নিয়েই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
মত-মতান্তরের জাল—
গ্রন্থকারের সময়েই অসংখ্য মত ও সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাদের সংখ্যার অনুমান এ থেকেই করা যায় যে, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত—এই তিনটি বৃহৎ মতের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব মতেরই নিম্নলিখিত একুশটি সম্প্রদায় ছিল, যারা পরস্পরকে মিথ্যা বলে অভিহিত করত—
১. শ্রীসম্প্রদায়, ২. বল্লভাচারী, ৩. মধ্যাচারী, ৪. সনকাদি সম্প্রদায়, ৫. রামানন্দী, ৬. রাধাবল্লভী, ৭. নিত্যানন্দী, ৮. কবীরপন্থী, ৯. খাকি, ১০. দাদূপন্থী, ১১. মালুকদাসী, ১২. রামদাসী, ১৩. সেনাই, ১৪. মীরাবাই, ১৫. সখীভাব, ১৬. চরণদাসী, ১৭. হরিশচন্দ্রী, ১৮. সাধনাপন্থী, ১৯. মাধবী, ২০. বৈরাগী, ২১. নাগে।
শৈবদের সাতটি প্রধান সম্প্রদায়—
১. সন্ন্যাসী বা দণ্ডী প্রভৃতি, ২. যোগী, ৩. জঙ্গম, ৪. ঊর্ধ্ববাহু, ৫. গুদড়, ৬. রুখড়, ৭. কড়ালিঙ্গী।
শাক্তদের প্রধান ভেদগুলি নিম্নরূপ—
১. দক্ষিণাচারী, ২. কানচেলিয়ে, ৩. বাণী, ৪. কসরি, ৫. অঘোরী, ৬. গণপত্য, ৭. সৌরপত্য, ৮. নানকপন্থী, ৯. বাবা লালো, ১০. সাঘ, ১১. সতনামী, ১২. প্রাণনাথী, ১৩. শিবনারায়ণী, ১৪. শূন্যবাদী।
কিছু অন্যান্য সম্প্রদায়— চার্বাক, বামমার্গ, চক্রাঙ্কিত, রামস্নেহী, ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, স্বামী-নারায়ণ।
বৌদ্ধ এবং তার ভেদ; জৈন এবং তার ভেদ।
বিদেশি মত— খ্রিস্টধর্ম ও তার ভেদ; ইসলাম ও তার ভেদ।
তখন থেকে এখন পর্যন্ত কত যে নতুন নতুন মত জন্ম নিয়েছে, তার হিসাব নেই; আর আজও কুকুরমুতোর মতো প্রতিদিন জন্ম নিয়েই চলেছে। যেমন— রাধাস্বামী, নিরঙ্কারী, ব্রহ্মাকুমারী, হংসামতী, সাইবাবা, রজনীশ, মহেশ যোগী, আনন্দমার্গ, ঝুলেলাল প্রভৃতি।
একধর্ম নির্ণয়ের প্রক্রিয়া—
এতগুলি মত-মতান্তরের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করে প্রকৃত ধর্মের সিদ্ধান্ত কীভাবে করা যায়, তার উপায় গ্রন্থকার একাদশ সমুল্লাসে বর্ণনা করেছেন। সেখানে লেখা আছে—
একজন জিজ্ঞাসু কোনো আপ্তপুরুষের কাছে গিয়ে বলল— “মহারাজ! এই সহস্র সম্প্রদায়ের ঝামেলায় আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। অতএব আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন, যা আমি গ্রহণ করতে পারি।”
আপ্তপুরুষ বললেন— “যে বিষয়ে সকলের একমত, সেটাই বেদমত এবং গ্রহণযোগ্য; আর যেখানে বিরোধ আছে, তা কল্পিত, মিথ্যা, অধর্ম এবং অগ্রহণযোগ্য।”
জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করল— “এর পরীক্ষা কীভাবে হবে?”
আপ্তপুরুষ বললেন—
“তুমি গিয়ে এই এই কথাগুলি জিজ্ঞেস করো। তখন সকলের একমত হয়ে যাবে।”
তখন সে সেই সহস্র জনের সমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল—
“শোনো সকলেই! সত্যভাষণে ধর্ম আছে, না মিথ্যাভাষণে?”
সবাই একস্বর হয়ে বলল— “সত্যভাষণে ধর্ম আছে এবং মিথ্যাভাষণে অধর্ম।”
ঠিক তেমনই— “বিদ্যা অর্জন, ব্রহ্মচর্য পালন, পূর্ণ যৌবনে বিবাহ, সৎসঙ্গ, পুরুষার্থ, সত্যব্যবহার প্রভৃতিতে ধর্ম আছে, না অবিদ্যা গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য না করা, ব্যভিচার, কুসঙ্গ, অসত্যব্যবহার, ছল-কপট, হিংসা, পরহানি প্রভৃতিতে?”
সবাই একমত হয়ে বলল— “বিদ্যা প্রভৃতির গ্রহণে ধর্ম এবং অবিদ্যা প্রভৃতির গ্রহণে অধর্ম আছে।”
যাঁরা স্বামী দয়ানন্দকে একটি সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উপস্থাপন করতে চান, তাঁরা উপরিউক্ত পংক্তিগুলিতে প্রতিফলিত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং দরবারের উপলক্ষে ঐক্যের পথে তাঁর গৃহীত প্রচেষ্টার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করলে তাঁদের এই ধারণা পরিবর্তিত না হয়ে থাকতে পারে না। সত্যের প্রতি গ্রন্থকারের নিষ্ঠার সাক্ষ্য স্থানে স্থানে, সর্বত্রই পাওয়া যায়। বিভিন্ন মত-মতান্তরের প্রত্যাখ্যান করতে গিয়েও তাঁর লক্ষ্য ছিল শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান করে সেই সত্যকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্বার্ধের সমাপ্তিতে দশম সমুল্লাসের শেষে তিনি লিখেছেন—
“বিদ্বানদের কাজ এই-ই যে, সত্যাসত্যের বিচার করে সত্য গ্রহণ এবং অসত্য ত্যাগ করে পরম আনন্দ লাভ করা।”
মনুষ্যের লক্ষণ—
“যে মননশীল হয়ে নিজের মতোই অপরের সুখ-দুঃখ এবং লাভ-ক্ষতি বোঝে, অন্যায়কারী শক্তিশালীকেও ভয় না করে এবং ধর্মাত্মা দুর্বলকেও ভয় করে—তাকেই মনুষ্য বলা যায়। শুধু তাই নয়, বরং নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ধর্মাত্মাদের—তাঁরা মহা অনাথ, দুর্বল ও গুণহীন হলেও—রক্ষা, উন্নতি ও প্রিয় আচরণ করে; আর অধর্মী ব্যক্তি—সে চক্রবর্তী, সনাথ, মহাবলবান ও গুণবান হলেও—তার বিনাশ, অবনতি ও অপ্রিয় আচরণ সর্বদা করে। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব অন্যায়কারীদের শক্তি হ্রাস এবং ন্যায়কারীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই কাজে যতই ভয়ানক দুঃখ আসুক, এমনকি প্রাণ গেলেও, এই মনুষ্যরূপ ধর্ম থেকে কখনও বিচ্যুত না হয়।”
— স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশ
সত্যাগ্রহ—
স্বামীজি যা বলেছেন, তা তিনি সারা জীবন যাপন করে দেখিয়েছেন। উপরিউক্ত পংক্তিতে যে ‘মনুষ্যরূপ ধর্ম’-এর উল্লেখ আছে, তার সজীব উদাহরণে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।
স্বামী দয়ানন্দ প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিলিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তৎকালীন কোটিপতি বলে পরিচিত খাজাঞ্চি লক্ষ্মীনাৰায়ণের কোঠিতে অবস্থান করেন। তখন ইংরেজদের শাসন চলছিল। লক্ষ্মীনাৰায়ণজি স্বামীজির সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টভাষিতা ও নির্ভীকতায় কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। বেরিলির কমিশনারের আদেশ পেয়ে একদিন ভয়ে ভয়ে তিনি স্বামীজিকে বললেন যে ইংরেজদের অসন্তুষ্ট করা ভালো নয়। সেই রাতেই টাউন হলে স্বামীজির বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। তখন সেখানে কমিশনার মিস্টার এডওয়ার্ডস, কালেক্টর রিড, পাদ্রি স্কট এবং আরও ১৫–২০ জন ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনের বক্তৃতার বিবরণ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (যিনি তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন) তাঁর আত্মকথা কল্যাণমার্গের পথিক গ্রন্থে এইভাবে লিখেছেন—
“বক্তৃতার বিষয় ছিল—আত্মার স্বরূপ। বক্তৃতার মধ্যে সত্যের শক্তির প্রসঙ্গ ওঠে। সত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য (দয়ানন্দ) বললেন— ‘লোকেরা বলে, সত্য প্রকাশ কোরো না, কালেক্টর রাগ করবেন, অসন্তুষ্ট হবেন, গবর্নর কষ্ট দেবেন। আরে! চক্রবর্তী রাজাও যদি অসন্তুষ্ট হন, তবু আমরা তো সত্যই বলব।’ এরপর একটি শ্লোক (সম্ভবত—‘নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাৱকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥’—গীতা ২.২৩) পাঠ করে আত্মার স্তব করলেন। কোনো অস্ত্র তাকে কাটতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না এবং বায়ু তাকে শুকাতে পারে না। সে নিত্য, সে অমর। তারপর গর্জনময় কণ্ঠে বললেন—‘এই দেহ অনিত্য; এর রক্ষার জন্য অধর্ম করা অর্থহীন।’ এরপর চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সিংহনাদ করে বললেন—‘কিন্তু সেই বীর পুরুষকে আমাকে দেখাও, যে আমার আত্মাকে নষ্ট করার দাবি করে। যতদিন পর্যন্ত এমন বীর পুরুষ এই সংসারে দেখা না যায়, ততদিন আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে রাজি নই যে আমি সত্যকে চাপা দেব কি দেব না।’ সমগ্র হলে নিস্তব্ধতা নেমে এল। রুমাল পড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছিল।”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
এটি এক দৃঢ় সংকল্প যে— “যদগ্রে বিষমিব ফলামে’মৃতোপমম্”—এই গীতার (১৮.৩৭) বচন। এর অভিপ্রায় এই যে, যে-যে বিদ্যা ও ধর্মপ্রাপ্তির কর্ম আছে, সেগুলি প্রথমে করবার সময়ে বিষের তুল্য এবং পরিণামে অমৃতের সদৃশ হয়। এই কথাগুলিকে চিত্তে ধারণ করেই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি। শ্রোতা বা পাঠকগণও প্রথমে প্রেমসহকারে এই গ্রন্থটি দেখে এর সত্য-সত্য তাত্পর্য অনুধাবন করে যথাযথ আচরণ করুন।
এতে এই অভিপ্রায় রাখা হয়েছে যে, সকল মতের মধ্যে যে-যে সত্য ও যথার্থ বিষয় রয়েছে, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিরুদ্ধ হওয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে; আর যে-যে মত-মতান্তরের মধ্যে মিথ্যা বিষয় রয়েছে, সেগুলির খণ্ডন করা হয়েছে। এতে আরও এই অভিপ্রায় রাখা হয়েছে যে, সকল মত-মতান্তরের গোপন বা প্রকাশ্য কু-বিষয়গুলির প্রকাশ করে বিদ্বান-অবিদ্বান সর্বসাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সকলে মিলিতভাবে বিচার-বিবেচনা করে, পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব পোষণ করে এক সত্য মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। যদিও আমি আর্যাবর্ত দেশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখানেই বসবাস করি, তথাপি যেমন এই দেশের মত-মতান্তরের মিথ্যা কথাগুলির প্রতি পক্ষপাত না করে যথাযথভাবে সত্য প্রকাশ করি, তেমনই অন্যান্য দেশের বাসিন্দা বা মতোন্নত ব্যক্তিদের সঙ্গেও একই রূপে আচরণ করি। যেমন স্বদেশবাসীদের সঙ্গে মানবোন্নতির বিষয়ে আচরণ করি, তেমনই বিদেশীদের সঙ্গেও করি; এবং সকল সজ্জনের পক্ষেও এইরূপ আচরণ করাই উচিত। কারণ আমি যদি কোনো এক পক্ষের প্রতি পক্ষপাতী হতাম, তবে আজকাল যেমন স্বমতের প্রশংসা, মণ্ডন ও প্রচারে এবং অপরের মতের নিন্দা, ক্ষতি ও দমনে লোকেরা তৎপর থাকে, তেমনই আমিও হতাম। কিন্তু এই ধরনের আচরণ মানবত্বের বাইরে। কেননা যেমন পশু শক্তিশালী হয়ে দুর্বলকে দুঃখ দেয় এবং হত্যা পর্যন্ত করে, তেমনই যদি মানুষ দেহ পেয়েও সেইরূপ কর্ম করে, তবে সে মানবস্বভাবসম্পন্ন নয়, বরং পশুর মতো। আর যে শক্তিশালী হয়ে দুর্বলের রক্ষা করে, সেই-ই “মানুষ” নামে অভিহিত হয়; আর যে স্বার্থবশত কেবল অপরের ক্ষতি করতেই থাকে, সে জেনো পশুদেরও বড় ভাই।
এখন আর্যাবর্তীয়দের বিষয়ে বিশেষভাবে একাদশ সমুল্লাস পর্যন্ত লেখা হয়েছে। এই সমুল্লাসগুলিতে যে সত্য মত প্রকাশ করা হয়েছে, তা বেদোক্ত হওয়ায় আমার নিকট সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য; আর যে নতুন পুরাণ, তন্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত কথাগুলির খণ্ডন করা হয়েছে, সেগুলি পরিত্যাজ্য।
যদিও দ্বাদশ সমুল্লাসে চার্বাকের মত লেখা হয়েছে, তা এই কালে প্রায় ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায়; এবং এই চার্বাক বৌদ্ধ ও জৈন মতের সঙ্গে অনীশ্বরবাদী প্রভৃতিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য রাখে। চার্বাকই সর্বাপেক্ষা বড় নাস্তিক। একে দমন করা অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ মিথ্যা কথা যদি রোধ করা না যায়, তবে সংসারে বহু অনর্থ প্রবৃত্ত হবে।
চার্বাকের যে মত, এবং বৌদ্ধ ও জৈনের যে মত, সেগুলিও দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের মতের সঙ্গেও চার্বাকের বহু মিল আছে, আবার কিছুটা বিরোধও আছে। জৈন মত বহু অংশে চার্বাক ও বৌদ্ধদের সঙ্গে মিল রাখে, আবার অল্প কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে; সেই কারণেই জৈনদের একটি পৃথক শাখা গণ্য করা হয়। সেই ভেদ দ্বাদশ সমুল্লাসে লেখা হয়েছে—যথাযথভাবে সেখানেই বুঝে নেওয়া উচিত। যা যা তাদের মধ্যে ভিন্ন, তা দ্বাদশ সমুল্লাসে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিষয়ও সেখানে বিবৃত হয়েছে।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
শাহপুরা থেকে যোধপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় আজমিরের আর্যপুরুষরা স্বামীজিকে যোধপুরে যেতে বিরত রাখার চেষ্টা করে বললেন—
“যোধপুরের লোকেরা সেখানকার মাটির মতোই শুষ্ক প্রকৃতির, সংবেদনাহীন এবং কঠোর স্বভাবের। আপনার সেখানে যাওয়া কোনোভাবেই কল্যাণকর হবে না।”
আজমিরবাসীরা তৎকালীন মারোয়াড়কে রাক্ষস-ভূমি বলে অভিহিত করলেন এবং স্বামীজির আসন্ন অকল্যাণের কল্পনায় তারা গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন; কিন্তু স্বামীজি নির্ভীক ও উদ্বেগহীন কণ্ঠে বললেন— “সত্যের প্রচারের জন্য যত বড় কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন, তাতে আমার কোনো সংকোচ থাকবে না।” নিজের এই বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে তিনি এখান পর্যন্ত বললেন— “যদি সেখানকার লোকেরা তাঁর সত্যকথনে বিরক্ত হয়ে তাঁর আঙুলগুলো বাতির মতো জ্বালিয়েও দেয়, তবুও তিনি সত্য বলার থেকে পিছপা হবেন না।”
উদয়পুর রাজ্য রাজস্থানের শিরোমণি। তৎকালীন শাসক মহারাণা সাজ্জনসিং একদিন স্বামীজিকে বললেন—“মেওয়াড় রাজ্যে একলিঙ্গ মহাদেবের অত্যন্ত প্রতিপত্তি রয়েছে। মেওয়াড়ের শাসকরাও নিজেদের একলিঙ্গ মহাদেবের দেওয়ান বলে মনে করেই রাজ্য শাসন করেন। আপনি যদি এর মহন্ত হয়ে যান, তবে কতই না ভালো হয়। লক্ষ লক্ষ সম্পত্তির আপনি অধিকারী হবেন, যা আপনি বেদভাষ্য প্রকাশ এবং অন্যান্য লোককল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি মূর্তিপূজা করবেন না—শুধু নীতিগতভাবে তার খণ্ডন করবেন না।”
মহারাণার এই সদ্ভাবনাপূর্ণ কিন্তু বিচিত্র প্রস্তাব শুনে দয়ানন্দের মতো ধীর প্রকৃতির পুরুষও একবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি ওজস্বী কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন— “রাণাজি! এই প্রস্তাব আপনি কার সামনে রাখছেন? আপনার রাজ্য তো এতটাই ছোট যে আমি এক দৌড়েই এর বাইরে চলে যেতে পারি, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের ব্রহ্মাণ্ডরূপী রাজ্য ছেড়ে আমি কোথায় যাব?”
জৈনদের গ্রন্থ—
আর্যসমাজ মুম্বইয়ের তৎকালীন মন্ত্রী শ্রী সেবকলাল কৃষ্ণদাস তাঁর ১৫ জানুয়ারি ১৮৮১ তারিখের পত্রে জৈনদের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতে, এই গ্রন্থগুলি সেবকলাল কৃষ্ণদাস স্বামীজি মহারাজের আদেশে সংগ্রহ করেছিলেন। এই পত্রের শেষে জৈনদের আরও বহু গ্রন্থের নামও লিখিত আছে, যেগুলিও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এই পত্রটি মহাত্মা মুনশীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) জি কর্তৃক সম্পাদিত ‘ঋষি দয়ানন্দের পত্রব্যবহার’ প্রথম ভাগে পৃষ্ঠা ২৫৫ থেকে ২৬৪ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। সত্যার্থপ্রকাশে মুদ্রিত নামগুলির সঙ্গে এই পত্রে যেসব নামের সামান্য পার্থক্য রয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ—
এগারো অঙ্গ ৩—ঠাণাঙ্গসূত্র
বারো উপাঙ্গ ২—রায়পসেনীসূত্র ৪—পত্রবণাসূত্র ৫—জম্বুদ্দীপপন্নত্তীসূত্র ৬—চন্দপন্নত্তীসূত্র ৭—সুরপন্নত্তীসূত্র ৮—নিরিয়াবলিসূত্র ১১—পুষ্পিয়াসূত্র ১২—পুষ্পচূলিয়াসূত্র
ছয় ছেদ ৪—পিণ্ডনির্যুক্তিসূত্র ৫—ঔঘনির্যুক্তিসূত্র ৬—পর্যুষণাসূত্র
দশপন্নসূত্র ১—চতুঃশরণসূত্র ২—পঞ্চখানসূত্র ৩—তন্দুলবৈয়ালিকসূত্র ৪—ভক্তিপরিগ্যানসূত্র ৭—গণিবিজ্বাসূত্র ৬—দেবেন্দ্রস্তবনসূত্র ১০—সংস্থারসূত্র
পাঁচ পঞ্চাঙ্গ ২—নির্যুক্তি ৩—চর্ণী
“না দিতে, না শুনাতে”—ইত্যাদি লেখার কারণে জৈন লেখকেরা গ্রন্থকারকে বহু কটু বাক্যেও আক্রমণ করেছেন। সত্যার্থপ্রকাশ ও সেবকলাল কর্তৃক নির্দেশিত গ্রন্থনামগুলিতে কিছু অশুদ্ধি রয়েছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করেছি। এমন লোকদের সন্তুষ্টির জন্য এখানে আমরা একজন প্রামাণিক জৈন বিদ্বানের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি—
“এর থেকেও খারাপ বিষয় হলো, জৈনরা ধর্মীয় কারণে অজৈনদের তাদের পবিত্র গ্রন্থ পড়তে তো দেয়ই না, এমনকি সেগুলি দেখা বা স্পর্শ করতেও দেয় না।”
— Outlines of Jainism, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১২, জগমন্দরলাল জৈন এম.এ.
অর্থাৎ—এর থেকেও নিকৃষ্ট কথা এই যে, জৈনরা তাদের পবিত্র গ্রন্থ অজৈনদের পড়তে দেওয়া তো দূরের কথা, দেখতেও বা ছুঁতেও দেয় না।
আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি এবং তাত্পর্য ছাড়া বাক্যের প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না।
১. ‘পয়ত্রাসূত্র’—ভুল পাঠসহ সংস্করণ থেকে মুদ্রিত হচ্ছে।
২. ৩০ নম্বর মুদ্রণ, সং. ৬-এ ‘দেবেন্দ্রস্তমনসূত্র’ এইরূপ ভুল পাঠ মুদ্রিত হয়েছে।
৩. চরণী = চূর্ণি।
৪. এর পরবর্তী অংশে সংস্করণ ৩৪ (আজমীর মুদ্রিত)-এ কোষ্ঠকের মধ্যে [তুলনা করুন—প্রকরণরত্নাকর, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৭১] এই পাঠ মূল গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। সং. ৩৫-এও এই পাঠ মুদ্রিত হয়েছে।
তাই গ্রন্থকার এখানে এটি নির্দেশ করা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। সাধারণভাবে 'আকাঙ্ক্ষা' বলতে বোঝায়—পদ থেকে উদ্ভূত অর্থের অন্বয়-বোধ করানোর মাধ্যমে অভিলাষের অনুপস্থিতি, কিন্তু গ্রন্থকারের মতে এর দ্বারা বাক্যস্থ পদগুলোর পরস্পরের সাথে এবং বক্তার মতো আকাঙ্ক্ষা করা অর্থে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বাক্যরচনা এমন হওয়া উচিত যাতে পদসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। তখনই তাদের মধ্যে যোগ্যতার সম্ভাবনাও থাকতে পারে।
গ্রন্থকারের এই মত অযৌক্তিক নয়, বরং আকাঙ্ক্ষা পদটির লোকসিদ্ধ অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাক্যে কোন পদ কোনটির সঙ্গে অন্বয় হবে, তা নির্ধারণ হয় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। অতএব আকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গ্রন্থকার প্রথম স্থান আকাঙ্ক্ষাকে দিয়েছেন। এইভাবে চিন্তা করলে আপত্তি ক্ষুদ্র হয়ে যায়।
বাৎস্য়ায়ন মুনি বলেছেন— ‘যস্য যেযার্থসম্বন্ধোঁ দূরস্থস্থাপি তস্য সঃ। অর্থতো হ্যসামর্থানামানন্তর্যমকারণম’-ন্যায়ভাষ্য ১.২৭৬।
অর্থাৎ—যে পদের যার সঙ্গে অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে, তা দূরে হলেও তারই। অর্থের কারণে অক্ষম বা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অযৌক্তিক পদগুলির নিকটতা অন্বয়ের কারণ হতে পারে না। এজন্য অলঙ্কারবিদরা আসত্তির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যদি একটি পদ 'গাম' সকালকালে এবং অন্য পদ 'আনয়' সন্ধ্যায় বলা হয়, তবুও এ পদগুলির অন্বয়ের যোগ্যতা থাকলেও এই বাক্যটি বলা যাবে না।
যোগ্যতা—যোগ্যতার সাধারণ অর্থ হলো—ক্ষমতা, সামর্থ্য, সঙ্গতি, উপযুক্ততা বা যৌক্তিকতা।
১। 'মন' শব্দের তৃতীয় একবচনের প্রতিরূপক শব্দ। এরই প্রাকৃতিক বিকৃত রূপ 'মংসা' ব্যবহৃত হয়। মংসা = ইচ্ছা বা চিন্তা।
দর্শনে এটি শব্দগুলির দ্বারা নির্দেশিত বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের অমিলের অভাবের প্রতীক।
'জলেন সিঞ্চতি' যোগ্যতার উদাহরণ, কিন্তু 'অগ্নিনা সিঞ্চতি' তে যোগ্যতা নেই। এর সংজ্ঞা হলো—‘এক পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে সংযোগই যোগ্যতা।’
আসত্তি—‘কারণং সন্নিধান তু পদস্য আসতিঃ’—যা দ্বারা নিকটস্থ পদগুলির সম্পর্ক এবং তাদের মাধ্যমে প্রকাশিত ভাব বোঝা যায়, তাকে আসত্তি বলে।
তাত্পর্য—‘বক্তুর ইচ্ছা তু তাত্পর্য পরিকীর্তিতঃ’—যে চিন্তাধারা দ্বারা বক্তা শব্দ উচ্চারণ করেন, তাকে তাত্পর্য বলে। এর নির্ধারক উপাদান এই শ্লোকে উল্লেখ আছে—
উপক্রমোপসংহারাভ্যসো’পুর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাত্পর্যনির্ণয়ে।।
অর্থাৎ, উপক্রম (আরম্ভ), উপসংহার (সমাপ্তি), পুনরুক্তি, অপূর্বতা, অর্থবাদ (প্রশংসা), অবাপ্তি (যুক্তিসঙ্গত হওয়া) এর মাধ্যমে তাত্পর্য নির্ধারণ করা হয়।
১। অর্থাৎ ‘মেরা’। এটি গুজরাটি ভাষার ব্যবহার। অজমের মুদ্রিত সংস্করণ ৪-এ 'করকে মেরা বা' এবং সংস্করণ ৫ থেকে 'করনা মেরা বা' পাঠ প্রকাশিত হয়েছে।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
এর মধ্যে বৌদ্ধদের দীপবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বৌদ্ধমত-সংগ্রহ ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’-এ যে বৌদ্ধমত প্রদর্শিত হয়েছে, সেখান থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর জৈনদের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি আছে। সেগুলির মধ্যে—
চারটি মূলসূত্র, যথা— ১. আবশ্যকসূত্র, ২. বিশেষ আবশ্যকসূত্র, ৩. দশবৈকালিকসূত্র, এবং ৪. পক্ষিকসূত্র।
এগারোটি অঙ্গ, যথা—
১. আচারাঙ্গসূত্র, ২. সুগডাঙ্গসূত্র, ৩. ঠাণাঙ্গসূত্র, ৪. সমবায়াঙ্গসূত্র, ৫. ভগবতীসূত্র, ৬. জ্ঞাতাধর্মকথাসূত্র, ৭. উপাসকদশাসূত্র, ৮. অন্তগড়দশাসূত্র, ৯. অনুত্তরোপপাইকসূত্র, ১০. বিপাকসূত্র, এবং ১১. প্রশ্নব্যাকরণসূত্র।
বারোটি উপাঙ্গ, যথা— ১. উপপাইকসূত্র, ২. রায়পসেনীসূত্র, ৩. জীবাভিগমসূত্র, ৪. পন্নগণাসূত্র, ৫. জম্বুদ্বীপপন্নতীসূত্র, ৬. চন্দপন্নতীসূত্র, ৭. সুরপন্নতীসূত্র, ৮. নিরিয়াবলীসূত্র, ৯. কপ্পিয়াসূত্র, ১০. কপবড়িসয়াসূত্র, ১১. পূপিয়াসূত্র, এবং ১২. পুষ্পচূলিয়াসূত্র।
পাঁচটি কল্পসূত্র, যথা— ১. উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ২. নিশীথসূত্র, ৩. কল্পসূত্র, ৪. ব্যবহারসূত্র, এবং ৫. জিতকল্পসূত্র।
ছয়টি ছেদ, যথা— ১. মহানিশী বৃহদ্বাচনাসূত্র, ২. মহানিশীথ লঘুবাচনাসূত্র, ৩. মধ্যমবাচনাসূত্র, ৪. পিণ্ডনিরুক্তিসূত্র, ৫. ঔঘনিরুক্তিসূত্র, ৬. পর্যুষণাসূত্র।
দশটি পয়ন্নসূত্র, যথা— ১. চতুর্শরণসূত্র, ২. পঞ্চখাণসূত্র, ৩. তন্দুলবৈয়ালিকসূত্র, ৪. ভক্তিপরিজ্ঞানসূত্র, ৫. মহাপ্রত্যাখ্যানসূত্র, ৬. চন্দাবিজয়সূত্র, ৭. গণীবিজয়সূত্র, ৮. মরণসমাধিসূত্র, ৯. দেবেন্দ্রস্তবনসূত্র, এবং ১০. সংসারসূত্র।
এছাড়া নন্দীসূত্র ও যোগোদ্ধারসূত্রকেও প্রামাণিক বলে মানা হয়।
পঞ্চাঙ্গ, যথা— ১. পূর্বোক্ত সকল গ্রন্থের টীকা,
২. নিরুক্তি, ৩. চরণী, ৪. ভাষ্য।
এই চারটি অবয়ব এবং সকল মূল গ্রন্থ মিলিয়ে ‘পঞ্চাঙ্গ’ বলা হয়।
এগুলির মধ্যে ঢুঁঢিয়া সম্প্রদায় অবয়বগুলি মানে না এবং এগুলি ছাড়াও বহু গ্রন্থ আছে, যেগুলি জৈনরা মান্য করে। এদের মতের উপর বিশেষ আলোচনা দ্বাদশ সমুল্লাসে দেখে নেওয়া উচিত।
জৈনদের গ্রন্থগুলিতে লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তিদোষ রয়েছে এবং এদের এই স্বভাবও আছে যে, যদি তাদের গ্রন্থ অন্য মতাবলম্বীর হাতে থাকে বা মুদ্রিত হয়, তবে কেউ কেউ সেই গ্রন্থকে অপ্রমাণ বলে ঘোষণা করে। এটি তাদের মিথ্যা কথা, কারণ কেউ মানুক বা না মানুক, তাতে কোনো গ্রন্থ জৈনমত থেকে বাইরে হয়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ, যাকে কেউই মানে না এবং কোনো কালেই কোনো জৈন মানেনি, তবেই তা অগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু এমন কোনো গ্রন্থ নেই যাকে কোনো জৈনই মানে না। সুতরাং যে যে গ্রন্থ মানে, সেই গ্রন্থস্থিত বিষয়ের খণ্ডন-মণ্ডনও তারই জন্য প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু এমন অনেকেই আছে, যারা সেই গ্রন্থ মানে ও জানে, তবু সভা বা সংলাপে এসে মত পরিবর্তন করে ফেলে। এই কারণেই জৈনরা নিজেদের গ্রন্থ গোপন রাখে। অন্য মতাবলম্বীদের দেয় না, শোনায় না, পড়তেও দেয় না। কারণ তাতে এমন সব অসম্ভব কথা ভরা আছে, যার কোনো উত্তর জৈনদের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। মিথ্যা কথা ত্যাগ করাই তার একমাত্র উত্তর।
তেরোতম সমুল্লাসে খ্রিস্টানদের মত লিখিত হয়েছে। এরা বাইবেলকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ মনে করে জপতপ করে। এদের বিশেষ বিবরণ ওই ত্রয়োদশ সমুল্লাসেই দেখবেন। আর চৌদ্দ নম্বর অধ্যায়ে মুসলমানদের মতবিষয় লিখিত হয়েছে। এরা কোরআনকে নিজেদের মতের মূল গ্রন্থ মনে করে। এদের আচরণ চৌদ্দতম সমুল্লাসে দেখবেন। এরপর বৈদিক মতের বিষয় লিখিত হয়েছে।
যে কেউ যদি এই গ্রন্থকে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ মানসিকতা নিয়ে দেখবে, তার কোনোই লাভ হবে না। কারণ বাক্যার্থবোধের চারটি কারণ আছে—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাত্পর্য। এই চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে ব্যক্তি গ্রন্থ পাঠ করে, তখন তার কাছে গ্রন্থের অভিপ্রায় যথাযথভাবে স্পষ্ট হয়।
আকাঙ্ক্ষা—কোনো বিষয়ে বক্তার এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকা।
যোগ্যতা—যার দ্বারা যা সম্ভব হয়। যেমন, জল দ্বারা সেচ করা যায়।
আসত্তি—যে শব্দের সঙ্গে যার সম্পর্ক, সেই শব্দটির নিকটেই তাকে বলা বা লেখা।
তাৎপর্য—যে উদ্দেশ্যে বক্তা শব্দ উচ্চারণ বা লিখন করেছেন, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গেই সেই বাক্য বা লেখাকে যুক্ত করা।
অনেক হঠকারী ও দুরাগ্রহী মানুষ আছে, যারা বক্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করে থাকে, বিশেষত মতবাদে আবদ্ধ লোকেরা। কারণ মতের আগ্রহে তাদের বুদ্ধি অন্ধকারে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। অতএব আমি যেমন পুরাণ, জৈনদের গ্রন্থ, বাইবেল ও কোরআনকে প্রথমেই কুদৃষ্টিতে না দেখে, সেগুলির গুণ গ্রহণ ও দোষ ত্যাগ করে এবং অন্যান্য মানবজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, তেমনি সকলেরই করা উচিত।
এই মতগুলির অল্প অল্প দোষই প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে তা দেখে মানুষ সত্য ও অসত্য মতের বিচার করতে পারে এবং সত্য গ্রহণ ও অসত্য ত্যাগ করা ও করানোতে সক্ষম হয়। কারণ এক মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করে, তাদের বুদ্ধিকে বিপরীত পথে চালিত করে, পরস্পরকে শত্রু বানিয়ে লড়াই ও হত্যায় প্রবৃত্ত করা বিদ্বানদের স্বভাবের বাইরে।
যদিও এই গ্রন্থ দেখে অবিদ্বান লোকেরা ভিন্নরূপে চিন্তা করবে, তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যথাযথভাবে এর অভিপ্রায় বুঝবে। এজন্য আমি আমার পরিশ্রমকে সফল মনে করি এবং আমার অভিপ্রায় সকল সজ্জনের সামনে নিবেদন করি। এটিকে দেখে ও দেখিয়ে আমার শ্রমকে সফল করুন এবং এইভাবেই পক্ষপাত না করে সত্যার্থের প্রকাশ করা আমার কিংবা সকল মহাশয়ের প্রধান কর্তব্য।
সর্বাত্মা, সর্বান্তর্যামী, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা তাঁর কৃপায় এই আশয়কে বিস্তৃত ও চিরস্থায়ী করুন।
অতিবিস্তার এখানে সমাপ্ত করা হল, বুদ্ধিমান বিদ্বানশ্রেষ্ঠ শিরোমণিদের উদ্দেশ্যে।
অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বিদ্দদ্দশিরোমণিষু
ইতি ভূমিকা।
['ওম' কী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা]
অর্থঃ (ও৩ম্) এটি ওংকার শব্দ পরমেশ্বরের সর্বোত্তম নাম। কারণ এতে যে অ, উ এবং ম্
---------------------------------
(ও৩ম্) শব্দের ব্যবহারকে মাঙ্গলিক বলা হয়, তা ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনভাবে প্রচলিত। দর্শনশাস্ত্রের প্রারম্ভিক সূত্র ও অন্যান্য সূত্রগ্রন্থের আদিতেই মাঙ্গলিক ব্যবহার এবং মঙ্গলাচারণ-ভাবনা স্পষ্ট। প্রারম্ভমান গ্রন্থের নামনির্দেশে 'অথ' পদ ব্যবহারের মধ্যেও এই ভাব প্রকাশ পায়।
যদিও 'অথ' পদ অর্থ ‘প্রারম্ভ করা’ বোঝায়, প্রাচীন পরম্পরা কেবল উচ্চারণমাত্রকেই মাঙ্গলিক মনে করত। অজ্ঞানকাল থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরা দ্বারা একটি শ্লোক প্রচলিত—
ওংকারশ্বাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা
কণ্ঠং নিত্যা বিনির্যাতি তস্মান্ মাঙ্গলিকাচুন্নৌ
গ্রন্থটি প্রারম্ভ করতে গ্রন্থকার প্রাচীন পরম্পরাগত শৈলীর অনুসরণ করেছেন।
‘ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা’-এর প্রারম্ভে 'সহনাববতু' ইত্যাদি পাঠও এই পরম্পরার উদাহরণ।
মঙ্গলাচারণের প্রথা মধ্যকালীন চার্যদের থেকে এসেছে; গ্রন্থকার এতে সম্মত নন। তাদের মতে মঙ্গলাচারণের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়, প্রাচীন বৈদিক প্রথা নয়। পৌরাণিক পরম্পরায় মঙ্গলাচারণের শব্দের উল্লেখকেই বিঘ্ন-বাধা নাশক মনে করা হয়। বৈদিক মান্যতায় অনুসারে কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য—কী নির্বাধ সম্পন্নতা অথবা কোনও গ্রন্থের সম্পূর্ণতা ব্যক্তি কে তদ্বিষয়ক জ্ঞান, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং অনবরত পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে। কোনও কার্যেও বিভিন্ন ধরনের বিঘ্ন-বাধা সম্ভাব্য। এই বাধাগুলির প্রতিকারও ভিন্ন-ভিন্ন হয়। মঙ্গলাচারণের শব্দের উল্লেখমাত্র থেকে তাদের প্রতিকার সম্ভব নয়, অতএব মঙ্গলাচারণের বাস্তবতা বুঝে তার উপযোগিতায় মনোযোগ দেওয়াই উপযুক্ত।
ও৩ম্—এখানে 'ও৩ম্' মন্ত্রের অংশ নয়। প্রারম্ভে প্লুত ওড়কারের উচ্চারণ শাস্ত্রে বিধিত হওয়ায় এখানে প্লুত ওড়কার মন্ত্রের প্রারম্ভে পড়া হয়েছে। (ওমব্যাদানে পাণিনি ৮/২৭৮৭) মন্ত্রগুলির উচ্চারণের সময় তাদের প্রারম্ভে 'ওম্' পদ উচ্চারণ করা প্রাচীন পরম্পরা। কার্য প্রারম্ভের সময় ভগবন্নাম স্মরণ সর্বসম্মত মঙ্গলাচারণ। বেদ নির্দেশ দেয় যে কার্য প্রারম্ভে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ অবশ্যই করা উচিত। ঋগ্বেদের প্রথম ঋচা 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি এর জ্বলন্ত উদাহরণ। অন্যত্র (ঋ০১১৫৭১৪) এর স্পষ্ট নির্দেশ এই শব্দে আছে— "ইসে তে ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষদুত যেতে প্রারম্ভ্য চরামসি প্রভূবসঃ।" বৈদিক বাঙ্ময়ে অনেক স্থানে এই সূত্রের মাধ্যমে পরমেশ্বরের সাহায্যে প্রারম্ভিক কার্য সফলতার কামনা করা হয়েছে। এই প্রার্থনা তো রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার যেসব অনুভূতি নিয়ে এই মহান গ্রন্থ প্রারম্ভ করেছেন, সেই প্রেক্ষাপটও এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবাক্য, তার সদুদ্দেশ্যের প্রতীক।
উদ্ধৃত সূত্র তৈত্তির্য আরণ্যক (প্রপাঠক, অনু° ১) এর অন্তর্গত। তৈত্তির্য আরণ্যক প্রপাঠকগণ ভাগে ভাগে আছে। তার ৭ম, ২য় এবং ৩য় প্রপাঠক তৈত্তির্য উপনিষদ রূপ। সেখানে (শিক্ষাবল্লী, অনু° ১) এটি যথা-সত্বেও উপলব্ধ। সূত্রানুসারে "শন্নো মিত্রা, তরুক্রমঃ" এ অংশ বেদমন্ত্র। (ঋগ্০ ১৭৬০১৬, যজুঃ০ ৩৬৭৬ ; অথর্ব০ ১৬১৬১৬)
ওম্—বেদাদি শাস্ত্রে ওমকার শব্দ প্রারম্ভে উচ্চারিত হলে তার ‘টি’ প্লুত হয়, এই নিয়ম বৈদিক। তাই ‘ও৩ম্’ এভাবে লেখা হয়। এখানে প্লুত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অর্থটি শুদ্ধ 'ওম্' পদ থেকেই। শাস্ত্রে সাধারণত এই রূপেই পাওয়া যায়।
যথা—
ওম্ ক্রতো স্মর ক্লিয়ে স্মর কৃতং স্মর। — যজুঃ০ ৪০/১৫
ওম্ খং ব্রহ্মা। — যজুঃ০ ৪০/১৭
ওমাসশ্বর্ষণিধৃতো বিশ্বে দেবাস অগত। দাশ্বাংশো দাশুষাঃসুতং। — ঋ০ ১৪৩৭৭
মনোজূতির জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টম্। যজ্ঞং সামিমং বজধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তাম্ প্রতিষ্ট॥ — যজুঃ০ ২৭১৩
উপনিষদে ওম্ শব্দের ব্যবহার—
ছান্দোগ্য-ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীতমুপাসীত। — ১/১/১
ওমিটি শুদ্ধ গায়তি। — ১১৪১১
ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীতঃ। — ১/১১৫
এতন্মিথুনম্ ওম্ ইত্যেতস্মিতক্ষরে সংসৃজ্যতে। — ১১১৭৬
যদ্ধি কিঞ্জানুজানাতি ওমিত্যেয় তদাহ। — ১/১১৮
ওমিত্যাশ্রাবয়তি, ওমিত্য শংসতি, ওমিত্য উদ্গায়তি। — ১১১১৮
ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীতমুপাসীত। — ১৯৪৭১
যদা বা ঋণমাপ্নোতি ওম ইত্যেভাতিশ্বরতি। — ১১৪১১
ওমিতি হোষ স্বর্ণেতি। — ১১৫১১
ও৩ম্ আদায়ম্, ও৩ম্ পিয়ায়ম্, ও৩ম্ দেবঃ …
অন্নমিহাহারাহার, ও৩ম্ ইতি। — ১৯১২৭৫
স ও৩ম্ ইতি বা হোদ্দামীয়তে। — ৮৩৬১৫
ঈশ-ও৩ম্ ক্রতো স্মর। — ১৭
কঠ-ততে পদ সংগ্রহণ গ্রবীমি ওমিত্যেতৎ। — ২০১৫
প্রশ্ন-পুনরেতৎ ত্রিমাত্রেণৈব ওমিত্যনৈবাক্ষরং পর পুরুষমভিধ্যায়তি। — ৫৭৫; দর্শনীয় — ৫/১, ৫/২
তামোংকারেণেভায়ত্নেনান্বেতি বিদ্বান্ যতচ্ছান্তমজরমমৃতসময়পর চেতি। — ৫৭
মুন্ডক-ওমিত্যেভং ধ্যায়থ আত্মানম্। — ২১২৭৬
মাণ্ডুক্য-ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। — ১
তৈত্তির্য-ওমิติ ব্রহ্ম, ওমিতীদং সর্বম্, ওমিত্যেতদুনুকৃতি হে স্ম বা আপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি,
ওমিতি সামানি গায়ন্তি, ওম শোমতি শাস্ত্রাণি শংসন্তি, ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগর প্রতিগৃণাতি, ওমিতি ব্রহ্মা
প্রস্তুতি। ওমিত্যাগ্নিহোত্রমঅনুজানাতি, ওমতি ব্রাহ্মণঃ প্রবর্তস্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানি, ব্রহ্মৌভোপাপ্নোতি। — ১৯৮/১
বৃহৎ-ওমিতি হোভাচ। — ৫/৬৭১ (এখানে ৭ বার এসেছে)
ওং খং ব্রহ্ম। — ৫/১১১
ওমিতি হোভাচ। — ৫/২৭১, ২, ৩; ৬/২/১
ওং ক্রতো স্মর — ৫/১৫/১
গীতা-ওং তৎসদিতি নির্দেশন ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। — ১৭১২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া:। — ১৭১২৪
'ওম' শব্দ—এই বিষয়ে দীর্ঘকাল থেকে দুই মত প্রচলিত। একটি মতে এটি অব্যুত্পন্ন প্রতিপদিক একাক্ষররূপ, এবং অন্যটি ব্যুত্পন্ন প্রতিপদিক। দ্বিতীয় ধারারও দুই রূপ। একটি—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্বারা নিস্পন্ন এক শব্দ, দ্বিতীয়—ভিন্ন-ভিন্ন তিন অক্ষরের সমষ্টি। প্রতিটি অক্ষরের নিজস্ব অর্থ রয়েছে এবং এই তিন অক্ষর মিলে 'ওম' গঠিত। এইভাবে তিনটি স্বীকৃত মান্যতা উপস্থিত—
১. অব্যুত্পন্ন প্রতিপদিক একাক্ষররূপ ওম।
২. প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্বারা নিস্পন্ন ওম।
৩. পৃথক পৃথক অর্থবিশিষ্ট তিন অক্ষর দ্বারা নিস্পন্ন ওম।
অব্যুত্পন্ন প্রতিপদিক
'ওম' কে অব্যুত্পন্ন প্রতিপদিক মনে করা ধারা গোপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। সেখানে ওংকারকে নিপাত এবং অব্যয় মনে করে একাক্ষররূপ অব্যুত্পন্ন লেখা হয়েছে—
স্বরিতোদাত্ত একাক্ষর ওংকার ঋগ্বেদে,
ত্রৈস্বর্যাদাত একাক্ষর ওংকারো যজুর্বেদে,
দীর্ঘপ্লুতোদাত একাক্ষর ওংকারঃ সামবেদে,
ঈস্বোদাত একাক্ষর ওংকারো অথর্ববেদে। — গো.পু. ১/১৫
অর্থাৎ একাক্ষর ওংকার ঋগ্বেদে স্বরিতোদাত্ত, যজুর্বেদে ত্রৈস্বর্যাদাত্ত, সামবেদে দীর্ঘপ্লুতোদাত্ত, অথর্ববেদে হ্রস্বোদাত্ত মনে করা হয়েছে।
পরে ব্রাহ্মণকার বলেন—
নিপাতেষু চেইনং বৈয়াকরণাঃ সমামনন্তি উদাত্তং তদব্যয়ীভূতং।
অর্থাৎ, বৈয়াকরণ এটিকে নিপাত মনে করে উদাত্ত, অর্থাৎ অব্যয় মনে করেন।
এই ব্যাখ্যায় ওংকার একই অক্ষর। তাই উপনিষদাদি ওংকারকে একাক্ষররূপ বলার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন—
ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীতমুপাশীত। — ছান্দোগ্য ১/১১১
ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব তস্যোপব্যাখ্যানম্। — মাণ্ডুক্য ১
ত ওমিত্যেতবেবাকার সমারোহন। — জৈমিনী উপনিষদ প্রস্তাব ১/১৮
এতদ্ধ্যেভাক্ষরং ব্রহ্মা এলদেবাক্ষরং পরম্।
ওমিত্যেকাক্ষর ব্রহ্ম ব্যাহারণ মা মঅনুস্মরন। — গীতা ০/১৩
উপরের সব উদাহরণে ওংকারকে একাক্ষর মনে করা হয়েছে। এইভাবে মনে করলে ‘বর্ণাত্ কারঃ’ (পা°৩/৩/১০৮) দ্বারা ‘কার’ প্রত্যয় হয়ে ‘ওংকার’ তৈরি হতে পারে। যোগসূত্রও বলে— ‘তস্য বাচকঃ প্রনয়ঃ’ (১৯২৫), অর্থাৎ ওংকার (প্রণবঃ) তার (তস্য) প্রতীক (বাচকঃ)। ‘প্রণব’ শব্দ ‘প্র’ উপসর্গ এবং ‘ণু স্তুতি’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। যে পদ দ্বারা প্রকৃতরূপে পরমেশ্বরের স্তুতি করা হয় তাকে ‘প্রণব’ বলা হয়, এবং সেই পদ হলো ‘ওম’। (য উদ্গীথঃ স প্রণযো বা প্রণয়ঃ স উদ্গীথঃ। — ছান্দোগ্য ১৭৫/১)
ওম্ ঈশ্বরের বাচক, এবং ঈশ্বর তার বাচ্য। ওম্ অভিধান এবং ঈশ্বর অভিধেয়। প্রাচীন সরাসরি অভিজ্ঞ ঋষিদের মতে ওম্ পদ এবং ঈশ্বরের বাচ্য-বাচক সম্পর্ক সংকেতজন্য নয়, নিত্য। প্রণব ঈশ্বরের বাচক। এটি পূর্ব থেকে বিদ্যমান সম্পর্ককে প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে না। যেমন— ‘দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তের পিতা এবং রাজ্যদত্ত, দেবদত্তের পুত্র’—এটি পিতা-পুত্র সম্পর্ক তৈরি করে না, কেবল বিদ্যমান সম্পর্ক প্রকাশ করে; ঠিক যেমন অন্ধকার ঘরে বাতি বিদ্যমান বস্তুগুলো আলোকিত করে, সৃষ্টি করে না।
ব্যুত্পন্ন প্রতিপদিক—প্রকৃতি-প্রত্যয়
বৈয়াকরণ ওম্ পদকে ‘আপ্’ ধাতু থেকে উৎপন্ন মনে করে ‘অবতীত্য ওম্’ ধরণের নির্বচন মনে করেন। আলিঙ্গন-হসা-দান-ভাগ বৃদ্ধিসু। ‘অবতেষ্ঠিলোপশ্চ’ (১৩১৪১) উণাদিসূত্র থেকে ‘মন’ প্রত্যয় এবং ‘টি’ লোপ হয়ে ‘আপ্’ ধাতু থেকে ওম্ শব্দ স্থির হয়। গ্রন্থকারও নির্বচন ‘অবতীত্য ওম্’ ধরি, কিন্তু অর্থের সম্পর্ক ‘রক্ষন’ থেকে ধরা হয়েছে; অর্থাৎ রক্ষা করার মাধ্যমে ভগবান ওম্ পদকে বাচ্য হিসেবে করেন।
যোগশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ওম্ এর নির্বচন হলো— ‘উশ্রময়তীত্য ওম্’।
যোগসংক্রান্ত বা শিব উপনিষদে লেখা আছে— ‘ঊর্ধ্বমুন্নয়তীত্য ওংকারঃ’।
এই অবস্থায় ‘উৎ’ পূর্বক ‘নম্’ ধাতু থেকে ওম্ তৈরি হবে। অর্থ—জীবনের উন্নয়ন করে ভগবান ওম্ বলেন।
অথর্বশিখে এভাবে বলা হয়েছে—
অথ কসমাদূরধ্বোচ্যতে ওংকারো, বসমদুচার্যমাণ এবং প্রাণানূর্ধ্বমুক্কাময়তি।
অর্থাৎ, ওম্ উচ্চারণে প্রাণের উৎক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাই তাকে ওম্ বলা হয়।
ওম্ এর সৃষ্টি সম্পর্কে ব্রাহ্মণকার বলেন— ‘কো ধাতু ইতি আপধাতুঃ অবতিমধ্যেক রূপসাম্যাদ্ অর্থসাম্যানীতিস্তরমাদাপের ওংকারঃ সর্বমাপ্নোতীত্যর্থঃ কৃদান্ অর্থযৎ প্রাতিপদিকম্’ (গো.পু. ১/২৬)।
আশয়—ওংকার কোন ধাতু থেকে তৈরি? ‘আপ্’ ধাতু থেকে (সম্ভবত পরে ‘আপ্লূ’ হয়েছে)। কিছু কিছু ওংকাররূপ সাদৃশ্যের কারণে ‘অব্’ ধাতু মনে করে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে ‘আপ্’।
ধাতু সমীপে আছে। ওঙ্কার কৃদন্ত প্রাতিপদিক। এর অর্থ—সবকিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়া। এই দৃষ্টিতে নির্বচন হয়েছে—“আপ্নোতীতি ওম্”।
ব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক—তিন অক্ষরের যোগ
এই মতে ‘ওম্’ অ-উ-ম্—এই তিন অক্ষরের সমষ্টি বলে মানা হয়েছে। কিন্তু এইভাবে গঠিত সমুদিত শব্দ ‘ওম্’ কি কোনো এক নির্দিষ্ট অর্থের বাচক, না কি নয়? যদি হয়, তবে তার বাচ্য কি কেবল ঈশ্বরই, না কি অন্য কিছু—এটাই আলোচ্য বিষয়।
অকার-উকার-মকার মিলিয়ে ওম্ গঠিত—এই ভাবনা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। সেখানে ঋগ্বেদ প্রভৃতির ক্রমান্বিত উৎপত্তির উল্লেখ করার পর পঞ্চম পঞ্চিকার পঞ্চম অধ্যায়ে লেখা হয়েছে—
“তান্ বেদানভ্যতপৎ। তেভ্যোऽমিতপ্তেভ্যস্ত্রীণি শুক্রাণ্যজায়ন্ত—ভূরিত্যেব ঋগ্বেদাদজায়ত, ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ, স্বর ইতি সামবেদাৎ। তানি শুক্রাণ্যভ্যতপৎ। তেভ্যোऽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত—অকার-উকারো মকার ইতি। তানেকদা সমভরত্ তদোমিতি।”
অর্থাৎ—বেদসমূহকে তপস্যা করানো হল। সেই তপস্যাকৃত বেদসমূহ থেকে তিনটি শুক্র উৎপন্ন হল—ঋগ্বেদ থেকে ভূঃ, যজুর্বেদ থেকে ভুবঃ এবং সামবেদ থেকে স্বঃ। তারপর সেই তিন শুক্রকে আবার তপস্যা করানো হলে সেখান থেকে তিনটি বর্ণ উৎপন্ন হল—অকার, উকার ও মকার। এই তিনটির সমষ্টিতেই ‘ওম্’ সৃষ্টি হল।
এর তাৎপর্য এই যে—ওম্ সমস্ত বেদের সার এবং সেই কারণেই ওম্ই বেদের প্রধান বিষয়। এই কথাটিই মনুস্মৃতিতে এইভাবে বলা হয়েছে—
“অকারং চাপ্যুকারং চ মকারং চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়াভিরদুহদ্ ভূর্ভূয়ঃ স্বরিতীতি চ॥” —২৭৬
অর্থাৎ—প্রজাপতি (পরমাত্মা) অকার, উকার ও মকার (অ-উ-ম্ = ওম্) এবং ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ (গায়ত্রীর তিন ব্যাহৃতি)—এই সবকিছুকে তিন বেদ থেকে দুহে নিয়ে সাররূপে গ্রহণ করেছেন।
মাণ্ডূক্য উপনিষদে এই ভাবটি এভাবে প্রকাশিত হয়েছে—
“সোऽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোমকারোऽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা, অকার উকার মকার ইতি॥”
অর্থাৎ—এই আত্মা (পরমাত্মা) অক্ষরে অধিষ্ঠিত। সেই অক্ষর হল ওঙ্কার = ওম্। ওঙ্কার মাত্রায় অধিষ্ঠিত, এবং সেই মাত্রাগুলি হল অকার, উকার ও মকার।
বিশ্বাদি—জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরোऽকারঃ প্রথমা মাত্রা (মাণ্ডূক্য ৬) অর্থাৎ—ওম্-এর প্রথম মাত্রা হল ‘অকার = অ’। এর সম্পর্ক জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে এবং এটি বৈশ্বানর বা বিশ্বসম্পর্কিত।
তৈজসাদি—স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা (মাণ্ডূক্য ১০) অর্থাৎ—ওম্-এর দ্বিতীয় মাত্রা হল ‘উকার = উ’। এর সম্পর্ক স্বপ্নস্থানের সঙ্গে এবং এটি তৈজস।
প্রাজ্ঞাদি—সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা (মাণ্ডূক্য ১১) অর্থাৎ—ওম্-এর তৃতীয় মাত্রা হল ‘মকার = ম্’। এর সম্পর্ক সুষুপ্ত অবস্থার সঙ্গে এবং এটি প্রাজ্ঞ।
(আপ্টের কোষে এই বিষয়ে লেখা আছে—
The letter 'A' is Vaishvanar, the spirit of waiking souls; 'U' is Taijas, the spirit of dreaming souls in the world of dreams and 'M' is Prajna, the spirit of siceping souls.)
গ্রন্থকারের লেখন থেকে চারটি বিষয় স্পষ্ট হয়—
১. ওঙ্কার পরমেশ্বরের সর্বোত্তম নাম।
২. এটি অ, উ ও ম—এই তিন অক্ষরের সমষ্টিগত রূপ। এই তিন অক্ষর মিলে এক ‘ও৩ম্’ সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই এক নামের দ্বারা পরমেশ্বরের বহু নাম প্রকাশ পায়। যেমন—
অকার থেকে বিরাট, অগ্নি ও বিশ্বাদি;
উকার থেকে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু ও তৈজসাদি;
মকার থেকে ঈশ্বর, আদিত্য ও প্রাজ্ঞাদি নামগুলির বাচকতা ও গ্রহণযোগ্যতা বোঝায়।
বেদাদি সত্যশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে প্রাসঙ্গিকভাবে এই সব নামই পরমেশ্বরের।
৩. অ, উ ও ম—এই তিনটি পৃথক পৃথকভাবে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নামের বাচক।
৪. ওঙ্কার বিরাট প্রভৃতি নামের গ্রাহক ও বাচক।
বাচকতা ও গ্রাহকতার ভেদ
বাচকতা ও গ্রাহকতার পার্থক্য এইভাবে বোঝা যায়—‘দ্বিরেফ’ পদটি ‘অমর’ শব্দের বাচক এবং সেই কালো বর্ণের জীবটির গ্রাহক, যা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে বেড়ায়। ওম্-এর অবস্থাও তেমনি। যখন ওম্-এর প্রতিটি উপাদান ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নামের বাচক, তখন তাদের সমষ্টিও সেই নামগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। সেই কারণে ওম্ শব্দটি গ্রাহক হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ বাচক নয়।
প্রকৃতি-প্রত্যয় থেকে নিষ্পন্ন ‘ওম্’ ঈশ্বরের বাচক। সেই রূপেই তা পরমেশ্বরের নিজস্ব নাম।
আবার এমন ব্যবস্থাও হতে পারে যে প্রতিটি অক্ষরের পৃথক পৃথক অর্থ স্বীকার করলেও সমুদিত পদটি ঈশ্বরের বাচক হতে পারে। গোপথ ব্রাহ্মণ (পূঃ ১৩৫)-এ অ, উ ও ম-কে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বাচক বলা হয়েছে। কোষকাররাও এই অক্ষরগুলির অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বলে গ্রহণ করেছেন।
বৈদিক দৃষ্টিতে—সৃষ্টি করার শক্তি ব্রহ্মা, পালন করার শক্তি বিষ্ণু এবং সংহার করার শক্তি শিব। পৌরাণিক মতেও ব্রহ্মার কাজ সৃষ্টি, বিষ্ণুর কাজ পালন এবং শিবের কাজ সংহার। অ, উ ও ম্ এই তিনটি তাদের প্রতীক। এইভাবে ওম্-এর বাচ্য হয়—“যাঁর দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে।” নিঃসন্দেহে তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।
এই বিষয়েই তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।৩।১)-এ বলা হয়েছে—
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।”
একেই বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তাঁর বেদান্তদর্শনে (ব্রহ্মসূত্র) সূত্রাকারে বলেছেন—
“জন্মাদ্যস্য যঃ” (১।১।২)
এইভাবে তিন অক্ষরের বাচ্য একটিতেই সমন্বিত হয়।
ওম্-এর মাহাত্ম্য
‘ওম্’ পরমেশ্বরের সর্বোত্তম নাম—এই বক্তব্যের পক্ষে বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—
“ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্।” —তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।৮
“ওমিত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম, তস্যোপব্যাখ্যানম্।” —মাণ্ডূক্য উপনিষদ ১
“তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।” —যোগসূত্র ১/২৭–২৮
“য উদ্গীথঃ স প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ।” —ছান্দোগ্য উপনিষদ ১।৭।৫/১
“প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যात्मা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।” —মুণ্ডক উপনিষদ ২।২।৪
“সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥” —কঠ উপনিষদ ২।১৫
“এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥” —কঠ উপনিষদ ২।১৬
“এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥” —কঠ উপনিষদ ২।১৭
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য চরন্তি ততে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ —গীতা ৮/১১
অর্থাৎ— যে অক্ষরকে বেদজ্ঞরা বলেন, যে অক্ষরে বৈরাগ্যসম্পন্ন যতিরা প্রবেশ করেন, এবং যে অক্ষর লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মচার্য পালন করা হয়— সেই পদকে আমি সংক্ষেপে বলছি।
ওমিত্যেকাক্ষর মহা ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্
যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ —গীতা ৮/১৩
অর্থাৎ— যে ব্যক্তি ‘ওম্’ এই এক অক্ষর উচ্চারণ করতে করতে আমাকে স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করে, সে সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছায়।
ওংকারঃ স্যাত্ পরং ব্রহ্ম সর্বমন্ত্রেষু নায়কঃ ॥ —বৃদ্ধহারীত ১০৩৩৫
অর্থাৎ— ওংকারই পরম ব্রহ্ম এবং সকল মন্ত্রের নায়ক।
অদৃষ্টবিগ্রহো দেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ
তস্যোংকারঃ স্মৃতো নাম তেনাহূতঃ প্রসীদতি ॥ —যোগিযাজ্ঞবল্ক্য
অর্থাৎ— যাঁর কোনো দৃশ্য রূপ নেই, যিনি ভাবের দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ও মনোময় দেবতা— তাঁর নামই ওংকার; সেই নামে আহ্বান করলে তিনি প্রসন্ন হন।
শংকরাচার্য মাণ্ডূক্যোপনিষদ (মাণ্ডূক্যোপনিষৎকারিকা) নামে বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্যে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন—
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্।
সর্বব্যাপিনমোংকারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥
অর্থাৎ— মানুষ যেন ‘ওম্’-কে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর বলে জানে। সেই সর্বব্যাপীকে ধ্যান করলে জ্ঞানী ব্যক্তি শোকাদিতে পতিত হয় না।
একসময় ওংকারের এত গুরুত্ব ছিল যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানরাও সামান্য রূপান্তর করে একে নিজেদের ধর্মের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং আজও করেন। মুসলমানদের ‘আমীন’ এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ‘এমন’ (Amen)— এগুলো সবই ওমের বিকৃত রূপ।
(Buddhists place OM at the beginning of their Shadakshari or mystical formulary in six Syllables, Viz.
On mani Padme Hum — Sanskrit English Dictionary by Monier Williams.)
অকারাদি থেকে গৃহীত নাম— অকারাদি থেকে বিরাট প্রভৃতির গ্রহণ কেবল ইচ্ছামতো নয়, বরং শাস্ত্রসম্মত। মাণ্ডূক্যোপনিষদ থেকে উদ্ধৃত প্রমাণের ভিত্তিতে অকার থেকে বৈশ্বানর, উকার থেকে তেজস এবং মকার থেকে প্রাজ্ঞের গ্রহণ স্পষ্ট।
অবশিষ্ট নামগুলির ব্যাখ্যা এইরূপ—
উপনিষদে ‘বৈশ্বানর’ শব্দটি এসেছে। বৈশ্বানর ও ‘বিশ্ব’ একই নাম। গৌড়পাদাচার্যের কারিকা, উপনিষদের ওপর শাংকরভাষ্য এবং তার ওপর আনন্দগিরির টীকায় বহু স্থানে বৈশ্বানরের পরিবর্তে ‘বিশ্ব’ শব্দের ব্যবহার হয়েছে—
বহিষ্প্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যান্তঃ প্রজ্ঞস্তু তেজসঃ।
প্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এবং ত্রিধাস্মৃতঃ ॥ —কা ০২
এই কারিকায় বৈশ্বানরের স্থানে ‘বিশ্ব’ ব্যবহৃত হয়েছে। মাণ্ডূক্যের শ্রুতি ৬-এ আনন্দগিরির টীকায় দেখা যায়—
বিশ্বস্য বৈশ্বানরস্য জগদ্ব্যাপ্তি শ্রুত্যবষ্টম্বেন স্পষ্টযতি।
এখানে স্পষ্টভাবে ‘বিশ্ব’ অর্থে বৈশ্বানর বোঝানো হয়েছে। বৈশ্বানর শব্দ অগ্নির প্রতিশব্দ— এটি বহু কোষে উল্লেখ আছে। শব্দকল্পদ্রুম কোষে অগ্নির প্রতিশব্দ হিসেবে বৈশ্বানর লেখা আছে। আপ্টে তাঁর কোষে লিখেছেন—
Vaishvanara: an epithet of fire — অগ্নির নাম।
২. ত্বতঃ খাণ্ডবরঙ্গতাণ্ডবনটো দূরে’স্তু বৈশ্বানরঃ —ভামিনী ১৩৫৭
৩. জঠরাগ্নি—
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ
প্রাণাপানসমাসযুক্তঃ পচাম্যানং চতুর্বিধম্ ॥ —বেদান্ত
৪. পরমাত্মা। [অর্থনির্ণয়ের হেতু]
প্রশ্ন— পরমেশ্বরের অর্থবাচক বিরাট প্রভৃতি নাম কেন নয়? ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং বৈদ্যকশাস্ত্রে শুণ্ঠী প্রভৃতি ঔষধেরও তো এই নাম রয়েছে?
উত্তর— আছে, কিন্তু পরমাত্মার অর্থেও এগুলো ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন— কেবল দেবতাদেরই কি এই নামগুলির দ্বারা গ্রহণ করা হয়?
উত্তর— আপনার গ্রহণের প্রমাণ কী?
বিরাট অগ্নির নাম— বিরাডগ্নিঃ। —শতপথ ৬/২/২১৪৪, ৬/১/১১৩১
অতএব অকার থেকে বিরাট, অগ্নি ও বিশ্বাদির গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। একইভাবে উকার থেকে তেজসের গ্রহণ মাণ্ডূক্যোপনিষদে করা হয়েছে। শংকরাচার্য তাঁর মাণ্ডূক্যভাষ্যে লিখেছেন—
তৈজসো হিরণ্যগর্ভঃ। —আগমাখ্য প্রথম সংস্করণ
শতপথে বলা হয়েছে— প্রজাপতিয়ে হিরণ্যগর্ভঃ। —৬/২/২৭৫
ঐতরেয়তে বলা হয়েছে— বায়ুহায় প্রজাপতিস্তদুক্তমৃষিণা পবমানঃ প্রজাপতিঃ। —৪/২৬
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী— তেজো বৈ বায়ুঃ। —৩/২৭৬/১
এতে স্পষ্ট যে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু ও তেজস— এই নামগুলির উকার দ্বারা গ্রহণ হয়।
মকার থেকে প্রাজ্ঞের গ্রহণ মাণ্ডূক্যে করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— মকার ‘মাড়্’ ধাতু থেকে, অর্থাৎ যিনি পরিমাপক, ন্যায় ও শাসনকারী। ন্যায় ও শাসন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারাই হয়, তাই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাজ্ঞের সরাসরি সম্পর্ক।
শতপথে বলা হয়েছে— আদিত্যো বা ঈশানঃ আদিত্যো হ্বাস্য সর্বস্বেষ্টে। (৬/১/১৩৭/১৭)
অতএব ঈশান ও আদিত্য সমার্থক, এবং মকার থেকে আদিত্য, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের গ্রহণ স্পষ্ট।
পঞ্চদশীতে এই নামগুলির উল্লেখ এইভাবে হয়েছে—
প্রাপ্তস্তত্রানিমানেন তেজসত্যং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োরব্যষ্টিসমষ্টি ॥ —১৯/২৪
তেজসা বিশ্যতা যাতা দেবতির্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ —১/২৬
অর্থবাচক শব্দ বিষয়ে— গ্রন্থকার ‘সর্বাণি নামান্যাখ্যাতজানি’ এই মতের সমর্থক। অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রায় সব শব্দই ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে গঠিত। এজন্য এগুলোকে যৌগিক বলা হয়। উণাদি সূত্র দেখলে স্পষ্ট হয় যে প্রত্যেক শব্দের মূলেই কোনো না কোনো ধাতু নিহিত।
যৌগিকবাদের মূল ভিত্তি হলো ধাতুর বহুবিধ অর্থ। এজন্য সকল ব্যাকরণবিদ ও বেদভাষ্যকার কমবেশি ধাতুর বহুঅর্থতা স্বীকার করেন। মহাভাষ্যকার তো স্পষ্ট বলেছেন—
“বহবার্থা অপি ধাতবো ভবন্তি” (১৩/৩/১১)।
১. উপরে উল্লিখিত ‘বিশ্ব’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ‘বিশ্বা’ আয়ুর্বেদিক নিঘণ্টুতে ‘শুণ্ঠী’-র প্রতিশব্দ হিসেবে মানা হয়েছে।
২. এখানে প্রশ্নে উল্লিখিত ‘বিরাট’ প্রভৃতি পদ ঈশ্বরবাচক— এই অর্থেই গ্রহণীয়, ‘ব্রহ্মাণ্ড… শুণ্ঠী’ প্রভৃতি অর্থে নয়।
যদি এক-একটি ধাতুর একাধিক অর্থ হয়, তবে সেগুলো থেকে নিষ্পন্ন শব্দগুলিও বহুঅর্থবাচক হবে। এমন অবস্থায় অর্থের নিয়ামকতা কীভাবে নির্ধারিত হবে? কোন স্থানে কোন শব্দের কোন অর্থ গ্রহণযোগ্য—তার নির্ধারণই বা কীভাবে হবে? এই বিষয়ে ভর্তৃহরি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে নিজের মত এভাবে প্রকাশ করেছেন—
“বাক্যাত্ প্রকরণাদর্থাদৌচিত্যাদ্ দেশকালতঃ ।
শব্দার্থঃ প্রবিভজ্যন্তে ন রূপাদেব কেবলাত্ ॥
সংসর্গো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্যমবিরোধিতা ।
অর্থঃ প্রকরণ লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ ॥ ২.৩১৬, ৩১৭”
শব্দের বাচ্যার্থ কেবল তার রূপ দেখেই নির্ধারণ করা উচিত নয়; বরং তার নির্ণয়ের জন্য বাক্য, প্রकरण, ঔচিত্য এবং দেশ-কাল প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সংসর্গ, বিপ্রযোগ, সাহচর্য, অবিরোধ, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ এবং অন্য শব্দের সান্নিধ্য—এই আটটি নিয়ম অনুসারে বাচ্যার্থের সিদ্ধান্ত করতে হয়।
মীমাংসা মতে—
“শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সময়ায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ”
(৩.৩.১৮)
অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা (সংজ্ঞা)—এই ছয়টি অর্থের নিয়ামক। এদের মধ্যে পরবর্তী অপেক্ষা পূর্ববর্তী অধিক শক্তিশালী।
লোকব্যবহারেও প্রকরণভেদে একটি শব্দ বহু অর্থের বাচক হয়। যেমন—‘গুণ’ শব্দ সাধারণত ধর্ম, স্বভাব, বিশেষত্ব, শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যাকরণশাস্ত্রে ‘অদেডূ গুণঃ’ (পাণিনি ১।১।২) সূত্রের অধীনে এটি গুণ-সংজ্ঞা হিসেবে প্রসিদ্ধ। অলংকারশাস্ত্রে এটি মাধুর্য প্রভৃতি গুণের বাচক, সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের অর্থে ব্যবহৃত, বৈশেষিক দর্শনে ছয় পদার্থের একটি, সঙ্গীতশাস্ত্রে বাদ্যযন্ত্রের তার, ধনুকের প্রসঙ্গে ডোরি, মেখলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধারণ দড়ির অর্থে ব্যবহৃত হয়। গণিতশাস্ত্রে সংখ্যার সঙ্গে সমাসের শেষে যুক্ত হয়ে (দ্বিগুণঃ, চতুর্গুণঃ) পুনরাবৃত্তির দ্যোতক হয়।
এইভাবেই বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্র প্রভৃতি নাম প্রকারভেদে পরমাত্মা এবং অন্যান্য পদার্থের বাচক হয়ে ওঠে। ‘ইন্দ্র’ শব্দ কীভাবে জীবাত্মা, পরমাত্মা, সূর্য, বিদ্যুৎ, আকাশ, অশ্ব, প্রাণ, বায়ু, রাজা প্রভৃতির বাচক—তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায়—
“ইন্দ্র ইতি হোতমাচক্ষতে য এষ (সূর্যঃ) তপতি ।”
— শতপথ ৪১৬/৭/১১
“স যস্য স আকাশ ইন্দ্র এবং সঃ ।”
— জৈমিনীয় উপনিষদ ১/২৮/২/১
“তস্মাদাহুরিন্দ্রো বাগিতি ।”
— শতপথ ১৯৭১৩৬/১৮
“প্রাণ এব ইন্দ্রঃ ।”
— শতপথ ১২৬৬/১১১৪
“হৃদয়মেবেন্দ্রঃ ।”
— শতপথ ১২৭৬/১/১৫
“স্তনবিত্নুরেবেন্দ্রঃ ।”
— শতপথ ১১১৩৬৭৩৭৬
“বীর্যং বা ইন্দ্রঃ ।”
— তৈত্তিরীয় ৬৭১৫/৮
“ইন্দ্রো বা অশ্বঃ ।”
— কৌষীতকি ১৫১৪
“তস্মাদাহ ইন্দ্রো ব্রহোতি ।”
— কৌষীতকি ৬/১২
মায়াবাদী শংকরস্বামীও ‘ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে’ এই স্থানে ইন্দ্র শব্দের অর্থ স্বর্গস্থ পৌরাণিক দেবতা না করে ‘ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ’ অর্থে গ্রহণ করেছেন (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।
মহর্ষি বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতিজ্ঞা করেন এবং পরবর্তী ১৮টি সূত্রে (২ থেকে ১৬ পর্যন্ত) ব্রহ্মার এই স্বরূপেরই বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন।
প্রশ্ন—দেবতাগণ তো সর্বপ্রসিদ্ধ এবং তাঁরা উত্তমও বটে, তাই আমি তাঁদেরই গ্রহণ করি।
উত্তর—পরমেশ্বর কি তবে অপ্রসিদ্ধ? তাঁর চেয়ে উত্তম কি আর কেউ আছে? আবার এই নামগুলো পরমেশ্বরেরই কেন মানবেন না? যখন পরমেশ্বর অপ্রসিদ্ধ নন এবং তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই, তখন তাঁর চেয়ে উত্তম আর কেউ কীভাবে হতে পারে? অতএব আপনার এই বক্তব্য সত্য নয়, কারণ এতে বহু দোষ উপস্থিত হয়। যেমন—
“উপস্থিতং পরিত্যজ্যানুপস্থিত যাচত ইতি বাধিতন্যায়ঃ।”
অর্থাৎ, কেউ কারও জন্য আহারের বস্তু প্রস্তুত করে রেখে বলল—“আপনি আহার করুন”; আর সে ব্যক্তি যদি সেই প্রস্তুত ও নিকটপ্রাপ্ত আহার ত্যাগ করে অপ্রাপ্ত আহারের জন্য এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়, তবে তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। কারণ সে উপস্থিত, নিকটে প্রাপ্ত বস্তু ত্যাগ করে অনুপস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য অনর্থক পরিশ্রম করছে। সুতরাং যেমন সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান নয়, তেমনি আপনার কথাও তেমনই হয়েছে। কারণ আপনি বিরাট প্রভৃতি নামগুলোর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ, প্রমাণসিদ্ধ পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি উপস্থিত অর্থ ত্যাগ করে অসম্ভব ও অনুপস্থিত দেবতাদের গ্রহণে পরিশ্রম করছেন। এতে কোনো প্রমাণ বা যুক্তি নেই।
[অর্থজ্ঞানেতে সহায়ক—প্রকরণ]
যদি আপনি বলেন—“যেখানে যার প্রকরণ, সেখানে তাকেই গ্রহণ করা উচিত।” যেমন, কেউ কাউকে বলল—
“হে ভৃত্য! ত্বং সৈন্ধবমানয়”,
অর্থাৎ, তুমি ‘সৈন্ধব’ নিয়ে এসো। তখন অবশ্যই সময় অর্থাৎ প্রকরণের বিচার করা প্রয়োজন, কারণ ‘সৈন্ধব’ নাম দুটি বস্তুর—একটি ঘোড়া, অন্যটি লবণ। যদি প্রভুর গমনের সময় হয়, তবে ঘোড়া নিয়ে আসা উচিত; আর ভোজনের সময় হলে লবণ আনা উচিত। আর যদি গমনের সময়ে লবণ এবং ভোজনের সময়ে ঘোড়া নিয়ে আসে, তবে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বলবে—“তুমি নির্বুদ্ধি মানুষ। গমনের সময়ে লবণ আর ভোজনকালে ঘোড়া আনার কী প্রয়োজন ছিল? তুমি প্রকরণবিদ নও। যদি হতে, তবে যে সময়ে যেটা আনা উচিত ছিল, সেটাই আনতে। তোমার প্রকরণের বিচার করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু তুমি তা করোনি—এই কারণে তুমি মূর্খ।”
আমরা এখানে প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রধানত এমন কিছু পদ নিয়ে আলোচনা করছি, যেগুলো উপনিষদাদি অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্রে ব্রহ্মার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু যেগুলো থেকে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে অন্যান্য অর্থের প্রতীতিও হয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মের বর্ণনা বহু পদ দ্বারা হয়েছে, যেগুলো লোকব্যবহারেও এবং বেদেও অন্যান্য অর্থের বাচক।
“আকাশস্তল্লিঙ্গাত্”, “অত এব প্রাণঃ” (বেদান্ত ১৭১।২২, ২৩)—এখানে ‘আকাশ’ ও ‘প্রাণ’ পদ ব্রহ্মবাচক। এর নির্ণায়ক চিহ্ন ঐ প্রসঙ্গগুলিতেই বিদ্যমান। শংকর, ভাস্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই শব্দগুলোকে পরমাত্মবাচক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। শংকরস্বামী শুধু মেনেই নেননি, বরং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে এইসব এবং এ ধরনের আরও বহু পদ পরমাত্মারই বাচক।
“অগ্নে নয় সুপথা রায়ে”—এখানে ‘অগ্নি’ শব্দের অর্থও পরমাত্মাই সঙ্গত হতে পারে, কারণ ভৌতিক অগ্নির দ্বারা সুপথ ও কুপথের বিবেক আশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইন্দ্র, সবিতা, বায়ু প্রভৃতি সকলেই পরমাত্মারই পরিভাষা বা প্রতিশব্দ। অগ্নি প্রভৃতি শব্দের অর্থ পরমাত্মা কীভাবে হয়—এর বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থকার তাঁর ঋগ্বেদভাষ্যে প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যানে বিস্তৃতভাবে করেছেন।
বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে—
“সর্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণঃ” (৩১১২৩৭১৩)
অর্থাৎ, এই সমস্ত নামই পরব্রহ্মের।
“উপস্থিতং পরিত্যজ্য” ইত্যাদি লোকব্যবহারোপযোগী এই প্রবাদটির একাধিক রূপ রয়েছে। মীমাংসান্যায়প্রকাশ গ্রন্থের প্রভাটীকার মধ্যে এর রূপ দেওয়া হয়েছে—
“উপস্থিতং পরিত্যজ্যানুপস্থিতকল্পনায়া অন্যায়্যত্বাৎ”।
উভয়টির অর্থ মূলত একই।
“সে চলে যা।” —এতে কী প্রমাণিত হলো? এই যে, যেখানে যার গ্রহণ করা উচিত, সেখানে তাকেই গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং এইভাবেই আমাদের ও আপনাদের সকলের মানা ও করা উচিত।
।। অথ মন্ত্রার্থঃ ।।
ওম্ খং ব্রহ্ম ।।৯।। — যজুঃ অঃ ৪০ / মং ১৭
দেখুন, বেদে এইরকম বহু প্রসঙ্গে ‘ওম’ ইত্যাদি পরমেশ্বরের নামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
।।২।। — ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১১১ ।।
ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব তস্যোপব্যাখ্যানম্ ।।৩।। — মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ১ ।।
খম্বাহ্যা—
‘খম্’ পদটি লোকব্যবহারে ‘আকাশ’-এর প্রতিশব্দ, কিন্তু অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ এবং সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে এটি পরমাত্মার বাচক এবং তাঁর সর্বব্যাপিত্বকে নির্দেশ করে। এইভাবে ‘খং ব্রহ্ম’ এর অর্থ ‘ব্রহ্ম আকাশ’ নয়, বরং ‘ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপক’—এই অর্থই হয়। বৈয়াকরণদের নিরুক্তি হল—
“খর্বত্যস্মিন্ জগদিতি খম্”
(খর্ব গতৌ—স্বা० ৫০)
অর্থাৎ, যাতে সমগ্র জগৎ গতি করে, সেটাই ‘খম্’। ‘খম্’ ও ‘আকাশ’ পরস্পরের সমার্থক। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (১৬৬/১)-এ প্রসঙ্গ আছে—প্রবাহণ জৈবলি শিলক শালাবত্যকে বলেন—
“অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোয়াচ, সর্বাণি হ বা ভূতান্যকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হ বৈশ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্।”
এই লোকের গতি-আশ্রয় কী? উত্তর দেওয়া হয়েছে—আকাশ। কারণ সব ভূত আকাশ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই লীন হয়। আকাশই এদের চেয়ে মহান, আকাশই এদের আশ্রয়। কিন্তু এই সব কথা ভৌতিক আকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ অনুযায়ী সেই ব্রহ্ম থেকেই আকাশের উৎপত্তি হয়েছে—
“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” (২/১)
এবং একই উপনিষদে আরও বলা হয়েছে—
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবনতি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মতি।”
অতএব, যাতে সমগ্র জগৎ গতি করে, সেটাই ‘খম্’ এবং সেটাই ব্রহ্ম। এইভাবে ‘খম্’ ব্রহ্মার বাচক।
উদ্গীথ—
‘গৈ শব্দে’ (ধাতুপাঠ) থেকে নিষ্পন্ন।
“উদুপপদাদ্ গাধাতোস্থক্। য উদ্গীয়তে উচ্চৈঃ শব্দয়তে স উদ্গীথঃ সামধ্যনিঃ প্রণয়ো বা” — উণাদি ২৩১০
“উদ্গীথঃ প্রণয়ঃ সামবেদধ্বনিঃ” — ইত্যরুণঃ
‘ওম’ উদ্গীথ নামে সোমযজ্ঞে উদ্গাতা দ্বারা উচ্চ স্বরে গীত হয়। সোমযজ্ঞ সাত প্রকার—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম। এই যজ্ঞগুলিতে সাধারণত ১৬ জন ঋত্বিক থাকেন, যাদের মধ্যে ৪ জন অবশ্যই সামবেদী। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন উদ্গাতা। ব্রতী উদ্গাতা সামবেদের অংশ ‘উদ্গীথ’ ওম দ্বারা শুরু করে গান করেন।
সর্ব তস্যোপব্যাখ্যানম্—
‘ওম’ একটি ক্ষুদ্র অক্ষর হলেও সমগ্র জগৎ তারই বিস্তার—তারই ব্যাখ্যা। যেমন ‘অদস্’ পরোক্ষের নির্দেশক, আর ‘ইদম্’ প্রত্যক্ষের নির্দেশক। প্রত্যক্ষ জগৎ শুধু ‘ইদম্’ নয়—যা ছিল, যা আছে এবং যা হবে (ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যৎ)—এই সবই তার ব্যাখ্যা। শুধু তাই নয়, এই তিন কালের বাইরেও যদি কিছু থাকে—“যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্”—তাও ওংকারই—“তদপি ওংকার এব”।
যাস্কাচার্য বলেছেন—
“মহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে, একস্য আত্মনোऽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি”
(নিরুক্ত ৭/১৪)
অর্থাৎ, সেই এক পরমাত্মদেব তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি বহু ঐশ্বর্যের কারণে নানাভাবে স্তূত হন; অন্যান্য দেবতা সেই এক পরমাত্মার শক্তির আংশিক প্রকাশমাত্র।
সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি
সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য চরন্তি ততে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ।।৪।।
— কঠোপনিষৎ, বল্লী ২ মং ১৫
প্রশাসিতারং
সর্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাতং পুরুষং পরম্ ।।৫।।
এতমগ্নিং বদন্ত্যেকে মনুমন্যে প্রজাপতিম্
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।।৬।।
— মনু অঃ ১২, শ্লোক ১২২, ১২৩
অর্থাৎ, বহু গুণের কারণে সেই এক সত্তাকেই বহু নামে বর্ণনা করা হয়। অন্যান্য সকল দেবতা সেই এক পরমাত্মা-মহাদেবের শক্তির আংশিক প্রকাশ। তাই গ্রন্থকারের মতে—
“নৈবেশ্বরস্য একস্মিন্নপি মন্ত্রার্থে অত্যন্তত্যাগো ভবতি”
(ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা—প্রতিজ্ঞাবিষয়ঃ)
অর্থাৎ, কোনো মন্ত্রার্থেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয় না। এইভাবে বেদের প্রধান প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরই।
সর্বে বেদা—
‘আ’ উপসর্গপূর্বক ‘ম্না’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ‘আমনন্তি’ শব্দের অর্থ—বারবার ঘোষণা করা। যে পদ দ্বারা বেদে পরমেশ্বরের বারবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং যাঁকে জানার ও পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত পালিত হয়, সেই সব কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ হল ‘ওম’। এই এক পদেই সবকিছুর সমাবেশ ঘটে।
এতমগ্নিমিতি—
মনু পরমেশ্বরের প্রধান নাম ‘ওম’ মেনেছেন (২৪৪৬, ৫৩)। বর্তমান শ্লোকে ‘ওম’ পদবাচ্য পরমাত্মার কয়েকটি গৌণ নামের উল্লেখ হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ ও গুণ স্পষ্ট হয়—
অগ্নি — ‘অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ’ বা ‘অগ্-অগি গতি’ ধাতু থেকে ‘অগ্নি’ শব্দ নিষ্পন্ন। গতি তিন প্রকার—জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি। পূজার অর্থ যথাযথ সম্মান।
“যোऽঞ্চতি, অচ্যতে, অগত্যঙ্গতে সয়মগ্নিঃ”—যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানবার যোগ্য, প্রাপ্তিযোগ্য ও পূজাযোগ্য, তিনিই অগ্নি। সেই অগ্নিই পরমাত্মা।
ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে—
“আত্মা এব অগ্নিঃ” (শত০ ৬/৭/১/২০)
“অগ্নিরেব ব্রহ্ম” (শত০ ১০/৪/৪/১/১৫)
“সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ” (অথর্ব ১৩/৪/১৫)
মনু—
‘মন্ জ্ঞানে’ অথবা ‘মনু অববোধনে’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।
“যো মন্যতে, জায়তে, অববুধ্যতে স মনুঃ”—যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞেয়, তিনি মনু।
প্রজাপতি—
‘প্রজা’ ও ‘পতি’—এই দুইয়ের সমাস। নিরুক্তে বলা হয়েছে—
“প্রজাপতিঃ পাতা বা পালয়িতা বা”
অর্থাৎ, প্রজাপতি প্রজার পালনকারী ও রক্ষক। ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে—
“ব্রহ্ম বৈ প্রজাপতিঃ” (শত০ ১৩/৭/৬/১২/৯৮)
“প্রজাপতিহি আত্মা” (শত০ ৬/২/২/৭/১২)
“প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহা” (যজুঃ ১১/৬/৬৬)
অর্থাৎ, প্রজাপালক মনু নামক ভগবানের প্রতি নিবেদিত বাক্য উচ্চারণ করো।
“প্রজাপতিয়ে মনুঃ স হীদং সর্বমমনুত” (শত০ ৬/৬/১/১১/৬)
অর্থাৎ, প্রজাপালক ভগবানের নাম মনু, কারণ তিনি সমগ্র জগতের মনন (জ্ঞান) করেন।
স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ স শিবসঃ স অক্ষরঃস পারমঃ স্বরাট্।
স ইন্দ্রঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।।।৭।। - কৈব্যাল্য উপনিষৎ ১৮৮
‘দিভো ধর্তা ভূবনস্য প্রজাপতিঃ’ (ঋক্ ৪৫৫৩৩২) অর্থাৎ প্রজাপতি হলো সেই যিনি সংসারকে ধারণ করেন।
‘এতোন্বিন্দ্র স্তভাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না’ (সাম ১৪০২) অর্থাৎ আহা, শুদ্ধ ইন্দ্র = পরমাত্মার শুদ্ধ সাম দ্বারা স্তুতি কর।
‘তস্মাদিন্দ্রো ব্রহোতি’ (কৌউপ ৬/১৪) অর্থাৎ ইন্দ্র ব্রহ্মার নাম।
ইন্দ্র—‘ইদি পরমঈশ্বর্য়ে’ ধাতু থেকে ‘ঋজেন্দ্রাগ্রবজঃ’ (উণাদি ২৯২৬) সূত্র ও ‘রণ’ প্রত্যয় মিলিয়ে ‘ইন্দ্রঃ’ শব্দ উৎপন্ন হয়।
‘ইন্দতি পরমঈশ্বর্যকর্মণঃ’ (নিরুক্ত ১০১৮)।
‘যো হ খলু যাভ প্রজাপতিঃ স উ বেভেন্দ্রঃ’ (তৈ ১/২/২৫)।
অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত হওয়ার কারণে পরমাত্মার নাম ইন্দ্র।
প্রাণ—‘প্র পূর্বক অন্ প্রাণনে’ ধাতু থেকে প্রাণ শব্দ উৎপন্ন হয়।
প্রাণনাত প্রাণঃ = সকল জীবের জীবনমূল, জীবনরক্ষক হওয়ার কারণে ঈশ্বরের নাম প্রাণ।
‘প্রাণাপানী দেব := ব্রহ্ম’ (গোপথ ১।২।১১)।
‘প্রাণো ব্রহ্মা’ (ছন্দোগ্য ৪৭১০/১৫)।
‘প্রাণো হ সর্বস্যেশ্বরী যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন’ (অথর্ব ০১১১৪৭১০)।
অর্থাৎ, কোনো বস্তু শ্বাস নিলে বা না নিলে—প্রাণই সকলের ঈশ্বর।
ব্রহ্মা—‘বৃদ্ধৌ’ ধাতু থেকে ‘বৃহের্নোচ্চ’ (উণাদি ৪৭১৪৬) সূত্র ও মনিন প্রত্যয় দ্বারা ব্রহ্ম শব্দ উৎপন্ন।
‘যো অখিল জগত্ নির্মাণেন বর্যতি বর্ধয়তি স ব্রহ্ম’ অর্থাৎ যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করেন, তিনি ব্রহ্ম।
(ব্রহ্ম শব্দ পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতির তিনটিরও বাচক। পরমাত্মার অর্থে এর সঙ্গে ‘জ্যেষ্ঠ’, জীবাত্মার অর্থে ‘ইদম্’, প্রকৃতির অর্থে ‘মহৎ’ পদ যোগ হয়। যেমন—
‘তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ’। -(অথর্ব ১০৩৮/১ : ১০৭৭৩৩২-৩৪)
‘তস্মাহৈ বিদ্বান পুরুষমিদং ব্রহ্মোতি মন্যতে’। -(অথর্ব ১১১৮০/৩২)
‘ইদং জানাসৌ বিদয় মহৎ ব্রহ্ম বলিষ্যতি’। -(অথর্ব ১৪৩২৭১)
‘মম যোনির মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভ দধাম্যহম্’। -(গীতা ০১৪১৩))
যেখানে শুধুমাত্র ব্রহ্ম পদ ব্যবহৃত হয়, সেখানে তার অর্থ প্রক্রিয়ানুসারে নির্ধারিত হয়। তবুও সাধারণত ব্রহ্ম পদ দ্বারা প্রায়ই পরমাত্মার গ্রহণ ঘটে।
স ব্রহ্মা—বর্তমানে উপলব্ধ সংস্করণগুলোতে সাধারণত পাঠ পাওয়া যায়:
স ব্রহ্মা স শিবঃ স ইন্দ্রঃ স অক্ষরঃ পারমঃ স্বরাট্।
স এৱং বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।
দুইয়ের অর্থে কোনো পার্থক্য নেই। বাস্তবে, বেদ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যে হয়তো এমন কোনো গ্রন্থ নেই যেখানে প্রকল্প না হয়েছে। বড় বড় প্রামাণিক গ্রন্থগুলোতে পাঠভেদ পাওয়া যায়।
আদ্য শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র ১/৩৩৩০-এর ভাষ্যে মনুস্মৃতির দুই শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন:
তান্যেব তে প্রপ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
হিংস্ত্রাহিসে মৃদুক্রূরে ধর্মাধর্মাবৃতানতে।
এই পাঠ বঙ্গাল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে মুদ্রিত, কিন্তু সিদ্ধান্তসাগর মুদ্রণালয় মুম্বই-তে প্রকাশিত সংস্করণে নেই:
যং তু কর্মাণি যাস্মিন স নিয়ুক্ত প্রধমং প্রভুঃ।
স তদেভ স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানা পুনঃ পুনঃ।
হিংস্ত্রাহিসে মৃদুক্রূরে ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোদদধাত্ সর্গে তৎস্য স্বয়ংমাবিশৎ।
এখানে গ্রন্থকার বা শঙ্করাচার্যকে ইচ্ছাকৃত পাঠপরিবর্তনের অভিযোগ দেওয়া যৌক্তিক নয়। বাস্তবে শঙ্করের কাছে যা পেয়েছেন, সেটিই তিনি তাঁর বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন, এবং সিদ্ধান্তসাগর মুদ্রণালয়ও যেই পাণ্ডুলিপি পেয়েছে, সেটিই মুদ্রিত হয়েছে। এভাবে কেবল্যোপনিষদ-এরও যেই প্রতিলিপি গ্রন্থকার পেয়েছেন, সেটিই এখানে উদ্ধৃত।
গ্রন্থকার ঈশা-আদি দশটি উপনিষদকে প্রমাণ মানেন। কৈব্যাল্য উপনিষদ সেখানে নেই। এই ভিত্তিতে বলা যায়, যে গ্রন্থকে তিনি প্রামাণিক মনে করেননি, সেটিকে প্রমাণরূপে উপস্থাপন কেন? বাস্তবতা হলো, যেসব গ্রন্থকে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ প্রামাণিক মনে করেননি, তাদের বেদানুকূলে বা বেদবিরুদ্ধ বক্তব্য মেনে নেওয়ায় কোনো বাধা নেই।
দ্বিতীয়ত, যারা কোনো গ্রন্থকে প্রামাণিক মনে করেন, যদি আমরা সেই প্রমাণ ব্যবহার করে আমাদের মত প্রদর্শন করি এবং তাদের মতের প্রয়োগ বা প্রত্যাখ্যান দেখাই, তা সত্য-অসত্য নির্ণয়ে সাহায্য করে।
(অনেক দিন আগে, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞ ডঃ সম্পূর্ণানন্দ ‘গণেশ’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি ‘গণানান্ত্বা গণপতি হৱামহে’ ইত্যাদি জনপ্রিয় মন্ত্র (যজু ২৩১১৬) এর অত্যন্ত অশ্লীল ও অসঙ্গত অর্থ উপস্থাপন করেছিলেন। আমরা প্রতিবাদ করলে, তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৬৫১ তারিখে লিখেছিলেন—
"যখন আমাকে সেই বিশ্বাস ও প্রথার খণ্ডন করতে হয় যা আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত, আমি সর্বদা এক কাজ করি। জনগণের সামনে আমি সেইই বই রাখি যেগুলোকে তারা প্রমাণ মনে করে, এবং সেই অর্থকে ভিত্তি করি যেগুলোকে তারা মেনে নেয়। এটাই ‘গণেশ’-এ করা হয়েছে। আমার কাজের রূপ হলো—
আমার ব্যক্তিগত মত যাই হোক, আপনি ল্যন্ট এবং মহীঘর-এর ভাষ্য প্রামাণিক মনে করেন। তারা দু’জন এই মন্ত্রকে অশ্বদেবতা মনে করেছেন এবং অশ্বমেধের এক বিশেষ ক্রিয়ায় এর ব্যবহার করেছেন। তাই আপনার বিশ্বাস করা আচার্যদের মতে এই মন্ত্র গণেশদেবতা হতে পারে না, কারণ আপনি গণেশকে অশ্বের প্রতিশব্দ মনে করেন না। অতএব, আপনার মেনে নেওয়া প্রমাণ অনুযায়ী শ্রুতি গণেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না।")
স ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু—ব্রহ্মা— ‘সব জগতের স্রষ্টা’ অর্থযুক্ত ‘ব্রহ্ম’ শব্দ ‘বৃহ উদ্যমনে’ (ধাতু ৬।১৬) ধাতু থেকে উৎপন্ন। ‘ব্রহ্মৌকো যায়তে যায়তে বিদ্যা বলতি। ব্রহ্মা সর্ববিদ্যা, সর্ব বেদিতুমার্হতি। ব্রহ্মা পরিশৃৎ শৃতিতঃ’ (নিরুক্ত ১।৮) ‘জাতবিদ্যা’ = সমগ্র পদটির বিশ্লেষণ: ‘যায়তে যায়তে বিদ্যা’ = বেদত্রয়ী বিষয়।
ব্রহ্মা হলো সমগ্র ত্রয়ী বিদ্যার।
যে জানবার যোগ্য হয়, সে-ই সবকিছু জানবার উপযুক্ত হয়। এই নির্বচনটি ব্রহ্মা নামক ঋত্বিককে দৃষ্টিতে রেখে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যিনি সর্বপ্রকারে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি ‘ব্রহ্মাণং বিদ্ধাতি পূর্ব যস্য বেদান্ প্রহিণোতি তস্মৈ’ (শ্বেত০ ৬/১৮), তিনিই ‘সর্বতঃ পরিবৃঠং’—সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসমর্থ; তিনিই ব্রহ্মা।
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ ।
ব্রহ্মা মা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে ।।
–অথর্ব০ ১৬/৪৩১৮
বিষ্ণু— ‘বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ’ এই ধাতু থেকে ‘নু’ প্রত্যয় যোগে বিষ্ণু শব্দ সিদ্ধ হয়—‘ভেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচর জগৎ স বিষ্ণুঃ’। যিনি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, তিনিই বিষ্ণু (স০ প্র০ প্র০ সং০)। শ্রুতির বচন—‘স ওত প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু’ (যজুঃ০ ৩২/১৮)। নিরুক্তকার বিষ্ণু শব্দটিকে ‘বি’ উপসর্গপূর্বক ‘চিত্ৰ বন্ধনে, বিশ প্রবেশনে’ এবং ‘বি’ উপসর্গসহ ‘অশূড় ব্যাপ্তৌ’ (১২/১৮) ধাতু থেকে নির্মিত বলেছেন। সেখানে লেখা আছে—‘অথ যদ্বিষতো ভবতি তদ্বিষ্ণুরিতি’। এখানে ‘বি’ উপসর্গসহ ‘ষিঞ্চ্’ ধাতু। নির্বচনের রূপ হবে—‘বিধিনোতি বিধিনাতি বা স বিষ্ণুঃ’। অথবা ‘বিষ্ণুর্বিশতের্বা’—এখানে ধাতু ‘বিশ প্রবেশনে’। নির্বচন হবে—‘বিশতীতি বিষ্ণুঃ’। অথবা—‘বিশতি সর্বস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তঃ প্রবিশতি যদ্বা ব্যশ্নুতে ব্যাপ্নোতি সর্ব জগৎ ইতি বিষ্ণুঃ’। (তৎসৃষ্ট্যা তদেবানুপ্রাবিশৎ—তৈ০ ২/৬/৬)। ‘বিবিধৈঃ কর্মভিঃ তৎফলৈশ্চ সিনোতি জীবান্ ইতি বিষ্ণুঃ’—অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলের বন্ধনে জীবদের আবদ্ধ করার কারণে ভগবান বিষ্ণু।
এই শব্দের নিম্নলিখিত নির্বচনগুলিও ভগবৎপরক—
‘বিশ্বং নিয়মপতীতি বিষ্ণুঃ’—সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে ঈশ্বর বিষ্ণু নামে অভিহিত।
‘বিশেষেণ নূয়তে স্তূয়তে জনৈরিতি বিষ্ণুঃ’—যাঁর নানাবিধভাবে স্তব করা হয়, তিনিই বিষ্ণু।
তদ্যথা—
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্য উৎসঃ (ঋক্০ ১/১৫৪/৫)
অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমেশ্বরের পরম পদে আনন্দের উৎস বিদ্যমান।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ।।
(ঋক্০ ৭/১২২/২০)
অর্থাৎ সর্বব্যাপক ভগবানের প্রাপ্য পরম পদকে বিদ্বজ্জনেরা আকাশে প্রকাশমান সূর্যের ন্যায় স্পষ্টভাবে দর্শন করেন।
রুদ্র— ‘রুদির্ অশ্রুবিমোচনে’ এই ধাতু থেকে ‘ণিচ্’ প্রত্যয়ান্ত হয়ে ‘রক্’ প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়ায় ‘রোদের্ণিলুক্ চ’ (উণাদিকোষ, ২/৭২/২) সূত্রে রুদ্র শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘যো রোদয়ত্যন্যায়কারিণো জনান্ স রুদ্রঃ’—যিনি দুষ্ট কর্মকারীদের কাঁদান, সেই কারণে পরমেশ্বর রুদ্র নামে পরিচিত। উণাদিকোষের উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার আবার লিখেছেন—‘পাপিনো রোদয়তীতি রুদ্রঃ’। সর্বত্র নির্বচনে মূল অর্থ—‘রোদয়তীতি রুদ্রঃ’। বিষ্ণুসহস্রনামের শাঙ্করসম্প্রদায়ানুসারী ভাষ্যে বলা হয়েছে—‘প্রজা সংহরন্ রোদয়তীতি রুদ্রঃ’—প্রজাদের সংহার করে কাঁদানোর কারণে ভগবান রুদ্র নামে অভিহিত।
এই শব্দ (রুদ্র)-এর আরও কিছু নির্বচন পাওয়া যায়, যা পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও গুণের নিদর্শন দেয়, যেমন—
(ক) তাপত্রয়াত্মকং সংসারদুঃখং রুত্ তং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ—জগতের তাপত্রয় থেকে উদ্ধার করার কারণে ভগবানকে রুদ্র বলা হয়।
দ্রষ্টব্য—‘রুত্ সংসারাখ্যং দুঃখম্, তদ্ দ্রাবয়ত্যপগময়তি বিনাশয়তীতি রুদ্রঃ’।
–সায়ণ, ঋগ্ভাষ্য ১/১১৪/১৪
(খ) রুদন্তি জনা, অস্মিন্নিতি রুত্, স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ, তং রাতি আদত্তে প্রলয়কালে ইতি রুদ্রঃ—অর্থাৎ জগতের প্রলয় সাধন করার কারণেও ভগবান রুদ্র।
(গ) রুত্ শব্দরাশির্বেদঃ, তং কল্পাদৌ রাতি দদাতীতি রুদ্রঃ—অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে বেদ দান করার কারণে ভগবান রুদ্র নামে অভিহিত।
দ্রষ্টব্য— রুত্ শব্দাত্মিকা বাণী, তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা, যা তাম্ উপাসকেভ্যো রাতি দদাতীতি রুদ্রঃ।
–সায়ণ, ঋগ্ভাষ্য ১/১১৪/১১
রূতঃ শব্দরূপা উপনিষদঃ, তাভিঃ দ্রূয়তে গম্যতে প্রতিপাদ্যতে ইতি রুদ্রঃ।
–তদেব
অর্থাৎ— বেদে প্রতিপাদিত বেদবিদ্যার প্রদান করার কারণে এবং উপনিষদে প্রতিপাদ্য হওয়ার কারণে ভগবান রুদ্র নামে অভিহিত।
নিম্ন মন্ত্রে ‘রুদ্র’ শব্দটি ভগবানের বাচক—
য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে।
–অথর্ব০ ৭/১৬/১৭১
শিব— ‘শিবু কল্যাণে’ এই ধাতু থেকে শিব শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘বহুলমেতন্ নিদর্শনম্’—এ থেকে ‘শিবু’ ধাতু মানা হয়। ‘সর্বনিঘৃষ্বরিষ্ঠলষ্ব’ প্রভৃতি উণাদিসূত্র (১/১৫৩)-এর ব্যাখ্যায় লেখা আছে—‘শেতে সর্বমস্মিন্নিতি শিবঃ’; অর্থাৎ প্রলয়কালে যেখানে সমগ্র জগৎ শান্তিপূর্বক নিদ্রিত থাকে, তিনিই ভগবান শিব।
নিরুক্তকার এই শব্দটিকে ‘শিষ্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলে মানেন। তিনি লেখেন—‘শেভ ইতি সুখনাম শিষ্যতেঃ বকারো নামকরণঃ অন্তঃস্থান্তরোপলিঙ্গী বিভাষিতগুণঃ, শিবমপ্যস্য ভবতীতি’ (নিরুক্ত ১০/১৭)। সারাংশ এই যে, ‘শেভ’ শব্দের অর্থ সুখ। এটি ‘শিষ্’ ধাতু থেকে ‘ব’ প্রত্যয়যোগে গঠিত। তখন নির্বচনের রূপ হবে—‘শিষ্যতে সুখাবহো ভবতীতি শিবঃ’। তাৎপর্য এই যে, যিনি সুখ প্রদান করেন বা কল্যাণ সাধন করেন, সেই ভগবানকে শিব নামে স্মরণ করা হয়।
‘শিবমস্যাস্তীতি শিবয়তীতি বা শিবঃ’—স্বয়ং কল্যাণরূপ হওয়া এবং জগতের কল্যাণ সাধন করার কারণে ভগবান শিব নামে অভিহিত। মহাভারতে লেখা আছে—‘মনুষ্যান্ শিবমন্বিচ্ছন্ তস্মাদেব শিবঃ স্মৃতঃ’ (অনু০ ১৬/১/১০)। অথবা—‘শেতে সর্বং কারণসহিত জগদস্মিন্নিতি শিবঃ, সর্বাধারঃ স্বয়ং চ নিরাধারঃ’; প্রলয়ে কারণসহিত সমগ্র জগৎ এতে লীন হয়ে থাকে, এই জন্য ভগবান শিব নামে পরিচিত।
নৈরুক্ত ধাতুপ্রক্রিয়াকে দৃষ্টিতে রেখে নির্বচন হবে—‘শিষ্যতে প্রলয়ানন্তরমিতি শিবঃ’; অর্থাৎ প্রলয়ের পরেও যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি শিব। শ্রুতি বলে—‘আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাসঃ’ (ঋক্০ ১০/১২৬/২)। ‘নমঃ শিবায়’ (যজুঃ০ ১৬/৪১)—অর্থাৎ কল্যাণকারী (শিব) পরমাত্মাকে নমস্কার।
‘বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি’ (শ্বেত০ ৪/১৪)। অর্থাৎ সকলকে পরিবেষ্টনকারী অদ্বিতীয় শিবকে জেনে চরম শান্তি লাভ করে।
অক্ষর— উণাদিসূত্র ‘অশেঃ “সরঃ”’ (৩/৭/৭/০)-এর ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার লিখেছেন—‘অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীত्यक्षরম্’। সর্বব্যাপী ও অবিনাশী হওয়ার কারণে ভগবানের নাম অক্ষর। অন্যত্র গ্রন্থকার এই শব্দটিকে ‘অশূড় ব্যাপ্তৌ’ এবং ‘ক্ষর সঞ্চলনে’—এই দুই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলেছেন—‘যঃ সর্বমশ্নুতে ন ক্ষতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্’। নিরুক্তকার লেখেন—‘অক্ষরং ন ক্ষরতি = ক্ষীয়তে বা ক্ষয়ং ভবতি, বাচো’ক্ষর ইতি বা’ (নিরুক্ত ১৩/৭/১২)। এই দৃষ্টিতে নির্বচনের রূপ হবে—‘ন ক্ষরতীত्यक्षরম্’—যার সঞ্চলন বা পরিবর্তন হয় না। এই নির্বচনের মূল—‘বাগ্বৈ সমুদ্রো ন বৈ বাক্ ক্ষীয়তে’ (ঐত. ব্রা০ ৫/৩/৭/১)। যদিও নিরুক্তকারের এই নির্বচন বর্ণবাচক অক্ষরের জন্য, তথাপি পরমেশ্বরের বেদরূপী বাণীর ক্ষয় না হওয়া, তথা তার আশ্রয় ও ধারক হওয়ার কারণে এটি ভগবৎপরকও হতে পারে।
সমস্ত ভৌতিক জগৎ ক্ষর, কারণ তা বিনাশী; আর ভগবান অবিনাশী হওয়ার কারণে অক্ষর।
তদনুসারে গীতায় বলা হয়েছে— ‘ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থো’ক্ষর উচ্যতে’ (গীতা ১৫/১৬)। এই শ্লোকে ‘অক্ষর’ পদের বাচ্য পর…
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমুগ্নিমাহুরথোং দিব্যঃ স সুপর্ণো গুরুত্মান্ ।
একং সদবিপ্রা বহুধা বন্দন্ত্যুগ্নি যমং
মন্তুরিশ্বানমাহুঃ ॥২॥
–ঋক্ ০ মণ্ডল ১, সূক্ত ১৬৪, মন্ত্র ৪৬॥
ঋধো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।
–ঋক্ ০ ১/১৬৪/৩৯
আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপক যে অবিনাশী ভগবানকে সমস্ত মন্ত্র প্রতিপাদন করে, তিনি ‘তদেতদক্ষর ব্রহ্ম’ (মুণ্ডক০ ১/২/৩)। সেই ব্রহ্মই অক্ষর, অর্থাৎ অবিনাশী।
স্বরাট্— ‘স্বরাট্ স্বয়মেব বশ্যঃ, অমরকবশ্যঃ, বিধিনিষেধকিংকরো ন ভবতীতি যাবৎ’। আশয় এই যে, যিনি কারও অধীন নন, সেই জন্য তিনি স্বরাট্ নামে পরিচিত। নিম্ন মন্ত্রসমূহে ‘স্বরাট্’ পদ ঈশ্বরের বাচক—
স্বয়ুরিন্দ্রঃ স্বরাডসি ।
(ঋক্০ ৩/৪৫/৭৫)
অর্থাৎ— তুমি স্বয়ংপ্রকাশ, ইন্দ্র এবং স্বরাট্।
য়ে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা, য আবিবিশুরুর্বন্তরিক্ষম্ ।
তেভ্যঃ স্বরাডসুনীতির্নো অদ্য যথাবশং তন্যঃ
কল্পয়াতি ॥
–অথর্ব০ ১৮/৩/৭৫/৬
অর্থাৎ— আমাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যাঁরা এই মহাশূন্যে প্রবেশ করেছেন, অর্থাৎ যাঁদের স্বর্গবাস হয়েছে, তাঁদের প্রাণ প্রদানকারী, অর্থাৎ পুনর্জন্মদানকারী স্বরাট্—পরম স্বাধীনেরূপ ভগবান—নিজ নিজ কর্মানুসারে দেহ প্রদান করেন।
কালাগ্নি— ‘ঝঃ কালকালো গুণী সর্ববিত্’ (শ্বেত০ ৬/১৬)। অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কালসমূহেরও কাল (কালাগ্নি), সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপক। প্রলয়কালে জগতের সংহারক হওয়ার কারণে ভগবান কালাগ্নি নামে অভিহিত।
‘কালো’স্মি লোকক্ষয়কৃত্ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ’।
–গীতা ১১/৩২
‘ততঃ কালাগ্নিরূপো’সৌ ভূত্বা সর্বহরো হরিঃ’।
–বিষ্ণুপুরাণ ৬/৩৩/২৪
চন্দ্রমা— ‘চদি আহ্লাদনে’ এই ধাতু থেকে চন্দ্র শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘চদি’ ধাতুর অর্থ দীপ্তিও—‘চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ’। ‘যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্রঃ’। আনন্দস্বরূপ এবং সকলকে আনন্দদানকারী হওয়ার কারণে ঈশ্বরের নাম চন্দ্র। যাস্ক লেখেন—‘চন্দ্রঃ চন্দতেঃ কান্তিকর্মণঃ’ (নিরুক্ত ১১/৩৫)। ‘চন্দ্রমা আহ্লাদং মিমীতে নির্মিমীতে, মিমীতে আনন্দম্ ইতি মা := চন্দ্রমা’। ‘চন্দ্রমা বৈ ব্রহ্মা’ (শত০ ১২/১/৭/১২), ‘প্রজাপতিবৈ চন্দ্রমা’ (শত০ ৬/১/৩/৩/১৬)। ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ (১/৩/৬/১২)-এ চন্দ্র শব্দের ভগবৎঅর্থে প্রয়োগ হয়েছে—
‘চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতং চারিষ্যামি ততে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ম্’।
‘ইন্দ্রং মিত্রমিতি’—(বিপ্রাঃ) বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা (অগ্নি) অগ্নিস্বরূপ (একং) এক, অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে (বহুধা) বহু নামে (বদন্তি) অভিহিত করেন, যেমন—ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মান, যম এবং মাতরিশ্বা। এখানে উত্তরপদ ‘অগ্নি’ বিশেষ্য, যা পরমেশ্বরের বাচক; অবশিষ্ট সব নাম বিশেষণরূপ।
মিত্র— ‘জিমিদা স্নেহনে’ ধাতু থেকে ‘ক্তু’ প্রত্যয়যোগে মিত্র শব্দ সিদ্ধ হয়—‘মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ’। যিনি সকলের প্রতি স্নেহবান এবং সকলের প্রীতির পাত্র, সেই জন্য পরমেশ্বর মিত্র নামে অভিহিত। নিরুক্তকার এই শব্দটিকে তিনটি পৃথক ধাতু থেকে নির্বচন করেছেন—‘মিত্রঃ প্রমীতেস্ ত্রায়তে সম্মিন্বানো দ্রবতি মেদয়তের্বা’ (নিরুক্ত ১০/১২)।
‘প্রমীতেস্ ত্রায়তে ইতি মিত্রঃ’—প্রমীতি অর্থাৎ কষ্ট বা দুঃখ থেকে যিনি রক্ষা করেন, সেই জন্য ঈশ্বর মিত্র। নিরুক্তসমুচ্চয়ের রচয়িতা বররুচির মতে—‘মাত্যা নির্মায় কৃত্স্নং জগত্ ত্রায়তে ইতি মিত্রঃ’; সমগ্র জগতের সৃষ্টি করে তার রক্ষা করার কারণে ভগবান মিত্র নামে পরিচিত।
মিত্র শব্দের নির্বচন আরও এইরূপ হতে পারে—
(ক) ‘ভাতি পরিমাপয়তি ইতি মিত্রম্’—সমগ্র সংসারকে পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন বলে ঈশ্বর মিত্র।
(খ) ‘মিতং কর্মফলং দদাতীতি মিত্রঃ’—কর্মফল দানকারী হওয়ার কারণেও ভগবান মিত্র নামে অভিহিত।
নিম্ন মন্ত্রে ‘মিত্র’ শব্দ ভগবানের বাচক—
মিত্রো জনান্ যাতযাতি ব্রুবাণো
মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে
মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥
–ঋক্ ০ ৩/৭৫/৬/১
(মিত্রঃ) কষ্ট ও দুঃখ থেকে রক্ষা প্রদানকারী ভগবান (ব্রুবাণঃ) বেদের উপদেশ দিয়ে (জনান্ যাতযাতি) মানুষকে শুভকর্মে প্রবৃত্ত করেন। (মিত্রঃ) জগতের স্রষ্টা ও ধারক ভগবান (পৃথিবীম্ উৎ দ্যাম্ দাধার) পৃথিবী ও আকাশসহ সমগ্র জগৎ ধারণ করে আছেন। (মিত্রঃ) শুভ ও অশুভ কর্মের ফলদাতা ভগবান (অনিমিষা) সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে (কৃষ্টীঃ) কর্মনিরত মানবগণকে (অভিচষ্টে) পর্যবেক্ষণ করেন। সেই (মিত্রায়) মিত্র, অর্থাৎ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে (ঘৃতবৎ হব্যং জুহোতন) ঘৃত ও হবিষ্য অর্পণ কর—অর্থাৎ যজ্ঞ প্রভৃতি শুভকর্মের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করো।
দিব্য— নিরুক্তকার লেখেন—‘দিব্যঃ দিবিজঃ’ (৭৮)। নিরুক্তের এই নির্বচন সূর্যকে বিশেষ্য ধরে করা হয়েছে। সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হওয়ার কারণে ভগবৎঅর্থে এই শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। বিদ্যা ও বিজ্ঞানসম্পন্ন প্রকাশস্বরূপ ভগবানের অর্থে নিম্ন মন্ত্রে এই শব্দ ব্যবহৃত—
‘দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভাগায় ।
দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং ন পুনাতু
বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু’
(যজুঃ০ ৬/১)
অর্থাৎ— নিজ পবিত্র জ্ঞান দ্বারা সংসারকে পবিত্রকারী, বেদবাণীর ধারক, দিব্য (প্রকাশ) স্বরূপ ভগবান আমাদের জ্ঞানকে পবিত্র করুন।
‘দিব্যো হ্যামূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যাজঃ’
(মুণ্ডক০ ২/১/২)
অর্থাৎ— বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র পরিপূর্ণ, অজ, অমূর্ত সেই পরমাত্মাই দিব্য।
‘দিব্যো গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যো বিক্বীড্যঃ’
(অথর্ব০ ২/২০/১)
অর্থাৎ— সেই পরমাত্মা দিব্য গন্ধর্ব, যিনি একাই সংসারের অধিপতি এবং একমাত্র নমস্কার ও পূজার যোগ্য।
বরুণ— ‘বৃত্ বরণে’ এবং ‘বর ঈপ্সায়াম্’—এই দুই ধাতু থেকে বরুণ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘বৃণোতি সর্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষুন্ মুক্তান্ ধর্মাত্মনো যঃ স বরুণঃ’। অথবা—‘ব্রিয়তে শিষ্টৈঃ মুমুক্ষুভিঃ মুক্তৈঃ ধর্মাত্মভিঃ যঃ স বরুণঃ’। অথবা—‘বরয়তি শিষ্টাদীন্ বর্যতে বা শিষ্টাদিভিঃ স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ’। অর্থাৎ যিনি শিষ্ট, মুমুক্ষু ও ধর্মাত্মাদের দ্বারা বরণীয়, তিনিই বরুণ—পরমেশ্বর। ‘বর’ অর্থ শ্রেষ্ঠ; যিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর, অন্য কেউ নন (স০ প্র০ প্র০ স০ পৃ০ ৭)।
আশয় এই যে, সর্বাধিক বরণীয়, কাম্য ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে ভগবান বরুণ নামে অভিহিত।
নিরুক্তকারও বরুণ শব্দের নির্বচন ‘বৃণোতীতি সতঃ’ (১০/১৪) লিখে ‘বৃত্ বরণে’ ধাতু থেকেই করেছেন, যদিও নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ সূর্য বা বিদ্যুৎরূপে গ্রহণ করেছেন। এই শব্দের রচনা চুরাদিগণীয় ‘বৃত্ আবরণে’ ধাতু থেকেও হতে পারে। তখন নির্বচন হবে—‘বারগাতীতি বরুণঃ’। সমগ্র জগতকে আচ্ছাদিত করার কারণে ভগবান বরুণ নামে অভিহিত।
অলব্ধমূল একটি লেখ এও আছে—
বরং বৃণন্তি তং
দেবা বরদশ্চ বরার্থিনাম্ ।
ধাতুরবৈ বরণে প্রোক্তঃ তস্মাৎ স বরুণঃ স্মৃতঃ ।।
এই আশয় থেকেই গ্রন্থকার লিখেছেন— ‘শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভিঃ ধর্মাত্মিভিঃ ব্রীয়তে’।
‘বরুণো বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা’ (শত০ ১৪/৭/৩/৩/২/৪/৪) অর্থাৎ বরুণ সমস্ত দেবতার আত্মা, অর্থাৎ অন্তর্যামী।
‘সর্বং তদ্রাজা বরুণো বিচষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎপরস্তাৎ। সংখ্যাতা অস্য় নিমিষো জনানাম্’ (অথর্ব০ ৪/৭/১৬/১৫)। অর্থাৎ সর্বপ্রকাশক জগদ্রাজা বরুণ এই ত্রিলোকের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তারও অতীত যা কিছু আছে—সবই দেখেন। প্রাণীদের নিমেষ-উন্মেষ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা গণিত।
যস্তিষ্ঠতি যশ্চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্ ।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা
তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ।।
(অথর্ব০ ৪/৭/১৬/৭২)
এই মন্ত্রে বরুণ রাজা (পরমেশ্বর)-এর সর্বান্তর্যামিতা, সর্বব্যাপকতা এবং গূঢ়বিজ্ঞানতা প্রদর্শনের জন্য বলা হয়েছে—যে দাঁড়িয়ে থাকে, যে চলে, যে অন্যকে প্রতারণা করে, যে লুকিয়ে কোথাও যায়, যে অন্যের ওপর অত্যাচার করে এবং যে দুই ব্যক্তি মিলিত হয়ে গোপনে পরামর্শ করে—তাদের দু’জনের মাঝখানে তৃতীয় রূপে বরুণ, অর্থাৎ পরমেশ্বর, তাদের সমস্ত কথা জেনে নেন।
সুপর্ণ— নিঘণ্টুতে ‘সুপর্ণ’ শব্দ পাওয়া যায়। তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবরাজ যজ্বা লিখেছেন—
‘শোভনং পৃণান্তি পালয়ন্তি জগৎ শীতাদিনিবারণাৎ অথবা পূরয়ন্তি বৃষ্ট্যা, শোভন পতনং গমনমেষামিতি বা, সুষ্ঠু প্রীণয়ন্তি তर्पয়ন্তি জগৎ বর্ষপ্রদানেরেতি বা সুপর্ণাঃ। যদ্বা সু: মত্বর্থে, ভাবে চ “ন” প্রত্যয়ঃ পতনাদিমন্তঃ সুপর্ণাঃ’।
নিঘণ্টুতে ‘সুপর্ণ’ শব্দকে কিরণবাচক বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী যজ্বা নির্বচন করেছেন। কিন্তু—
সু = শোভন, পৃণাতি = পালন করে জগৎ, পূরয়তি চ বিবিধৈঃ পদার্থৈঃ; শোভন পতনং জ্ঞানং যস্য, সুষ্ঠু প্রীণয়তি তर्पয়তি চ জগদ্—এই অর্থে সুপর্ণ পরমেশ্বর। এইভাবে এই নির্বচনগুলোও ভগবৎপরক হয়ে যায়।
বিষ্ণুসহস্রনামের ব্যাখ্যায় এই শব্দের তিনটি নির্বচন দেওয়া হয়েছে—
১. শোভনং পর্ণ যস্যেতি সুপর্ণ—যাঁর পর্ণ শোভন। এখানে ‘পর্ণ’ বলতে ফলপ্রদানের সামর্থ্য বোঝানো হয়েছে।
২. শোভনধর্মাধর্মরূপপূর্ণত্বাৎ সুপর্ণ—উত্তম ধর্ম ও অধর্মরূপ পর্ণযুক্ত হওয়ার কারণে ভগবান সুপর্ণ। এখানে ধর্মাধর্ম বলতে ধর্মাধর্মজনিত ফল বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যথাযথভাবে ধর্ম ও অধর্মের ফল প্রদান করার কারণে ভগবান সুপর্ণ।
৩. শোভনানি পর্ণানি ছন্দাংসি সংসারতরুরূপিণো’স্যেতি সুপর্ণ—অর্থাৎ যাঁর সুন্দর পর্ণরূপ ছন্দ, অর্থাৎ বেদসমূহ। গীতায় বলা হয়েছে—
ঊর্ধ্বমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিত্ ॥
–গীতা ১৫/১
বিশিষ্টাদ্বৈতানুসারী ব্যাখ্যায় লেখা আছে—
সংসারপারনয়নাত্ সুপর্ণ ইতি বা মতঃ
প্রত্যায়নসমাধীন্ যঃ সমাধেঃ পরিপাকতঃ
তমসঃ পারং নয়তি সুপর্ণ ইতি কথ্যতে
আশয় এই যে—সামর্থ্যবান হওয়ার কারণে, সংসারসাগর পার করানোর কারণে এবং সমাধির পরিপাক হলে অজ্ঞানের নাশ করে পরমপদে উপনীত করার কারণে ভগবানকে সুপর্ণ বলা হয়।
এই ব্যাখ্যায় ত্রৈতবাদ—অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি—এই তিনটির পৃথক পৃথক সত্তার প্রতিপাদন হয়েছে: পার করিয়ে নেওয়াবালা পরমাত্মা, পার হয়ে যাওয়াবালা জীবাত্মা এবং যে তমস্=প্রকৃতি (সংসারসাগর) থেকে পার হতে হয়, তা।
বৃদ্ধহারীত (১০৫৫২)-এর মতে ‘ছন্দোময়মুদাহৃতম্’—বেদমন্ত্র দ্বারা বর্ণিত হওয়ার কারণে ভগবানকে সুপর্ণ বলা হয়। তিনি বলেন— ‘সুবর্ণ এবং সুপর্ণঃ বর্ণব্যত্যয়াত্’। নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহে সুপর্ণ নাম দ্বারা ভগবানের উল্লেখ হয়েছে—
একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিদেশ সে ইদং ভুবনং বি চষ্টে।
– ঋক্ ০ ১০/১১৪/১৪
অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় সুপর্ণ = উত্তম পালক পরমাত্মা সংসারে অবশিষ্ট আছেন, সর্বব্যাপী। তিনিই এই জগতের জ্ঞাতা এবং জ্ঞানদানকারী।
সুপর্ণ বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্ত বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্যরেষু গ্রহান্ত্সোমস্য মিমতে দ্বাদশ।।
– ঋক্ ০ ১০/১১৪/৭৫
এর আশয় এই যে, বেদজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ অজ্ঞান নাশ করে সংসার-সাগর পার করিয়ে দেওয়া সুপর্ণ নামধারী ভগবানকে নানা রূপে ও নানা নামে স্মরণ করেন এবং সোমাদি যজ্ঞের দ্বারা তাঁদেরই উপাসনা করেন।
এই মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে সায়ণাচার্য লিখেছেন—
বিপ্রা মেধাবিনঃ কবয়ঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞা মনুষ্যাঃ সুপর্ণং সুপতনমেকং সন্তং পরমাত্মানং বচোভিঃ
স্তুতিলক্ষণৈর্যচনৈর্ বহুধা বহুপ্রকারং কল্পয়ন্তি কিং চ ত এবং কবয়ো’ধ্যরেষু যজ্ঞেষু ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি সপ্ত
ছন্দাংসি দধতঃ ধারয়ন্তো দ্বাদশ সংখ্যাকান্ সোমস্য গ্রহান্ গ্রহনসাধনানি পাত্রাণ্যুপাংশ্বন্তর্যামাদীনি মিমতে
নির্মিমতে।
এইভাবে সুপর্ণ শব্দের অর্থ সায়ণ করেছেন—‘সুপতনমেকং সন্তং পরমাত্মানম্’।
সুপর্ণ নামকে পরমাত্মা রূপে গ্রহণ করলে এই মন্ত্রস্থিত অন্যান্য নামগুলিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরমাত্মাবাচক প্রমাণিত হয়।
গরুত্মান্—নিরুক্তকার বলেন—‘গরুত্মান গরণবান্ গুর্যাত্মা মহাত্মেতি বা’ (নিরুক্ত ৭/১৮)। এখানে প্রথম নিরুক্তি আধিভৌতিক, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। গ্রন্থকার দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করেছেন—‘যো গুর্বাত্মা স গরুত্মান্’।
নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার স্কন্দ গরুত্মান্-এর ব্যাখ্যা করতে লিখেছেন—‘গরুত্ = গরণং ভৌমানাং রসানাং রশ্মিভির্গরণেন তদ্বান্ অথবা গুর্যাত্মা সন্ গরুত্মান্’। এখানে প্রথম ব্যাখ্যা আধিভৌতিক ও সূর্যপরক, কিন্তু—‘গরুত্ গরণং নিগরণং প্রলয়ে সর্বস্য জগতঃ নিগরণেন গরুত্মান্ পরমেশ্বরঃ’—এইভাবে পরমাত্মাবাচক অর্থও হয়; অর্থাৎ প্রলয়ে সমগ্র জগতকে গ্রাস করার কারণে ভগবান গরুত্মান।
‘প্রজাপতিবৈ সুপর্ণো গরুত্মান্’ (শতপথ ১০/২/২৪/৪)—অর্থাৎ পরমেশ্বরই সুপর্ণ = সুপালক, গরুত্মান।
যজুর্বেদে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এরই বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে—
সুপর্ণো’সি গরুত্মান্ পৃষ্ঠে পৃথিব্যাঃ সীদ।
ভাসান্তরিক্ষমাপৃণ জ্যোতিষা দিবমুত্তভান্ তেজসা দিশ উদ্দণ্ড।।
– যজুঃ ০ ১৭/৭২
অর্থাৎ হে পরমেশ্বর! আপনি গরুত্মান—আপনার চেয়ে অধিক বল বা শক্তি কারও নেই, অতএব আপনি সুপর্ণ। আপনার তেজে সব কিছু দীপ্ত, প্রকাশিত, উদ্ভাসিত। আপনি আমার হৃদয়াকাশে এমন আলোক দান করুন যাতে অজ্ঞান নাশ হয়ে জ্ঞানের উদয় হয়।
মাতরিশ্বা—নিরুক্তকার মাতরিশ্বার নিরুক্তি এইভাবে করেছেন—‘মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বাসিতি মাতর্যাশ্বনিতীতি বা’ (নি ৭/২৬)। এই নিরুক্তি মাতরিশ্বাকে বায়ুর প্রতিশব্দ ধরে করা হয়েছে। কিন্তু অন্তর্নিহিত ণ্যর্থ গ্রহণ করলে এটিও ঈশ্বরবাচক হয়—
‘মাতরি মাতুর্যোনৌ শ্বাসিতি প্রাণয়তি আশু অনিতি আনয়তি বা স মাতরিশ্বা ভগবান্’।
অর্থাৎ যিনি মাতৃগর্ভেও প্রাণ সঞ্চার করেন, তিনিই ভগবান মাতরিশ্বা।
‘ঋতস্য তন্তু মনসা মিমানঃ সর্বা দিশঃ পয়তে মাতরিশ্বা’
(অথর্ব ১৩/৩/৭১/৬) — অর্থাৎ মাতরিশ্বা সর্বব্যাপী পরমেশ্বর জ্ঞানপূর্বক সৃষ্টির বিস্তার নির্মাণ করে সকল দিককে পবিত্র করেন।
সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবা সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।
– ঋক্ ০ ১০/৮৫/৪৭
এই মন্ত্রটি বিবাহ-প্রকরণে ব্যবহৃত। স্বামী-স্ত্রী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—বায়ুর ন্যায় বলবান ও প্রাণবায়ুর ন্যায় প্রিয় মাতরিশ্বা ভগবান যেন তাঁদের হৃদয়কে পরস্পর এক করে দেন।
ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬-এ ‘এক সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ এবং ১০/১১৪/৭৫-এ ‘এক সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি’—এই উক্তিগুলিতে স্পষ্টভাবে বৈদিক একেশ্বরবাদের প্রতিপাদন হয়েছে। এ বিষয়ে ডক্টর গ্রিসওল্ড (Dr. Griswold)-এর মন্তব্য—
"Swami Dayananda's theory of Monotheism in the Rigveda -- Taking his case from the late passages
R.V.I. 164-46 and X .114-5, the founder of Arya Samaj held that all the gods mentioned in the Rigveda are simply variant names for one God. This process of reduction from multiplicity to unity would have been easier if there had been no dual gods or group gods mentioned in the Rigveda ....... The monotheistic inter- pretation of the Rigveda involved on the part of Swami Dayananda much wild and unscientific exegesis ...... "-Religion of the Rigveda, Pages 109, 110.
অর্থাৎ—
“স্বামী দয়ানন্দের ঋগ্বৈদিক একেশ্বরবাদ—আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ঋগ্বেদের পরবর্তী অংশ ঋক্ ১/১৬৪/৪৬ ও ১০/১১৪/৭৫-কে ভিত্তি করে এই মত দাঁড় করান যে ঋগ্বেদে উল্লিখিত সকল দেবতাই এক পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম। বহু থেকে একে নামিয়ে আনার এই প্রক্রিয়া আরও সহজ হতো, যদি ঋগ্বেদে দ্বৈত দেবতা বা গণদেবতার উল্লেখ না থাকত। ঋগ্বেদ-মন্ত্রগুলির একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী দयानন্দকে বহু অপ্রাসঙ্গিক ও বিজ্ঞানবিরোধী টানাটানি করতে হয়েছে।”
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রিসওল্ডের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কারণ গ্রন্থকারের এই মত কখনোই নয় যে বেদে সব দেবতাই সব স্থানে পরমাত্মাবাচক, এবং তিনি তাঁর বেদভাষ্যে এমন অর্থ করার চেষ্টা করেননি। গ্রন্থকারের মত হলো—
“যেখানে-যেখানে স্তব, প্রার্থনা, উপাসনা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিশেষণ রয়েছে, সেখানে-সেখানে এই নামগুলির দ্বারা পরমেশ্বরই গৃহীত হন। যেখানে-যেখানে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, অল্পজ্ঞ, জড়, দৃশ্য ইত্যাদি বিশেষণ রয়েছে, সেখানে-সেখানে পরমেশ্বর গৃহীত হন না। যেখানে-যেখানে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রচেষ্টা, সুখ ও অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি বিশেষণ থাকে, সেখানে-সেখানে জীব গৃহীত হয়।”
এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে গ্রন্থকারের মতে দেবতাবাচক পদগুলি প্রসঙ্গভেদে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতিরও বাচক হতে পারে। যখন তাঁর মূলনীতিই এই নয় যে প্রত্যেক দেবতা সর্বত্র ঈশ্বরবাচক, তখন টানাটানি করে তেমন প্রমাণ করার প্রশ্নই ওঠে না। দ্বৈত দেবতা (Dual gods) এবং গণদেবতা (Group gods) প্রসঙ্গভেদে ভিন্ন অর্থবোধক হতে পারে—এটি প্রমাণ করতে এখানে একটি করে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—
ঋগ্বেদ ১/১০৮ সমগ্র সূক্তের দেবতা ইন্দ্রাগ্নি। এর মন্ত্র ১, ২, ৩-এ গ্রন্থকার ইন্দ্রাগ্নির অর্থ করেছেন ‘বায়ু-পাবকৌ’, অর্থাৎ বায়ু ও অগ্নি। মন্ত্র ৪, ১১, ১২-এ বায়ু ও বিদ্যুৎ; ৫, ৭, ৮-এ স্বামী ও ভৃত্য; ৬, ১০-এ বিচারক ও সেনাপতি; ৬-এ স্বামী ও শিল্পী; এবং ১৩-এ পরম ধনবান ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী—কিন্তু একটিতেও পরমাত্মা অর্থ করা হয়নি।
ঋগ্বেদ ১/১১০-এর দেবতা ঋভু (গণদেবতা)। এই সূক্তে ঋভু শব্দের অর্থ করা হয়েছে—মেধাবী, সূর্যের কিরণসমূহ এবং বহু বিদ্যার আলোকপ্রদাতা বিদ্বান। এই সমগ্র সূক্তে এই শব্দটিকে কোথাও পরমাত্মার বাচক বলা হয়নি। প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণে দ্বিত্ব দেবতা এবং গণদেবতাকে পরমাত্মার শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো টানাটানির প্রয়োজন নেই।
ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে ডঃ তারাচন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী আদিশঙ্করাচার্য একেশ্বরবাদের প্রেরণা নবম শতাব্দীতে মালাবার উপকূলে অবতরণকারী আরব ব্যবসায়ীদের থেকে পেয়েছিলেন। ভারতীয় উৎসের ভিত্তিতে আদিশঙ্করের জন্ম ৫০৬ খ্রিষ্টপূর্বে হয়েছিল। শঙ্কর ছয় বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বেদাধ্যয়নের জন্য নর্মদা-তটে অবস্থিত ওঁকারনাথের নিকটস্থ গোবিন্দ ভগবৎপাদের আশ্রমে চলে আসেন। পাশ্চাত্য মতানুসারে শঙ্কর স্বামীর কাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পড়ে। ডঃ তারাচন্দ এতটুকুও ভেবে দেখেননি যে (তাঁর মতে) সপ্তম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী এবং নর্মদা-তটে বসবাসকারী একজন ব্যক্তির সঙ্গে নবম শতাব্দীতে মালাবার উপকূলে আগত আরবদের কীভাবে যোগাযোগ হতে পারে? তদুপরি শঙ্করের জন্মকালে (সপ্তম শতাব্দী) তখনও মুহাম্মদ সাহেব মক্কায় ইসলামের প্রচার শুরু করেছিলেন মাত্র। এটাও উল্লেখযোগ্য যে স্বয়ং মুহাম্মদ সাহেব একেশ্বরবাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন আব্রাহাম থেকে, অথচ শঙ্করাচার্যের দাদাগুরু গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন গৌড়পাদাচার্য।
-Influence of Islam on Hindu Culture.
বাস্তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তাধারার ভিত্তিমূলক নীতি হলো বিকাশবাদের পূর্বাগ্রহ। তাঁদের কাছে প্রথমে বিকাশবাদের তত্ত্ব, তার পরে যা কিছু আসে তাকে সেই তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে ফিট করিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়। বিকাশবাদের মানদণ্ডে যাচাই করেই তাঁরা কোনো বিষয়ে সঠিক বা ভুল নির্ণয় করেন। এই ধরনের চিন্তনকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না।
শ্রী অরবিন্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন—“পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের মত হলো, বেদের ঋষি যখন অগ্নির উপাসনা করতেন, তখন তিনি অগ্নির মধ্যে অন্য সব দেবতার গুণাবলি আরোপ করতেন। যখন তিনি বায়ুর উপাসনা করতেন, তখন বায়ুর মধ্যেও অন্য দেবতাদের সকল গুণ আরোপ করতেন। এতে মনে হয় যে তিনি এক দেবতার উপাসক ছিলেন না, বরং বহু দেবতায় বিশ্বাস করতেন। এই ধারণাটি তাঁদের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কারণ একেশ্বরবাদের ধারণা মানব-মস্তিষ্কে অনেক পরে এসেছে। যখন তাঁদের বলা হয় যে বেদে ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নি যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ’—এই মন্ত্র দ্বারা বলা হয়েছে যে ঈশ্বর এক, আর অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি সেই এক ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম—তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলে ওঠেন যে এই মন্ত্রটি পরে সংযোজিত হয়েছে। (ম্যাক্সমূলারের প্রধান শিষ্য ম্যাকডানেল তাঁর ‘A Vedic Reader for Students’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে আটটি আগে রচিত, তারপর নবম এবং শেষে দশম। তাঁর বক্তব্যের অর্থ হলো—প্রথম আটটি ও পরবর্তী দুটি (৯–১০) মণ্ডলের রচনাকাল ভিন্ন। অথচ ‘এক সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ তো ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেরই মন্ত্র। তবুও একে পরবর্তী সংযোজন বলে ধরা হয়—শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি তাঁদের বিকাশবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না)। এই চিন্তাধারার ধারাবাহিকতায় ম্যাক্সমূলার বহুদেবতাবাদ (Polytheism) ও একেশ্বরবাদ (Monotheism)-এর মধ্যবর্তী একটি নতুন মত কল্পনা করেন, যার নাম তিনি দেন হেনোথিইজ়ম (Ilenotheism)। হেনোথিইজ়মের অর্থ হলো—যখন কোনো নির্দিষ্ট দেবতার উপাসনা করা হয়, তখন তার মধ্যেই সকল গুণ আরোপ করে নেওয়া হয় এবং অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় তাকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যদের হীন বলে কল্পনা করা।
ভূরংসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রী ।
পৃথিবীং যচ্ছ
পৃথিবী দুঁ. হ পৃথিবী মা হিং, সীঃ ।।১।।
– যজুঃ০ ১৩/৭/১৮
ইন্দ্রো মহন্না রোদসী পপ্রথচ্ছবইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ত্ ।
ইন্দ্রে হে বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্যানাস ইন্দবঃ ।
– সামবেদ প্রপাঠক ৭ / ত্রিক ৬ / মন্ত্র ২ ।।
(The Oxford English Dictionary defines Henotheism as the belief in a single God, without asserting
that he is the only God; a stage between Polytheism and Monotheism. According to Prof. Clayton it denotes
that each of the several divinities is regarded as the highest, the one that was worshipped and, therefore,
treated as if he were the absolute being, independent and supreme for the worshipper.)
কিন্তু এই কল্পনা করা হয় এই কারণে যে, ম্যাক্সমূলার বিকাশবাদের বিপরীতে এই কথা মানতে প্রস্তুত নন যে মানব-সংস্কৃতির প্রারম্ভিক কালে একেশ্বরবাদের মতো উৎকৃষ্ট চিন্তা মানব-মস্তিষ্কে আসতে পারত। ম্যাক্সমূলার এই কথার কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি যে ‘এক সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ মন্ত্রটি বেদে পরে সংযোজিত হয়েছে। এই মন্ত্র বেদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং এর দ্বারা যদি বিকাশবাদ খণ্ডিত হয়, তবে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের তার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—নিজের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য স্বয়ং বেদের অন্তঃসাক্ষীই প্রমাণ হবে, না কি রুডলফ, রাথ ও ম্যাক্সমূলার যা বলবেন সেটাই প্রমাণ হবে। যদি বেদের অর্থ বেদ থেকেই স্পষ্ট হয়, তবে সেই প্রক্রিয়ারই সর্বোচ্চ স্থান থাকা উচিত। বেদ নিজেই বলে—‘একং সত্’ ঈশ্বর এক, ‘বহুধা বদন্তি’ তাঁকে বহু নামে ডাকা হয়। স্বয়ং বেদে একেশ্বরবাদের এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও ম্যাক্সমূলারের হেনোথিইজ়ম কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?”
শ্রী অরবিন্দ এরপর লেখেন—
"We are aware how modern scholars twist away from the evidence. This hymn, they say, was a late
production; this lofty idea which it expresses with so clear a force rose up somehow, or was borrowed by
those ignorant fire-worshippers from their cultured and philosophic Dravadian enemies. But throughout the
Veda we have conformatory hymns and expressions. Agni or Indra or another is expressed hymned as one
with all other Gods. Agni contains all other divine powers within himself; the Maruts are described as all the
gods; the one deity is addressed by the names of others as well as his own, or, more commonly, he is given
as Lord and King of the universe, attributes appropriate to the Supreme Deity. Why should not the
foundation of Vedic thought be natural monotheism? Well, because primitive barbarians could not possibly
have risen to such high conceptions, and if you allow them to have so risen, you imperil our theory of
evolutionary stages of human development. Truth must hide itself, common sense disappears from the field
so that a theory may flourish. I ask—in this point, and it is the fundamental point, who deals more
straightforwardly with the text, Dayananda or the Western scholars?"
শ্রী অরবিন্দের বক্তব্য হলো—পাশ্চাত্য বেদভাষ্যকাররা বেদের ভাষ্য করতে গিয়ে বিকাশবাদের পূর্বাগ্রহ সঙ্গে নিয়ে চলেন। যদি বেদের অর্থ তাঁদের বিকাশবাদী ধারণাকে সমর্থন না করে, তবে তাঁরা কেন সেই অর্থকে ভেঙে-মোচড়ে নিজেদের অনুকূলে গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন? শ্রী অরবিন্দের মতে, দयानন্দের ভাষ্যে এমনটি করা হয়নি।
ইন্দ্রো মহন্না ইতি—(ইন্দ্র) পরমেশ্বর তাঁর (মহন্না) মহিমা দ্বারা (রোদসী) দ্যুলোক ও ভূলোকে (শবঃ) নিজের অনন্ত শক্তি (পপ্রথৎ) বিস্তার করেছেন। (ইন্দ্রঃ) পরমেশ্বর (সূর্যম্) সূর্যকে (অরোচয়ত্) দীপ্ত করেছেন। (ইন্দ্রে) পরমেশ্বরে (বিশ্বা ভুবনানি) সমস্ত লোক ও লোকান্তর (যেমিরে) নিয়ন্ত্রিত। (ইন্দবঃ) জ্ঞানসম্পন্ন
প্রাণায়ু নমো যস্য যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরী যস্মিন্সয়ু প্রতিষ্ঠিতম্
– অথর্ববেদ কাণ্ড ১১, সূক্ত ৪, মন্ত্র ১
অর্থ—এখানে এই সকল প্রমাণ লেখার উদ্দেশ্য এটুকুই যে, যেখানে-যেখানে এই প্রকার প্রমাণে ওঁকারাদি নামের দ্বারা পরমাত্মার গ্রহণ হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।
এবং পরমেশ্বরের কোনো নামই অর্থহীন নয়—যেমন সংসারে দরিদ্র ব্যক্তিরও ‘ধনপতি’ প্রভৃতি নাম হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো নাম গৌণিক, কোনো নাম কার্মিক এবং কোনো নাম স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।
‘ও৩ম্’ প্রভৃতি নাম অর্থবহ। যেমন—
(ওং খং) ‘অবতীতিওম্’—রক্ষা করার কারণে ‘ও৩ম্’; আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপক হওয়ার কারণে ‘খং’; এবং সকলের চেয়ে বৃহৎ হওয়ার কারণে ‘ব্রহ্ম’—এই সবই ঈশ্বরের নাম। ।।১।।
(ওমিত্যেত্) ‘ও৩ম্’ যাঁর নাম, এবং যিনি কখনো নষ্ট হন না, কেবল তাঁরই উপাসনা করা উচিত, অন্য কারও নয়। ।।২।।
(ওমিত্যেতৎ) সকল বেদাদি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রধান ও নিজস্ব নাম বলা হয়েছে ‘ও৩ম্’-কে; অন্য সব নাম গৌণ। ।।৩।।
(সর্বে বেদাঃ) কারণ সকল বেদ ও ধর্মানুষ্ঠানরূপ তপস্যা যাঁকেই নির্দেশ করে ও স্বীকার করে, এবং
(প্রশাসিতা) যিনি সকলকে শাসন ও শিক্ষা দেন, অতি সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সমাধিস্থ বুদ্ধির দ্বারা যাঁকে জানা যায়—তাঁকেই পরমপুরুষ বলে জানা উচিত। ।।৫।।
(এতম্) স্বপ্রকাশ হওয়ার কারণে ‘অগ্নি’, বিজ্ঞানস্বরূপ হওয়ার কারণে ‘মনু’, সকলকে পালন করার কারণে ‘প্রজাপতি’, পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন হওয়ার কারণে ‘ইন্দ্র’, সকলের জীবন-মূল হওয়ার কারণে ‘প্রাণ’, এবং নিরন্তর সর্বত্র ব্যাপক হওয়ার কারণে পরমেশ্বরের নাম ‘ব্রহ্ম’। ।।৬।।
প্রকাশিত ও শীতল স্বভাববিশিষ্ট উপাসকেরা (স্বানাসঃ) সদুপদেশ প্রদান করতে করতে (ইন্দ্রে) পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থেকেই (রেমিরে) নিজেদের নিয়ম পালন করেন।
প্রাণায় ইতি—(প্রাণায়) সমগ্র জগতের প্রধান প্রাণ পরমেশ্বরকে (নমঃ) নমস্কার। (যস্য বশে) যাঁর বশে (ইদং সর্বম্) এই সমস্ত জগৎ। (ভূতঃ) অনাদি কাল থেকে বর্তমান সত্যস্বরূপ যিনি, (যঃ) সেই প্রাণ (সর্বস্য) সমগ্র জগতের (ঈশ্বরঃ) অধীশ্বর, এবং (যস্মিন্) যাঁর মধ্যে (প্রতিষ্ঠিতম্) সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত।
জড়-চেতন জগতের প্রতিটি পদার্থের মধ্যে নিজস্ব প্রাণ রয়েছে, যার দ্বারা সেই পদার্থের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই প্রত্যেককীয় প্রাণ পরমেশ্বররূপ প্রাণের দ্বারাই প্রত্যেক পদার্থে প্রাপ্ত। অতএব পরমেশ্বর—
১. গৌণিক = গুণনিমিত্তক, কার্মিক = কর্মনিমিত্তক, স্বাভাবিক = স্বভাবনিমিত্তক। দ্রষ্টব্য—এই সমুল্লাসেই ১০০ নামের পরবর্তী প্রসঙ্গ— ‘তাদের প্রত্যেকটি গুণ, কর্ম ও স্বভাবের একটি করে নাম।’
২. জার্মান পণ্ডিত বুহলার এখানে Sleep (like abstraction) অনুবাদ করেছেন, যা মূল অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ।— ভগবদ্দত্ত
৩. নিরন্তর = কোনো বাধা ছাড়াই ভিতরে-বাইরে সর্বত্র ব্যাপক, অর্থাৎ সর্বাধিক বৃহৎ। এই অর্থে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি ‘বৃहि বৃদ্ধৌ’— (ধাতু ১।৪৮৮) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।
(স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ)
সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করার কারণে ‘ব্রহ্মা’, সর্বত্র ব্যাপক হওয়ার কারণে ‘বিষ্ণু’, দুষ্টদের দণ্ড দিয়ে কাঁদিয়ে তোলার কারণে ‘রুদ্র’, মঙ্গলময় ও সকলের কল্যাণকারী হওয়ার কারণে ‘শিব’।
“যঃ সর্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্” ।।১।।
“যঃ স্বয়ং রাজতে স স্বরাট্” ।।২।।
“যোऽগ্নিরিয় কালঃ কলয়িতা প্রলकर्त্তা সে কালাগ্নিরীশ্বরঃ” ।।৩।।
‘অক্ষর’—যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত ও অবিনাশী; ‘স্বরাট্’—যিনি স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ; এবং ‘কালাগ্নি’—যিনি প্রলয়ের সময় অগ্নির ন্যায় সকলের কাল এবং কালেরও কাল—এই কারণে পরমেশ্বরের নাম ‘কালাগ্নি’। ।।৭।।
(ইন্দ্রং মিত্রং …)
যিনি এক ও অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁরই ইন্দ্র প্রভৃতি সকল নাম।
“যুয়ু শুদ্ধেষু পদার্থেষু ভবো দিব্যঃ”;
“শোভনানি পর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কর্মাণি বা যস্য সা সুপর্ণঃ”;
“যো গুরু আত্মা স গরুত্মান্”;
“যো মাতরিশ্বা বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিশ্বা”।
‘দিব্য’—যিনি প্রকৃতি প্রভৃতি দিব্য পদার্থে ব্যাপ্ত;
‘সুপর্ণ’—যাঁর উত্তম পালন ও পূর্ণ কর্ম রয়েছে;
‘গরুত্মান্’—যাঁর আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহান;
‘মাতরিশ্বা’—যিনি বায়ুর ন্যায় অনন্ত বলবান।
এই কারণে পরমাত্মার নাম ‘দিব্য’, ‘সুপর্ণ’, ‘গরুত্মান্’ ও ‘মাতরিশ্বা’। অন্যান্য নামের অর্থ পরে লেখা হবে। IlelI
(ভূমিরসি …)
“ভবন্তি ভূতানি যস্যাং সা ভূমিঃ”—যাঁর মধ্যে সমস্ত জীবসত্তা অবস্থান করে, সেই কারণে ঈশ্বরের নাম ‘ভূমি’। অন্যান্য নামের অর্থ পরে লেখা হবে। ।।১।।
(ইন্দ্রো মহনা …)
এই মন্ত্রে ‘ইন্দ্র’ পরমেশ্বরেরই নাম—এই কারণেই এই প্রমাণ লেখা হয়েছে। ।।১০।।
(প্রাণায় …)
যেমন প্রাণের অধীনে সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে, তেমনি পরমেশ্বরের অধীনে সমস্ত জগৎ থাকে—এই কারণে পরমেশ্বরের নাম ‘প্রাণ’। ।।১১।।
তিনি সমগ্র জগতের প্রধান প্রাণ।
যাস্ক প্রভৃতি নৈরুক্তদের সিদ্ধান্ত হলো—“অর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত” (নি০ ২/১১)।
অর্থাৎ প্রচলিত পরম্পরা বা ব্যবহারপ্রাপ্ত অর্থকে নির্বচনের দ্বারা সমর্থন করা উচিত। ন্যায়সম্মত, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও ব্যবহারপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল শব্দই ভগবানের বাচক। অতএব অর্থানুসারী নির্বচন করার জন্য তার উপযুক্ত প্রকৃতি ও প্রত্যয় গ্রহণ করা আবশ্যক।
‘প্রাণ’ শব্দের নির্বচন করতে গিয়ে গ্রন্থকার এই নিয়মই অনুসরণ করেছেন। যদি এই শব্দের নির্বচন করা হয়—“প্রাণতীতি প্রाणঃ”, অর্থাৎ শ্বাস নেওয়ার কারণে ভগবানকে ‘প্রাণ’ বলা হয়—তবে তা ভুতার্থ হবে না, কারণ ভগবান শ্বাস গ্রহণ করেন না। সুতরাং মুখ্যার্থে এই প্রয়োগ সম্ভব নয়; তখন এই ব্যবহার উপচারমূলক হয়ে পড়ে।
এই কারণে গ্রন্থকার নির্বচনের রূপ নির্ধারণ করেছেন—
“সর্বেষাং প্রাণস্য = জীবস্য মূলং প্রাণঃ”।
অর্থাৎ—“প্রাণকারণত্বাৎ প্রाणং ব্রহ্ম, যথা আয়ুষ্কারণত্বাৎ আয়ুঃ ঘৃতম্”।
উপনিষদে বলা হয়েছে—
“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বৈ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ” (কেন০ ১/২)।
অর্থাৎ ভগবান কর্ণকে শ্রবণশক্তি, মনকে মননশক্তি, বাক্কে উচ্চারণশক্তি এবং প্রাণকে প্রাণনশক্তি প্রদান করেন।
এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ‘প্রাণ’ শব্দের ঈশ্বরার্থে ব্যবহার—
১. এই অর্থে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি ‘বৃহ্ উদ্যমনে’ (ধাতু০ ৬৭৫৬) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।
২. ‘ভূমি’ শব্দটি ভীমাদি গণে পঠিত; অতএব ‘ভীমাদয়োऽপাদানে’ (অষ্টা০ ৩/৪/৪৭/৭৪) নিয়ম অনুসারে অপাদানে প্রত্যয় হওয়া উচিত। গ্রন্থকারের স্বীয় উণাদিকোষ ৪৭/৪৬-এর বৃত্তিতেও “ভবন্তি পদার্থা অস্যামিতি ভূমিঃ”—এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা উচিত।
ইত্যাদি প্রমাণগুলোর যথাযথ অর্থ জানলে এই সমস্ত নামের দ্বারা কেবল পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করা হয়।
কারণ ‘ওঁ৩ম্’ এবং অগ্নি প্রভৃতি নামগুলোর মুখ্য অর্থেই পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয়। যেমন ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতি ঋষি-মুনিদের ব্যাখ্যানে পরমেশ্বরের গ্রহণ দেখা যায়, তেমন গ্রহণ করাই সকলের পক্ষে যোগ্য।
[‘অগ্নি’ প্রভৃতি নামের ঈশ্বরার্থ বা ভৌতিকার্থ নির্ধারণের জন্য নিয়ামক প্রসঙ্গ। কিন্তু ‘ওঁ৩ম্’ তো কেবলমাত্র পরমাত্মারই নাম। আর ‘অগ্নি’ প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমেশ্বরের গ্রহণে প্রসঙ্গ ও বিশেষণই নিয়ামক কারণ। এর দ্বারা কী প্রমাণিত হলো—যেখানে যেখানে স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এবং সর্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিশেষণ লেখা আছে, সেখানেই সেখানেই এই নামগুলোর দ্বারা পরমেশ্বরের গ্রহণ হয়।
আর যেখানে যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে যে—
ততো বিরাডঞ্জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ ।।১।।
শ্রোত্রোদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদুগ্নিরেজায়ত ।।২।। —যজুঃ ৩১/১২
তেন দেবা অযজন্ত ।।৩।। —যজুঃ ৩১/১৬
পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ।।৪।। —যজুঃ ৩১/৭৫
সেগুলিকে দৃষ্টিতে রেখেই উক্ত শব্দগুলি লেখা হয়েছে।
অন্যত্র লেখা আছে—
‘প্রাণঃ প্রজাপতিঃ’ (শত০ ৬/৩/১/৬);
‘প্রাণস্য প্রাণম্’ (বৃহদ্ ৪/৪/১৮);
‘অতএব প্রাণঃ’ (বেদান্ত ১/১/২৩)।
এই সূত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য লিখেছেন—
‘ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রাণশব্দঃ দৃশ্যতে, প্রাণশব্দঃ ব্রহ্মৈব’।
পুনরায় ‘প্রাণস্তথানুগমাৎ’ (বেদান্ত ১/১/২৮) সূত্রে শঙ্করাচার্য লিখেছেন—
‘প্রাণশব্দো ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্’।
এই সূত্রগুলির উপর ভামতী ও রত্নপ্রভা টীকাতেও একই কথা স্বীকার করা হয়েছে।
‘ততো বিরাড্’ ইত্যাদি পূর্ণ মন্ত্র এইরূপ—
ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ।।
—যজুঃ ৩১/৭৫
অধ্যাত্মের প্রসঙ্গে ‘বিরাট্’ শব্দটি পরমেশ্বরবাচক, কিন্তু সৃষ্টি-উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রসঙ্গে তার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহণ হয়। ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায় সৃষ্টিবিদ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিতে করতে গিয়ে লিখেছেন—
‘সর্বশরীরাণাং সমষ্টিদেহঃ বিভিন্নৈঃ পদার্থৈঃ রাজমানঃ সন্ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ’।
মন্ত্রটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেখানে লেখা হয়েছে—
“(ততো বিরাডজায়ত) ততঃ তস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ডশরীরঃ সূর্যচন্দ্রনেত্রো বায়ুপ্রাণঃ পৃথিবীপাদ ইত্যাদি অলংকারলক্ষণলক্ষিতঃ হি সর্বশরীরাণাং সমষ্টিদেহঃ, বিভিন্নৈঃ পদার্থৈঃ রাজমানঃ সন্ বিরাট্ জায়ত উৎপন্নোऽস্তি। (বিরাজো অধিপুরুষঃ) তস্মাৎ বিরাজোऽধি উপরি পশ্চাৎ ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বাবয়বৈঃ পুরুষঃ, সর্বপ্রাণিনাং জীবাধিকরণো দেবঃ পৃথক্-পৃথক্ অজায়ত উৎপন্নোऽভূত। (স জাতঃ) স দেহঃ ব্রহ্মাণ্ডাবয়বৈরেব বর্ধতে, নষ্টঃ সন্ তস্মিন্নেব প্রলীয়ত ইতি। পরমেশ্বরস্তু সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোऽতিরিচ্যত অতিরিক্তঃ পৃথগ্ভূতোऽস্তি। (পশ্চাৎ ভূমিমথো পুরঃ) পুরঃ পূর্বং ভূমিমুৎপাদ্য ধারিতবান্, ততঃ পুরুষস্য সামর্থ্যাৎ স জীবোऽপি ধারিতবানস্তি। স চ পুরুষঃ পরমাত্মা ততস্তস্মাজ্জীবাদপ্যত্যরিচ্যত পৃথগ্ভূতোऽস্তি।”
অর্থাৎ—
যে ব্রহ্মাণ্ডকে অলংকাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সেই পুরুষের সামর্থ্য থেকে উৎপন্ন, যাকে মূল প্রকৃতি বলা হয়; যার দেহ ব্রহ্মাণ্ডের সমতুল্য, যার সূর্য-চন্দ্র নেত্রস্বরূপ—
“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যাঃ ঔষধয়ঃ। ঔষধিভ্যোऽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোऽন্নরসময়ঃ।” ।।৫।।
—এইটি তৈত্তিরীয় উপনিষদ (ব্রহ্মানন্দ বল্লী ১)-এর বচন।
যার প্রাণ বায়ু এবং যার পাদ পৃথিবী—এইরূপ লক্ষণযুক্ত যে সমষ্টি দেহ, তাকেই বিরাট্ বলা হয়। তিনি প্রথমে কলারূপ পরমেশ্বরের সামর্থ্যে উৎপন্ন হয়ে জড় ও চেতন উভয়ের পৃথক পৃথক দেহরূপে প্রকাশ পেয়েছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত জীব বাস করে এবং যে দেহ পৃথিবী প্রভৃতি অবয়ব ও অন্ন-ঔষধি দ্বারা বৃদ্ধি পায়—সে বিরাট্ পরমেশ্বর থেকে পৃথক, এবং পরমেশ্বরও সর্বদা এই সংসাররূপ দেহ থেকে পৃথক থাকেন। প্রথমে ভূমি প্রভৃতি জগৎ উৎপন্ন করে পরে যিনি তা ধারণ করছেন।
আচার্য সায়ণও এখানে বিরাট্ শব্দের অর্থ ব্রহ্মাণ্ড করেছেন—
“বিস্পষ্ট রাজতে ইতি ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ পুরুষো বিরাট্।”
কোথাও কোথাও তিনি ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবকেও বিরাট্ বলেছেন—
“বিরাট্ কৃত্স্নব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবঃ।”
গ্রন্থকার এখানে যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাটের নির্দেশ করেছেন, অথর্ববেদ (১০/৭/৩২-৩৪)-এ সেই ব্রহ্মের পুরুষাকৃতির অলংকারমূলক বর্ণনা স্পষ্টভাবে উপলব্ধ। (দ্রষ্টব্য—অথর্ববেদ ১০/৭/১৮-১৬; ৬৫/২০-২১ এবং ১১/৩/৩১-২)
মহাভারতে লোকাত্মার এইরূপ বর্ণনা করা হয়েছে—
যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌরমূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ ।
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে
তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥
—শান্তিপর্ব ৪৭/১৬৬
উপরোক্ত অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, যেখানে সৃষ্টির উৎপত্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ থাকে, সেখানে বিরাট্, অগ্নি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের গ্রহণ হয় না। সৃষ্টির নিমিত্তকারণরূপে অথবা স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনার প্রসঙ্গেই কেবল এই শব্দগুলোর দ্বারা পরমেশ্বরের গ্রহণ হয়। এই তত্ত্বটি না বোঝার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁদের অনুসারী ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই ধারণা করে নিয়েছেন যে বেদে জড় পদার্থ (অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি)-এর পূজার বিধান আছে।
‘তস্মাদিতি’ (তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ) সেই আত্মতত্ত্ব থেকে আকাশ উৎপন্ন হলো। (আকাশাদ্বায়ুঃ) আকাশ থেকে বায়ু। (বায়োরগ্নিঃ) বায়ু থেকে অগ্নি। (অগ্নেরাপঃ) অগ্নি থেকে জল। (অদ্ভ্যঃ পৃথিবী) জল থেকে পৃথিবী। (পৃথিব্যাঃ ঔষধয়ঃ) পৃথিবী থেকে ঔষধি। (ঔষধিভ্যঃ অন্নম্) ঔষধি থেকে অন্ন। (অন্নাদ্রেতঃ) অন্ন থেকে বীর্য। (রেতসঃ পুরুষঃ) বীর্য থেকে প্রাণী উৎপন্ন হলো।
দেহ অন্নের রস থেকে গঠিত হওয়ার কারণে পুরুষকে ‘অন্নরসময়’ বলা হয়েছে—
“সঃ বা এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ।”
এখানে সৃষ্টিউৎপত্তির প্রসঙ্গ থাকায় আকাশ প্রভৃতি নামগুলি লৌকিক অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের বাচক, পরমেশ্বরের নয়।
সৎ থেকেই সৎ হয়; অসৎ বা অভাব থেকে সৎ বা ভাব উৎপন্ন হয় না। অতএব উপনিষদ যখন বলে যে আত্মা থেকে আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়েছে, তখন তার অর্থ এই যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী—এই সমস্তই বীজরূপে আত্মার সঙ্গে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়—
১. তৈত্তিরীয় উপনিষদ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে প্রায়ই ‘ঔষধিভ্যোऽন্নম্ অন্নাৎ পুরুষঃ’ পাঠ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার নির্দেশিত পাঠটি তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৮/২-এর পাঠান্তরে উপলব্ধ। দ্রষ্টব্য—আনন্দাশ্রম, পুণে সংস্করণ। বোম্বাই থেকে মুদ্রিত ‘মণিপ্রভাযুক্ত একাদশোপনিষদ’-এও এই পাঠ পাওয়া যায়।
এইরূপ প্রমাণগুলিতে বিরাট্, পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি প্রভৃতি নাম লৌকিক পদার্থেরই হয়ে থাকে; কারণ যেখানে-যেখানে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, অল্পজ্ঞ, জড়, দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষণও লেখা থাকে, সেখানে-সেখানে পরমেশ্বরের গ্রহণ হয় না। তিনি উৎপত্তি প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহার থেকে পৃথক। আর উপরোক্ত মন্ত্রগুলিতে উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার রয়েছে, এই কারণেই এখানে ‘বিরাট’ প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমাত্মার গ্রহণ না হয়ে সংসারী পদার্থেরই গ্রহণ হয়। কিন্তু যেখানে-যেখানে সর্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে, সেখানে-সেখানে পরমাত্মার গ্রহণ হয়; আর যেখানে-যেখানে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রয়াস, সুখ, দুঃখ এবং অল্পজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে, সেখানে-সেখানে জীবের গ্রহণ হয়। এই বিষয়টি সর্বত্র এইভাবেই বোঝা উচিত, কারণ পরমেশ্বরের কখনও জন্ম-মরণ হয় না। অতএব ‘বিরাট’ প্রভৃতি নাম এবং জন্মাদি বিশেষণের দ্বারা জগতের জড় ও জীবাদি পদার্থেরই গ্রহণ করা যুক্তিসংগত, পরমেশ্বরের নয়।
এখন যে প্রকারে ‘বিরাট’ প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমেশ্বরের গ্রহণ হয়, সেই প্রকারটি নিচে লিখিত প্রমাণের দ্বারা জানো—
[‘ওঁ’-এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা]
অথ ওঙ্কারার্থঃ— ‘বি’ উপসর্গপূর্বক ‘রাজূ দীপ্তৌ’ এই ধাতু থেকে ‘ক্রিপ্’ প্রত্যয় প্রয়োগ করলে ‘বিরাট’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘যো বিবিধং নাম চরা’চরং জগদ্ রাজয়তি প্রকাশয়তি স বিরাট্’—অর্থাৎ যে নানাবিধ চরাচর জগতকে প্রকাশ করে, সেই কারণে ‘বিরাট’ নামের দ্বারা পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয়।
কারণ আত্মা (পরমাত্মা) সৃষ্টির উপাদানকারণ নন, তিনি নিমিত্তকারণ; যার দ্বারা পূর্ব থেকেই কারণাবস্থায় বিদ্যমান প্রকৃতিতত্ত্ব থেকে জগৎ সম্ভূত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়। এইরূপই সদৃশ বর্ণনা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬/২/১–৪) পাওয়া যায়।
‘বিরাট’—বৈয়াকরণদের মতে দীপ্ত্যর্থক ধাতুগুলি আকর্ষক হয়, যেমন—
‘লজ্জাসত্তাস্থিতিজাগরণং, বৃদ্ধিক্ষয়জীবিতমরণম্ … রুচিদীপ্ত্যর্থান্ ধাতুগণানকর্মকমাহুঃ’।
অতএব এখানে ‘রাজতে’ শব্দটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ত্র দীপ্ত্যর্থক ‘কাশৃ’ ধাতু থেকে ণিজন্ত ‘প্রকাশয়তি’ অর্থে গ্রহণ করাও সহজেই যুক্তিযুক্ত হয়।
বিবিধ জগতকে প্রকাশ করার অর্থ অব্যক্তাবস্থা থেকে ব্যক্ত করা; অভাব থেকে ভাব উৎপন্ন করা নয়। এইভাবে ভগবানের মধ্যে জগত্কর্তৃত্ব আরোপিত হওয়ায় তিনি জগতের কর্তা প্রমাণিত হন।
‘বিশেষেণ রাজতে ইতি বিরাট্’—বিশেষরূপে প্রকাশিত হওয়ার কারণে ভগবানকে বিরাট বলা হয়। ভগবানের প্রকাশে বিশেষত্ব এই যে তিনি পরপ্রকাশ্য নন, স্বয়ংপ্রকাশ। এই নিরুক্তির মূল নিহিত আছে—
‘তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি’ (মুণ্ডক ২/২/১০) এই শ্রুতি-বচনে।
আচার্য সায়ণ ‘ততো বিরাডজায়ত’ মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে বিরাট পদের নিরুক্তি করেছেন—
‘বিবিধানি রাজন্তে বস্তুন্যত্র ইতি বিরাট্’। যেখানে নানাবিধ বস্তু (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগত) বিরাজমান, সেই ভগবান বিরাট।
শ্রুতির বচন—
পুরুষ এবেদꣳ সর্বং॒ য়দ্ভূ॒তং য়চ্চ॑ ভাব্য᳖ম্ (যজুঃ ৩১/২)। এখানে ‘এবেদং সর্বং’-এর অর্থ ‘পুরুষস্থ এবেদং সর্বং’, অর্থাৎ “এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত”—এইভাবে বোঝা উচিত।
‘যো ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তরবহিরব্যাপ্নোতি স বিরাট’ (রামোত্তরতাপনীয় উপনিষদ ৫)— অর্থাৎ যে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র ব্যাপ্ত, তিনিই বিরাট। ‘প্রজাপতির্বিরাট্ চৈব’ (চূলিকোপনিষদ ১৩)— প্রজাপতিই বিরাট। ‘বিরাড়্ বাক্ বিরাট্ পৃথিবী … স মে ভূতং ভব্যম্ বশে কৃণোতু’ (অথর্ব ৬/১০/২৪)।
এর আশয় এই যে, সমগ্র জগত্ ভগবানের শক্তির দ্বারা ব্যক্ত হয়ে তাঁর মধ্যেই বিরাজমান, এই কারণেই তিনি বিরাট নামে অভিহিত।
‘অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ’— ‘অগ্’, ‘অগি’, ‘ইণ্’ এই সব গত্যর্থক ধাতু, এদের থেকে ‘অগ্নি’ শব্দ সিদ্ধ হয়।
‘গতেস্ ত্রয়ো অর্থাঃ— জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। পূজনং নাম সত্কারঃ।’ ‘যোऽঞ্চতি’ অচ্যতে, অগতি, অঙ্গতি, এতি বা স অয়মগ্নিঃ— অর্থাৎ যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানবার, প্রাপ্ত হবার ও পূজার যোগ্য, সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম ‘অগ্নি’।
অগ্নির ‘গতি’ অর্থে গমন ও প্রাপ্তি অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানার্থ ততটা প্রসিদ্ধ নয়; এজন্য কিছু প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে—
(১) ‘সর্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ’ (স্কন্দস্বামী নিরুক্তটীকা ২/৭/১৬)।
(২) ‘গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাদ্ গমের্জ্ঞানার্থতা’ (ঋগ্ভাষ্যটীকা, জয়তীর্থ, পৃঃ ২)।
(৩) ‘গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ’ (ন্যায়সংগ্রহ, হৈমপরিভাষাপাঠ, পৃঃ ২০)।
নিরুক্তকার অগ্নি শব্দের বহু নিরুক্তি দিয়েছেন। প্রথম নিরুক্তি— ‘অগ্রণীর্ভবতি’ এবং দ্বিতীয় নিরুক্তি— ‘অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে’। যেহেতু যাস্ক প্রধানত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন, সেই কারণে তাঁর নিরুক্তিগুলিও তদ্রূপ। কিন্তু গ্রন্থকার ঋগ্ভাষ্যের নমুনা অংশে এবং ঋগ্বেদভাষ্য (১/১১১)-এ ‘অগ্রণীঃ’-এর অর্থ করেছেন ‘সর্বোত্তমঃ’ এবং ‘অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে’-এর অর্থ করেছেন— ‘সর্বেষু যজ্ঞেষু পূর্বমীশ্বরস্যৈব প্রতিপাদনাত্’।
আচার্য শঙ্করও ‘অগ্রণীর্ভবতি’-এর অর্থ তাঁর বেদান্তভাষ্যে এইভাবে করেছেন—
‘অগ্নিশব্দোऽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগাশ্রয়েণ পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি’ (১/২/২৮)।
পরমেশ্বর ‘অগ্রণীর্ভবতি’, কারণ যে কোনও কার্যেই সর্বপ্রথম তাঁরই স্মরণ ও স্তবন করা হয়।
‘তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যঃ’ (যজুঃ ৩২/৩১) মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে মহীধর লিখেছেন—
‘অগ্নিঃ তদেব কারণং ব্রহ্মৈব আদিত্যস্তদেব বায়ুস্তদেব চন্দ্রমাস্তদেব … উ এবার্থে। শুক্রং শুক্লং তৎ প্রসিদ্ধম্ … তাঃ প্রসিদ্ধা আপঃ জলানি স প্রসিদ্ধঃ প্রজাপতিরপি তদেব ব্রহ্মা’।
এখানে মহীধর স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে পরমাত্মার বাচক বলেছেন।
‘শ্রুতিসিদ্ধান্তসংগ্রহ’-এ অগ্নির একটি নতুন নিরুক্তি এইভাবে দেওয়া হয়েছে—
‘ন গচ্ছতি স্বতো ন প্রবর্ততে ইত্যগঃ, বিশ্বম্ অগং নয়তীতি অগ্নিঃ’—অর্থাৎ এই জড় জগতকে পরিচালনা করার কারণে ভগবানকে অগ্নি বলা হয়। এই পরিচালনা দুই প্রকার—এক, সর্গাদি কালে প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপন্ন করে জগৎরচনার মাধ্যমে; দুই, নির্মিত জগতের নিয়ন্ত্রণরূপে।
বৈয়াকরণেরা ‘অগি’ ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ করেন। উণাদি সূত্র—
‘অঙ্গের্নলোপশ্চ’ (৪৭/৫০)। তখন নিরুক্তি হবে— ‘অঙ্গতীতি অগ্নিঃ’। এই উণাদি সূত্রের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার লিখেছেন— ‘অঙ্গতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি জানাতি বা সোऽগ্নিঃ’।
বৈদিক বাঙ্ময়ে বহু স্থানে অগ্নির পরমেশ্বরবাচক হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—
‘অগ্নিরেব ব্রহ্ম’ (শত ১০/৪/৪/১৭৫)। ‘অগ্নিপরেশমাহুঃ’ (ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬-এ আত্মানন্দের ভাষ্য)।
‘ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ’ (কৌষীতকি ৬/১/১৫; শত ২/৩/৫/৪/৮ এবং তৈত্তিরীয় ৩/৬/১৬/১)।
পাহি নোऽগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ভানো যাবিষ্ঠ্য ।।
—ঋক্ ১/৩৬/১৫
এই মন্ত্রে অগ্নি নামক পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যেন তিনি ধূর্ত ও রাক্ষসদের থেকে রক্ষা করেন।
অগ্নির পরমেশ্বরবাচক হওয়ার সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র—
অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্যিজম্ ।
হোতারং রত্নধাতমম্ ।।— ঋক্ ১/১/১
বিশ্ ধাতু থেকে ‘বিশ্ব’ শব্দটি সিদ্ধ হয়।
‘বিশন্তি প্রবিষ্টানি ভবন্তি সর্বাণ্যকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্, যো বা আকাশাদিষু সর্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বরঃ’—যার মধ্যে আকাশাদি সমস্ত ভূত প্রবেশ করে, অথবা যিনি আকাশাদি সমস্ত ভূতে ব্যাপ্ত হয়ে প্রবিষ্ট রয়েছেন, সেই জন্য সেই পরমেশ্বরের নাম ‘বিশ্ব’। ইত্যাদি নামের গ্রহণ ‘অকারমাত্র’ থেকে হয়।
‘জ্যোতিবৈ হিরণ্যম্’; ‘তেজো বৈ হিরণ্যম্’—ইত্যৈতরেয়শতপথব্রাহ্মণে।
‘যো হিরণ্যানাং সূর্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ’—যার দ্বারা সূর্যাদি তেজস্বী লোকসমূহ উৎপন্ন হয়ে যার আধারে অবস্থান করে, অথবা যিনি সূর্যাদি তেজঃস্বভাব পদার্থসমূহের গর্ভ (উৎপত্তি) ও নিবাসস্থান—এই জন্য সেই পরমেশ্বরের নাম ‘হিরণ্যগর্ভ’। এতে যজুর্বেদের মন্ত্রের প্রমাণ আছে।
এই মন্ত্রে আগত বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ এই কথাই প্রমাণ করে যে এখানে ‘অগ্নি’ শব্দটি পরমাত্মার বাচক। ভৌতিক অগ্নি দ্বারা সুপথ–কুপথের ভেদ করা এবং তারপর প্রার্থনাকারীকে সুপথে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা বা আশা কীভাবে করা যায়?
(অগ্নি শব্দ ব্রহ্মের বাচক—এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে গ্রন্থকারের ঋগ্বেদভাষ্যের নমুনা অংশ এবং ঋগ্ভাষ্যের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন। গ্রন্থকারের সমকালীন পণ্ডিত মহেশচন্দ্রের এ বিষয়ক আপত্তির উত্তর গ্রন্থকার তাঁর ‘ভ্রান্তিনিবারণ’ গ্রন্থে দিয়েছেন।)
বিশ্ব—উণাদিসূত্র ১/১৫১-এর ব্যাখ্যায় এক নিরুক্তি করা হয়েছে—‘বিশতি সর্বত্র স বিশ্বঃ’। এই নিরুক্তি ভগবানের সর্বব্যাপকতার দৃষ্টিতে করা হয়েছে। ভগবান এই জগতে ওতপ্রোত—‘স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু’ (যজুঃ ৩২/৮)। বিষ্ণুসহস্রনামের শাঙ্করমতানুসারী ব্যাখ্যায় এই শব্দের দুটি নিরুক্তি এইরূপ পাওয়া যায়—
১) ‘বিশতীতি বিশ্বং ব্রহ্ম’—অর্থাৎ জগতে প্রবেশ করার ফলে তিনি ‘বিশ্ব’ নামে অভিহিত হন। এই নিরুক্তির মূল ‘তৎসৃষ্ট্যা তদেবানুপ্রাবিশৎ’ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১৬) এই উপনিষদবাক্যে নিহিত।
২) ‘সংহৃতৌ বিশন্তি সর্বাণি ভূতান্যস্মিন্নিতি বিশ্বং ব্রহ্ম’—প্রলয়কালে সমগ্র জগত তাতে লীন হয়; এই জন্য পরমাত্মাকে ‘বিশ্ব’ বলা হয়। এই নিরুক্তির মূল ‘যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি’—এই উপনিষদবাক্যে উপলব্ধ।
ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—
“গর্ভা যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাম্। অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ।” (ঋক্ ১/৭০/১২)
অর্থাৎ যিনি জলের গর্ভ = আধার, যিনি বনের আধার, যিনি স্থাবরের আধার, যিনি জঙ্গমের আধার—প্রজাদের ন্যায় দেহে বিদীর্ণ না হওয়া জীবাদির মধ্যে অবস্থানকারী এই ‘বিশ্ব’ = পরমাত্মা অবিনাশী ও স্বাধার। যিনি সমগ্র কার্যজগতে প্রবিষ্ট এবং সমগ্র কার্যজগত যাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট—এই দুই দিক থেকেই ‘বিশ্ব’ ব্রহ্ম।
টীকা
১) উত্তরবর্তী সংস্করণে ‘অকারমাত্রা, উকারমাত্রা’ পাঠ পাওয়া যায়। গ্রন্থকারও এই প্রकरणের শেষে ‘এক-এক মাত্রা থেকে’ এই নির্দেশ দিয়েছেন। ‘মাণ্ডুক্য উপনিষদ’-এও ‘মাত্রা’ শব্দেরই ব্যবহার আছে। অতএব ‘অকারমাত্র’ ইত্যাদিতে ‘মাত্রা’-এর পুংলিঙ্গ প্রয়োগই জানা উচিত।
২) শতপথ ব্রাহ্মণ ৬/৭/৭/১৩/২। ‘জ্যোতিবৈ শুক্রং হিরণ্যম্’। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/১২।
৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৮/১৭/৬/১।
৪) মূলপাঠ এটিই। উত্তরবর্তী সংস্করণে ‘ঐতরেয়েশতপথে চ ব্রাহ্মণে’ পাঠ করা হয়েছে। মূলপাঠে ‘ঐতরেয়ং চ শতপথং চ = ঐতরেয়শতপথম্, ঐতরেয়শতপথং চ তদ্ ব্রাহ্মণং চ ঐতরেয়শতপথব্রাহ্মণং তস্মিন্’—এইরূপ সমাস জানা উচিত।
৫) যজুর্বেদ ৪০/১৩/৪৪—‘হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রং ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত্। স দাধার পৃথিবীং দ্যামু তেমা কর্মণে দেবায়েন হুবিষা বিধেম।’ ইত্যাদি স্থলে ‘হিরণ্যগর্ভ’ দ্বারা পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয়।
হিরণ্যগর্ভ—গ্রন্থকার এই শব্দে বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ উভয় সমাসই মেনেছেন ‘হিরণ্যং তেজসো নাম, হিরণ্যানি সূর্যাদীনী তেজাংসি গর্ভে যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ’ এবং ‘হিরণ্যানাং সূর্যাদীনাং তেজসাং গর্ভঃ হিরণ্যগর্ভঃ’। (সা. প্র. প্র. সং.) নিঘণ্টুতে ‘হিরণ্য’ শব্দ ধনের পরিভাষায় লেখা আছে। দেবরাজ যজ্বা এর ব্যাখ্যা করতে লিখেছেন—‘অথবা দ্বিধাতুজং রূপং হিনোতেঃ রমতেশ্চ ধাতুদ্বয়াৎ সমুদিতাৎ কন্যন্ প্রত্যয়ো বাহুলকাদ্ রূপসিদ্ধিশ্চ, হিতং চ তদ্ আপদি দুর্ভিক্ষাদৌ রময়তি চ সর্বদা সর্বমিতি।’ অর্থাৎ হিতকর ও রমণীয় হওয়ায় ধনের নাম ‘হিরণ্য’। এই নিরুক্তি ভগবানে এইভাবে সংগত ‘হিতং চ রমণীয়ং চ হিরণ্যম্’; অর্থাৎ হিতকর ও রমণীয় পদার্থকে ‘হিরণ্য’ বলা হয়, এবং হিরণ্যের গর্ভ বা নিবাসস্থান হওয়ায় ভগবান ‘হিরণ্যগর্ভ’। শ্বেতাশ্বতর-এর ভাষ্যকার নিরুক্তিকে সামনে রেখে ‘হিরণ্যগর্ভ’-এর এক সুন্দর নিরুক্তি করেন ‘হিতং রমণীয়মত্যুজ্জ্বলং জ্ঞানং গর্ভে অন্তঃসারো যস্য’ অর্থাৎ রমণীয় ও উজ্জ্বল জ্ঞান যাঁর অন্তঃসারে বিদ্যমান, তিনি ভগবান ‘হিরণ্যগর্ভ’।
সুবোধিনীকার বলেন—‘হর্ষতে স্বপ্রভয়া দীপ্যতে ইতি হিরণ্যম্’—অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ পিণ্ডকে ‘হিরণ্য’ বলা হয়; ‘এতাদৃশানাং হিরণ্যানাং গর্ভ উপাদাতা হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ’—এই তেজস্বী পদার্থসমূহের উপাদাতা হওয়ায় ভগবানের নাম ‘হিরণ্যগর্ভ’।
মৈত্র্যুপনিষদ ৬/১৮-এ লেখা আছে— ‘এবং হি খল্য আত্মেশানঃ শম্ভুর্ভবো রুদ্রঃ প্রজাপতির্বিশ্বসৃগ্ঘিরণ্যগর্ভঃ’। এখানে আত্মা, ঈশান, শম্ভু, ভব, রুদ্র, প্রজাপতি, বিশ্বসৃক ও হিরণ্যগর্ভ—এগুলো পরমাত্মার নাম। শতপথ ব্রাহ্মণ ৬/২/২/২৭৫-এ বলা হয়েছে— ‘প্রজাপতিবৈ হিরণ্যগর্ভঃ’। গ্রন্থকার উদ্ধৃত মন্ত্রটি ঋগ্বেদ ১০/১২১ (হিরণ্যগর্ভসূক্ত)-এর প্রথম মন্ত্র। এটির ভাষ্য করতে সায়ণাচার্য লিখেছে— ‘প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ’। এবং তৎপরি তৈত্তিরীয় সংহিতা— ‘প্রজাপতিবৈ হিরণ্যগর্ভঃ …’ (তৈ. সং. ৫/৫/১/২)।
মন্ত্রস্থিত ‘হিরণ্যগর্ভ’ শব্দটি অত্যন্ত সারগর্ভিত। এটি ঈশ্বর ও প্রকৃতির জন্য প্রযোজ্য এক যৌগিক পদ, যার সরল অর্থ—হিরণ্যকে নিজের গর্ভে ধারণকারী। এখানে ‘হিরণ্য’ প্রকৃতির উপলক্ষণ। প্রলয়াবস্থায় প্রকৃতি পরমাত্মার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ব্যবহারগতভাবে না থাকায় সৃষ্টির উৎপত্তির পূর্বে এই প্রকৃতি অব্যক্তাবস্থায় অদৃশ্য থাকে। সর্গের পূর্বে প্রলয়কালে পরমাত্মা একা নন, প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে সংহত করে রাখেন—‘আনীতবাতং স্বধ্যা তদেকম্’ (নাসদীয়সূক্ত)। যদি সেই কালে প্রকৃতির অভাব হতো, তবে সর্গকালে তা কোথা থেকে আসত—‘কথমসতঃ সজ্জায়েত’ (ছান্দোগ্য)। সেই হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বরই সর্গকালে পৃথিবী–দ্যৌ প্রভৃতিকে ধারণ করে রেখেছেন। এই কারণেই অন্যত্র বলা হয়েছে—‘যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিত যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ’ (যজুঃ ৩২/১৬)।
নিউটনের আগমনের পূর্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রধান প্রশ্ন ছিল যে, কোনো মাধ্যম ছাড়া সূর্য কীভাবে গ্রহ প্রভৃতিকে আকর্ষণ করতে পারে। নিউটনের সমকালীন প্রধান দার্শনিক জন লক (John Locke)-এর ধারণা ছিল—একটি পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে সংঘর্ষে না এলে তাতে গতি সৃষ্টি করতে পারে না এবং সংস্পর্শে না এলে তাকে প্রভাবিতও করতে পারে না। কিন্তু নিউটন যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা দেখিয়ে দেন যে নিরাকার হয়েও বিভিন্ন তরঙ্গ চলমান হয়ে অন্য পদার্থকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।
‘বা গতিগন্ধনয়োঃ’—এই ধাতু থেকে ‘বায়ু’ শব্দটি সিদ্ধ হয়।
‘গন্ধনং হিংসনম্’। ‘যো বাতি চরাচরং জগদ্ধরতি [জীবয়তি] প্রলয়তি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ’—যিনি চরাচর জগতের ধারণ, জীবন ও প্রলয় করেন এবং সকল বলবানদের মধ্যেও সর্বাধিক বলবান, সেই কারণে সেই ঈশ্বরের নাম ‘বায়ু’।
এখানে এই তথ্যটিও সামনে এসেছে যে, বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গগুলি নির্বাতে, একেবারে শূন্য আকাশেও মহাবেগে চলতে চলতে দূরবর্তী পদার্থকে প্রভাবিত করে। সূর্য কর্তৃক অন্যান্য লোককে আকর্ষণ করার এটিই ভিত্তি। অথর্ববেদের একটি সূক্তে (১০/৭৭) বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—এই সমগ্র বিশ্ব যে খম্ভের উপর স্থিত, সেই খম্ভটি বলো—‘স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ’। এর উত্তরে বলা হয়েছে—তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। শেষ পর্যন্ত লককে স্বীকার করতে হয়েছিল যে—‘আমাদের বোধগম্যের বাইরে যা কিছু আছে, তা পরমাত্মার শক্তির বাইরে নয়।’ এই ‘সঃ (পরমেশ্বর) দাধার’—এই বৈদিক সিদ্ধানেরই বিজয় ছিল।
বায়ু—‘বী’ ধাতুর দুই অর্থ—ব্যাপ্তি ও প্রজনন—‘বী গতিব্যাপ্তিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষু’ (ধাতুপাঠ)। তখন নিরুক্তির রূপ হবে—‘বেতি ব্যাপ্নোতি প্রজনয়তি বা সর্ব জগত্ স বায়ুঃ’। সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হওয়া এবং সমগ্র জগতকে উৎপন্ন করার কারণে ভগবান ‘বায়ু’ নামে অভিহিত।
‘কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূন্য উণ্’—এই উণাদিসূত্র (১৩১)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বায়ুর নিরুক্তি হবে—‘বাতি গচ্ছতি জানাতি বেতি বায়ুঃ’। এখানে ‘গচ্ছতি’ সাধারণ বায়ুর দৃষ্টিতে, আর ‘জানাতি’ ভগবানের দৃষ্টিতে।
এখানে একটি সংশয় হতে পারে—হিংসার্থক ধাতু থেকে ‘ধারণ’ অর্থ কীভাবে হয়? আরেকটি সংশয় হতে পারে—‘বলিনাং বলিষ্ঠঃ’ এর সঙ্গে নিরুক্তির সম্পর্ক কী?
প্রথম সংশয়ের সমাধান এই যে, যদিও ধাতুর সম্পর্ক প্রলয়ের সঙ্গেই, তথাপি উৎপত্তি ছাড়া প্রলয়ের কল্পনা করা যায় না; অতএব অবিনাভাব-সম্পর্কের কারণে উৎপত্তির গ্রাহ্যতা আপনাতেই হয়ে যায়। এই দৃষ্টিতেই গ্রন্থকার উপলক্ষণপরকতায় উৎপত্তি ও স্থিতির উল্লেখও করে দিয়েছেন।
নিরুক্তকারের মতে দেবতা মাত্র তিনজন—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য—
‘তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ; অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ, বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্যো দ্যুস্থানঃ’ (নিরুক্ত ৭/৫)।
পরে আবার বলা হয়েছে—‘যা কা চ বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈব তৎ’ (নিরুক্ত ৭/১০)। এখানে ব্যাখ্যাকারগণ বহু তর্ক উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে বায়ু ও ইন্দ্র—এই দুই নাম একই দেবতার। এইভাবে সমগ্র বলসম্পর্কিত কার্য বায়ুরই; অতএব গ্রন্থকার কর্তৃক বায়ুর প্রসঙ্গে ‘বলিনাং বলিষ্ঠঃ’ বলা যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয়ে—বায়ুর ঈশ্বরবাচকত্বে নিম্নোক্ত মন্ত্র প্রমাণ—
‘স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুঃ।’—অথর্ব ১৩/৭/৪/৭/৩
‘তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুঃ।’—যজুঃ ৩২/৩১
**তৈজস—**নিঘণ্টুতে ‘তেজঃ’ শব্দকে কিরণের পরিভাষায় পাঠ করা হয়েছে। দেবরাজ যজ্বা একে ‘তিজ নিশানে’ এবং ‘তেজ পালনে’—এই দুই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলেছেন।
‘তিজ নিশানে’—এই ধাতু থেকে ‘তেজঃ’, এবং তাতে তদ্ধিত ‘অণ্’ প্রত্যয় করলে ‘তেজস’ শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং সূর্যাদি তেজস্বী লোকসমূহকে প্রকাশিত করেন, সেই কারণে সেই ঈশ্বরের নাম ‘তেজস’। ইত্যাদি নামার্থ উকারমাত্র থেকে গৃহীত হয়।
ঈশ্বর—‘ঈশ ঐশ্বর্যে’—এই ধাতু থেকে ‘ঈশ্বর’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘য ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্যবান্ বর্ততে স ঈশ্বরঃ’—যাঁর সত্য বিচারশীল জ্ঞান ও অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, সেই কারণে সেই পরমাত্মার নাম ‘ঈশ্বর’।
‘বা’—এই নিরুক্তি অনুসারে—‘তেজসি = নিশ্যতি তনুকরোতি বা অজ্ঞানং পাপ বেতি তেজঃ’, স্বার্থে ‘অণ্’—‘তেজসঃ’। এইভাবে এই শব্দটি পরমাত্মার বাচক সিদ্ধ হয়।
‘স্বপ্নস্থানস্তৈজসঃ’ (মাণ্ডুক্য ১০)।
এর উপর গৌড়পাদাচার্যের কারিকা—
‘বিশ্বো হি স্থূলভুগ্ নিত্যং তেজসঃ প্রবিবিক্তভুক্’—কারিকা ৩।
**ঈশ্বর—**উণাদিকারদের দৃষ্টিতে ‘ঈশ্বর’ শব্দের নিরুক্তি—‘আশুঃ করোতীতীশ্বরঃ’, ধাতু—‘অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ’। সেখানে সূত্র—‘অশ্নোতেরাশুকর্মণি বরট্’ (৫৫/৭)। এইভাবে ঈশ্বরে ব্যাপকত্ব ও আশুকর্তৃত্ব—উভয়ই আসে।
অথর্ববেদ (১১/৪/৪/১১) অনুসারে—‘যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরী যস্মিন্ সর্ব প্রতিষ্ঠিতম্’—যিনি সকলের ঈশ্বর এবং যাঁর মধ্যে সবকিছু প্রতিষ্ঠিত (তিনিই ঈশ্বর)।
যজুর্বেদে বলা হয়েছে—‘য ঈশে মহতো মহান্’—যিনি মহানদের মধ্যেও মহান-এর সর্বোচ্চ স্বামী (তিনি ঈশ্বর)।
গীতা (১৮/৬১)-এ বলা হয়েছে—‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃद्दেশেऽর্জুন তিষ্ঠতি’—হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন।
ন্যায়দর্শন অনুসারে ঈশ্বর ব্যতীত কর্মফলের ব্যবস্থা সম্ভব নয়—‘ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাত্’ (৪/১/১৬)।
মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যে গৌড়পাদাচার্য লিখেছেন—
‘প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাত্ সর্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্বব্যাপিনমোংকারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥’—কারিকা ২৮।
এখানে সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান প্রণবকে ঈশ্বরের পরিভাষা বলা হয়েছে।
ঋক্-পরিশিষ্ট (২৩/৭/১৮)-এ লেখা আছে—
‘যোऽসৌ সর্বেষু বেদেষু পথ্যতেऽনব ঈশ্বরঃ।
অকার্যো নির্বর্ণো হ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥’
লোক ও লোকান্তরের ঈশনকর্তা = রচয়িতা হওয়ায় বেদ যাঁদের প্রাণদাতা ঈশ্বর বলে (স উ প্রাণস্য প্রাণঃ—কেন ২), যিনি সর্বব্যাপক, নিত্য (অকার্য) ও অবিকারী (অব্রণ)—তিনি ভগবান আমার মনকে শুভ সংকল্পে পূর্ণ করুন।
বিষ্ণুসহস্রনামের শাঙ্কর-সম্প্রদায়ানুসারী ভাষ্যে বলা হয়েছে— ‘নিরুপাধিকমৈশ্বর্যমস্যেতীশ্বরঃ’—যাঁর ঐশ্বর্য নিরুপাধিক, তিনিই ঈশ্বর।
অদ্বৈতমতানুসারে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—এই নামে অভিহিত দুটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ব্রহ্ম সর্বথা নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় সত্তা; অপরদিকে ঈশ্বরে কর্তৃত্ব থাকায় তিনি সৃষ্টির কার্যব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত। শাঙ্করমতে ব্রহ্মের দুই রূপ—একটি পরব্রহ্ম, যা সর্বথা নির্গুণ; অপরটি অপরব্রহ্ম, যা মায়ার উপাধির কারণে গঠিত। পরব্রহ্ম কেবল সত্তামাত্র এবং নির্বিকল্প সমাধির বিষয়। মায়ার উপাধিতে গঠিত অপরব্রহ্ম ‘ঈশ্বর’ নামে অভিহিত, যিনি সবিকল্প সমাধির বিষয়। পরব্রহ্ম সৃষ্টির উৎপত্ত্যাদি জটিলতায় প্রবেশ করেন না।
টীকা
১) ধাতু ২/৪৩।
২) দ্রষ্টব্য—‘বস্ত গন্ধ অর্দনে’ (ধাতু ১০/১৫২), ‘অর্দ হিংসায়াম্’ (ধাতু ১০/২৫৫)। ‘গন্ধনং মর্দনম্’—ইতি ক্ষীরতরঙ্গিণ্যাং ক্বাচিত্কঃ পাঠঃ (২/৪৩, পৃষ্ঠা ১৭৮, রামলাল কপুর ট্রাস্ট সংস্করণ)।
৩) ধাতু ২/১০।
‘দো অবখণ্ডনে’—এই ধাতু থেকে [নঞ্ অব্যয় উপপদ হওয়ায়] ‘অদিতি’ এবং তাতে তদ্ধিত প্রত্যয় করলে ‘আদিত্য’ শব্দ সিদ্ধ হয়।
‘ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোऽয়মদিতিঃ, অদিতিরেব আদিত্যঃ’—যাঁর কখনো বিনাশ নেই, সেই ঈশ্বরেরই ‘আদিত্য’ সংজ্ঞা।
‘জ্ঞা অববোধনে’—এই ধাতুতে ‘প্র’ উপসর্গ যুক্ত হলে ‘প্রজ্ঞ’ এবং তাতে তদ্ধিত প্রত্যয় করলে ‘প্রাজ্ঞ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। মায়ার উপাধিতে অভিভূত ব্রহ্মের নীচু রূপই ঈশ্বর। তিনিই জগতের নিমিত্ত–উপাদান কারণ। মায়ারূপী নিজের শক্তি (প্রকৃতি)-র সহায়তায় তিনি লোকসমূহের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন—
‘ব্রহ্মৈব স্বশক্তিপ্রকৃত্যভিধেয়মাশ্রিত্য লোকান্ সৃষ্ট্যা নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ’।
বাস্তবতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—একই সত্তার দুই নাম।
বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্তদর্শন) ব্রহ্মের এই ভেদ কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভ—‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’। এইভাবে এর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। দ্বিতীয় সূত্রে—‘জন্মাদ্যস্য যতো’—সেই একই ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। উভয় সূত্র একত্রে পাঠ করলে স্পষ্ট হয় যে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মই সেই সত্তা, যাঁর থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি–স্থিতি–প্রলয় ঘটে। শাঙ্করমত অনুসারে এই লক্ষণ অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা হয়; কিন্তু সূত্রে এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই যে অপর ব্রহ্ম বা মায়ার উপাধিতে গঠিত ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই সৃষ্ট্যাদির কারণ। যদি দুর্জনতোষন্যায়ে একে মায়ার উপাধিতে অধ্যস্ত ব্রহ্ম বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে বাদরায়ণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে অধ্যস্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরই উপস্থাপন করেছেন—এই দোষে দুষ্ট হবেন। এটি জলতৃষ্ণার্তকে মরীচিকার দিকে পাঠানোর মতো। আবার যেমন ঝিনুকে অধ্যস্ত রৌপ্য দিয়ে অলঙ্কার হয় না এবং দড়িতে অধ্যস্ত সাপের সন্তান জন্মায় না, তেমনি অতাত্ত্বিক = অধ্যস্ত ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি ইত্যাদি সম্ভব নয়।
বাস্তবতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ নেই। এক হয়েও পরমাত্মাকে নানা নামে অভিহিত করা হয়।
(In the eyes of the Hindus, there is but one Supreme God. This was stated long ago in the Rigveda in the following words—‘Ekam sadvipra bahudha vadanti’ which may be translated as—‘The sages name the One Being variously’—An Englishman defends Mother India by Ernest Wood, P.128.)
বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত বচন দ্বারা স্পষ্ট যে পরমাত্মাকে ঈশ্বর বলা হয় এই কারণে যে তাঁর ঐশ্বর্য নিরুপাধিক, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন—এই জন্য নয় যে তিনি উপাধিগ্রস্ত।
আদিত্য— ‘দো অবখণ্ডনে’—এই ধাতু থেকে ‘দিতি’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘অবখণ্ডনং নাম বিনাশঃ’; তাতে ক্তিন্ প্রত্যয় করলে ‘দিতি’ শব্দ হয়। ‘দিতি’ কার নাম?—যার নাশ হয়। তাতে যখন নঞ্—
টীকা
১) ধাতু ৪/৭৩/৬।
২) ‘অদিতি’ শব্দের সিদ্ধির জন্য বন্ধনীর অন্তর্গত পাঠ আবশ্যক। তুলনা কর—‘শনৈশ্চর’ নামের ব্যাখ্যা। ‘চর গতিভক্ষণয়োঃ’—এই ধাতু থেকে ‘শনৈস্’ অব্যয় উপপদ হওয়ায় …।
৩) ‘অদিত’ শব্দ থেকে অষ্টাধ্যায়ী ৪/১/৯৮৫ সূত্রানুসারে প্রাগ্দীव्यতীয় অর্থে ‘ণ্য’ প্রত্যয় হয়ে ‘আদিত্য’ শব্দ সিদ্ধ হয়। গ্রন্থকার স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় গ্রহণ করেছেন। অতএব এখানে ‘চাতুর্বর্ণ্যাদীনাং স্বার্থ উপসংখ্যানম্’ (মহাভাষ্য ৫/১/১২৪) বার্ত্তিক অনুসারে স্বার্থে ‘ব্যঞ্’ প্রত্যয় বোঝা উচিত। ‘চাতুর্বর্ণ্য’ প্রভৃতি আকৃতিগণভুক্ত।
৪) ধাতু ১/৪/০।
৫) অষ্টাধ্যায়ী ৫/৪/৩৮/৫ সূত্রে স্বার্থে ‘অণ্’।
সমাস হলে তখন অদিতি শব্দ সিদ্ধ হয়। অদিতি—যার কখনো নাশ হয় না। যে আদিতি, সেই-ই আদিত্য।
— সত্যার্থপ্রকাশ, প্রথম সংস্করণ
এখানে এই শঙ্কা হয় যে ‘দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্যঃ’ (৪৭১৯৮৫) সূত্র অনুযায়ী অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় হয়—এমনটাই পাণিনির মত; তবে স্বার্থে ণ্য প্রত্যয় কীভাবে হতে পারে? কিন্তু পাণিনি ‘দিত্যদিত্যাদিত্য’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ণ্য প্রত্যয় কেবল অপত্যার্থেই বিধান করেননি, বরং ‘প্রাগ্দীভ্যতীয়ার্থ’-এও করেছেন। ‘তস্যেদম্’ অর্থই প্রাগ্দীভ্যতীয়। শব্দের স্বার্থও ‘তস্য-ইদম্’—তার সম্পর্কীয়। অতএব এখানে ‘তস্যেদম্’ (৪৭৩৭১২০) সূত্র থেকে স্বার্থে ণ্য হতে পারে। সূত্রকার এই একই সূত্র থেকেই আদিত্য শব্দেও তো ণ্য প্রত্যয়ের বিধান করেছেন। এই আদিত্য পদ অপত্যার্থক প্রত্যয় ছাড়াই তো গঠিত। অপত্যার্থক প্রত্যয় অপত্য অর্থের অতিরিক্ত অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়—এমনটাই প্রাচীন আচার্যগণ মেনে এসেছেন। পূর্বমীমাংসার বেদাপৌরুষেয়াধিকরণে ‘ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত’ এই বাক্যে প্রাবাহণি কোনো প্রবাহণ-এর পুত্র ব্যক্তিবিশেষ নয়—এ কথা প্রতিপাদন করতে গিয়ে পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার শবরস্বামী লেখেন—
‘ইকারস্তু যথৈবাপত্যে সিদ্ধঃ তথা ক্রিয়ায়ামপি কর্তরী, তস্মাদ্ যঃ প্রবাহয়তি, স প্রবাহণিঃ’ (পূর্বমীমাংসা ১৭১৯৮৩৩০)।
অর্থাৎ অপত্যার্থক ইজ্ প্রত্যয় কর্তা অর্থেও হয়। সেইরূপেই এখানে উক্ত্যর্থক ণ্য প্রত্যয় স্বার্থে হয়েছে; কিন্তু এই ইনের দ্বারা উপসর্গ ও ধাতু—উভয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি হতে পারে না।
উপনিষৎকারেরা এর নির্বচন ভিন্নভাবে করেন—
‘যস্মাৎ সর্বমাদত্তে তস্মাদাদিত্যঃ’—সবকিছুর আদান করার জন্য ভগবানকে আদিত্য বলা হয়।
(তুলনা করুন—‘যস্মাৎ সর্বমাপ্নোতি সর্বমাদতে সর্বমতি চ ...’ শাণ্ডিল্য উপনিষদ্ ৩/২৭১)।
এখানে প্রথমে ‘আদানাত্ অদিতিঃ তস্য ভাবঃ আদিত্যঃ’—এই স্বরূপ বোঝা উচিত। বৃহদারণ্যকে আড়্-সহ দদ্ এবং ইণ্ ধাতু থেকে আদিত্য গঠন করা হয়েছে। সেখানে নির্বচন—
‘তে যদিদং সর্বমাদদানাযন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি’ (বৃহদ্ ৩৭৬৭৫)।
বিষ্ণুসহস্রনামের শাঙ্করসম্প্রদায়ানুসারী ভাষ্যে আদিত্য পদের এই নির্বচনগুলি পাওয়া যায়—
(ক) ‘অদিতায়া অখণ্ডিতায়াঃ পতিঃ’
(খ) ‘আদিত্যাৎ সাধর্ম্যদ্ আদিত্যঃ’।
আশয় এই যে—ভগবান তাঁর অখণ্ডতা, অবিনাশিনী শক্তির স্বামী; তাই তাঁকে আদিত্য বলা হয়। অথবা আদিত্য সকলের প্রকাশক; সেই সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করার জন্য ভগবান আদিত্য নামে অভিহিত হন।
আদিত্য-এর পরমাত্মবাচক হওয়ার কয়েকটি প্রমাণ—
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ । —যজুঃ ৩২/৩১
সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে
আদিত্যং বিষ্ণু সূর্য ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ —সাম ১/২/১০/১
অসৌ বা আদিত્યો ব্রহ্ম । —শত ৭/১৪॥১॥১৪
আদিত्यो বৈ ব্রহ্ম । —জৈ ৩/৪/৪/৭৬
হন্তেতি চন্দ্রমা ওমিত্যাদিত্যঃ । —জৈ ৩/১/৬/৭২
ওমিত্যাদিত্যঃ । —জৈ ৩/১৩/১২
প্রাজ্ঞঃ—স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রজ্ঞ থেকে প্রাজ্ঞ শব্দ গঠিত হয়। প্রাজ্ঞ শব্দের নিম্নলিখিত নির্বচনও হয়—
‘প্রজ্ঞা অস্যাস্তীতি প্রাজ্ঞঃ’—এই নির্বচনটি বৈয়াকরণদের। অর্থাৎ—‘যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরস্য জগতঃ ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ; প্রজ্ঞ এভং প্রাজ্ঞঃ’—যিনি নির্ভ্রান্ত জ্ঞানযুক্ত হয়ে সমস্ত চরাচর জগতের ব্যবহার যথাযথ জানেন, সেই ঈশ্বরের নাম প্রাজ্ঞ। ইত্যাদি নামার্থ মাত্রা থেকে গৃহীত হয়। যেমন এক-এক মাত্রা থেকে তিন-তিন অর্থ এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনি অন্যান্য নামার্থও ওংকার থেকে জানা যায়।
[মন্ত্রগত ‘মিত্র’ প্রভৃতি নামের ব্যাখ্যা]
যে ‘শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ’ এই মন্ত্রে মিত্র প্রভৃতি নাম রয়েছে, সেগুলিও পরমেশ্বরেরই নাম; কারণ স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা শ্রেষ্ঠেরই করা হয়। ‘শ্রেষ্ঠ’ সেই-ই—যিনি গুণ, কর্ম, স্বভাব ও সত্য-সত্য ব্যবহারে সর্বাধিক। সেই সকল শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁকেই ‘পরমেশ্বর’ বলা হয়। যার তুল্য কেউ ছিল না, নেই এবং হবে না। তুল্যই যদি না থাকে, তবে তাঁর চেয়ে অধিক কীভাবে হতে পারে? যেমন পরমেশ্বরের সত্য, ন্যায়, দয়া, সর্বসামর্থ্য ও সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অনন্ত গুণ আছে—অন্য কোনো জড় পদার্থ বা জীবের তেমন নেই। যে পদার্থ সত্য, তার গুণ, কর্ম ও স্বভাবও সত্য হয়।
শ্রেষ্ঠ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে—
ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ —৬/৮৮
অর্থাৎ তিনি (পরমাত্মা) না কারও কার্য, না তাঁর কোনো কারণ আছে। তাঁর সমান কেউ নেই, আর তাঁর চেয়ে বড়ও কেউ নেই। তাঁর মহাশক্তি নানা প্রকারে শ্রুত হয়—তাঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক।
বাস্তবতঃ চেতন সত্তা না কারও কার্য হয়, না কারও উপাদানকারণ হতে পারে। তিনি নিত্য। সংসারিক মিত্র প্রভৃতি নশ্বর; পারস্পরিক আপেক্ষিকতায় ছোট-বড়ও হয়। তাই উপাসনার প্রসঙ্গে ‘মহেশ্বর’ ও ‘পরমদেব’ (তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্—শ্বেত ৬/৭) একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় উপাসনার যোগ্য—তিনিই ‘ঈড্য’।
শন্নো মিত্র—
‘দেবো দেবানামসি মিত্রোऽদ্ভুতাঃ’ (ঋক্ ১/৭৬/৪/১৩)—অর্থাৎ আপনি দেবদের দেব এবং আশ্চর্য মিত্র। ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে— ‘ব্রহ্ম বৈ মিত্রঃ’ (শত ৪/১/৪/৭১); ‘ব্রহ্ম হি মিত্রঃ’ (শত ৫/৩/২/৪৪)।
মিত্রং পবিত্রং বনিতাং বিনীতাং সম্পত্তিমাপত্তিহরীমুর্কে ।
ত্যেজৎ স্বতঃ কো গুণবান্ সমর্থো বৈধোऽন্তরায়ো যদি নান্তরো স্যাত্ ॥
এই ও এ ধরনের বহু বাক্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে দেবতাবাচক, সূর্যার্থক মিত্র শব্দ পুংলিঙ্গ হয় এবং সখিবাচক শব্দ নপুংসকলিঙ্গ; কিন্তু বেদে বহু স্থানে মিত্র শব্দ সখিবাচক হয়েও পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরিউক্ত মন্ত্রে (ঋক্ ১/৭৬/৪/১৩) মিত্র শব্দ স্পষ্টতই সকলের সখা পরমাত্মার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে—সূর্যের জন্য নয়। এই শব্দ সখাবাচক—এ বিষয়ে এই মন্ত্রে সায়ণের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
অতএব মানুষের উচিত একমাত্র পরমেশ্বরেরই স্তব, প্রার্থনা ও উপাসনা করা; তাঁর থেকে ভিন্ন কারও কখনোই করা উচিত নয়। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব নামধারী পূর্বজ মহাশয় বিদ্বানগণ, দৈত্য–দানব প্রভৃতি নিকৃষ্ট মানুষ, এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ—সকলেই পরমেশ্বরেই বিশ্বাস রেখে কেবল তাঁরই স্তব, প্রার্থনা ও উপাসনা করেছেন, তাঁর থেকে ভিন্ন কারও নয়। তেমনই আমাদের সকলেরও করা উচিত। এর বিশেষ বিচার মুক্তি ও উপাসনা-বিষয়ে করা হবে।
[মিত্রাদি এখানে ঈশ্বরেরই বাচক]
প্রশ্ন— মিত্রাদি নাম থেকে সখা, এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহার দেখে সেগুলোকেই গ্রহণ করা উচিত।
উত্তর— এখানে সেগুলোর গ্রহণ করা যোগ্য নয়। কারণ যে মানুষ কারও বন্ধু, তাকেই অন্য কারও শত্রু এবং কারও প্রতি উদাসীনও দেখা যায়। তাই মুখ্যার্থে সখা প্রভৃতির গ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন পরমেশ্বর সমগ্র জগতের নির্দিষ্ট বন্ধু—তিনি কারও শত্রু নন, কারও প্রতি উদাসীনও নন—এই রকম আর কোনো জীব কখনোই হতে পারে না। অতএব এখানে কেবল পরমাত্মারই গ্রহণ হয়। তবে গৌণ অর্থে মিত্রাদি শব্দ দ্বারা সুহৃদ প্রভৃতি মানুষের গ্রহণ হয়।
‘ত্রিমিদা স্নেহনে’ এই ধাতু থেকে ঔণাদিক ‘ভত্র’ প্রত্যয় হলে ‘মিত্র’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ’—যিনি সকলের প্রতি স্নেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রীতির যোগ্য, সেই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম ‘মিত্র’।
‘বৃত্ বরণে; বর ঈপ্সায়াম্’ এই ধাতুসমূহ থেকে ঔণাদি ‘উনন্’ প্রত্যয় হলে ‘বরুণ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘যঃ সর্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ ধর্মাত্মনো বৃণোতি, অথবা যঃ শিষ্টৈঃ মুমুক্ষুভিঃ ধর্মাত্মভিঃ ত্রিয়তে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ’—যিনি আত্মযোগী বিদ্বান, মুক্তির ইচ্ছুক মুমুক্ষু ও ধর্মাত্মাদের গ্রহণ করেন, অথবা যিনি শিষ্ট মুমুক্ষু, মুক্ত ও ধর্মাত্মাদের দ্বারা গ্রহণীয় হন—তিনি ঈশ্বর ‘বরুণ’ নামে অভিহিত। অথবা ‘বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ’—পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই তাঁর নাম ‘বরুণ’।
‘হে অগ্নে দেবো দ্যোতমানস্ত্বং দেৱানাং সর্বেষামদ্ভুতো মহান্ মিত্রোऽসি প্রৌঢ়ঃ সখা ভয়সি।’
এইরূপে নিম্নলিখিত মন্ত্র এবং তার উপর সায়ণভাষ্যও গ্রন্থকারের মতের সমর্থক—
ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ ।
সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥
—ঋক্ ০ ১/৭/৫/১৪
এর উপর সায়ণভাষ্য—
“হে অগ্নে ত্বমুক্তপ্রকারেণাচিন্ত্যরূপোऽপ্যনুগ্রহীতৃতয়া সর্বেষাং জনানাং জামির্বন্ধুরসি, তথা প্রিয়ঃ প্রীণয়িতা ত্বং যজমানানাং মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়কোऽসি।”
‘মিত্রং বয়ং হবামহে’ (ঋক্ ১/৭/১৩/৪৪) — এই দুই মন্ত্রেই মিত্র শব্দ পুংলিঙ্গ হয়েও স্পষ্টতই সখাবাচক।
১. ধাতু ৪/১২৬।
২. ‘অমিচিমিদিশংসিভ্যঃ ক্ত্রঃ’ (উ ৪/১৬৫) থেকে। সূত্রের এই পাঠই প্রায়িক। উণাদিকোষ ৪/১৬৫-এ ‘অমিচিমিদিশংসিভ্যঃ ক্ত্রঃ’ পাঠ মেনে ‘মিত্র’ (স্বাদি) ধাতু থেকে ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে।
৩. বৃজ্-ধাতু ৫/৫৮; ‘বর’ ধাতু ১০/২৮০।
৪. ‘কৃবৃদারিভ্য উনন্’ (উ ৩/৭৫৩) বহুল-গ্রহণের ফলে ‘বর’ ধাতু থেকেও ‘উনন্’ জানা উচিত।
‘ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ’ এই ধাতু থেকে ‘যত্’ প্রত্যয় হলে ‘আর্য্য’ শব্দ সিদ্ধ হয়, এবং ‘অয়্য’ পূর্বক ‘মাডূ মানে’ এই ধাতু থেকে ‘কনিন্’ প্রত্যয় হলে ‘আর্য্যমা’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘যোऽর্য্যান্ স্বামিনো ন্যায়াধীশান্ মিমীতে মান্যান্ করোতি সোऽর্য্যমা’—যিনি সত্য-ন্যায় পালনকারী মানুষদের মান্য করেন এবং পাপ ও পুণ্যকর্মকারীদের পাপ-পুণ্যের ফল যথাযথ সত্য-সত্য নিয়মে প্রদান করেন—এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম ‘আর্য্যমা’।
বরুণ—
মেধাং মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ
মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাং ধাতা দদাতু মে স্বাহা ॥
—যজুঃ ৩২/১৫
এই মন্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বরুণ পরমাত্মা এবং অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি নামে অভিহিত পরমাত্মার নিকট মেধার প্রার্থনা করা হয়েছে। মৈত্র্যুপনিষদে বলা হয়েছে—
ত্বমগ্নির্বরুণো বায়ুস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং নিশাকরঃ । —৫/১
সন্ধ্যার অন্তর্গত ‘প্রাচী দিগগ্নিঃ’ প্রভৃতি মনসাপরিক্রমার মন্ত্রসমূহ ও তাদের ঋষিকৃত অর্থ দেখে এই ভ্রান্তি হতে পারে যে অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি শব্দ দিক্পালদের বাচক, পরমাত্মার নয়। কিন্তু মনসাপরিক্রমা মন্ত্রের অর্থের শুরুতেই গ্রন্থকার লিখেছেন—
‘সর্বাসু দিক্ষু ব্যাপকমীশ্বরং সন্ধ্যায়ামগ্ন্যাদিভিঃ নামভিঃ প্রার্থয়েত্’—অর্থাৎ সন্ধ্যায় অগ্ন্যাদি নাম দ্বারা সর্বদিকব্যাপী পরমেশ্বরের প্রার্থনা করতে হবে।
‘প্রতীচী দিগ্বরুণো ...’ মন্ত্রের অর্থ করতে গিয়ে তিনি লেখেন—‘বরুণঃ সর্বোত্তমোऽধিপতিঃ পরমেশ্বরঃ’ (পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি)।
আর্য্যমা— ভাষার দৃষ্টিতে নির্বচন হবে—‘ঋচ্ছতি মনুষ্যাণাং শুভাশুভানি কর্মাণি জানাতি অথ চ তেভ্যস্তেষাং ফলানি প্রাপয়তীত্যেতদর্য্যমা’। এই নির্বচনে শব্দটি ‘ঋ’ ধাতু থেকে ‘মনিন্’ প্রত্যয়ে নীপতনে সিদ্ধ হবে। ‘শ্বন্–উক্ষন্–পূষন্’ ইত্যাদি উণাদি সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থকার আরেকটি নির্বচন করেছেন—‘আর্য স্বামিনং মিমীতে মন্যতে জানাতীতি বা আর্য্যমা’। শুভাশুভ কর্মের জ্ঞানপূর্বক ফলপ্রদাতা হওয়ার জন্য, শুভাশুভ কর্ম জেনে ফলবণ্টনে নিয়ম করার জন্য, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ মানুষদের সম্মান করার জন্য ভগবানকে ‘আর্য্যমা’ বলা হয়।
বৈয়াকরণগণ ‘আর্য্যমা’-র নির্বচন করেন ‘ঋ গতৌ’ জুহোত্যাদিগণী ধাতু থেকে। তখন নির্বচন হবে—‘ইয়র্তীত্যার্য্যমা’। এই অবস্থায় সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকার জন্য ভগবান আর্য্যমা, কারণ গতি দ্বারা জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণকারেরা বলেন—‘আর্যমেতি তমাহুর্যো দদাতি’ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১/১/২/৪৪)। আশয় এই যে—যিনি দাতা, তিনিই আর্য্যমা। তখন নির্বচন হবে—‘আর গচ্ছতীত্যার্য্যমা’ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১/১/২/৪৪)। সর্বকর্মফলদাতা ঈশ্বরই—এ কথা সর্বতোভাবে সত্য।
অথর্ববেদে বলা হয়েছে—
‘সোऽর্য্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ সোহ্গ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এবং মহাযমঃ’ (১৩/৪/৫/৫) — তিনি আর্য্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনি মহাদেব, তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য এবং তিনিই মহাযম। সেখানে আরও বলা হয়েছে—
১. ধাতু ১/৬/৬/৭০।
২. ‘আর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ’ (অ ৩/১/৭/১০৩) সূত্রে স্বামী অর্থে যৎপ্রত্যয়ান্ত নীপতন করা হয়েছে।
৩. ধাতু ৩/৭/৬।
৪. ‘শ্বভুক্ষন্ … আর্যমন্ …’ (উ ১/৫/৬) সূত্রে কনিন্-প্রত্যয়ান্ত নীপতিত।
‘ইদি পরমেশ্বরয়ে’ এই ধাতু থেকে ‘রন্’ প্রত্যয় হলে ইন্দ্র শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘য ইন্দতি পরমৈশ্বর্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ’—যিনি অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত, সেই কারণে সেই পরমাত্মার নাম ইন্দ্র।
‘বৃহৎ’ শব্দপূর্বক ‘পা রক্ষণে’ এই ধাতু থেকে ‘ডতি’ প্রত্যয়, ‘বৃহৎ’-এর তকার লোপ এবং ‘সুডাগম’ হলে বৃহস্পতি শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘যো বৃহতামাকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ’—যিনি বড়দের থেকেও বড় এবং বৃহৎ আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের স্বামী, সেই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম বৃহস্পতি।
অর্থমণং যজামহে সুবন্ধু পতিবেদনম্ ।
উর্বারুকমিব বন্ধনাত্ প্রেতো মুঞ্চতু নামুতঃ ॥
—অথর্ব ১৪/১১/১৭
ইন্দ্র-সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতেঃ ।
ত্বামভি প্রনোনুমো জোতারমপরাজিতম্ ॥
—সাম ২/১/১৬
কৌষীতকি ব্রাহ্মণের বচন—‘তস্মাদাহেন্দ্রো ব্রহ্মেতি’ (৬/১৪)।
শঙ্করাচার্যও ইন্দ্র শব্দ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র নামক কোনো ব্যক্তিবিশেষকে গ্রহণ করেন না। বৃহদারণ্যক ২/৭/৫/১৬-এর ভাষ্যে তিনি লিখেছেন—‘ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ’।
বৃহস্পতি—গ্রন্থকার ‘বৃহৎ’ এবং ‘পতি’ এই দুই শব্দ মিলিয়ে বৃহস্পতি শব্দ গঠন করেছেন (দ্রষ্টব্য—‘তদ্ বৃহতোশ্চোরদেবতয়োঃ সুড্ তালোপশ্চ’—মহাভাষ্য ৬/১/১৫৭)। এই শব্দের নির্বচনসংক্রান্ত পাশ্চাত্য মতের নিরাকরণের জন্য শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসক-কৃত বৈদিকস্বরমীমাংসা গ্রন্থের অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য। এখানে বৃহস্পতি শব্দের তিনটি অর্থ করা হয়েছে—
১. বড়দের থেকেও বড়—নিরুক্তকার ‘বৃহৎ’ পদের অর্থ করতে গিয়ে লেখেন—‘বৃহদিতি মহতো নামধেয়ং পরিবৃঢ়ং ভবতি’ (নি ১/৭)। ‘পরিবৃঢ়’ শব্দের বিষয়ে পাণিনি বলেন—‘প্রভো পরিবৃঢ়ঃ’ (৭/২/২১), অর্থাৎ পরিবৃঢ়ের অর্থ প্রভু বা পতি। এইভাবে বৃহস্পতি-র অর্থ দাঁড়ায়—বড়দের থেকেও বড়।
২. আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী—জড় পদার্থসমূহের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্ প্রভৃতি মহান; ব্রহ্মাণ্ডও মহান। এই বৃহৎগুলির পালক ও রক্ষক ভগবান বৃহস্পতি—এই অর্থে তিনি আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।
৩. ব্রহ্মাদিদের স্বামী—চেতনদের মধ্যে ব্রহ্মা সর্বাপেক্ষা বড়, মহান ও পূজ্য; কারণ তিনি সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন চারটি বেদের প্রবক্তা মহাপুরুষ—‘যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ’ (শ্বেতা ৬/১৮)। যিনি সেই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করে বেদের জ্ঞান দান করেছেন, সেই ভগবান নিশ্চয়ই ব্রহ্মার থেকেও বড়। আশয় এই যে—জড় ও চেতন জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় ভগবানকে বৃহস্পতি বলা হয়।
‘পতি’ শব্দের অর্থ যোগক্ষেমকারকও হয়। সেই হিসাবে—‘বৃহতাং ব্রহ্মাণ্ডানাং পতিঃ যোগক্ষেমকরঃ বৃহস্পতিঃ’। ভগবানই সমগ্র চরাচরের পালক ও সংরক্ষক। ‘পতি’ শব্দ ‘পা পানে’ ধাতু থেকেও নিষ্পন্ন।
১. ধাতু ১/৭/৫/১।
২. ‘ঋজেন্দ্রাগ্র’ (উ ২/৭/২৬) সূত্রে রন্-প্রত্যয়ান্ত নিপাতিত।
৩. ধাতু ২/৪/৪/৬।
৪. পাতের্ডতিঃ (উ ৪/৩/৫/৮)।
৫. ‘তদ্ বৃহতোশ্চোরদেবতয়োঃ সুড্ তালোপশ্চ’ (গণ ৬/১/১৫১)—পারস্করাদিস্থ গণসূত্র।
‘বিশ্লৃ ব্যাপ্তৌ’ এই ধাতু থেকে ‘নু’ প্রত্যয় হলে বিষ্ণু শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘বেভেষ্ঠি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগত্ স বিষ্ণুঃ’—চর ও অচররূপ জগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়ায় পরমাত্মার নাম বিষ্ণু।
‘উরুর্মহান্ ক্রমঃ পরাক্রামী যস্য স উরুক্রমঃ’—অনন্ত পরাক্রমযুক্ত হওয়ায় পরমাত্মার নাম উরুক্রম।
আবার বৃহস্পতি-র আরেকটি নির্বচন—‘বৃহতঃ ব্রহ্মাণ্ডান্ লোকান্ পিবতি বিনাশকালে ইতি বৃহস্পতিঃ’; অর্থাৎ প্রলয়কালে বৃহৎ বৃহৎ লোকলোকান্তরকে নিজের মধ্যে লীন করেন—এই কারণে ভগবান বৃহস্পতি।
সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে
আদিত্যং বিষ্ণু সূর্য ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥
—সাম ৬/১
এই মন্ত্রে পরমাত্মার বহু নাম এসেছে; তাদের মধ্যে একটি বৃহস্পতি।
আরও কিছু প্রমাণ—‘স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু’ (ঋক্ ১/৯/৮/৬৬); ‘ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ’ (ঐত ১/১৩/১১/১৬; কৌশী ৬/১০; শত ৩/১/৭/১৪–১৫; জৈ ১/৩/৭/১৬); ‘ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ’ (গোপথ ৬/৭/৭)।
বিষ্ণু—
‘যস্মাদ্ বিষ্টমিদং সর্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাত্ ॥’
—বিষ্ণু ৩/১/৪৫
অর্থাৎ যিনি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, তিনিই বিষ্ণু। ব্যাপ্তি-অর্থবাচক ‘বিষ্ণু’ ধাতু থেকে নুক্ প্রত্যয় যোগে বিষ্ণু শব্দ হয়।
উরুক্রম—এই শব্দের আরেকটি নির্বচন—‘উরুঃ মহান্ ক্রমঃ ক্রান্তির্যস্য’; অর্থাৎ যার ক্রান্তি মহান। তিনি ‘ধাবতোऽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্’ (ঈশ ৪)—নিজে স্থির থেকেও দৌড়নেওয়ালাদের অতিক্রম করেন; কারণ তিনি ‘পূর্ববৎ’ সর্বব্যাপী হওয়ায় আগেই সর্বত্র বিদ্যমান—এইটাই তাঁর ক্রান্তি। নিম্নোক্ত স্থানে উরুক্রম শব্দ ভগবানের জন্য ব্যবহৃত—
সদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যান্ নরো যত্র দেবমবো ভবন্তি ।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্য উৎসঃ ॥
—ঋক্ ১/১৫/৪/৫
বাচস্পত্য কোষে ‘উরু’ শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে—‘উরবো ভূম্যাদিব্যাপকত্বাত্ ক্রমাঃ পাদবিক্ষেপো যস্য’।
মিত্রাদি শব্দগুলির ব্যাখ্যার পর গ্রন্থকার লিখেছেন—
‘ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব নামক পূর্বজ মহাশয় বিদ্বান্ ইত্যাদি।’
কিন্তু এর পূর্বে তিনি দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন যে বেদে ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, বরং যৌগিক অর্থে পরমেশ্বরেরই বাচক শব্দ আছে, যা তাঁর বিভিন্ন গুণ ও ধর্মের বোধ করায়। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধ মনে হলেও, গ্রন্থকারের বক্তব্য সঠিকভাবে না বোঝার কারণেই এই আপত্তি ওঠে। বাস্তবে তিনি কোথাও বলেননি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি নাম অন্য বস্তু বা মানুষের হতে পারে না। তাঁর বক্তব্য হলো—
(যে পরমাত্মা) উরুক্রম—মহাপরাক্রমযুক্ত; মিত্র—সকলের সুহৃদ, অবিরোধী; তিনি শম্—সুখকারক; তিনি বরুণ—সর্বোত্তম; তিনি শম্—সুখস্বরূপ; তিনি আর্য্যমা—ন্যায়াধীশ, সুখপ্রচারক; তিনি ইন্দ্র—সকল ঐশ্বর্যবান ও ঐশ্বর্যদাতা; তিনি বৃহস্পতি—সকলের অধিষ্ঠাতা ও বিদ্যাপ্রদ; এবং তিনি বিষ্ণু—সর্বব্যাপী পরমেশ্বর—সেই তিনি আমাদের শম্, কল্যাণকারী হোন।
‘বায়ো তে ব্রহ্মণে নমোऽস্তু’—‘বৃহ্ বৃদ্ধৌ’ এই ধাতু থেকে ‘ব্রহ্ম’ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। যিনি সকলের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, সর্বাপেক্ষা বড় ও অনন্তবলসম্পন্ন পরমাত্মা—সেই ব্রহ্ম-কে আমরা নমস্কার করি।
‘ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি’—আপনিই অন্তর্যামীরূপে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম।
‘ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদন্তি’—আপনাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা হয়, কারণ আপনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে সকলকে নিত্যই প্রাপ্ত।
‘ঋতং বদন্তি’—আপনার বেদস্থিত যথার্থ আজ্ঞাকেই আমি উপদেশ ও আচরণে গ্রহণ করব।
‘সত্যং বদন্তি’—সত্য বলব, সত্য মান্য করব এবং সত্যই পালন করব।
‘তন্মামবতু’—অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন।
‘তদ্বক্তারমবতু’—সত্যবক্তা আমাকে রক্ষা করুন, যেন আপনার আজ্ঞায় আমার বুদ্ধি স্থির থাকে এবং কখনো বিরুদ্ধ না হয়; কারণ আপনার আজ্ঞাই ধর্ম, আর তার বিরোধই অধর্ম।
“বিশেষণ নিয়ামক।”
‘বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে।’
বাচস্পতি, বরুণ, বৃহস্পতি, আদিত্য, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি নাম পরমেশ্বরেরও এবং লোকে বহু মানুষেরও; কিন্তু বেদে এই নামগুলি যৌগিক, আর লোকে রূঢ়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যক্তিবাচক নাম বেদ থেকে লোকে এসেছে, লোক থেকে বেদে নয়।
অতএব মিত্র প্রভৃতি শব্দে মুখ্যার্থে পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করা উচিত; গৌণার্থে সুহৃদ প্রভৃতি মানুষের গ্রহণ করা যায়। একইভাবে মাতা, পিতা, পতি প্রভৃতি শব্দে মুখ্যরূপে পরমেশ্বর এবং গৌণরূপে ঐ সম্পর্কযুক্ত মানুষদের গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। কারণ পূর্ণরূপে এই শব্দগুলির অর্থ কেবল পরমেশ্বরেই সম্পূর্ণভাবে ঘটে; অন্য বস্তুতে তো তার সামান্য অংশমাত্রই দেখা যায়।
যেমন—অগ্নির গুণ প্রকাশ; কিন্তু ভৌতিক অগ্নিতে অল্প প্রকাশ থাকে এবং তাও কিছু সময় পরে নষ্ট হয়ে যায়। এর বিপরীতে পরমেশ্বর নিত্য প্রকাশস্বরূপ। অন্য নামগুলির ক্ষেত্রেও এইভাবেই বুঝতে হবে। তাই অগ্নি প্রভৃতি নামেও মুখ্যার্থে পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করা উচিত।
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ ন্যায়দর্শনে এইভাবে বলা হয়েছে—
‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্’ (১/১/৪)।
এর অনুসারে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ব্যতীত—
১. বৈয়মু সংস্করণে ‘শম্’ পদ পূর্বপংক্তিতে ‘বিদ্যাপ্রদ’ শব্দের পূর্বে অন্য স্থানে পাঠিত।
২. ধাতু ১/৪/৮/৮।
৩. ‘বৃংহেণোচ্চ’ (উ ৪/১/৪৭) সূত্র থেকে ‘বৃহি (বৃহ)’ ধাতু দ্বারা গঠিত; ‘বৃহ’ পক্ষেতে বহুলগ্রহণে ‘অম্’ আগম গ্রহণীয়।
কোনো পদার্থের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত—এই বিষয়ে সকলেই একমত। অতএব গ্রন্থকার পরমেশ্বরের জন্য ‘ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি’ বলেছেন—এ কথা কোনোভাবেই উপপন্ন হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের এই উক্তি উপনিষৎকারের অনুকূল, এবং উপনিষৎকার সाक्षাৎকৃতধর্মা ঋষি। সুতরাং এই বচন অন্যথা হতে পারে না।
চক্ষু, শ্রোত্রাদি পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয়। এগুলির অতিরিক্ত একটি আন্তরেন্দ্রিয় ‘মন’। (‘একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্যম্’; ‘কর্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্’ (সাংখ্য ২।১৭, ১৬))—অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয় মন। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শ্রেণিতে মন-এর উল্লেখ তাদের ধর্মভেদের কারণে করা হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহ ভৌতিক; ভূতসমূহ থেকে যথাযথভাবে এদের উৎপত্তি হয়। এর বিপরীতে মন অভৌতিক পদার্থ, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত থেকে উৎপন্ন নয়। এর অতিরিক্ত, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নির্দিষ্ট বিষয়—রূপাদি—গ্রহণকারী না হয়ে মন রূপ, রস প্রভৃতি সকলকেই গ্রহণ করে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন-এর এই ভেদের কারণেই ইন্দ্রিয়বর্গে এর পাঠ করা হয় না; কিন্তু এটি একটি আন্তর ইন্দ্রিয় এবং এর দ্বারাই আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়ের (মানস) প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের সংযোগে ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি উৎপন্ন হয়। জলের প্রত্যক্ষে স্পর্শে শীতলতা, জিহ্বায় রস, চক্ষে রূপ ও তরলতা ইত্যাদি পৃথক-পৃথক অনুভূতি লাভ হয়। আলাদা আলাদা এই অনুভূতিগুলি কেবল শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সূচনামাত্র। মনের মধ্যে এই সকল সূচনার একত্র সমাবেশ হলে তাদের সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা বুদ্ধি ঐ অনুভূতিগুলিকে সমবেত রূপ দিয়ে কোনো একটি নাম দ্বারা অভিহিত করে। একেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে গুণের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু গুণ-গুণীর সমবায় সম্পর্ক থাকার ফলে গুণের সঙ্গে গুণীর প্রত্যক্ষও স্বীকৃত হয়।
যেমন ঘ্রাণ প্রভৃতির দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি গুণের প্রত্যক্ষ হওয়ায় গুণী পৃথিবীর প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই পরমাত্মার লিঙ্গসমূহ দেখে লিঙ্গী পরমাত্মার প্রত্যক্ষ হয়। জগতের রচনা দেখে তার রচয়িতার, নিয়মসমূহের উপপত্তি দেখে তার নিয়ামকের, কর্মফলব্যবস্থা দেখে তার ব্যবস্থাপকের—এই সকলের প্রত্যক্ষ হয়, যেমন বাগানের শোভা ও ব্যবস্থাপনা দেখে মালীর। শিল্পকর্মকে চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে করতে শিল্পীর মানস প্রত্যক্ষ হয়ে যায়।
এই ব্যবস্থার মূল ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে পাওয়া যায়—
অয়মস্মি জরিতঃ পশ্য মে হ বিশ্বা জাতান্যভ্যস্মি মহান। — ৮।৭৫।১৪
পরমেশ্বর বলেন—হে স্তোতাকর্তা! আমি তোমার সামনে প্রত্যক্ষ আছি। আমাকে এখানে এই জগতের রূপে দেখ। আমি আমার মহান সামর্থ্যে সকল পদার্থকে বশে রেখেছি।
উপনিষদ তাঁকে ‘আবিঃ সন্নিহিতং গুহারন্’ (মুণ্ডক ২/২/৭)—প্রকাশিত, নিকট এবং হৃদয়ে অবস্থিত বলেছেন। যজুর্বেদ (৪০।৭৫)-এ তাঁকে ‘তদ্দূরে তদ্বন্তিকে’—দূর ও নিকট—বলা হয়েছে। নিজের মধ্যেই নিকটস্থ হওয়ায় তাঁকে দেখা যায়—‘দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শীভিঃ’। সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী যোগীদের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ, চর্মচক্ষুতে দেখনেওয়ালাদের জন্য পরোক্ষ।
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বেদবিদ্যায় পারঙ্গত, পরম তপস্বী এবং যোগবিদ্যায় নিষ্ণাত যোগী ছিলেন। সাক্ষাৎকৃতধর্মা হওয়ার কারণেই তিনি গ্রন্থের আরম্ভে ঘোষণা করেন—‘ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি’, এবং নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাই গ্রন্থের শেষে ঘোষণা করেন—‘ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্’। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ বৈদিক বিদ্বান আচার্য নারদেব শাস্ত্রী বেদতীর্থ এবং মহর্ষির শিষ্য ও বেদভাষ্যে তাঁর সহকারী পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্মার মধ্যে হওয়া নিম্নলিখিত কথোপকথন দ্রষ্টব্য—
আচার্যজি পণ্ডিত জ্বালাদত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজি বেদভাষ্য কীভাবে করতেন? পণ্ডিতজি বললেন—
“প্রাতঃ নিত্যকর্ম সেরে আমরা সকল পণ্ডিত (৩ বা ৪ জন) নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতাম। ততক্ষণে স্বামীজি এসে বসতেন। এসেই বলতেন—চলো, বেদমন্ত্র পড়ো। আমাদের মধ্যে কেউ বেদমন্ত্র পড়ত (সাধারণত আমি-ই পড়তাম)। দুই-তিনবার বেদমন্ত্র পড়ার পর স্বামীজি আমাদের পদচ্ছেদ, অন্বয় লিখাতেন, তারপর জিজ্ঞাসা করতেন—নিরুক্ত কী বলে, পূর্বমন্ত্রে কী আছে, পরের মন্ত্র পড়ো ইত্যাদি। এসব শেষ হলে স্বামীজি পাশের ঘরে চলে যেতেন, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, এবং এক ঘণ্টা পরে স্বামীজি বেরিয়ে এসে সংস্কৃতে ভাষ্য লিখাতেন, ভাবার্থও লিখাতেন। তারপর আমাদের বলতেন—এর হিন্দি করে দাও। ভিতরের ঘরে স্বামীজি সমাধি করতেন। তাঁর সমাধির ফলই বেদভাষ্য। কোনো কোনো সময় স্বামীজি আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে আসতেন। স্বামীজির সমাধি ও তর্ক—ঋষি-ই সিদ্ধান্ত করতেন।”
এই কথার সমর্থন স্বামীজির প্রত্যক্ষদর্শী ইতিহাসপুরুষ শ্রী নথমল তিওয়ারীর ‘পरोপকারী’ পত্রিকার আগস্ট ১৮৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকেও পাওয়া যায়। ঋষি দयानন্দের কাছে পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ ছিলেন। পরমেশ্বর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি না বেদগুলির সত্যার্থ করতে পারত, না ‘ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি’ ঘোষণাসহ প্রতিজ্ঞা করতে পারত।
ঋত ও সত্য—বেদে বহু স্থানে ঋত ও সত্য একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাতপসোऽধ্যজায়ত’ (ঋগ্বেদ ১০/১৬০/১১) মন্ত্রেও এই দুই শব্দ একত্র এসেছে। এতে বোঝা যায়, দুইটি একই শ্রেণির হলেও সম্পূর্ণ একার্থবাচক নয়। ঋগ্বেদ ৬/১১/১৮-এ ঋত শব্দটি সত্যের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—‘ঋতবাকেন সত্যেন’। এতে স্পষ্ট যে সত্যের তুলনায় ঋত উচ্চতর। সত্য কেমন হওয়া উচিত? ঋতবাক্—অর্থাৎ সত্যের বাক্যে ঋত থাকতে হবে। এসব বিচার করে সিদ্ধান্ত এই যে, ঋত হল দৈবীয় নিয়ম এবং সত্য সামাজিক নিয়ম। ঋত অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরীয় বিধানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং সত্য সামাজিক বিধানের জন্য। ঈশ্বরীয় বিধান অবিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তনীয়; সামাজিক বিধান সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। তাই সামাজিক বিধান ঈশ্বরীয় বিধানের অনুকূল হওয়া উচিত।
গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থসমূহে বহুবার এই দুই শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে—
ঋতম্—যথার্থসর্ববিদ্যাঽধিকরণং বেদশাস্ত্রম্; ঋতস্য প্রাপ্তসত্যস্য; সর্ববিদ্যাযুক্তস্য বেদচতুষ্টয়স্য সনাতনস্য জগৎকারণস্য বা।
সত্যম্—যদ্ বেদবিদ্যয়া, প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ, বিদুষাং সঙ্গেন সুবিচারণাঽত্মশুদ্ধ্যা বা নির্শ্রমং, সর্বহিতং, তত্ত্বনিষ্ঠং, সত্যপ্রভবং সম্যক্ পরীক্ষ্য নিশ্চীয়তে তৎ।
যখন মানুষের মধ্যে বেদের জ্ঞান, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান এবং অনুভূত জ্ঞান একত্র হয়, তখন সে বলতে পারে—‘ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি’। সেই অনন্ত জ্ঞানময় সামর্থ্য থেকেই সকল বিদ্যার আদিমূল বেদের প্রকাশ হয়েছে এবং সেই শক্তি থেকেই ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃত জগতের আবির্ভাব হয়েছে। আমি অধ্যাত্ম ও ভৌতিক—উভয় ক্ষেত্রেই সত্যের পোষণ এবং অসত্যের খণ্ডন করব। সত্যার্থপ্রকাশে গ্রন্থকার এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন। এই কারণেই শেষে তিনি লিখেছেন—‘ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষম্’।
(অবতু মামবতু বক্তারম্) —এখানে দ্বিতীয়বার পাঠ অধিকার্থের জন্য। যেমন—‘কশ্চিত্ কশ্চিত্ প্রতি বদন্তি ত্বং গ্রাম গচ্ছ গচ্ছ’—এখানে দুইবার ক্রিয়ার উচ্চারণে ‘তুমি শীঘ্রই গ্রামে যাও’—এই অর্থ সিদ্ধ হয়। তেমনি এখানে—আপনি অবশ্যই আমার রক্ষা করুন; অর্থাৎ ধর্মে দৃঢ় প্রীতি ও অধর্মে ঘৃণা আমি সর্বদা করি—এই কৃপা আমার উপর করুন। আমি আপনার বড় উপকার মান্য করব।
[ত্রিবিধ তাপ-নিবারণ]
(ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ)—এখানে তিনবার শান্তিপাঠের উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ এই সংসারে তিন প্রকার দুঃখ আছে। এক ‘আধ্যাত্মিক’—যা আত্মা ও শরীরে অবিদ্যা, রাগ-দ্বেষ, মূর্খতা ও জ্বর-পীড়া প্রভৃতি থেকে হয়। দ্বিতীয় ‘আধিভৌতিক’—যা শত্রু, ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় ‘আধিদৈবিক’—অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অতিশীত, অতিউষ্ণতা, মন ও ইন্দ্রিয়ের অশান্তি থেকে হয়। এই তিন প্রকার ক্লেশ থেকে আপনি আমাদের দূরে রেখে কল্যাণকর কর্মে সদা প্রবৃত্ত রাখুন; কারণ আপনি-ই কল্যাণস্বরূপ, সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধার্মিক মুমুক্ষুদের কল্যাণদাতা। অতএব আপনি নিজ করুণায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হোন, যাতে সকল জীব ধর্ম আচরণ করে, অধর্ম ত্যাগ করে, পরমানন্দ লাভ করে এবং দুঃখ থেকে পৃথক থাকে।
সত্যের অনুশীলন অত্যন্ত দুষ্কর। ‘সত্যং ব্রূয়াত্ প্রিয়ং ব্রূয়াত্ ন ব্রূয়াত্ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।’ (মনু ৪।১৩৮); ‘অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ’ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব); ‘হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ’। এত বাধা থাকা সত্ত্বেও সত্যবাদী হওয়া ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারায় চলার সমান—‘ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া’ (কঠ ৩/১৪)। এই কঠিন পথে দयानন্দের মতো দৃঢ়ব্রতীরাই চলতে পারেন—‘দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি’ (কঠ ৩/১৪)। এই পথে চলতে গিয়ে গ্রন্থকারকে কত বিঘ্ন-বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা সর্ববিদিত। অচিন্ত্য ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তা সম্ভব হতো না। তাই গ্রন্থকার অত্যন্ত বিনীত ভাষায় ভগবানের রক্ষার প্রার্থনা করেছেন।
‘তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারম্’—এই উক্তিতে পুনরুক্তিদোষ আছে বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ‘প্রয়োজনশূন্যত্বে পদবাক্যয়োঃ পুনঃ পুনঃ কথনং পুনরুক্তিদোষঃ’—অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন শব্দ বা বাক্য বারবার বলা পুনরুক্তিদোষ। কিন্তু যেখানে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি উদ্দেশ্যসহ হয়, সেখানে তা পুনরুক্তি নয়, ‘অনুবাদ’। ‘অনুবাদোপপত্তেঃ’—ন্যায়দর্শনের (২।১।৩৬০) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বাত্স্যায়নভাষ্যে বলা হয়েছে—
‘অনর্থকোऽভ্যাসঃ পুনরুক্তম্, অর্থবানভ্যাসোऽনুবাদঃ শীঘ্রতরগমনোপদেশাত্।’
অর্থাৎ নিরর্থক পুনরুক্তি দোষজনক, কিন্তু অর্থপূর্ণ পুনরাবৃত্তি অনুবাদ। এখানে ‘মামবতু তদ্বক্তারমবতু’ দ্বিতীয়বার বলার উদ্দেশ্য বক্তার অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ করা।
সূর্য—‘সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ’ (যজুঃ ৭।৪২)—এটি লিঙ্গ। সূর্য শব্দের অর্থ পরমেশ্বর করলে নিরুক্তকার সূর্যের ব্যাখ্যায় লেখেন—
১. ‘অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে।’ (নিরুক্ত ১০।৪২)
২. এই পদগুলির ব্যাখ্যা দেখুন—সত্যার্থপ্রকাশ সমুল্লাস ৬এর শেষে
[অন্যান্য ঈশ্বর-নামগুলির ব্যাখ্যা]
‘সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ’। এই যজুর্বেদের বচন অনুসারে যে ‘জগৎ’ নামক প্রাণী—চেতন ও জঙ্গম, অর্থাৎ যারা চলে-ফিরে; এবং ‘তস্থুষঃ’ অর্থে অপ্রাণী, স্থাবর জড়, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি—এই সকলের আত্মা হওয়া, এবং স্বপ্রকাশরূপে সকলকে প্রকাশ করার কারণে পরমেশ্বরের নাম ‘সূর্য্য’।
‘অত্ সাতত্যগমনে’ এই ধাতু থেকে ‘আত্মা’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘যোऽততি ব্যাপ্নোতি স আত্মা’—যিনি সকল জীবাদি চরাচর জগতে নিরন্তর ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ‘পরশ্চাসাব্ আত্মা চ, যা আত্মভ্যো জীবেভ্যঃ সূক্ষ্মেভ্যঃ পরোऽতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা’—যিনি সকল জীবাদি থেকে উৎকৃষ্ট, এবং জীব, প্রকৃতি ও আকাশ থেকেও অতিসূক্ষ্ম, এবং সকল জীবের অন্তর্যামী আত্মা—এই কারণে ঈশ্বরের নাম ‘পরমাত্মা’।
সামর্থ্যবান-এর নাম ‘ঈশ্বর’। ‘য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ’—যিনি ঈশ্বরদের ঈশ্বর, অর্থাৎ সমর্থদের মধ্যে সর্বাধিক সমর্থ, যার তুল্য আর কেউ নেই—তাঁর নাম ‘পরমেশ্বর’।
‘সূর্যঃ সর্বের্বা সুবতের্বা স্বীর্যতের্বা’ (নিরুক্ত ১২।১৪)—নিরুক্তকারের এই বচনগুলি ভৌতিক সূর্যের দৃষ্টিতে বলা, কিন্তু নিম্নরূপে এই নির্বচনগুলি ভগবৎপরক হয়ে যায়—
(ক) ‘সরতি জানাতি ব্যাপ্নোতি বা সর্বং জগৎ স সূর্যঃ’—সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপক হওয়ার কারণে ভগবান সূর্য।
(খ) ‘সুবতি প্রেরয়তি চরাচরং স্বস্বকর্মসু ইতি সূর্যঃ’—সমগ্র জগতের প্রেরক হওয়ার কারণে ভগবান সূর্য। গীতায় বলা হয়েছে—‘অহং সর্বস্য প্রভবঃ মতঃ সর্বং প্রবর্ততে’ (গীতা ১০।৮)।
(গ) ‘সুষ্ঠু ঈর্যন্তে কম্প্যন্তে স্বীর্যন্তে উপতাপ্যন্তে বা দস্যবঃ অনেনেতি সূর্যঃ’—দুষ্টদের উপতাপন করার কারণে ভগবান সূর্য নামে অভিহিত।
নিঘণ্টু-ব্যাখ্যাকার যজ্বা মহাশয় সূর্য শব্দের ব্যাখ্যায় আরও দুটি নির্বচনের নির্দেশ করেছেন—
(ক) ‘সূর্যো মেধাবিনস্তান্ অর্হতীতি সূর্যঃ’।
(খ) ‘সূরিষু সাধুরিতি সূর্যঃ’।
এই দুই নির্বচনই পরমেশ্বরের অর্থে সঙ্গত। ভগবানকে মেধাবী পুরুষেরাই লাভ করতে পারেন, এবং মেধাবীদের প্রতি তিনি সাধুও বটে। সূরি-র লক্ষণ—
আত্মন্যেব গতির্যেষাং স্বস্মিন্ ব্রহ্মণি চাচলে
তে সূরা ইতি বিখ্যাতাঃ সূরয়শ্চাপি তে মতাঃ
অর্থাৎ সূর ও সূরি—উভয়ই একই অর্থবাচক। যারা অবিচলভাবে ভগবানের ধ্যান করে, ভগবানের প্রতি প্রেম রাখে, তারা ‘সূর’ বা ‘সূরি’ নামে অভিহিত।
নিঘণ্টুতে স্তৃ ধাতু পূজার্থকও পাঠ করা হয়েছে—‘স্বরতিরর্চতিকর্মা’ (নিঘণ্টু ৩।৭১)। ‘স্বীর্যতে অর্চ্যতে ভক্তৈরিতি সূর্যঃ’—অর্থাৎ ভক্তগণের দ্বারা পূজিত হওয়ার কারণে ভগবান সূর্য নামে পরিচিত।
বিশিষ্টাদ্বৈতমতানুসারী ভাষ্যে বলা হয়েছে—‘সরত্যস্মাদিতি সূর্যঃ’—কারণ তাঁর ভয়ে সমগ্র সংসার নিয়মিতভাবে চলতে থাকে; এই জন্য পরমাত্মার নাম সূর্য। এই নির্বচনের মূল উপনিষদে বিদ্যমান—
(ক) ‘ভীষাস্মাত্ পবতে বাতঃ ভীষোদেতি সূর্যঃ’ —তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ ৮
(খ) ‘তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি’ —কঠ ৫/১১
নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে সূর্য শব্দ ঈশ্বরবাচক—
উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতয়ঃ । দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ।।
—ঋক্ ১।৫০।১
অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান ভগবান সূর্যকে, চরাচর জগতের আত্মাকে, সকলের দেখানোর জন্য সকল পদার্থ চিহ্নস্বরূপ হয়ে উৎকৃষ্টভাবে ধারণ করছে।
‘সূর্যো বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা’ (শতপথ ১৩।৭।৩।৭।১৬)—সূর্য (পরমাত্মা) সকল পদার্থের জীবনাধার।
আত্মা—উণাদিকোষে ‘সাতিভ্যা মনিন্মনিণৌ’ (৪/১৫৩)-এর ব্যাখ্যায় ‘অততি নিরন্তরং কর্মফলানি প্রাপ্নোতি ব্যাপ্নোতি বা স আত্মা’—এই নির্বচন জীব ও ঈশ্বর উভয়ের দৃষ্টিতে করা হয়েছে। জীব কর্মফল প্রাপ্ত করার কারণে আত্মা, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপক হওয়ার কারণে আত্মা। গ্রন্থকার জীবকে পরিচ্ছিন্ন মনে করেন, বিভু নয়।
‘আত্মা অততের্বা আপ্নোতির্বা আপ্ত ইব স্যাদ্ যাবৎ ব্যাপ্তিভূতঃ’ (নিরুক্ত ৩।৭।১৫)। এই অবস্থায় নির্বচন হবে—
(ক) আপ্নোতি সর্বং ব্যাপ্নোতীতি আত্মা।
(খ) সর্বত্র আপ্ত ইব প্রাপ্ত ইবেত্য আত্মা।
দ্বিতীয় নির্বচনে ‘ইব’ উপমা বা উৎপেক্ষায় নয়, বরং ‘এবং’ (অর্থাৎ ‘হি’) অর্থে—অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্তই, তাই আত্মা।
নিরুক্তের প্রাচীন ব্যাখ্যাকার স্কন্দস্বামী এই শব্দের মূলে আঙ্পূর্বক তনু বিস্তারে, বুদাঞ্ দানে এবং অদ্ ভক্ষণে—এই ধাতুগুলিকেও গ্রহণ করেন—‘আতনোতেরাদদাতেরতেরাপ্নোতের্বা আত্মা’। তদনুসারে নির্বচন—
(ক) আতননাত্ আত্মা।
(খ) জীবেনান্তঃকরণেন আদত্ত ইত্য আত্মা।
(গ) আসমন্তাদ্ অতিক্রম্য আত্মা।
বেদান্তসিদ্ধান্তে আত্মার নির্বচন চারটি পৃথক ধাতু থেকে করা হয়েছে—
যচ্চ্যাপ্নোতি যদাদত্তে
যচ্চ্যাত্তি বিষয়ানিহ ।
যচ্চ্যাস্য সন্ততো ভাবঃ তস্মাদাত্মেতি গীয়তে ।।
তদনুসারে নির্বচন—
(ক) আপ্নোতি বিষয়ান্ ইত্য আত্মা।
(খ) আদত্তে বিষয়ান্ ইত্য আত্মা।
(গ) অতি বিষয়ান্ ইত্য আত্মা।
(ঘ) অততি সাতত্যেন গতো ভবতীতি আত্মা।
এই চারটিই জীবাত্মার দৃষ্টিতে করা, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্তে আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ মানা হওয়ায় এগুলি পরমাত্মাপরক বলেও ধরা যায়। অল্প ধাতু-রূপান্তর করলেই এই চারটি নির্বচন ভগবানের ক্ষেত্রেও সঙ্গত—
(ক) আপ্নোতি ব্যাপ্নোতি জগদ্ ইত্য আত্মা পরমেশ্বরঃ।
(খ) আদত্তে প্রলয়কালে জগদ্ ইত্য আত্মা।
(গ) অতি বিনাশকালে জগদ্ ইত্য আত্মা।
(ঘ) অততি সন্ততো ভবতীতি আত্মা।
নিম্নলিখিত স্থানে আত্মা শব্দ ভগবানের অর্থে ব্যবহৃত—
চিত্রং দেবানাং ..... আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ । —ঋগ্ ১।১১।১৫।১, যজুঃ ৭।১৪।২
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভে যথাবশং চরতি দেব এষঃ । —ঋগ্ ১০/১৬৬/৪৪
তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ । —তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১
আত্মত এবেদং সর্বম্ । —ছান্দোগ্য ৭/২৬/১
ঐতরেয়োপনিষদ ১।৭।১-এ শাঙ্করভাষ্য—
‘আত্মেতি—আত্মা আপ্নোতেরত্তেরততের্বা পরঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরশনায়াদিসর্বসংসারধর্মবিবর্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোऽজোऽজরোऽমৃতোऽভয়োऽদ্বয়ো হি।’
পরমাত্মা—গ্রন্থকারের নির্বচনের উপর এই আপত্তি করা যেতে পারে যে ‘পরশ্চাসাব্ আত্মা’ এইরূপ বিগ্রহ করলে ‘পরাত্মা’ পদ হবে, ‘পরমাত্মা’ নয়। সুতরাং ‘পরম’ শব্দের সঙ্গে আত্মা শব্দের সম্পর্ক স্থাপন করে ‘পরমশ্চাসাব্ আত্মা’ এই বিগ্রহ হওয়া উচিত ছিল; অতএব গ্রন্থকারের প্রদত্ত বিগ্রহ অশুদ্ধ। এর সমাধান এই যে, গ্রন্থকার এখানে ব্যাকরণগত নিরুক্তি করেননি, বরং শব্দের অর্থমাত্র ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ‘পরশ্চাসাব্ আত্মা’ বাক্যটি বিগ্রহবাক্য নয়, বরং ফলিতার্থকথনপরক বাক্য। প্রাচীন আচার্যদের লেখায় এ ধরনের ব্যবহার বহুস্থানে দেখা যায়। যেমন—
‘প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি’—এই ন্যায়সূত্র (১/১/৩) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাত্স্যায়ন লেখেন— ‘অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বিত্তং প্রত্যক্ষম্’। কেউ যেন একে ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দের বিগ্রহ মনে করে আপত্তি না তোলে, তাই বার্ত্তিককার লেখেন— ‘প্রতিগতামক্ষং প্রত্যক্ষমিতি প্রাদিসমাসঃ; ভাষ্যং তু ফলিতার্থকথনপরম্, অন্যথা অব্যয়ীভাবসমাসাশ্রয়ণে অক্ষস্যেতি ষষ্ঠীশ্রবণানুপপত্তেঃ’। অর্থাৎ ‘অক্ষস্যাক্ষস্য’ প্রভৃতি ভাষ্যকারের বাক্য বিগ্রহ নয়, ফলিতার্থকথন।
এখানেও একই কথা বুঝতে হবে।
‘নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধম্’ (ঋগ্ ৫।৮৫।৭)—এই মন্ত্রে ‘নীচীনবারং’ পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্কন্দস্বামী নিরুক্তভাষ্য (১০।৪৪)-এ লেখেন— ‘নীচং বারং যস্য স নীচীনবারোऽধোমুখম্’। এখানেও আচার্য ‘নীচীন’ শব্দের স্থলে ‘নীচ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন; ‘নীচং বারং যস্য’ বাক্যটি ফলিতার্থকথনপরক।
নিরালম্বোপনিষৎকার বলেন— ‘দেহাদেঃ পরতরত্যাত্ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা’। এখানে নির্বচন হবে— ‘পরমশ্চাসাব্ আত্মা পরমাত্মা’। নিম্নলিখিত স্থানে পরমাত্মা শব্দ ভগবানের বাচক—
যো বৈ বেদ মহাদেবং প্রণবং পুরুষোত্তমম্
ওঙ্কারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ।। —ঋক্পরিশিষ্ট ৩।২২।১
পরমাত্মানং পরমং ব্রহ্ম । —নৃসিংহোত্তরতাপিনী ৪
আত্মানং সন্ধতে পরমাত্মনি । —ব্রহ্মোপনিষদ ৩
স বৈ ব্রহ্ম পরমাত্মোচ্যতে । —হংসোপনিষদ ১
পুত্র অভিধয়ে; বূঝ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে—এই ধাতুগুলি থেকে ‘সবিতা’ শব্দ সিদ্ধ হয়।
‘অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোৎপাদনম্। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে ভোট্পাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ’—যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি করেন, সেই জন্য পরমেশ্বরের নাম ‘সবিতা’।
দিয়ু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু—এই ধাতু থেকে ‘দেব’ শব্দ সিদ্ধ হয়।
(ক্রীড়া) যিনি শুদ্ধ জগতকে ক্রীড়া করান,
(বিজিগীষা) ধর্মিকদের জয়লাভের ইচ্ছাযুক্ত,
(ব্যবহার) সকল চেষ্টার উপকরণ ও উপসাধনের দাতা,
(দ্যুতি) স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ও সকলের প্রকাশক,
(স্তুতি) প্রশংসার যোগ্য,
(মোদ) নিজে আনন্দস্বরূপ এবং অন্যদের আনন্দদাতা,
(মদ) মদোন্মত্তদের দমনকারী,
(স্বপ্ন) সকলের শয়নার্থ রাত্রি ও প্রলয় কর্তা,
(কান্তি) কামনীয়, এবং
(গতি) জ্ঞানস্বরূপ—এই সকল কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম ‘দেব’।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
—গীতা ০১৫/১৭
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে
—যোগ ১/২৮-এ ব্যাসভাষ্য
পরমেশ্বর—‘য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ’—এটি পরমেশ্বর শব্দের ব্যাকরণগত বিগ্রহ নয়, কেবল ফলিতার্থকথনমাত্র। প্রকৃত বিগ্রহ হবে—‘পরমশ্চাসাবীশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ’।
স.প্র. প্রথম সংস্করণে বিশেষভাবে বলা হয়েছে—
“ঈশ্বর নাম সামর্থ্যবানের। যে ঈশ্বরদের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ, তার নাম পরমেশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেক ঐশ্বর্যের অধিকারী। যেমন মানুষের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেক ঐশ্বর্যের অধিকারী, তেমনি ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চক্রবর্ত্যাদি রাজাদের মধ্যেও যিনি পরম শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরমেশ্বর।”
মৈত্রেয়ুপনিষদ-এর নিম্ন উদ্ধৃতিতে পরমেশ্বর শব্দটি ভগবদ্বাচক—
সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যকাম এষ পরমেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূपालঃ —৭৭৭
সবিতা
নিরুক্তকার ‘ঘূ প্রেরণে’ ধাতু থেকে সবিতা শব্দ নির্মাণ করেছেন— সবিতা সর্বস্য প্রসবিতা (নিরুক্ত ১০/৩৩১)। পরমেশ্বর জগৎ উৎপন্ন করে তার প্রতিটি উপাদানকে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত করেন এবং মানবমাত্রকে শুভ কর্মে প্রেরণা দেন। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থসমূহে সবিতা শব্দটি প্রায়শই উৎপাদক ও প্রেরক অর্থে গ্রহণ করেছেন।
সবিতা পশ্চাত্তাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতি সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ॥—ঋক্ ১০/৩৬/১৪
ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে সবিতা শব্দ সর্বত্র ভগবদর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮২তম সূক্তের নয়টি মন্ত্রের দেবতাও সবিতা।
সখায় আ নিষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি—ঋক্ ১/২২/৮৮
এখানে পরমেশ্বরকে উৎপাদক, স্তোতব্য ও দাতা রূপে সবিতা নামে স্মরণ করা হয়েছে।
দেব
স.প্র. প্রথম সংস্করণে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়েছে—
১. ধাতু ৪৭১॥
২. এই পদটি অসংলগ্ন বলেও মনে হতে পারে, অথবা একে পরমাত্মার বিশেষণ ধরা যেতে পারে—অর্থাৎ নিজে শুদ্ধ ও নির্লেপ থেকেও জগতকে ক্রীড়া করান। অথবা—‘যো দীব্যতি ক্রীড়তি স দেবঃ’—যিনি নিজ আনন্দে নিজ স্বরূপে ক্রীড়া করেন, অথবা কোনো সহায় ছাড়াই ক্রীড়ার ন্যায় সহজ স্বভাবে সমগ্র জগৎ রচনা করেন এবং সকল ক্রীড়ার আধার—তাই দেব।
‘যো বিজিগীষতে স দেবঃ’—যিনি সকলকে জয় করেন অথচ নিজে অজেয়।
‘যো ব্যবহারয়তি স দেবঃ’—যিনি ন্যায় ও ন্যায়স্বরূপ ব্যবহারের জ্ঞাতা ও উপদেশক।
‘যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি স দেবঃ’—যিনি সমগ্র চরাচর জগতের প্রকাশক।
‘যঃ স্তূয়তে স দেবঃ’—যিনি সর্বজনের স্তুতিযোগ্য, নিন্দার অযোগ্য।
‘যো মোদয়তি স দেবঃ’—যিনি নিজে আনন্দস্বরূপ এবং অন্যদের আনন্দ দান করেন।
‘যো মাদ্যতি স দেবঃ’—যিনি সদা হর্ষিত ও শোকরহিত।
‘যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ’—যিনি প্রলয়ের সময় সকলকে অব্যক্তে শয়ন করান।
‘যঃ কাময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ’—যাঁর সকল কামনা সত্য এবং যাঁর প্রাপ্তি সকল শিষ্ট কামনা করেন।
‘যো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ’—যিনি সর্বত্র গত ও জ্ঞেয়।
এই সব কারণেই পরমেশ্বরের নাম দেব।
“দিভু ক্রীড়াবিজিগীষা … কান্তিগতিষু”—এই ধাতু থেকে দেব শব্দ সিদ্ধ।
‘দিভ্যতি স দেবঃ’—যিনি স্বয়ংপ্রকাশ ও জগতপ্রকাশক।
‘ক্রীড়তে স দেবঃ’—যিনি নিজ আনন্দে ক্রীড়া করেন বা ক্রীড়ার ন্যায় জগত রচনা করেন।
‘বিজিগীষতে স দেবঃ’—যিনি সকলকে জয় করেন, অথচ অজেয়।
‘ব্যবহারয়তি স দেবঃ’—যিনি ন্যায়-অন্যায়ের উপদেষ্টা ও সকল ব্যবহারের আধার।
‘দ্যোতয়তি স দেবঃ’—যিনি সকল আলোর আধার।
‘স্তূয়তে স দেবঃ’—যিনি সর্বত্র স্তুতিযোগ্য।
‘মোদয়তি স দেবঃ’—যিনি নিজে আনন্দস্বরূপ ও আনন্দদাতা।
‘মাদ্যতি স দেবঃ’—যিনি সদা হর্ষিত ও শোকহীন।
‘স্বাপয়তি স দেবঃ’—যিনি প্রলয়ে সকলকে অব্যক্তে শয়ন করান।
‘গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ’—যিনি সর্বব্যাপী ও জ্ঞেয়।
অতএব দেব নাম পরমেশ্বরেরই।
নিরুক্তকার দেব শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন—
দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুঃস্থানো ভবতীতি বা (নিরুক্ত ৭/৩/১৫)।
অর্থাৎ দেব শব্দ ডুদাঞ্ দীপি দানে, দীপ্তৌ, এবং দ্যুত্ দীপ্তৌ ধাতু থেকে গঠিত—কারণ দেব ঐশ্বর্যের দাতা, তেজোময় ও অন্যদের প্রকাশক। যদিও নিরুক্তকার দিভু ধাতু থেকে দেব শব্দ নির্মাণ করেন না, অনেক বৈয়াকরণ ‘দীব্যতীতি দেবঃ’ বলে দিভু ধাতু থেকেই দেব শব্দ সিদ্ধ করেন।
তৈত্তিরীয় সন্ধ্যাভাষ্যে কৃষ্ণ পণ্ডিত দেব শব্দের তিনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন—
(ক) দীব্যতি প্রকাশতে স দেবঃ।
কুবের
কুবি আচ্ছাদনে—এই ধাতু থেকে কুবের শব্দ সিদ্ধ।
‘যঃ সর্বং কুম্বতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছাদয়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ’—যিনি নিজের ব্যাপ্তিতে সকলকে আচ্ছাদিত করেন, তাই পরমেশ্বরের নাম কুবের।
(খ) ধ্যানত্বাৎ হৃদয়ারবিন্দে ক্রীড়তীতি দেবঃ।
(গ) দ্যুলোকবর্তিত্বাদ্বা দেবঃ।
প্রথম দুটি ধাত্বর্থনির্ভর, তৃতীয়টি নিরুক্তের ‘দ্যুঃস্থানো ভবতীতি’ অবলম্বনে। বিষ্ণুসহস্রনামের শাঙ্করসম্প্রদায়ানুসারী ভাষ্যে বলা হয়েছে “যতো দীব্যতি ক্রীড়তি সর্গাদিভিঃ, বিজিগীষতে অসুরাদীন্, ব্যবহারতি সর্বভূতেষু আত্মতয়া দ্যোততে, স্তূয়তে স্তুত্যৈঃ, সর্বত্র গচ্ছতি তস্মাদ্ দেবঃ।” অর্থাৎ সৃষ্টি-লীলায় ক্রীড়া, দুষ্টদমন, সর্বব্যবহারের উপদেশ, স্বপ্রকাশ, স্তুতিযোগ্যতা ও সর্বব্যাপ্তির জন্য ভগবান দেব নামে অভিহিত।
নিম্ন স্থানে দেব শব্দ ভগবদর্থে ব্যবহৃত—
দেবো দেবানামসি মিত্রোऽদ্ভুতো বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে। —ঋক্ ১৩/৬/৪৭/১৩
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি। —অথর্ব ১০/২/৩২
একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। —শ্বেতোপনিষদ ৬/১১
নিবৃত্তে সর্বদুঃখানামীশানঃ প্রমুখ্যঃ।
অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্যো বিভুঃ স্মৃতঃ॥ —গৌড়পাদকারিকা ১০
কুবের (পুনরুক্তি)
উণাদিসূত্র ‘কুম্বের্নলোপশ্চ’ (১।৫৬)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— ‘কুম্বত্যন্যানাচ্ছাদয়তি ইতি কুবেরঃ’—সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র জগত আচ্ছাদিত করেন বলে পরমেশ্বর কুবের। আরও এক ব্যাখ্যা— ‘কুম্বত্যাচ্ছাদয়তি পরেষামৈশ্বর্যমিতি কুবেরঃ’—যিনি সকলের ঐশ্বর্য আচ্ছাদিত করেন। পরমৈশ্বর্যবান বলেই পুরাণে কুবেরকে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে।
নিম্ন স্থানে কুবের শব্দ ভগবদ্বাচক—
কুবের তে মুখং রৌদ্রং নন্দিন আনন্দমাবহঃ
জ্বরমৃত্যুভয়ং ঘোরং বিশ নাশয় মে জ্বরম্॥ —ঋক্পরি ২৬/৪/৪২
কুবেরঃ সর্বপক্ষাণাং ক্রতুনাং বিষ্ণুরুচ্যতে। —মহাভারত অনু ১৪৭/৩/১৬
তস্য কুবেরো বৈশ্রবণো বৎস আসীদামপাত্রং পাত্রম্। —অথর্ব ১০/১০/১০
পৃথিবী
প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছে— “যিনি আকাশাদির চেয়েও বিস্তৃত, তাঁর নাম পৃথিবী; সেই জন্য পরমেশ্বরের নাম পৃথিবী।” যেখানেই ‘প্রথ্’ ধাতু থেকে পৃথিবী শব্দ নিষ্পন্ন ধরা হয়েছে, সেখানেও মূল ধাতু হিসেবে ‘প্রথ্ বিস্তারে’ গৃহীত হয়েছে। আচার্য যাস্ক উল্লেখ করেছেন—
১. ধাতুপাঠ ১/২৬০।
পরবর্তী টীকা অনুযায়ী ‘কুবি/কুম্বতি/কুবের’ শব্দে বকারযুক্ত পাঠই শুদ্ধ; ‘কুবের’ই যথার্থ, ‘কুবের’ (দন্ত্যোষ্ঠ্য বকারবিহীন) উচ্চারণদোষজাত ভ্রষ্ট পাঠ।


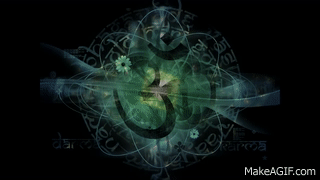




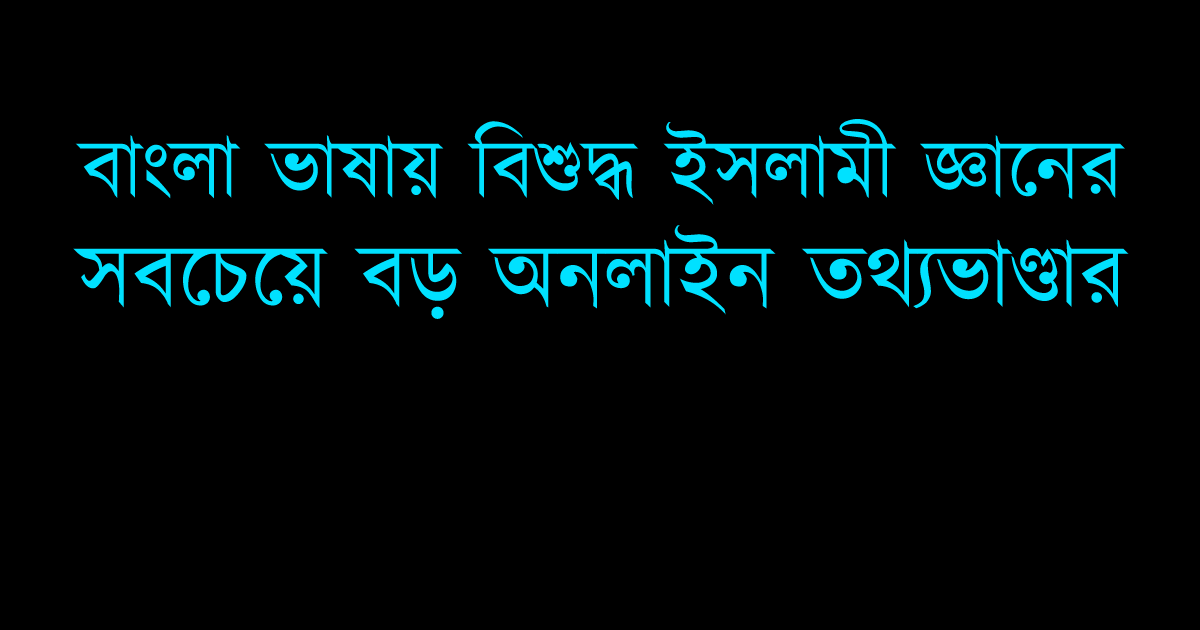


















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ