সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা মানুষ পৃথিবীতে তিনজন — (১) গ্রন্থকার, (২) চিত্রকার এবং (৩) শিল্পকার। এদের মধ্যে গ্রন্থকারের উপকরণ খুবই নমনীয়, তাই তাদের কাজ খুব সহজ হয়ে যায়; তবু তাদের সৃষ্টির সামনে হাত জোড় করে স্বীকার করতেই হয় যে—
“তোমার মহিমা বর্ণনা করতে গেলে আমাদের বাক্য যে ভোঁতা হয়ে যায়, তা তোমার গুণ ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য নয়; বরং তা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অথবা বর্ণনা করার শক্তি যার রয়েছে এমন উপযুক্ত শব্দই তার কাছে নেই বলে।”
এই গ্রন্থকাররা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সব কিছুর অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে তাদের প্রয়াস বহুবার ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, ফোনোগ্রাফের মতো বস্তু তাদের ঝুলিতে মিথ্যাও ভরে দেয়।
চিত্রকারদের উপকরণ গ্রন্থকারদের উপকরণের মতো এতটা নমনীয় নয়; তবু বেশ নমনীয় বটে। কিন্তু এরা কেবল দৃষ্টেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সব অভিজ্ঞতা জানানোর কাজ করায় তাদের কাজ অনেকখানি অপূর্ণ থেকে যায়। চোখের পক্ষে অগম্য এমন অনেক কিছু রয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতা এই চিত্রকারদের দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই গ্রন্থকারদের তুলনায় চিত্রকার কিছু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেও, কিছু বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ প্রমাণিত হয়। কোনো বস্তুর একটি মুহূর্তকে সীমাবদ্ধ করে ব্যাপক জ্ঞান দেওয়া চিত্রকারদের পক্ষে সম্ভব, সে কাজ গ্রন্থকারদের পক্ষে নয়। কিন্তু রুচি, গন্ধ বা হাওয়া, ভূতের মতো অদৃশ্য বস্তু—এগুলোর বর্ণনা গ্রন্থকার দিতে পারেন, চিত্রকার তা দেখাতে পারেন না। সিনেমা ইত্যাদি জিনিস চিত্রকারদের ভণ্ডামি বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ করে তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটাতে পারে।
শিল্পকারেরা দেখলেন, এ দু’জন একপাক্ষিকভাবে কাজ করতে গিয়ে কীভাবে ব্যর্থ হন, তাই বহু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং তাতে তারা যথেষ্ট সাফল্যও পেলেন। সৃষ্টির হুবহু নকল করায় শিল্পকারের সমকক্ষ আর কেউ নেই; তবে সৃষ্টির ক্ষণিকত্ব শিল্পকার সাধতে পারেন না। গোলাপের…কুঁড়ি মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রমশ বেশি করে ফুটতে ফুটতে যখন পুরো ফুটেই যায়, তখনই মুঞ্জে যেতে শুরু করে—এই কাজ শিল্পকারের দ্বারা সাধন হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টিতে যে কাজ ‘কাল’ করে, তা শিল্পকারের পক্ষে সম্ভব নয়; কাল-এর সঙ্গে শিল্পকার প্রতিযোগিতাও করতে পারে না। কালের সামনে শিল্পকারদের হাত জোড় করতেই হয়। প্রত্যক্ষ সৃষ্টিতে অবিরাম পরিবর্তন চলতে থাকে এবং সেই পরিবর্তনের জোরেই সৃষ্টি কালকে নিজের বশে রাখে, কিন্তু শিল্পকার বহু চেষ্টা করেও এমন কোনো শিল্প রচনা করতে পারে না, যাতে কালের ঘা লাগবে না। কালের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কাজ স্রষ্টার অंशবিশিষ্ট কিছু জীব কিছু সময় করে বটে, কিন্তু শেষে তাদেরও হার মানতেই হয়, তখন শিল্পকারদের আর কী অবস্থা!
এই তিন প্রতিসৃষ্টি-সৃষ্টিকারী মানুষই বর্ণেরই ব্যবহার করে। গ্রন্থকারের বর্ণে ‘স্বর’ ও ‘ব্যঞ্জন’ এমন ভেদ আছে; চিত্রকারের ক্ষেত্রে ‘উজ্জ্বল’ ও ‘ছায়া’ এমন ভেদ আছে; আর শিল্পকারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী—এমন ভেদ আছে। এই বর্ণগুলোর নানা প্রকার মিশ্রণ ঘটিয়ে কাজ করার পদ্ধতি—তিনজনেরই এক। কিন্তু তাতে বহু ইন্দ্রিয়-গম্যতা যুক্ত থাকায় শিল্প অন্য দু’টির তুলনায় বেশি ফলদায়ী। গ্রন্থকারের গ্রন্থ মুখস্থ থাকলে তা বেশি অবিনশ্বর, বরং দীর্ঘস্থায়ী—এই বিশেষতা আছে। সম্পূর্ণ বস্তুর একসঙ্গে জ্ঞান করিয়ে দেওয়া—এটা চিত্রকারের বিশেষতা; আর বহু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অজ্ঞ লোককেও কোনো বিষয় বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া—এটা শিল্পের বিশেষতা। এই বিশেষতা মাথায় রেখেই হিন্দি শিল্পের অধ্যয়ন করা উচিত।
হিন্দু ধর্মের (সম্প্রদায়ের) মূর্তিপূজাই এই তিন প্রতিসৃষ্টি-সৃষ্টিকারীদের ঐক্যসাধন। সাজসজ্জা—এটা চিত্রকারের কাজ; মূর্তি—এটা শিল্পকারের কাজ; আর মন্ত্র—এটা গ্রন্থকারের কাজ; এবং এই তিনেরই সহায়তা নিয়ে পরমাত্মার সৃষ্টি-মাধ্যমে জ্ঞান করিয়ে দেওয়াই মূর্তিপূজার বৈশিষ্ট্য। মূর্তিপূজায় সব ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটে, এবং সেই তৃপ্তির অভিজ্ঞতা নিতে নিতে একদিন পরমাত্মার বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়। যেভাবে রোদ, হাওয়া ইত্যাদির যথাযথ উপভোগের উদ্দেশ্য থাকলেও প্রতিটি মালিকের ঘর আলাদা রকমের হয়, সেভাবেই পরমাত্মার জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য থাকলেও প্রত্যেক ভক্তের মূর্তি আলাদা হয়। মালিক ও ভক্ত—নিজ নিজ সুবিধামতো আকার ইত্যাদি পরিবর্তন করে নেয়। এইরকমভাবে শিল্পই পরমাত্মার জ্ঞান করিয়ে দেওয়ার সহজ মাধ্যম।কুঁড়ি মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রমশ বেশি করে ফুটতে ফুটতে যখন পুরো ফুটেই যায়, তখনই মুঞ্জে যেতে শুরু করে—এই কাজ শিল্পকারের দ্বারা সাধন হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টিতে যে কাজ ‘কাল’ করে, তা শিল্পকারের পক্ষে সম্ভব নয়; কাল-এর সঙ্গে শিল্পকার প্রতিযোগিতাও করতে পারে না। কালের সামনে শিল্পকারদের হাত জোড় করতেই হয়। প্রত্যক্ষ সৃষ্টিতে অবিরাম পরিবর্তন চলতে থাকে এবং সেই পরিবর্তনের জোরেই সৃষ্টি কালকে নিজের বশে রাখে, কিন্তু শিল্পকার বহু চেষ্টা করেও এমন কোনো শিল্প রচনা করতে পারে না, যাতে কালের ঘা লাগবে না। কালের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কাজ স্রষ্টার অंशবিশিষ্ট কিছু জীব কিছু সময় করে বটে, কিন্তু শেষে তাদেরও হার মানতেই হয়, তখন শিল্পকারদের আর কী অবস্থা!
এই তিন প্রতিসৃষ্টি-সৃষ্টিকারী মানুষই বর্ণেরই ব্যবহার করে। গ্রন্থকারের বর্ণে ‘স্বর’ ও ‘ব্যঞ্জন’ এমন ভেদ আছে; চিত্রকারের ক্ষেত্রে ‘উজ্জ্বল’ ও ‘ছায়া’ এমন ভেদ আছে; আর শিল্পকারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী—এমন ভেদ আছে। এই বর্ণগুলোর নানা প্রকার মিশ্রণ ঘটিয়ে কাজ করার পদ্ধতি—তিনজনেরই এক। কিন্তু তাতে বহু ইন্দ্রিয়-গম্যতা যুক্ত থাকায় শিল্প অন্য দু’টির তুলনায় বেশি ফলদায়ী। গ্রন্থকারের গ্রন্থ মুখস্থ থাকলে তা বেশি অবিনশ্বর, বরং দীর্ঘস্থায়ী—এই বিশেষতা আছে। সম্পূর্ণ বস্তুর একসঙ্গে জ্ঞান করিয়ে দেওয়া—এটা চিত্রকারের বিশেষতা; আর বহু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অজ্ঞ লোককেও কোনো বিষয় বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া—এটা শিল্পের বিশেষতা। এই বিশেষতা মাথায় রেখেই হিন্দি শিল্পের অধ্যয়ন করা উচিত।
হিন্দু ধর্মের মূর্তিপূজাই এই তিন প্রতিসৃষ্টি-সৃষ্টিকারীদের ঐক্যসাধন। সাজসজ্জা—এটা চিত্রকারের কাজ; মূর্তি—এটা শিল্পকারের কাজ; আর মন্ত্র—এটা গ্রন্থকারের কাজ; এবং এই তিনেরই সহায়তা নিয়ে পরমাত্মার সৃষ্টি-মাধ্যমে জ্ঞান করিয়ে দেওয়াই মূর্তিপূজার বৈশিষ্ট্য। মূর্তিপূজায় সব ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটে, এবং সেই তৃপ্তির অভিজ্ঞতা নিতে নিতে একদিন পরমাত্মার বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়। যেভাবে রোদ, হাওয়া ইত্যাদির যথাযথ উপভোগের উদ্দেশ্য থাকলেও প্রতিটি মালিকের ঘর আলাদা রকমের হয়, সেভাবেই পরমাত্মার জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য থাকলেও প্রত্যেক ভক্তের মূর্তি আলাদা হয়। মালিক ও ভক্ত—নিজ নিজ সুবিধামতো আকার ইত্যাদি পরিবর্তন করে নেয়। এইরকমভাবে শিল্পই পরমাত্মার জ্ঞান করিয়ে দেওয়ার সহজ মাধ্যম।
এ কাজটি কীভাবে করে, তা তার অধ্যয়নের মাধ্যমে বোঝা যাবে; পরবর্তী প্রবন্ধটি সেই অধ্যয়নের দিকে মন আকৃষ্ট হোক—এই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।
যারা কিছু জানে, তাদের বিরোধিতা করারই চেষ্টা।
হিন্দি প্রাচীন শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের সূচিপত্র
১. ভূমিকা
২. শিল্পসংহিতার বিস্তার ও বিভাগ, ন’টি শাস্ত্র, বত্রিশ বিদ্যা, চৌষট্টি কলা
৩. শিল্পজ্ঞ ও তার সহকারী—তাদের গুণ ও কাজ
8. কৃষিশাস্ত্র—গাছ, পশু ও মানুষের প্রসব, প্রতিস্থাপন ও পালন
৫. জলশাস্ত্র—সিঞ্চন, সংহরণ ও স্থম্ভন—এর বিন্যাস ও ব্যবহার
৬. যন্ত্রশাস্ত্র—দণ্ড, চক্র, দন্তসরণি ও ভ্রম—এসবের প্রকার ও প্রয়োগ
৭. বায়ুস্তম্ভ ও বিদ্যা
৮. খনিশাস্ত্র—পাথর ও খনিজ ধাতু তোলা, পোড়ানো ও মিশ্রণ করা
৯. নৌকাবিদ্যা—নৌকার নির্মাণ ও ব্যবহার
১০. রথশাস্ত্র—রাস্তা ও বাহনের নির্মাণ ও প্রয়োগ
১১. বিমানশাস্ত্র—বিমানের নির্মাণ ও ব্যবহার
১২. শকুন্তবিদ্যা—পাখি পালন ও প্রশিক্ষণ
১৩. বাস্তুবিদ্যা—তাঁবু, কুঁড়েঘর ও বাড়িঘরের সাধারণ নকশা ও বিন্যাস
১৪. ভবন-সামগ্রীর পরীক্ষা ও গুণবৃদ্ধি
১৫. অধিষ্ঠানবিদ্যা—পাঁতা ভরাট এবং জোত ইত্যাদির বিন্যাস
১৬. তলবিদ্যা—জমিন ও তলার (মেঝে) বিন্যাস
১৭. মৃত্তিকাকর্মবিদ্যা—মাটি, ইট ও পাথরের নির্মাণকাজ
১৮. ছাদনবিদ্যা—সুতার (কারিগরির) কাজ
১৯. শিখরবিদ্যা—অগভীর অংশ ও তার অনুষঙ্গিক উপাদান
২০. সক্রিয় বিদ্যা—পোলিশ, রং, চিত্রাদি ইত্যাদি
২১. অঙ্গনবিদ্যা—ভিত, বাগান, কূপ ইত্যাদি
২২. প্রকারশাস্ত্র—দুর্গ, শাখা-অখা ও যুদ্ধসংক্রান্ত শাস্ত্র
২৩. নগর-নকশা—জলসরবরাহ, নিকাশি, বাজার ও পল্লীর বিন্যাস
২৪. রাজগৃহবিদ্যা—রাজপ্রাসাদ, দরবার ইত্যাদির নকশা
২৫. দেবালয়বিদ্যা—মন্দির নির্মাণের বিদ্যা
২৬. চিত্ররচনা—মূর্তি করা; পাথরের, কাঠের, ধাতুর, গিলাওয়া-জাত বস্তুগুলির গোলাকৃতি নির্মাণ
২৭. বনোপবনবিদ্যা—বাগান, শালা, শিক্ষার জন্য ও যজ্ঞের জন্য স্থাপনার বিন্যাস
২৮. উপসংহার
‘শিল্প’ অসামান্য অর্থবৎ শব্দ। এর সঙ্গে ‘শাস্ত্র’ শব্দের সংযুক্তি এই বিষয়ে গাম্ভীর্য তো দেয়ই, কলাক্ষেত্রের নানারূপকেও প্রতিফলিত করে। শিল্পে বহু বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট রূপ এসে যায়। বাল্মীকি রামের জন্য ‘বৈহারিকাণাং শিল্পানাং জ্ঞাতা’-জাতীয় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সংকেত শিল্পের নানাবিধ গুঢ়ার্থকে নির্দেশ করার জন্য করেছেন। শিল্পের বিষয়গুলির মধ্যে এই মহাকাব্যে চিত্রকলা, তক্ষণকলা, স্থাপত্যকলা, সংগীত, রঙ্গকর্ম, নৃত্য এবং স্থাপত্যের মতো বহু ক্ষেত্রের নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রমাণ দেখায় যে ভারতীয়রা শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-কালে-ই যথেষ্ট উন্নতি করে নিয়েছিল।
এই শিল্পেই স্থাপত্যকলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হয়েছে। একে বাস্তু-তত্ত্বও বলা হয়েছে—এতে তত্ত্ব ও ব্যবহার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিল্পী ও স্থপতিরা আঞ্চলিক অবস্থা, দেশাচার, প্রয়োজন এবং গুরুত্বকে মনে রেখে বাস্তু-নিবেশন করেছেন। তাঁদের সামনে তত্ত্বের পাশাপাশি বাস্তব প্রয়োগও ছিল। এই তত্ত্বগুলিতে শুধু বিশ্বকর্মাই নন, ময়-আদি আঠারো এবং কখনও কখনও তারও বেশি আচার্যের মতও বিবেচিত হয়েছে। বাল্মীকি ইঙ্গিত দেন যে সেই কালের মধ্যে তক্ষণ-ময় স্থাপত্যের জন্য বিশ্বকর্মার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রতিমাদি-র জন্য ময়ের শিল্প উপমেয় ছিল—
তনুমধ্যা পৃথুশ্রেণী শরদিন্দুশুভাননা।
হেমবিম্বিনিভা সৌম্যা মায়েব ময়নির্মিতা। (রামায়ণ ৬, ১২, ১৪)
তথা—
হেমসোপানযুক্তং চ চাহপ্রবরবেদিকম্।
জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি॥
ইন্দ্রনীলমহানীলমণিপ্রবরবেদিকম্।। (তত্রৈব ৫, ৯, ১৫–১৬)
বাস্তবিকই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের সুস্পষ্ট ধারাগুলি দৃশ্যমান হয়। ভেসর বা মিশ্রণ শৈলীর মন্দির—উভয়েরই মিশ্র রূপ বলে গণ্য করা হয়। পুরাণে-ও এটি…
বাস্তবিকই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের সুস্পষ্ট ধারাগুলি প্রতিভাত হয়। ‘বেসর’ বা মিশ্রণধর্মী শৈলীর মন্দির উভয়েরই মিশ্র রূপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পুরাণগুলিতেও এই ভেদ–অভেদ, মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তবে বিশ্বকর্মাকে আদ্য শিল্পাচার্য রূপে স্বীকৃতি সর্বত্র বিস্তৃতরূপেই প্রতিভাসিত। বিশ্বকর্মাকে শুধু শিল্পের নয়, শ্রমের দেবতা হিসেবে গ্রহণ করার মূলে সাধনা, তৎপরতা এবং পর-সুখ-হিতার্থ চিন্তনের মতো গুণ-মূল্যই প্রধান।
ভবন, পুর, গ্রামাদি বিন্যাস থেকে শুরু করে দেবালয়, যানাদি উপস্কর এবং অন্যান্য কলাপূর্ণ নির্মাণের জন্য যে জ্ঞান পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছে, তা ঋষিকুলাশ্রিত পরিপাটির অনুসারে বিশ্বকর্মীয় জ্ঞান নামে পরিচিত হয়েছে। বাস্তু-শিল্পাদি ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আচার্যদের মতামতও শিল্পী ও স্থপতিদের পৃথক শ্রেণি গড়ে তুলেছিল—এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু এটি নিশ্চিত যে বিশ্বকর্মার মতের বিস্তার ছিল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্রায় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়।
রাজস্থান, গুজরাত থেকে শুরু করে বঙ্গ, অসম, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশাদি অঞ্চলে বিশ্বকর্মার মতের বিস্তার ছিল। এই দৃষ্টিতে এসব অঞ্চলে বিশ্বকর্মা-মতাভিত্তিক গ্রন্থের রচনা, সংগ্রহ-সম্পাদনার পরম্পরাও লক্ষিত হয়। ওড়িশার স্থপতিদের মধ্যে বিশ্বকর্মার প্রতি বিশেষ ভক্তিভাব ছিল। সেখানে শিল্পগ্রন্থ রচনার দীর্ঘ ঐতিহ্য বিদ্যমান। রামচন্দ্র কৌলাচার্য রচিত ‘শিল্পপ্রকাশ’, স্থাপক নিরঞ্জন মহাপাত্র বিরচিত ‘শিল্পরত্নকোষ’ প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থ এই পরম্পরার উজ্জ্বল আসন।
শিল্পীদের সম্প্রদায়কে স্বয়ং ‘বিশ্বকর্মা’ নামেই জানা যেত; গৃহকর্ম সমাপ্ত হলে প্রবেশাদি উপলক্ষে তাদেরকেও ব্রাহ্মণদের মতোই বরন করা হতো, যেমনটি ‘শিল্পশাস্ত্র’-এ বলা হয়েছে— “বিসিক্রমা বরন …”।
ওড়িশায় মহাপাত্র, মহারাণা জাতি শিল্পীসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত ছিল; তাদের কাছে শিল্পগ্রন্থের ভাণ্ডারও ছিল এবং তারা এসবের প্রতি ভক্তিভাবসহ যুক্ত থেকেছে। পুরী, ভুবনেশ্বরের বহু মন্দির সেই শ্রম-स…
অল্পের পরিচায়ক। পুরী ও ভুবনেশ্বর…
ভারতীয় স্থাপত্য নিয়ে আধুনিক যুগের প্রথম গম্ভীর ও সুসংগঠিত কাজ, রাম রাজের Essay on the Architecture of the Hindus মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রায় দেড় শতাব্দী আগে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৮৩৪ সালে—সেই একই বছর যখন জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী লিপি পাঠোদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের অধ্যয়নকে আমূল বদলে দেন। রাম রাজের প্রবন্ধটিকে ঘোষণা করা হয়েছিল “স্থাপত্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুধু নয়, হিন্দুদের ইতিহাসেও এক যুগান্তকারী ঘটনা” হিসেবে; এবং বাড়াবাড়ি প্রশংসা থাকলেও তা পুরোপুরি অযৌক্তিক নয়। মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় লেখক যে মূলত সঠিক ও বিচক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, তা একজন দেশীয় বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য যথার্থই ছিল—যিনি নিজে নিজেই অমেয় ইংরেজি শিখেছিলেন এবং বিদ্যা ও প্রতিভার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের একটি ঐতিহ্যবাহী স্তূপ-সংক্রান্ত গ্রন্থ, মানসারার একটি খণ্ডাংশ (যে গ্রন্থটি প্রায় একশো বছর পরে পি. কে. আচার্য এত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসন্ধান করেছিলেন) খুঁজে বের করেন, এবং তা যথেষ্ট সঠিকভাবে অনুধাবন করেন একজন প্রথাগতভাবে শিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিত এবং “কাম্মাটা সম্প্রদায়ের একজন দক্ষ ভাস্কর, যিনি স্থাপত্যচর্চা ও এর ব্যবহৃত পরিভাষায় সুপরিচিত ছিলেন”–এর সাহায্যে। অর্জিত জ্ঞান তিনি বাস্তব স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাইও করেছিলেন। এই ধরনের প্রথম কাজ হিসেবে এর কাছে আরও কী প্রত্যাশা করা যায়? যদি এর পদ্ধতিগুলো আরও বেশি প্রয়োগ করা হতো এবং যে গবেষণার দিকটি এটি নির্দেশ করেছিল, তা আরও দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা হতো, তাহলে ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিতে পারত।
রাম রাজ যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলো ছিল নানা ধরনের—এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকেরাও সেগুলোর সঙ্গে খুবই পরিচিত। তখনও গ্রন্থ ছিল অপ্রতুল, আর যেসব স্থপতি বা শিল্পী সেগুলো নিজেদের কাছে রাখতেন, তারা অত্যন্ত গোপনীয় ছিলেন এবং যা তাদের কাছে ছিল তার অন্তর্নিহিত অর্থও খুব কমই বুঝতেন।
‘ক্যাপ্টেন হার্কনেসের ভূমিকাঃ Ram Raz, Essay on the Hindus, লন্ডন ১৮৩৪, পৃ. iii। রাম রাজের রিচার্ড ক্লার্ক-কে লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত, একই গ্রন্থে, পৃ. x।
অন্যদিকে যেসব পুরোহিতদের পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার হিসেবে ধরা হয়, তারাও সেগুলোর অর্থ খুব বেশি বুঝতে পারতেন না। কারণ এই গ্রন্থগুলো শুধু স্মরণশক্তিনির্ভর রূপেই ছিল না, এগুলো ভরপুর ছিল প্রযুক্তিগত পরিভাষায়ও—অর্থাৎ আপাত পরিচিত শব্দগুলো বিশেষ প্রযুক্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদের তাৎপর্য ছিল স্বাভাবিক অর্থের থেকে আলাদা, যার ফলে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যেত। তবে রাম রাজ কর্মকার ও পুরোহিত—উভয়ের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে যে পাঠটি তিনি পেয়েছিলেন, সেটিকে যথেষ্ট সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন; অর্থ পরিষ্কার করার জন্য তিনি সুন্দরভাবে আঁকা ও লিথোগ্রাফ করা ৪৮টি ফলক ব্যবহার করেছিলেন।
রাম রাজের কাজ যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সময়েই জেমস ফার্গুসন (১৮০৮–১৮৮৬) প্রিন্সেপের সৃষ্ট প্রচণ্ড উৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি অঞ্চল জুড়ে নিরলস অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন, “এই সংকল্প নিয়ে যে স্থাপত্যকে বিজ্ঞানের আওতার মধ্যে আনা সম্ভব কি না তা যাচাই করবেন।” ভারতে বাণিজ্যিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়েও তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি স্কুল থেকে কাউন্টি হাউসে, সেখান থেকে নীলচাষি ও বৃহৎ ব্যবসার অংশীদার হওয়ার জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তবু তিনি ভারতীয় স্থাপত্যের অধ্যয়নে অসাধারণ নিষ্ঠা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এর গবেষণার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পকর্মের মধ্যেই সরাসরি অধ্যয়ন কোনো তত্ত্বগ্রন্থের তুলনায় বেশি শিক্ষামূলক; তাই তিনি দীর্ঘ ভ্রমণ করেন—একক ব্যক্তির স্থাপত্য-সমীক্ষার মতো—মাসের পর মাস বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের মাঝে কাটান, নোট নেন এবং নিজেই অঙ্কন, রূপরেখা ও পরিকল্পনা তৈরি করেন, যা তাদের নিখুঁততার জন্য বিস্ময়কর। ভারতীয় স্থাপত্য নিয়ে তাঁর প্রথম প্রকাশনা বের হয় ১৮৪৫ সালে, এবং ১৮৭৬ সালের মধ্যে, জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহামের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদনসমূহ (যার প্রথম পাঁচটি খণ্ড তখন প্রকাশিত), জেমস বার্জেসের সাম্প্রতিক গবেষণা এবং সর্বোপরি আলোকচিত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সাহায্যে—যার গুরুত্ব তিনি দ্রুতই বুঝেছিলেন—তিনি যথেষ্ট ন্যায্যভাবেই দাবি করতে পারতেন যে তিনি ভারতীয় স্থাপত্যকে “আংশিকভাবে হলেও পূর্ণাঙ্গ”ভাবে আলোচনা করেছেন এবং এর একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।
এর ঐতিহাসিক বিকাশকে যে সাধারণ নীতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের একটি স্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করতে পেরেছেন।*
ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে ফার্গুসনের অবদান মূল্যায়ন করার আগে স্থাপত্য সম্পর্কে তাঁর সাধারণ তত্ত্বগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ কেবল এই প্রেক্ষাপটেই আমরা তাঁর কাজের তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি। শুরুতেই যে বিষয়টি সবচেয়ে চোখে পড়ে তা হলো—ফার্গুসন নিজস্ব একটি পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। স্থাপত্যচর্চা ও অতীতের স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল ভারতে, এবং ১৮৪৯ সালে, নিজের গৌরবময় কর্মজীবনের সূচনায়, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে এভাবে বর্ণনা করেন—
“আমি সৌভাগ্যবান যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো কাটিয়েছি এমন দেশগুলোতে, যেখানে শিল্পকলা, যদিও বৃদ্ধ ও অবক্ষয়গ্রস্ত, তবুও তার যৌবন ও শক্তির দিনে যে পথে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়েছিল সেই পথই অনুসরণ করে; এবং যদিও সে ক্লান্ত, কিন্তু উন্মাদ নয়। প্রাচ্যে এখনো মানুষ শিল্প সম্বন্ধে কথা বলায় তাদের বিবেকবুদ্ধি ব্যবহার করে, এবং তাদের মতামত কার্যকর করতে সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে। আধুনিক ইউরোপের মতো তারা এমন অদ্ভুত ভ্রমে আক্রান্ত হয় না, যা কেবল দৃষ্টিনন্দন ব্যর্থতার দিকেই নিয়ে যেতে পারে; এবং ফলস্বরূপ, আমরা যদিও ফলাফলগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে প্রবণ হতে পারি, তবুও এশীয় ও অ্যাংলো-স্যাক্সনদের আপেক্ষিক শারীরিক ও নৈতিক সামর্থ্যকে বিবেচনায় নিলে, তারা আমাদের অর্জনের তুলনায় নিজেই পরিপূর্ণতা।”**
অতীতের স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি—তার জীবিত কারিগরদের মাধ্যমে—এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে; মন্দির নির্মাণে নিয়োজিত স্থপতি ও কর্মকাররা…
পালিতানা “স্থাপত্যকলার দার্শনিক ছাত্রের” কাছে শুধু ভারতীয় স্থাপত্যের সত্যই প্রকাশ করবে না, বরং “মধ্যযুগে যেসব প্রক্রিয়ায় ক্যাথেড্রাল নির্মিত হয়েছিল সেগুলিও প্রকাশ করবে।” এই সরাসরি পদ্ধতি—অর্থাৎ ভবনকে সরাসরি ধরার মতো করে দেখা—ফার্গুসনের কাজের বড় শক্তি ছিল; আর তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এশিয়ার তুলনায় অ্যাংলো-স্যাক্সনদের শ্রেষ্ঠত্বে তার অটল বিশ্বাস, বিশেষত যখন তিনি এশীয় স্থাপত্য নিয়ে লেখেন। এতে তার স্থায়ী কৃতিত্বের দিক থেকে আমাদের মনোযোগ সরে যায় এবং তাকে, নিজের অজান্তেই, এক ধরনের অন্ধত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যার কারণে তিনি স্বভাবতই যেসব অনুসন্ধানের পথে এগোতে পারতেন সেগুলো আর অনুসরণ করেননি।
ফার্গুসন যে তীব্রতার সঙ্গে ভবনগুলো অন্বেষণ ও অধ্যয়ন করেছিলেন, তা তার এই সরাসরি স্থাপত্য-দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ফল। তিনি স্মৃতিস্তম্ভগুলোর মাঝে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন, অন্তহীন চিন্তায় ও মননে ডুবে থেকে “যতক্ষণ না আমি পাথরের গায়ে ছেনির দাগ থেকে বুঝতে পারি, শিল্পীকে তার নকশায় কোন ভাবনাগুলো পরিচালিত করেছিল, যতক্ষণ না আমি নিজেকে তার পাশে দাঁড় করাতে পারি এবং তার কাজের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারি।” এভাবেই ভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে—পূর্বধারণা ছাড়া এবং যুগের ছাঁচে বাঁধা মতামতের বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে (অবশ্যই ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসটি ছাড়া)—তিনি তার দার্শনিক নীতিগুলো গড়ে তুলতে পারেন এবং এক ধরনের স্থাপত্য-তত্ত্ব নির্মাণ করেন, যা নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে তিনি সমগ্র বিশ্বের স্থাপত্যের সমালোচনায় প্রয়োগ করতে শুরু করেন। আর তার কাছে বিশ্ব কেবল ইউরোপ নয়, বরং সমগ্র পৃথিবী—যার মধ্যে ভারত, আর্মেনিয়া এবং প্রাক-কলম্বীয় আমেরিকার মতো অবহেলিত অঞ্চলও ছিল।
ফার্গুসন স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে তিনি যাকে “সত্যিকারের ধারা” বলতেন তার সঙ্গে “অনুকরণ বা নকল ধারার” একটি তীব্র পার্থক্য কল্পনা করেছিলেন। সত্যিকারের ধারায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভবনই “যাদের জন্য নির্মিত, তাদের প্রয়োজন সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে পূরণ করার উদ্দেশ্যে সাজানো ছিল; এবং এদের উপর প্রয়োগ করা অলংকরণ হয় তাদের নির্মাণশৈলী থেকেই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত, নয়তো তা তাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।”
ফলত, এই ধরনের ভবনগুলো, তাদের যেকোনো ত্রুটি সত্ত্বেও, অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি “উদ্দেশ্যমূলক সত্যনিষ্ঠতা” এবং “স্থাপত্য নৈপুণ্যের কয়েকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান” ধারণ করত। এই সত্যনিষ্ঠতাই, তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে সত্যিকারের স্থাপত্যকর্মের সঙ্গে প্রকৃতির কাজের মধ্যে তুলনা টানতে অনুমতি দেয়; ফলে সত্যিকারের স্থাপত্য দেখলে আমরা প্রকৃতি থেকে যে আনন্দ পাই তারই সমজাতীয় আনন্দ পাওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে—“কারণ যদিও তারা একই উচ্চ বুদ্ধির উৎস থেকে উদ্ভূত নয়, তবু যতটা আমরা তা বুঝতে পারি তার সীমার মধ্যে একই প্রক্রিয়ার ফল; তাদের গঠনরূপ একই, আবার তারা আমাদের অনুভূতিতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আবেদন করে এবং আমাদের ইচ্ছাকে আরও প্রত্যক্ষভাবে তৃপ্ত করে।”
অন্যদিকে অনুকরণধর্মী শৈলী হলো চিন্তাহীন নকল, এবং এদের অন্য যেকোনো গুণ থাকুক না কেন, “সত্যনিষ্ঠতার উপাদান সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত,” ফলে স্থাপত্যকে “অর্ধ-প্রাকৃতিক উৎপাদনের উচ্চ অবস্থান থেকে নামিয়ে এনে নিছক অনুকরণশিল্পে পরিণত করে।” এই শ্রেণীতেই ফার্গুসন ১৫০০ সালের পরের সমস্ত ইউরোপীয় স্থাপত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে তার নিজের যুগের পুনরুজ্জীবনবাদী স্থাপত্যও ছিল; আর সত্যিকারের ধারায় পড়ত মিশরীয়, শাস্ত্রীয়, চীনা, মধ্যযুগীয় এবং অবশ্যই ভারতীয় স্থাপত্য।
ফার্গুসনের কাজ সাধারণ মানুষের ওপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু প্রথমে তার অধিক বিদ্বান সহকর্মীরাই তাকে গভীর সম্মান প্রদান করেন। শ্লিমান যখন Tiryns বইটি উৎসর্গ করেন, তিনি ফার্গুসনকে প্রশংসা করে বলেন—“স্থাপত্যের ইতিহাসবিদ, যিনি শিল্প সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং এর সবচেয়ে জটিল সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা মৌলিক প্রতিভা—উভয়ের জন্যই সমানভাবে খ্যাত।” আর যদিও ফার্গুসনের কাজ এখন অনেকটাই অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তবুও আমাদের নিজের শ্রমের প্রস্তাবনায় শ্লিমানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার সেই মৌলিক প্রতিভাকে স্বীকার করা যথাযথ মনে হয়—যা তাকে ভারতীয় স্থাপত্যের মৌলিক গুণাবলি স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করেছিল, এমন সময়ে যখন ইউরোপে ভারতীয় শিল্পকে সামগ্রিকভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হতো। তিনি উপকরণের জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে বিমোহিত হননি—যা অনেকের কাছে ছিল বন্যতার লক্ষণ—অথবা সে সময়ে প্রচলিত বেপরোয়া সমালোচনায়ও তিনি প্রভাবিত হননি। বরং, তিনি উপকরণের স্বভাবকে অসম্মান করার কোনো লক্ষণ দেখেননি, এবং তার ধারণা অনুযায়ী কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি কোনো অবহেলাও দেখেননি। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি ভারতীয় মন্দিরগুলিতে রূপ ও কর্মের নিখুঁত অভিযোজন অনুভব করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও সেই কর্ম বা উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্টভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারেননি এবং কখনও তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাও করেননি।
প্রতীকী সম্ভাবনাগুলো আরও অনুসন্ধান করার প্রবণতা তার মধ্যে দেখা যায়নি। এটি বেশ দুর্ভাগ্যজনক, এবং সম্ভবত এর কারণ ছিল ভাষাজ্ঞানের অভাব; এই অভাব, তার বিরক্তিকর জাতিগত পক্ষপাতের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাকে কখনোই এই ধারণা করতে দেয়নি যে একজন ভারতীয়ও অ্যাংলো-স্যাক্সনের মতোই গভীর চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং শিল্পে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। আমরা অনুমান করতে পারি যে এই কিছুটা সরল পক্ষপাত না থাকলে ফার্গুসনের কাজ আরও অধিক গুণসম্পন্ন হতে পারত, কিন্তু বৈপরীত্যপূর্ণভাবে, তার এই পক্ষপাত স্বীকার করাই আমাদেরকে তার অবদানের মৌলিক শক্তিগুলো আরও পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।
এবার ফার্গুসনের ভারতীয় স্থাপত্য সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কাজের দিকে ফিরে তাকালে, এবং তার চিন্তার বিবর্তন-প্রক্রিয়া জানা থাকলে, স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসেবে শিল্পের ইতিহাসের উপর তার জোর দেওয়া দেখে খুব একটা আশ্চর্যের কিছু থাকে না — অন্য শাস্ত্রের সহচরী হিসেবে নয়। উদাহরণ হিসেবে, ফার্গুসন দ্রুতই ইঙ্গিত করেছিলেন যে কানিংহামের কাজ, যদিও উপকারী, “স্থাপত্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে” করা হয়েছিল; আর নিজে তিনি সবসময় তার সিদ্ধান্তকে ভিত্তি দিতে পছন্দ করতেন সরাসরি শিল্পকর্ম বা স্থাপত্যকর্ম যে প্রমাণ দেয় তার উপর, ইতিহাস বা নৃতত্ত্ব যে প্রমাণ দেয় তার চেয়ে। আরও উল্লেখ্য, বিশেষত ভারতের প্রসঙ্গে, ফার্গুসন মনে করতেন যে স্থাপত্যই নৃতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ধর্মের রূপকে স্থির করে এবং ইতিহাস পুনর্গঠন করে। এমনকি ভাষা এবং সাহিত্যিক উৎসও যথেষ্ট বিকল্প নয়; কারণ স্থাপত্য “আরও সুস্পষ্ট, এটি কখনো নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে না, এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না,” এবং এটি আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে জানার সুযোগ দেয় যারা এসব স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে তাদের ধর্ম, শিল্প ও সভ্যতার প্রকৃতি।
এই অবস্থান গ্রহণ করে, এবং কখনো কখনো অন্যান্য প্রমাণের মূল্যায়ন কম করে, ফার্গুসন বিশেষত তার প্রাথমিক রচনাগুলোতে কিছু ভুল করেছিলেন যা পরে সংশোধন করতে হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে তার ভুলগুলোকে কঠোর একগুঁয়েমির ফলে যতটা মনে হয়, তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল তৎকালীন ঐতিহাসিক গবেষণার অস্পষ্ট এবং দুর্বল স্বরূপ, যার উপরে তিনি স্মৃতিস্তম্ভ নিজেই যে প্রমাণ দেয় তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যদিও তিনি কখনো কখনো নির্দিষ্ট কিছু স্মৃতিস্তম্ভের তারিখ নির্ধারণে ভুল করেছিলেন, তবুও যে ধারাবাহিক রূপরেখা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা মোটের উপর আজও বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যেকোনো অবস্থায়, দেখা যায় যে যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক তর্ক তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলে ফার্গুসন খুব কমই নিজের মত সংশোধন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিল্পকর্মের নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রমাণের উপর তার মৌলিক নির্ভরতা, যদিও প্রথমদিকে নতুন ও বিস্ময়কর ছিল—
History of Indian and Eastern Architecture, Vol. I, p. v.
On the Study of Indian Architecture, p. 11.
যখন প্রথমবার এই প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, তখন যা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, এখনো হয়তো পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে, কারণ বিপরীত মতামত এখনো কিছু ভারতীয় শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণায় দৃশ্যমান, এক শতাব্দী পরেও। এখনও কেউ কেউ একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা অন্য কোনো শিল্পকর্মকে তার নিজস্ব স্বকীয়তা এবং যে শাস্ত্রের অংশ তা তার যুক্তির ভিত্তিতে নয়, বরং এমন কিছু পার্শ্ববর্তী বিবেচনার ভিত্তিতে অধ্যয়ন করতে আগ্রহী, যা প্রায়ই অত্যন্ত সন্দেহজনক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু করলার বৃহৎ চৈত্যগৃহটির তারিখ নির্ধারণের প্রচেষ্টার কথাই মনে করলেই যথেষ্ট, যেখানে স্মৃতিস্তম্ভের শৈলী ও ভাস্কর্য ছিল না মূল বিবেচ্য, বরং একটি শিলালিখনে উল্লেখিত কোনো শাসকের নাম ছিল প্রধান ভিত্তি—যার পরিচয় এবং তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল অত্যন্ত দুর্বল প্রমাণের উপর। এর অর্থ এই নয় যে ইতিহাস, প্যালিওগ্রাফি বা এমনকি কার্বন-১৪ পদ্ধতি কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে অবদান রাখতে পারে না; কিন্তু শিল্প-ইতিহাসবিদের দায়িত্ব হলো প্রধানত নিজের শাস্ত্রের উপকরণের ওপর নির্ভর করা, অন্যদের নয়—বিশেষত যখন সেই অন্য উপকরণগুলো দুর্বল এবং অবিশ্বস্ত।
সময় সময় আমরা যখন ফার্গুসনের কাছে ফিরে যাই, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল স্থাপত্য-ইতিহাসের যে নীতিগুলো তিনি দেখেছিলেন তার প্রতি তার অটল আনুগত্য, এবং ভারতীয় স্থাপত্যের একটি কার্যকর রূপরেখা প্রতিষ্ঠায় তার সাফল্য—যাকে তিনি নিজেই একটি ‘হ্যান্ডবুক’ বা প্রাথমিক ব্যাকরণ বলে অভিহিত করতে পারতেন, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈন শৈলীতে যে মৌলিক শ্রেণিবিভাগ তিনি করেছিলেন, তা আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। ফার্গুসন নিজেও মনে হয় জটিলতাগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে “ভারতে কেবল একটি হিন্দু এবং একটি মুহাম্মদীয় শৈলীই ছিল না, বরং প্রত্যেকটির বেশ কয়েকটি প্রকরণ ছিল; এগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর স্বীকৃত নৃতাত্ত্বিক বিভাগগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।” তিনি আঞ্চলিক শ্রেণিবিভাগের কথাও ভাবতেন—যেমন দ্রাবিড়ীয়, উত্তর বা ইন্দো-আর্য এবং হিমালয়ীয়—তদুপরি একটি রাজবংশভিত্তিক শ্রেণি, চালুক্য—যে পরিভাষা নিয়ে তিনিই পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং এটিকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন উত্তর ও দ্রাবিড়ীয় শৈলীর মাঝামাঝি এখনো অনাবিষ্কৃত সীমান্তভূমিতে বিদ্যমান শৈলীর জন্য একটি সাময়িক ও প্রচলিত নাম হিসেবে। এভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সুস্পষ্ট শ্রেণিবিভাগ ও অধ্যয়নের সমস্ত উপাদানই উপস্থিত আছে ফার্গুসনের পথিকৃৎসুলভ কাজের মধ্যে, এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে সেইসব যুক্তির প্রক্রিয়া যার উপর এগুলো ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এটি পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে—যা জ্ঞানচর্চার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য শর্ত—এবং যা তার পরবর্তী অনেকের ক্ষেত্রে বলা যায় না।
History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II, p. 6.
ভারতীয় গবেষণার প্রাথমিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে বলা যায়, ভারতীয় স্থাপত্য-অধ্যয়নের ভিত্তি এর চেয়ে ভালোভাবে স্থাপন করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। অধিক সংখ্যক স্মৃতিস্তম্ভ সম্পর্কে অজ্ঞতা, যা তার কাজের প্রামাণ্যতা আরও বৃদ্ধি করতে পারত, সে-জন্য ফার্গুসনকে দায়ী করা চলে না; কারণ তিনি একাই কাজ করেছিলেন, মূলত নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, এবং সর্বদা আরও বিস্তৃত ও সমগ্রমূলক নথিবদ্ধকরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। “ইংল্যান্ডেই নয়, ইউরোপের প্রতিটি দেশেই সর্বজনীনভাবে গৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নীতিসমূহ” প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি অসাধারণভাবে সফল হয়েছিলেন। তবে আমার দৃষ্টিতে, তার কাজের একটি মৌলিক দুর্বলতা ছিল—এবং যার ফলে, বিস্তৃত পরিসর থাকা সত্ত্বেও তার কাজে একটি বিশেষ ধরনের প্রাদেশিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে—তা হলো ভারতীয় মন্দিরগুলোকে তাদের নির্মাতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যাদের জন্য এগুলো নির্মিত হয়েছিল তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে তার অক্ষমতা; যারা সেখানে পূজা করত এবং প্রতিমাদের আরাধনা করত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি না দেখা; এবং শিল্পশাস্ত্রসমূহে নিহিত জ্ঞান ও প্রথাগত স্থপতিদের কাছে থাকা জ্ঞানকে কাজে লাগাতে ব্যর্থতা।
আমরা দেখি, উদাহরণস্বরূপ, যে ফার্গুসন উপেক্ষা করেছিলেন রাম রায়ের সূচিত গবেষণার ধারা, যার কাজ প্রকাশিত হয়েছিল তখনই যখন তিনি নিজে তার গবেষণার গভীরতায় নিমগ্ন; এবং সে কাজের প্রভাব তার উপর প্রায় অনুপস্থিত বলেই প্রতীয়মান হয়। এর একটি ব্যাখ্যা—যা আগেই বলা হয়েছে—হতে পারে ভারতীয় ভাষার সঙ্গে তার নিজস্ব স্বীকৃত অপরিচয় এবং দেশীয় বিদ্বানদের প্রতি এক ধরনের গোপন অবিশ্বাস। তবে এই সমালোচনা সত্ত্বেও ফার্গুসনের মৌলিক কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না—অত্যন্ত অপ্রতুল এবং অনিশ্চিত তথ্যভিত্তির কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, ভারতীয় স্থাপত্যের অধ্যয়নকে তিনি সেই সময়ের ইউরোপীয় স্থাপত্য-অধ্যয়নের সমপর্যায়ের বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করেছিলেন। যখন তিনি শুরু করেছিলেন, তার নিজেরই রসিক ভাষায় বলতে গেলে, সবকিছু ছিল “অন্ধকার এবং অনিশ্চয়তায় ঢাকা, এবং এমন কোনো স্থাপত্য-গ্রন্থ বা বক্তৃতা প্রায় নেই যা ভারত ও মিশরের শৈলীর তুলনা দিয়ে শুরু হয় না; এবং ইউরোপে যা এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস হিসেবে গণ্য, সেই সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়, যদিও বাস্তবে দুটি শৈলীর মধ্যে এর চেয়ে বেশি অমিল আর হয় না।”
“... কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার প্রকৃত কারণ হলো যারা শাসকদেরও শাসন করে তাদের উদাসীনতা ও অনাগ্রহ; এবং যাদের ইচ্ছা থাকলে অল্প কয়েক মাস বা বছরে, সামান্য ব্যয়ে পুরো রহস্যটিই উদঘাটন করা যেত, নিজেদের কেবল একটি ইচ্ছা প্রকাশ করলেই।”
আজন্টার গুহাগুলোর যুগ-নির্ধারণ নিয়ে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধ বিষয়ে নোটে ফার্গুসন এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।
ফার্গুসনের কাজে রাম রায়ের উল্লেখ একমাত্র যেটি আমি লক্ষ্য করেছি তা হলো Rock Cut Temples of India গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ৮-এ—যেখানে তিনি ‘বিমান’ ও ‘মণ্ডপ’ শব্দের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।
লেখক সাধারণত এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন—এ দুটির মধ্যে কোনটি অধিক প্রাচীন—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীনত্বের শিরোপা প্রদান করেন ভারতীয় স্থাপত্যকে, যাকে তিনি আদিরূপ বলে মনে করেন। প্রায় চল্লিশ বছর পরে যখন তিনি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করেন, তখন বিপুল সংখ্যক স্মৃতিস্তম্ভ বর্ণিত ও সমীক্ষিত হয়েছিল এবং একটি বিস্তৃত শৈলীগত বিকাশ-ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে তা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও প্রশংসনীয়। ভারতীয় স্থাপত্যের অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল ভারতীয় শিল্পের অন্য যেকোনো শাখা—ভাস্কর্য বা চিত্রকলার চেয়ে—অনেক বেশি উন্নত স্তরে কাজ করে; যদিও দুর্ভাগ্যবশত এই অগ্রগতির গতি ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকেনি।
যখন ফার্গুসন ভারতীয় গ্রামাঞ্চল চষে বেড়াচ্ছেন, তখন কলকাতায় এসে পৌঁছালেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের একজন অফিসার, আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪–১৮৯৩), বয়সে ছয় বছরের ছোট, এবং যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম মহান অগ্রদূত হয়ে ওঠেন। বছরটি ছিল ১৮৩৩, এবং কানিংহাম তৎক্ষণাৎ মোহিত হলেন ক্যারিশম্যাটিক প্রিনসেপের ব্যক্তিত্বে; যিনি আসলে ফার্গুসনেরও অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। কানিংহামের সঙ্গে প্রিনসেপের সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ এবং সেই সূত্রেই প্রথমে তিনি মুদ্রা-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন; তার প্রাথমিক রচনাগুলির অধিকাংশই ছিল মুদ্রা-সংক্রান্ত। সরকারি দায়িত্বের কারণে কখনো কখনো তাকে ভ্রমণ ও ভৌগোলিক অনুসন্ধানে যেতে হতো; এবং সীমানা-সংক্রান্ত আলোচনার সময় কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিংহের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কের সুবিধা নিয়ে তিনি কাশ্মীরের মন্দিরসমূহ সমীক্ষা করেন এবং পরে একটি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তী দশ বছর তার প্রধান প্রাচীনতত্ত্ব-সংক্রান্ত গবেষণা আবর্তিত হয় ভিলসার স্তূপসমূহকে ঘিরে; এবং ১৮৬১ সালে তিনি ভারতের সরকারকে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে রাজি করান, যার তিনি হন সার্ভেয়ার। ১৮৬৫ সালে তা বিলুপ্ত হলেও ১৮৭০ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত কানিংহামই ছিলেন এর প্রধান। জরিপের জন্য তিনি যে অঞ্চলসমূহ আচ্ছাদিত করেন তার মধ্যে ছিল সমগ্র উত্তর ভারত—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বেঙ্গল পর্যন্ত—এবং আধুনিক রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বৃহৎ অংশ। ১৮৬৩–১৮৮৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত তার প্রতিবেদনের ২৩ খণ্ড শুধু ভারতীয় স্থাপত্যের ছাত্রদের জন্যই নয়, অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনের গবেষকদের জন্যও এক অমূল্য উপাদানভাণ্ডার। কানিংহামের মতে, “স্থাপত্য-নিদর্শন স্বভাবতই সবচেয়ে…
প্রত্নতত্ত্বের একটি প্রধান শাখা” এবং এটি অনিবার্য ছিল যে তিনি একটি বিশাল সংখ্যক মন্দির আবিষ্কার, বর্ণনা এবং তারিখ নির্ধারণ করবেন, বিশেষত মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের সমীক্ষায়, যা কেবল ১৮৭৬ সালে ফার্গুসনের History of Indian and Eastern Architecture প্রকাশের পর প্রকাশিত হয়েছিল। যদি কানিংহামের প্রতিবেদনের প্রকাশ আগেই হয়ে যেত, তা ফার্গুসনের কাজের মান আরও বৃদ্ধি করত। অনুসন্ধানের ফলে অর্জিত অমূল্য আবিষ্কার ছাড়া, কানিংহামের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান ভারতীয় স্থাপত্যের অধ্যয়নে ছিল গুপ্ত যুগের মন্দির নিয়ে তার কাজ। তিনি প্রথমবারের মতো তার বিস্তৃত রূপরেখা চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে সেই বিবর্তনমূলক ধারণার প্রভাবে যা আগে ফার্গুসনকে প্রভাবিত করেছিল, একটি সমতল ছাদের মন্দির থেকে শিখরযুক্ত মন্দিরে বিকাশের অনুমান করেন।
এ ছাড়াও কানিংহামের অবদান মূলত স্মৃতিস্তম্ভের ভাণ্ডার সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ফার্গুসন যে স্থাপত্য-ইতিহাসের ধারণা উদ্ভাবন করেছিলেন তা অনুসরণ করেননি। বরং তার জোর কিছুটা ভিন্ন ছিল, যা দেখা যায় ১৮৭১ সালে ফার্গুসনের প্রতি তার সমালোচনায়; যেখানে তিনি জোর দেন যে কালানুক্রমিক বিষয়ে স্থাপত্যগত প্রমাণ শুধুমাত্র সহযোগী প্রকৃতির এবং প্রধান মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য প্রমাণ হলো শিলালিপি। দুই দৃষ্টিভঙ্গিই মোটেও বিরোধপূর্ণ নয় এবং কানিংহাম প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের কালানুক্রমে ফার্গুসনের সঙ্গে একমত, উল্লেখ করে যে এই ক্ষেত্রে “বাস্তব তারিখের ভিত্তিতে নিরূপণের প্রক্রিয়া” গ্রহণযোগ্য ছিল; এবং আমরা জানি যে ফার্গুসন সবসময় তার সিদ্ধান্ত সংশোধনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন যদি তার কাছে গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে তারিখের প্রমাণ আসে।
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো কানিংহামের জোর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে, যা তাকে…
ASIR III (1873), পৃ. iv.
Allchin, “Ideals of History in Indian Archaeological Writing,” in C.H. Philips (সম্পাদক), Historians of India, Pakistan and Ceylon, পৃ. 242, থমাস হাক্সলির একটি আকর্ষণীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যিনি ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভার পর বলেন:
“একমাত্র ভুল ছিল ভয়ঙ্কর ‘ডারউইনিজম’ যা সেকশনে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আপনি যখন সবচেয়ে কম আশা করতেন, তখনও বেরিয়ে আসে, এমনকি ফার্গুসনের ‘বৌদ্ধ মন্দির’ বক্তৃতাতেও।” ফার্গুসন আসলে তার তত্ত্বগুলো, বা অন্তত তাদের মধ্যে কিছু, Origin of Species ১৮৫৯ সালের প্রকাশের আগে থেকেই তৈরি করেছিলেন, তবে নিঃসন্দেহে পরে তার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন।
ASIR 1874-75, 1876-77, X (1880), পৃ. 110 অনুসারে, এই তত্ত্বটি লেখককে এত প্রভাবিত করেছিল যে তিনি সমস্ত সমতল ছাদের মন্দিরকে সহজেই গুপ্ত যুগের হিসেবে নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, ১১শ শতাব্দীর পাটাইনি দেবী মন্দিরও তিনি গুপ্ত যুগের বলে বিবেচনা করেছিলেন (ASIR IX, পৃ. 31), যদিও এটি একসময় ফিখোরা থাকত, যার টুকরো এখনও স্থানে পড়ে আছে।
ASIR I, পৃ. xx.
তাঁর জ্ঞানের মধ্যে থাকা মন্দিরগুলোর মধ্যে যেগুলোতে কোনো শিলালিপি নেই, সেগুলো পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ রাখার প্রবণতা ছিল। স্থাপত্য, তার নিজস্ব মর্যাদায়, ছিল দ্বিতীয়তামূলক। কানিংহামের স্থাপত্য-গবেষণার মান (যা তার সহকারী-গণ থেকে আলাদা) সম্ভবত এসেছে তার ভারত এবং ভারতীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে গভীর পরিচিতি থেকে। দীর্ঘকালীন বসবাস, শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত ভ্রমণ, মাটির সঙ্গে সরাসরি পরিচয়, জনগণ এবং তাদের প্রথাগুলো সম্পর্কে প্রথম হাতের অভিজ্ঞতা, এবং ইতিহাস ও ধর্মের ব্যাপক জ্ঞান তাকে এমন একটি অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছিল যা প্রায়শই বিদেশী গবেষকদের মধ্যে পাওয়া যেত না। তাই তিনি প্রায়ই সঠিক প্রমাণিত হন, তা স্পষ্ট যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হোক বা না হোক।
কানিংহামকে ক্রেডিট দেওয়া উচিত, কারণ তিনি সময়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের ওপর জোর দিয়েছিলেন, ধর্মভিত্তিক নয়, যদিও তিনি তার সময়কালগুলোর জন্য ইন্দো-গ্রিসিয়ান, ইন্দো-স্কাইথিয়ান, ইন্দো-সাসানিয়ান ইত্যাদি অনন্য নাম দেন, যা পরিষ্কারভাবে ভারতীয় কৃতিত্বকে আংশিক ঋণী হিসেবে নির্দেশ করে। এটি একটি গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত পক্ষপাত ছিল, যা তার সময়ের অধিকাংশ বিদেশী গবেষকের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানকালে এতটাও মৃত নয়।
ফার্গুসন ও কানিংহামের কাজের পাশাপাশি, ভারতে বিভিন্ন স্থানে এলোমেলো অনুসন্ধানমূলক প্রচেষ্টা চলছিল, যা মূলত বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয়ের দিকে নিবদ্ধ ছিল। এই প্রচেষ্টাগুলিতে দেখা যায় ফার্গুসনের অক্লান্ত হাত, যিনি কখনোই লন্ডনের নিজের অবস্থান থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ বন্ধ করেননি। তিনি ভারত থেকে ফেরার পর লন্ডনে বসবাস গ্রহণ করেছিলেন এবং, যেমন আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, ভারতের ও বিশ্ব স্থাপত্যের ইতিহাসের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
এভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বোম্বে কেভ টেম্পল কমিশন (জুলাই ১৮৪৮–১৮৬১), যার সভাপতি ছিলেন জন উইলসন, এবং পরে বোম্বের প্রজ্ঞাবান গভর্নর সার বার্টল ফ্রেরের উদ্যোগে স্থাপত্য-প্রাচীন নিদর্শন কমিশন গঠন করা হয়, যা গুরুত্বপূর্ণভাবে শহরের ভারতীয় জমিদারদের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়। ভারতের স্থাপত্য নিয়ে একাধিক খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল, তবে কেবল তিনটি প্রকাশিত হয়—আহমেদাবাদ ও বিজাপুরের স্থাপত্য সম্পর্কিত দুটি এবং মাইসোর ও ধরওয়ারের স্থাপত্য সম্পর্কিত একটি খণ্ড, সবগুলোই ফটোগ্রাফ দ্বারা চিত্রিত এবং ফার্গুসনের নিজস্ব ভূমিকা সংবলিত।
১৮৬৬ সালে কানিংহামের জরিপ সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পর, কাজ কিছুটা এলোমেলোভাবে এগিয়েছিল, যার মধ্যে রাজেন্দ্রলালাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এছাড়া কানিংহাম একটি মন্দিরের কথা শুনেছিলেন, যেটি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, কিন্তু তা পরিদর্শন করেননি কারণ সেখানে কোনো শিলালিপি ছিল না। (ASIR XXI, পৃ. 100-101) আমার ধারণা, এটি সেই একই মন্দির যা আমি ১৯৬৮ সালে পরিদর্শন করেছিলাম, এবং এটি গুপ্ত স্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক আলো ফেলেছে।
মিত্রর ওড়িশার প্রাচীন নিদর্শনের সমীক্ষা, যা তাকে এবং বৃদ্ধ ফার্গুসনের মধ্যে এক অশোভন এবং তিক্ত বিতর্কে যুক্ত করেছিল। মাদ্রাস সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরের ফটোগ্রাফ তোলার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল এবং বোম্বে সরকার স্থানীয় আর্ট স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা অম্বারনাথ মন্দিরের একটি সিরিজ চিত্র অঙ্কনের কাজ কমিশন করেছিল।
উত্তর প্রদেশ বা পূর্ব ও উচ্চ প্রদেশে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ গঠিত হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন মেজর কোল, যিনি ১৮৬৯ সালে Illustrations of the Ancient Buildings of Kashmir প্রকাশ করেন, যা খুবই সীমিত মানের একটি কাজ এবং মূলত কানিংহামের বিংশ শতাব্দীর আগের লেখার উপর নির্ভর করেছিল। Illustrations of the Archaic Architecture of India (১৮৬৯) রিপোর্ট, যা ফরবস ওয়াটসনের দ্বারা রচিত এবং ফার্গুসন, কানিংহাম ও কর্নেল মিডোস টেইলরের অবদান সংবলিত, স্মৃতিস্তম্ভের অধ্যয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি সংকলন। এটি স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব বেশি উন্নীত করেনি, তবে এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে কত বিশাল পরিমাণ কাজ বাকি রয়েছে।
যতদূর স্থাপত্য-গবেষণার বিষয়টি, উপরের মতো, কানিংহাম ফার্গুসনের অনুসারী ছিলেন না, না পদ্ধতি তে, না দর্শনে; এবং এটি স্থাপত্য-গবেষণার শিখরে ফার্গুসনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার দায়িত্ব পড়ে জেমস বার্গেস (১৮৩২–১৯১৬)-এর ওপর, যিনি কানিংহামের মতোই স্কটল্যান্ডের ডামফ্রিসশায়ার থেকে আগত। তিনি এটি দক্ষতার সঙ্গে এবং প্রায় ক্লান্তিকর আনুগত্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন, কারণ তার কাজ তুলনামূলকভাবে সাধারণ এবং স্থির, ফার্গুসনের গভীর বিশ্লেষণ এবং শক্তিশালী উপস্থাপনার মতো নয়।
বার্গেস ১৮৫৫ সালে কলকাতার ডোভেটন কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে ভারতে আসেন, এবং ১৮৬১ সালে তিনি বোম্বেতে স্থানান্তরিত হন, যেখানে তিনি জে.জে. পারসি বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশনের প্রধান নিযুক্ত হন। শহরে অবস্থানের সময় তিনি স্থাপত্যে গভীর আগ্রহী হন এবং এই সময়ের কাছাকাছি ফার্গুসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন বলে মনে হয়।
তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ছিল সাতরুণজয়ার মন্দির (১৮৬৯) সম্পর্কিত, এবং এর দুই বছর পর ১৮৭১ সালে এলিফ্যান্টার রক কাট টেম্পলস। ১৮৭৪ সালে তিনি পশ্চিম ভারতের জন্য সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভেয়ার ও রিপোর্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী চার বছরে তিনটি চমৎকার খণ্ড প্রকাশ করেন: Report on the Antiquities of Belgam and Kaladgi District (১৮৭৪), Report on the Antiquities of Kathiawad and Kachh (১৮৭৬), এবং Antiquities of Bidar and Aurangabad Districts (১৮৭৮)। সবগুলোই চিত্রসহ সুসংগঠিত এবং কিছু ফটোগ্রাফ দ্বারা সমৃদ্ধ।
ফার্গুসনের History of Indian and Eastern Architecture এর সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকা লেখায় ১৯১০ সালে বার্গেস তার ফার্গুসনের সঙ্গে কটি বছরের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন—প্রায় দুই দশকের বেশি। এটি নির্দেশ করে যে দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রায় ১৮৬৬ সালের কাছাকাছি, যখন ফার্গুসন ১৮৮৬ সালে মারা যান।
নিচের অংশটির সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ শৈলী অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়া হলো—
ফটোগ্রাফসহ, এগুলো জ্ঞানমূলক দিক থেকে কানিংহাম এবং তার সহকারীদের সমসাময়িক কাজের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল, এবং মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের তথ্যভান্ডারকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। ১৮৮০ সালে বার্গেস ফার্গুসনের সঙ্গে যৌথভাবে Cave Temples of India প্রকাশ করেন, যেখানে ফার্গুসন নিজে স্পষ্ট করেছেন যে তার এবং বার্গেসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা ছিল: "তবে, বাস্তবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একমত না ছিলাম এমন কিছুই নেই।"
যতই বিশাল কাজ হোক, কিছু উপকরণ যা এতে স্থান পায়নি, তা ১৮৮৩ সালে দুইটি চমৎকার এবং সুসংগঠিত খণ্ডে প্রকাশিত হয়, যথা Report on the Buddhist Cave Temples এবং Report on the Ellura Cave Temples, যেখানে শিলালিপি বিশ্লেষণ করেন বিশিষ্ট লিখনবিশারদ জি. বুহলার। এদিকে, দক্ষিণ ভারত, যা স্থাপত্য-গবেষণায় পিছিয়ে ছিল, তা ১৮৮১ সালে বার্গেসের দায়িত্বের মধ্যে যুক্ত হয়, যখন তাকে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য সার্ভেয়ার এবং রিপোর্টার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।
তিনি পশ্চিম ভারতের জন্য হেনরি কাউসেন্স এবং দক্ষিণ ভারতের জন্য অ্যালেক্সান্ডার রেয়ার যোগ্য সহায়তাও secured করেন, এবং তারা একসাথে পুরো অঞ্চলে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানমূলক জরিপ সম্পন্ন করেন। ক্ষেত্র কাজের উপর মনোযোগ এবং অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বের কারণে প্রকাশনা কিছুটা ধীরগতিতে এগোয়। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য সম্পর্কিত কাজটি প্রকাশিত হয় Antiquities of the Town of Dabhoi in Gujarat (১৮৮৮), যা কানিংহামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বার্গেসের দায়িত্ব গ্রহণের তিন বছর পর প্রকাশিত হয়।
বার্গেস প্রকাশনার প্রতি এতটা মনোযোগী ছিলেন যে তিনি ১৮৮৯ সালে অফিস থেকে পূর্ববয়সে অবসর নেন, যাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। এরপর প্রকাশিত হয় Architectural Antiquities of North Gujarat (১৯০৩), যা কাউসেন্সের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত এবং মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০ সালে বার্গেস ফার্গুসনের History of Indian and Eastern Architecture এর নতুন, সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত, পুনর্বিন্যস্ত, সংশোধিত ও সম্প্রসারিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, যেটিতে তার নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে অনেক নতুন তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং যা এখনও ভারতীয় স্থাপত্যের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত।
তার দায়িত্বকালীন সময়ে বিপুল পরিমাণ উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল, এবং ১৯০৫ সালে তিনি তাদের প্রকাশের জন্য আবেদন করেন। ফার্গুসনের ইতিহাসের নতুন সংস্করণের ভূমিকা লেখায় তিনি ইতিমধ্যেই সার্ভে থেকে সহযোগিতার অভাবের অভিযোগ করছেন, যা তাকে ভারতীয় সেক্রেটারি অব স্টেটের মতো উচ্চ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চাইতে বাধ্য করে। চিহ্নগুলি স্পষ্ট ছিল। ভারতীয় স্থাপত্য অধ্যয়নের প্রাথমিক উজ্জ্বল পর্যায়ে সরকারি অবদানের প্রমাণ এইভাবে দৃশ্যমান।
০ জেমস ফার্গুসন এবং জেমস বার্গেস, Cave Temples of India, লন্ডন, ১৮৮০, পৃষ্ঠা xviii।
৩১ জেমস বার্গেস, “Sketch of Archaeological Research in India during Half a Century,” JBBRAS XXI, বিশেষ সংখ্যা (১৯০৫), পৃষ্ঠা ১৪৮।
ফার্গুসনের উদ্যোগে শুরু হওয়া কাজ, যিনি সবসময় ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতেন এবং সরকারের তেমন সহযোগিতা ছাড়াই এগিয়েছিলেন, শেষের দিকে পৌঁছেছিল। কাউসেন্সের প্রধান কাজগুলো, যা স্যার জন মার্শাল ডিরেক্টর-জেনারেল থাকাকালীন প্রকাশিত হয়েছিল, মূলত বার্গেসের অধীনে সম্পন্ন কাজের দীর্ঘ বিলম্বিত প্রকাশই বলা যায়।
ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের সকল পণ্ডিতের মধ্যে, যাদের কর্মকাণ্ড ভারতের স্থাপত্য গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বলা চলে যে বার্গেসের তুলনা করার মতো কেউ স্থাপত্য ইতিহাসে এত নিবেদিত ছিল না। এবং তার পদ্ধতি, যা প্রায় ফার্গুসনের সঙ্গে অভিন্ন, সরকারী স্থাপত্য গবেষণার দিকনির্দেশনাকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাবিত করেছে, ভাল বা মন্দের জন্য।
‘প্রত্নতত্ত্ব কেবল শিল্পের ইতিহাস’ (এটি কত আনন্দদায়ক শোনাচ্ছে এমন সময়ে, যখন অন্তত সকল প্রত্নতাত্ত্বিক এটি অস্বীকার করেন) তিনি ‘প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের একটি যথাযথ এবং সম্পূর্ণ চিত্র ও ইতিহাস প্রদান করার চেষ্টা করেছিলেন, মুহাম্মদীয় শৈলীর পতন পর্যন্ত’। তিনি এটি যে পরিমাণে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন, তা আশ্চর্যজনক। তবে বার্গেসের পদ্ধতিকে কানিংহামের সঙ্গে তুলনা করা ভুল হবে, কারণ এগুলো সুস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠ, এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি সরবরাহ করেছে ফার্গুসনের স্থাপত্য দর্শন।
বার্গেসের কাজ শিলালিপি উৎসের ব্যবহার বেশি করেছে, তবে এটি মূলত আকস্মিক বিষয়, সম্ভবত এই শাখার অধ্যয়নে প্রাপ্ত উন্নতির কারণে এবং তার সময়ের প্রধান শিলালিপি বিশেষজ্ঞদের, বিশেষ করে জি. বুহলার এবং জেমস ফ্লিটের সহযোগিতা লাভে তার প্রদর্শিত সুপরামর্শের কারণে। বার্গেস কানিংহামের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডাংশমূলক উপস্থাপনার স্বীকৃতি দেননি; তার আদর্শ ছিল যত্নসহকারে বিন্যস্ত এবং বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা, “‘মন্দিরগুলোর পূর্ণ এবং সঠিক বিবরণসহ, যা ইতিমধ্যেই জানা বিষয়গুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, আপেক্ষিক কালানুক্রমিক অবস্থান নির্দেশ করে, এবং সাধারণভাবে, এমনভাবে তথ্য সরবরাহ করে যাতে ইতিহাসবিদ ও শিল্পগবেষক উভয়ই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের গবেষণায় প্রাপ্ত আলোকের জন্য রিপোর্টগুলো ব্যবহার করতে পারে।’”
বার্গেস লক্ষ্য করতেন যে তিনি যা উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং সরকারের রিপোর্টের জন্য তাত্ক্ষণিক ফলাফলের দাবি মধ্যে বিরোধ ছিল—তার রিপোর্ট ঠিক তেমন হয়নি যেমনটি তিনি চাইতেন; তবুও তিনি তার ভ্রমণের ক্ষেত্রকে আরও সীমিতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, ফলে তার রিপোর্টগুলোতে সামগ্রিক একরূপতা আসে। তার প্রকাশনা, সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রচুর চিত্রসহ এবং উৎকৃষ্ট শিলালিপি অধ্যয়নের সমৃদ্ধি সহ, তাদের ধরনের নিদর্শন, এবং পণ্ডিতরা এগুলোকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এবং ব্যবহার করেন।
বার্গেসের প্রধান অর্জন ছিল বৃহৎ কাঠামোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা।
৩২ উদ্ধৃত: এস. রায়, Story of Indian Archaeology, নিউ দিল্লি ১৯৬১, পৃ. ৬৬।
৩৩ জেমস বার্গেস, Sketch of Archaeological Research, পৃ. ১৪৭।
ফারগুসনের দ্বারা নির্মিত ভারতীয় স্থাপত্য। ফারগুসনের কাজের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল, এবং তাতে কোনো আলোকপাতমূলক ধারণা যোগ করা হয়নি। যেখানে বার্জেসনে ফারগুসনের ‘দর্শনমূলক অনুসন্ধান’ করার প্রবণতা ছিল না, তার কাজ আরও বিস্তৃত ছিল, অধিক নির্ভরযোগ্য ও সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা উপকরণ সরবরাহ করেছিল, যার মাধ্যমে সে তার কাঠামোটি পরিবর্তন করতে, আরও বিস্তারিত দিতে এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলির কালক্রম স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তবুও সে ফারগুসনের ধর্মীয় শ্রেণীবিন্যাস বজায় রেখেছিল, যদিও ফারগুসন নিজেই এ নিয়ে অনিশ্চিত ও দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং বার্জেসনে যথেষ্ট নতুন স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কার করেছিলেন যা তাকে এই সমস্যার নতুনভাবে মুখোমুখি হতে পারত। তাই বার্জেসকে নতুন প্রয়াসের পথপ্রদর্শক বলার চেয়ে একজন নিবেদিত অনুসারী হিসেবে বর্ণনা করা ভুল হবে না। আমরা জানি যে সে ফারগুসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ করেছে, কিন্তু যেখানে ফারগুসনের জ্ঞানপ্রখরতা, চ্যালেঞ্জিং, চিন্তাপ্ররোচক এবং সাহিত্যিকভাবে অনবদ্য উপস্থাপনা ছিল, সেখানে বার্জেস একজন পদ্ধতিবদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, উদ্ভাবক নয়, স্থিতিশীল ও বাস্তবভিত্তিক, দক্ষতার সঙ্গে তার পরামর্শদাতাকে সমর্থন, প্রশস্তকরণ ও সহায়তা করেছেন। কৌতূহল জন্মায় যে, ফারগুসনের অপরিসীম শক্তি এবং প্রভাবশালী খ্যাতি কি নতুন চিন্তাভাবনাকে নিরুৎসাহিত করার প্রভাব ফেলেনি কি না, এবং আমরা লক্ষ্য করি যে, একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ই.বি. হ্যাভেল ছাড়া Few পশ্চিমা পণ্ডিতরা তার শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন।
ফলস্বরূপ, ফারগুসনের পর পশ্চিমা স্থাপত্যের অধ্যয়ন সবচেয়ে বিস্ময়করভাবে এবং বিভিন্নভাবে বিকশিত হলেও, ভারতীয় স্থাপত্যের, বিশেষ করে ভারতীয় সরকারি মহলে, অধ্যয়ন ফারগুসনের কাঠামোর মধ্যে নিরাপদভাবে আবদ্ধ মনে হয়। এটি নতুন বিকাশের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ দেখায়নি এবং ধীরে ধীরে একটি পশ্চাদপদায়ী অবস্থা হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় উৎসগুলি এখনও যথাযথভাবে এড়ানো হতো। বার্জেস ফারগুসনের মতোই রাম রাজের উল্লেখ সামান্য করেছেন, যা ত্রিশ বছর আগে ফারগুসন করেছিলেন, যা বিশেষভাবে আশ্চর্যজনক, কারণ বার্জেস কিছু সময় সত্রুঞ্জয়ায় কাজ করেছিলেন, যেখানে সক্রিয় ঐতিহ্যবাহী স্থপতিদের একটি সমৃদ্ধ বিদ্যালয় ছিল। ১৯০৩ সালে, বার্জেসের সহকারী হেনরি কুসেন্স যখন তার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে আরও বিস্তৃত ভারতীয় পদব্যবহার প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন, বার্জেসের প্রতিক্রিয়া কিছুটা নেতিবাচক ছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন, “এই পদগুলির মধ্যে খুব কমই আমাদের অভিধানে পাওয়া যায় এবং তাদের সঠিক রূপ ভারত ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।”
34 জেমস বার্জেস, Report on the Antiquities of the Belgam and the Kaladgi Districts, লন্ডন 1874, পৃ. 2। ক্যানিংহাম, “Essay on the Arian Order,” পৃ. 295 ইত্যাদি, রাম রাজের কাজ কিছুটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন কাশ্মীর স্থাপত্য বিশ্লেষণে, তবে খুব সফল হয়নি এবং পরবর্তী কাজগুলিতে সম্ভবত তিনি এই প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন।
35 জেমস বার্জেস এবং হেনরি কুসেন্স, Architectural Antiquities of North Gujarat, লন্ডন 1903, পৃ. Vi।
ফারগুসন তার ভারতীয় স্থাপত্য সংক্রান্ত রচনায় বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন আকারের উৎস সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রতি, যেখানে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান গুহামন্দিরগুলির কাঠের পূর্বসূরির দিকে, এবং বৌদ্ধ স্তূপের প্রবেশদ্বার ও রেলিং-এর দিকে, যা আমাদের চিন্তার অংশ হওয়ায় প্রায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই, তবে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন এটি এক ধরণের উদ্ভাবন ছিল। ডব্লিউ. সিম্পসন, ফারগুসনের অনুরাগী, যিনি ১৮৬১ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে Transactions of the Royal Institute of British Architects এবং Journal of the Royal Asiatic Society-এ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তিনি ভারতীয় স্থাপত্যের উৎস ও রূপান্তরের সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন আকারের সম্পর্ক এবং সেগুলি কীভাবে অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা সম্পর্কে অনেক আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফারগুসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে, তিনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং সতর্ক যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমস্যায় বেশ কিছু মৌলিক অবদান রেখেছিলেন। সিম্পসনের ধরনের কাজ অ-এ.এ. ম্যাকডোনেলের কল্পনাকে উৎসাহিত করেছিল, যিনি একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতপণ্ডিত, যিনি ভারতীয় মন্দিরের উৎস বৌদ্ধ স্তূপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে অনুসন্ধান করেছেন। ম্যাকডোনেলের মতে, এই বিকাশের প্রথম প্রগতি ছিল স্তূপের সাধারণ, দৃঢ় ও অর্ধ-সপ্তভূজ গম্বুজ, যা সিলিন্ড্রিকাল ড্রামের উপর বিশ্রাম করত, থেকে একটি দীর্ঘায়িত গম্বুজে রূপান্তরিত হওয়া, যার অভ্যন্তরে একটি কক্ষ থাকে, যেখানে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হয়।
পরবর্তী পর্যায়ে গোলাকার ড্রামটি একটি বর্গাকৃতি আকার গ্রহণ করেছিল, যা সেল্লার জন্য আরও উপযুক্ত ছিল, যখন মন্দিরের শিখর দীর্ঘায়িত গম্বুজ থেকে বিকশিত হয়, তার বক্রতা বজায় রেখে, এবং আমলাসারকা উদ্ভূত হয় ছাতার থেকে।** এ.এইচ. লংহার্স্ট, এই তত্ত্বটিকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে, ভারতীয় স্থাপত্যে ছাতার গুরুত্বকে অনেকটা অতিরঞ্জিত করেছিলেন।** তবে তার মন্তব্যগুলি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের উত্স সম্পর্কে আরও যুক্তিসঙ্গত ছিল, যেখানে তিনি “ডলমেন মন্দির” এবং স্তূপের সঙ্গে এর সম্পর্কের দিকে, ফারগুসন ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছিলেন এমন বিধির সঙ্গে, মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।
ফ.এস. গ্রোর্স, একজন অসাধারণ নাগরিক, যিনি Mathura, A District Memoir, 3য় সংস্করণ, 1883-এ লিখেছিলেন, ইতিমধ্যেই 1878 সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ( “Mathura Notes,” JASB XLVII (1878), পৃ. 114-115) সিখারার উৎপত্তি স্তূপে হতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন; একটি ধারণা যা ফারগুসন প্রথমে ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (Cave Temples of India, পৃ. 32), যদিও পরে সম্ভবত তিনি দ্বিতীয়বার ভাবেন (Archaeology in India, লন্ডন 1884, পৃ. 68-74)। গ্রোর্স দেশীয় স্থাপত্যের একজন বড় প্রবক্তা ছিলেন এবং বাস্তবে তিনি মথুরায় একটি অদ্ভুত রোমান ক্যাথলিক চার্চ স্থানীয় পদ্ধতিতে নির্মাণ করেছিলেন, যা ভারতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রাথমিক—যদিও কিছুটা অদ্ভুত—উদাহরণ।
এ.এইচ. লংহার্স্ট, “Influence of the Umbrella on Indian Architecture,” Journal of Indian Art XVI, No. 122 (অক্টোবর 1914), পৃ. 1-8।
“লক্ষ্য করা হলো।” যদিও ম্যাকডোনেল এবং লংহার্স্টের যুক্তি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে, তবু এগুলি স্থাপত্য সংলাপে একটি নতুন ধাপ নির্দেশ করে এবং আকর্ষণীয় ধারণায় পরিপূর্ণ।
ফারগুসন-বার্জেস পরম্পরা হেনরি কুসেন্স (১৮৫৪-১৯৩৪) এবং আলেকজ্যান্ডার রেয়া দ্বারা চালিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যারা উভয়ই বার্জেসের তত্ত্বাবধানে তাদের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, এবং তাদের কাজ স্পষ্টভাবে তার পদ্ধতির প্রতি ঋণী। রেয়া দুটি কাজ প্রকাশ করেছিলেন, একটি চালুক্য এবং অন্যটি পাল্লব স্থাপত্য নিয়ে, যেখানে স্মৃতিস্তম্ভের জ্ঞানকে ধৈর্য্যের সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে। কুসেন্স তিনটি বড় মনোগ্রাফ প্রকাশ করেছিলেন—একটি কানারে জেলার চালুক্য স্থাপত্য (১৯২৬), দ্বিতীয়টি সোমনাথ এবং কাথিয়াওয়াদের অন্যান্য মধ্যযুগীয় মন্দির (১৯৩১), এবং তৃতীয়টি ডেকানের মধ্যযুগীয় মন্দির (১৯৩১)—যা বার্জেস জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতেন; কারণ এগুলি তার পদ্ধতিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিল, প্রচুর চিত্র সহ উপস্থাপিত ছিল এবং শৈল্পিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপসংহারে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছিল। এই কাজগুলির একটি সমালোচনা হতে পারে যে শুধুমাত্র মন্দিরের দলগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে, কোনো পৃথক মন্দিরকে বিস্তৃত এবং বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও এটি হতাশাজনক যে কুসেন্সের ১৯০৩ সালের নিজস্ব প্রচেষ্টা, যেখানে তিনি ঐতিহ্যবাহী স্থপতি ও গ্রন্থের সঙ্গে কাজ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন, তা কোনোভাবে অনুসরণ করা হয়নি।
সেই সময়ে, যখন তার কর্মজীবন শুরু হওয়ার পর্যায়ে ছিল, কুসেন্স মনে হয় গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী সলাতদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছিলেন, যারা প্রাচীন কালের মহান স্থাপত্য সংঘের বেঁচে থাকা সদস্য ছিলেন, এবং তারা যে গুজরাটী স্থাপত্য গ্রন্থ ব্যবহার করতেন তা দেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে এগুলি জৈন মন্দিরের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত স্তূপ-শাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, “যেখানে এগুলি বড় বড় সিন্দুকের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণভাবে সংরক্ষিত।” কুসেন্স দ্রুত এদের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন: “পুরানো স্তূপ গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের যোগ্য, যাতে আমরা প্রাচীন পদ্ধতি এবং প্রাচীন নির্মাণের অবশিষ্টাংশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং সঠিকভাবে বুঝতে পারি। এগুলির স্থান ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এমন, যেমন ভিত্রুভিয়াসের স্থান পশ্চিমা কলায়।” তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে রাম রাজের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পরবর্তী প্রকাশ করা হয়নি।
39 §©6ASIAR, SC, 1915-16, পৃ. 28-35।
40 এ. রেয়া, Chalukyan Architecture of the Bellari District, মাদ্রাস 1896 এবং Pallava Architectures, মাদ্রাস 1909।
41 এই কাজগুলি সম্ভবত পূর্বে লেখা হয়েছিল, তবে প্রকাশ অনেক দেরিতে হয়েছে; 1931 সালের খণ্ডগুলি কুসেন্সের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে প্রকাশিত হয়, যখন তিনি তিরাশি বছরে ছিলেন, এবং সার্ভে থেকে অবসর গ্রহণের দুই দশকের বেশি সময় পরে।
42 জেমস বার্জেস এবং হেনরি কুসেন্স, Architectural Antiquities of North Gujarat, পৃ. 21-28।
® Ibid., পৃ. 27।
“4 Ibid., পৃ. 23।
উত্তর ভারতের গ্রন্থগুলির কথা তিনি জানতেন। এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যায় থাকা সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত পদগুলো প্রায়শই সাধারণ অর্থের থেকে ভিন্ন অর্থ বহন করত। তবু তিনি সম্ভবত কাজকর্মরত স্থপতিদের সহায়তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির একটি যথাযথ অনুবাদ প্রদান করেছিলেন, সাথে একটি আকর্ষণীয় স্তম্ভের চিত্র, যেখানে তার বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করা ছিল, ফলে স্তম্ভের বিভিন্ন উপাদান স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কুসেন্স কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন এই পদগুলো ব্যবহার করতে গুজরাট স্থাপত্য নিয়ে কাজ করার সময়, যার ফলে তার বর্ণনায় সেই মাত্রায় সঠিকতা এবং যথার্থতা এসেছে যা আগে পাওয়া যায়নি, এবং এটি নিশ্চয়ই এক কারণ যে কুসেন্সের কাথিয়াওয়াদ স্থাপত্যের কাজ চালুক্য বা ডেকান স্থাপত্যের কাজের তুলনায় আরও সন্তোষজনক।
কুসেন্স বিশেষভাবে স্থাপত্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অন্বেষণে ঐতিহ্যবাহী স্থপতিদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছিলেন, বিশেষত সিদ্ধপুরের ব্যাপকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত রিদ্রামহালয়ার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, যেখানে তিনি পুনরায় আধুনিক স্থাপত্য ইতিহাসবিদ এবং প্রথাগত স্থপতিদের মধ্যে ফলপ্রসূ এবং সহযোগিতামূলক কাজের পথ নির্দেশ করেছিলেন। তবে তার এই দিকনির্দেশনা, অন্তত পেশাদার প্রত্নতত্ত্ববিদদের দ্বারা অনুসরণ করা হয়নি, যারা স্মৃতিস্তম্ভের ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের কারণে এই পদ্ধতিকে সবচেয়ে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারতেন।
এদিকে, একটি ভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করেছিলেন খ্যাতনামা ফরাসি পণ্ডিত এ. ফুশের (১৮৬৫-১৯৫২)। ১৮৯৫-১৮৯৭ সালের মধ্যে করা বিস্তৃত ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর ভিত্তি করে তিনি গন্ধার শিল্প সংক্রান্ত তার বিশাল কাজ প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে ১৫০ পৃষ্ঠারও বেশি স্থাপত্য সম্পর্কিত।** তিনি বেঁচে থাকা স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের নিবিড় অধ্যয়ন করেছিলেন, যা, যেমন তিনি বিদ্রুপাত্মকভাবে উল্লেখ করেছেন, মিলিটারি ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগ থেকে রক্ষা পেয়েছিল, এবং রিলিফ ভাস্কর্যে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরনের ভবন বিশ্লেষণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি এগুলোকে বৌদ্ধ সাহিত্যিক প্রমাণের সঙ্গে, স্থাপত্যিক গ্রন্থ থেকে ভিন্নভাবে, সম্পর্কিত করে দেখতে পেরেছিলেন। এর ফলে তিনি শুধুমাত্র গন্ধারের স্থাপত্যই নয়, খৃষ্টপূর্বের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্যেরও খুব স্পষ্ট চিত্র আঁকতে সক্ষম হন।
এই অত্যন্ত তথ্যবহুল প্রবন্ধে তিনি সেই যুগের ভারতীয় স্থাপত্যকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হন, যেখান থেকে প্রায় কোনো স্মৃতিস্তম্ভ—যতোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক—অবশিষ্ট ছিল না; আরও গুরুত্বপূর্ণ, তিনি পরবর্তী মন্দির স্থাপত্যের বহু সমস্যা, বিশেষ করে উৎপত্তি সংক্রান্ত, আলোকিত করেছিলেন। অনুরূপ কাজ পূর্বে ফারগুসন কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন, যিনি প্রাথমিক ভারতীয় রিলিফ ব্যবহার করেছিলেন, এবং সিম্পসনও করেছিলেন, কিন্তু ফুশের এগুলিকে পরিপূর্ণভাবে বিশদভাবে প্রসারিত করেছেন।
9 Ibid., পৃ. 65।
© A. Foucher, L’art gréco-bouddhique du Gandhara, প্যারিস 1905, খণ্ড I, পৃ. 45-201।
ফারগুসনের পর থেকে ভারতীয় স্থাপত্যের অধ্যয়নে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী অবদানের মধ্যে একটি এসেছে আরেকজন ফরাসি পণ্ডিত, জি. জুভো-ডুব্রেইলের দ্বারা, যিনি ১৯১৪ সালে ড্রাবিড় স্থাপত্য ও আইকনোগ্রাফি নিয়ে তার চমৎকার দুই-খণ্ডের গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, যা বিশেষভাবে ফুশেরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।* প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণভাবে স্থাপত্যকে উৎসর্গিত এবং এটি কেবল তামিলভাষী অঞ্চলের মন্দিরগুলিকেই আড়াল করেছে, যা কোরোম্যান্ডেল উপকূল বরাবর পুলিক্যাট হ্রদ থেকে কেপ কোমোরিন পর্যন্ত বিস্তৃত।* গুহামন্দির এবং উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির তুলনায়, দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য এখনও খুব কম মনোযোগ পেয়েছিল, এবং ফারগুসনের অধ্যয়ন, যা অগভীর পরিচিতির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল, সংক্ষিপ্ত, বিস্ময়করভাবে তুচ্ছ এবং পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের উৎপত্তি বৌদ্ধ বীধ্রার সঙ্গে সহজে সম্পর্কিত হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, তবে তা ছাড়া তিনি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেননি।
যদিও বার্জেস এটি স্বীকার করে দক্ষিণ ভারতের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলির একটি জরিপ শুরু করেছিলেন, যা আর. সিউয়েল দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং পরে এ. রেয়া অনুসরণ করেন, যার ফলে একটি তালিকা এবং পল্লব স্থাপত্যের একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়, উভয়ই মূলত বর্ণনামূলক, বিশেষত পরে খণ্ডটি ভাল পরিকল্পনা এবং উচ্চতার সঙ্গে উপস্থাপিত,** প্রকৃত অগ্রগতি অপেক্ষা করছিল জুভো-ডুব্রেইলের জন্য। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে ভাল ফটোগ্রাফ ও বর্ণনা স্থাপত্য অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গঠন করলেও, শুধুমাত্র বর্ণনা এবং বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যা তুলনা ও পদ্ধতিগত শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ নিয়ম আবিষ্কার করতে সহায়ক: “‘I] importe de faire l’anatomie et la paléontologie des edifices.’”*
জুভো-ডুব্রেইল যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন ড্রাবিড় স্থাপত্যের শৈলীর ভিত্তি গঠনের নিয়ম আবিষ্কারের জন্য, তা ছিল অলঙ্কারিক নকশার তুলনামূলক অধ্যয়ন। প্রথমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নকশাগুলির সেট আলাদা করেছিলেন, যা অর্ডারগুলোকে যথাযথভাবে গঠন করে, কুড্ডালোরের তিরুপাপ্পুলিয়ুর মন্দিরের নির্মাতাদের থেকে লিখিত বা মৌখিকভাবে বিভিন্ন অংশের সঠিক স্থানীয় নাম সংগ্রহের মাধ্যমে। পরবর্তীতে, যেসব মন্দিরের শিলালিপি অনুযায়ী সঠিকভাবে তারিখ নির্ধারণযোগ্য, সেগুলো বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রতিটি ড্রাবিড় মন্দির শৈলীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত নকশার নিখুঁত প্যাটার্ন নির্ধারণ করতে সক্ষম হন এবং এভাবে সমস্ত ড্রাবিড় স্থাপত্যকে কালানুক্রমিক ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করেন।
ড্রাবিড় মন্দির স্থাপত্যের অধ্যয়ন জুভো-ডুব্রেইলকে পরবর্তীতে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে, প্রতিটি সময়কালে কেবল একটি শৈলী বিদ্যমান ছিল, যা তিনি বেশ ভারসাম্যপূর্ণভাবে “la principe du synchronisme des monuments dravidiens” হিসেবে অভিহিত করেন, ফলে স্থাপত্য ইতিহাসবিদের কাজ অনেক সহজ হয়, যেটি অনেক শৈলী থাকলে যেমন ফরাসি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে হতে পারে।
দ্রাবিড় মন্দির স্থাপত্যকে পল্লব (সা. খ্রিস্টাব্দ ৬০০-৮৫০), চোলা (সা. খ্রিস্টাব্দ ৮৫০-১১০০), পাণ্ড্য (সা. খ্রিস্টাব্দ ১১০০-১৩৫০), বিজয়নগর (সা. খ্রিস্টাব্দ ১৩৫০-১৬০০) এবং মাদুরা (সা. খ্রিস্টাব্দ ১৬০০-এর পরবর্তী) শৈলীতে বিভক্ত করে, জুভো-ডুব্রেইল শৈলীর পার্থক্যগুলোর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন যে এটি তামিল অঞ্চলের বাইরের কোনো প্রভাবের কারণে হয়েছে এবং উল্টোভাবে বলেন যে দ্রাবিড় স্থাপত্যের অলঙ্কারিক নকশাগুলো কোনো চালুক্য, ইসলামি বা বিজয়নগর প্রভাবের অধীনে নয়। দ্রাবিড় শৈলীর ১৩০০ বছরের ইতিহাসে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা হয় প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে—‘voie d’évolution naturelle’; অথবা জীববৈজ্ঞানিক অনালজির মাধ্যমে বলতে গেলে, “দ্রাবিড় স্মৃতিস্তম্ভের রূপরেখা আমাদের শেখায় যে স্থাপত্য আকারগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন প্রাকৃতিক মানববিজ্ঞান দেখায় যে মানুষের череп প্রায় বানর-সদৃশ রূপ থেকে বর্তমান রূপের মধ্যে সমস্ত মধ্যবর্তী পর্যায় পার হয়েছে। মাদুরার মন্দির শৈলী এবং তাঞ্জোর বিমানার শৈলীর মধ্যে পার্থক্যও তেমনই, যেমন বর্তমান মানুষ এবং ক্রো-ম্যান রেসের মধ্যে পার্থক্য।”*
জুভো-ডুব্রেইল পরবর্তীতে তার নামকরণ সংশোধন করে ৮৫০-১১০০ সময়কালকে প্রারম্ভিক চোলা এবং পাণ্ড্য শৈলীর বেশিরভাগ অংশ, ১১০০-১৩০০, পরবর্তী চোলা হিসেবে উল্লেখ করেন।
জুভো-ডুব্রেইল বিশেষভাবে এই অনালজিগুলোর প্রতি অনুরাগী ছিলেন: “যেমন একই প্রজাতির সব প্রাণীর বৈশিষ্ট্য একরকম, তেমনি একই যুগের সব পাগোডা একরকম,” এবং তিনি স্থাপত্যকেও উপাদান ও সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর দৃষ্টিতে দেখেছেন, যেমন প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর নিয়মের অধীন থাকে।
32 Ibid., পৃ. 5।
33 Jouveau-Dubreuil, Dravidian Architecture, Madras 1917, পৃ. 36।
54 Jouveau-Dubreuil, Archéologie du sud de l’Inde, খণ্ড I, পৃ. 8, 9, 154।
মন্দির, প্রসাদ, পুরুষা হিসেবে পূজিত হওয়া উচিত। একটি পরবর্তী গ্রন্থ, সিল্পরত্ন, এটি এত সহজ কথায় বলে। কিন্তু সেই পুরুষা কী, যারূপে মন্দির পূজিত হওয়া উচিত? পবিত্র কাঠামোর ধারণা, মণ্ডপ, এবং পরবর্তীতে মন্দির হিসাবে পুরুষা, তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে পাঠ্যগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, এবং এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি কেবল বিদ্যমান নয়; এটি বহু শৈলীতে, ভারতের বিভিন্ন অংশে, যুগে যুগে মন্দিরের প্রকৃত স্বরূপ গঠন ও সংজ্ঞায়িত করে।
প্রতিটি শিল্পরূপ, প্রতিটি মহান পরম্পরা কিছু ধরণের অনুমানের উপর ভিত্তি করে; যদি আমরা এগুলোকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধি, ধর্মীয় প্রেরণা বা প্রকাশনা বলতে না চাই, আমরা কেবল এগুলোকে অনুমান বলি। এবং পুরুষার এই মৌলিক অনুমান ভারতীয় চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিশীল রূপকে ঋগ্বেদ থেকে onward আকৃতির দিক থেকে আকার দিয়েছে। এখানে আমরা মূলত আকারের প্রতি, স্থাপত্যকে আকার হিসাবে, একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে আগ্রহী, যা নিজের স্পর্শযোগ্য, দৃশ্যমান মাধ্যমের দ্বারা সেই সর্বব্যাপী ধারণা, পুরুষা, সমতুল্য রূপ তৈরি করে।
পুরুষা কে বা কী? ঋগ্বেদ ১০.৯০ বলে, তিনি সমস্ত জগৎ। তাঁর মধ্য থেকে জন্ম নেয় বিরাজ, এবং বিরাজ থেকে জন্ম নেয় পুরুষা। এই স্ব-উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্ক কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন। পুরুষা কে? পুরুষা হল মানুষ, কিন্তু এখানে মানুষ একটি রেফারেন্সের টার্ম, নিকটস্থ, যদি আমরা অভিজ্ঞতা করি, অনুভব করি এবং আভাসমূলকভাবে চিন্তা করি কিছু এমন কিছুর দিকে যা আকারের বাইরে। কারণ কি না সৃষ্টি করা আকারের বার্তা হলো যা সমস্ত আকারের বাইরে তা প্রকাশ করা?
পুরুষা, যা আকারের বাইরে, হলো প্রকাশের প্রতি উদ্দীপনা।
এই প্রকাশের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞ হয় মানুষের চিত্রে—সুপেরনাল মানুষ, আদিম মানুষ, বা “মানুষ হিসাবে সৃষ্টিশীল উদ্দীপনার” চিত্রে। তবে এই সৃষ্টিশীল উদ্দীপনা, একবার অনুভূত এবং ধারণা করা মাত্রই, তা অবিলম্বে উৎপাদনশীল বা প্রজননশীল হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্য থেকে জন্ম নেয় বিরাজ। বিরাজ হলো মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা, যা প্রকাশের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে; এবং সেই মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধিমত্তা থেকেই পুনরায় সেই উদ্দীপনা স্ব-উৎপাদনশীলভাবে জন্ম নেয়। এই সম্পর্কের চিরন্তন, চরম যুক্তি মাইক্রোকসম হিসেবে অভিজ্ঞ মানুষ থেকে projected হয় তাঁর…অভিজ্ঞ মাইক্রোকসমে এটি projected হয়। মানুষ ও মহাজগত—এই দুইয়ের মধ্যে এটিই একমাত্র প্রাধান্য। প্রতিটিতে পুরুষা ও বিরাজের সম্পর্ক একই। তারা সেখানে বিদ্যমান, এবং সৃষ্টির মুহূর্তে এক অপরের উপস্থিতি পূর্বধারণা হিসেবে থাকে। তারা হলো উদ্দীপনা এবং তার নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধিমত্তা, যেখানে latter উদাহরণস্বরূপ, পূর্বের মধ্যে latent এবং imperative উভয়ভাবেই বিদ্যমান।
অগ্নি পুরাণ, সিল্পরত্ন-এর চেয়ে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, বলে যে মন্দিরের প্রভাব, শক্তি (শক্তি), এবং আকার (আকৃতি) হলো প্রকৃতি। প্রকৃতি হলো আদিম পদার্থ, সেই পদার্থ যা পদার্থ হওয়ার আগে পদার্থ ছিল, পদার্থের নীতি।
পদার্থের নীতি, তার প্রভাব, শক্তি, যা আকারে প্রকাশিত, তা বিরাজের সঙ্গে সমন্বিত হয়, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। পদার্থ নিজেই পরিমাপিত। যা কিছু পদার্থগত, তার নিজস্ব পরিমাপ, সীমা, এবং ক্রম থাকে; এই ক্রম মহাজগতে মন্দিরে প্রতিফলিত হয়, যা মানুষের কাজ, এবং মানুষ সন্তুষ্টি পায় যখন সে ধরে নেয় যে স্রষ্টা মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন। মন্দির হলো প্রক্রতির মাধ্যমে কল্পিত পুরুষা।
অগ্নি পুরাণ, প্রায় একইভাবে বলে, “মন্দিরের দরজা হলো তার মুখ; স্কন্ধ, বা সুপারস্ট্রাকচারের ট্রাঙ্ক শেষ হওয়া মঞ্চ, হলো পুরুষার কাঁধ; ভদ্রা, বা প্রক্ষেপণ, হলো বাহু; এবং এভাবে দেয়াল, জায়গ, বা ‘পা’, এবং সবচেয়ে নীচের ছাঁচ (পদ্দুক) পর্যন্ত, হলো পা। মানুষের দেহের এই এবং অন্যান্য একক অংশের নামগুলো মন্দিরের কাঠামোগত উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে এগুলোর অবস্থান বা অনুপাত মন্দিরের দেহে মানুষের দেহের সঙ্গে মিলিয়ে বা পুনঃরেফারেন্স করার উদ্দেশ্য নয়। অগ্নি পুরাণ আরও বলে যে মন্দিরের প্রতিমা, বা প্রতিমূর্তি, মন্দিরেরই জীব, মন্দিরেরই প্রাণ। এই ধরনের উল্লেখ মূলত প্রতিমারূপ; এগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে নেওয়া হয় না; এগুলো রেফারেন্সের পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে যাতে আমরা সেই সত্তার জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতে এবং দেখতে পাই, যাকে পুরুষা বলা হয়।
অন্যান্য গ্রন্থ, প্রাচীন ও পরবর্তী, যেমন বিষ্ণুসংহিতা এবং শিল্পরত্ন, প্রসাদের বৈরাজ রূপ সম্পর্কে কথা বলে, পুরুষাকে বিরাজ হিসেবে, অর্থাৎ স্থাপত্যের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্রম, পরিমাপ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্য হিসেবে জোর দেয়। এখানেও, মুখ, মস্তক বা মাস্তক, জায়ঘড় বা পা—অর্থাৎ মধ্যবর্তী উল্লম্ব দেয়াল—সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কেবল বাহ্যিক চিহ্ন, যা পুরুষার জীবন্ত উপস্থিতি নির্দেশ করে।
প্রতিমা বা লিঙ্গের মাধ্যমে অভিহিত এই নীতির, জীবের, জীবন্ত উপস্থিতি স্থপতির দ্বারা মন্দিরের কাঠামো, তার ধারণা এবং আকারে অনুবাদ করা হয়, এমনকি সর্বশেষ উদাহরণগুলিতেও, এমনকি যেগুলো শিল্পগত দিক থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত নয়, যেমন চিত্তরের জৈন মন্দির। সেখানে পর্যন্ত প্রকাশক উদ্দীপনাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পুরুষার নীতি দৃশ্যমান রূপে নির্মিত হয়েছে।
মন্দিরটি পুরুষার উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ, যা মন্দিরের বাহ্যিক অংশে প্রকাশ পায়। এর প্রভাব কেবল ভরের ওপর নির্ভর করে, এবং ভর এমনভাবে স্তূপিত করা হয়েছে যাতে তা দৃশ্যত, গতিশীলভাবে সংহত হয়; একটি আকার অন্যটির ওপর বিশ্রাম নেয়, শারীরিক চাপ বা প্রকৃত উত্তেজনা ছাড়া, তবে সমস্ত স্তরে এটি সকল দিকে প্রসারিত হয় এবং দৃশ্যত এর প্রভাব উপরের দিকে। নাগরা শৈলীর সবচেয়ে বিশদ মন্দিরগুলোতে, এই গতিশীল আন্দোলন একদিকে সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ভবনের কেন্দ্র, সবচেয়ে অভ্যন্তরীণ অভয়ারণ্যের দিকে, পুনঃপ্রবেশী কোণে সংগঠিত থাকে।
মূলত, প্রসাদা হিসাবে পুরুষা বাহ্যিক দিক থেকে দেখা হওয়ার জন্যই তৈরি। অভ্যন্তরে রয়েছে কেবল গর্ভগৃহ, বা গর্ভ-কক্ষ, একটি সরল, ঘনাকার স্থান, যার বাইরে যেমন সমৃদ্ধ অলংকরণ নেই। এর রহস্য মানুষের মধ্যে নারীশক্তির ক্ষেত্রে নিহিত, কারণ এটি গর্ভধারণ, সৃষ্টির এবং রূপান্তরের স্থান, ভ্রূণ এবং নতুন জন্মের স্থান, যেখানে দেবতা প্রতিমা বা প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত হয়। সন্দহারা প্রসাদে, যেখানে গর্ভগৃহ অভ্যন্তরীণ পথের জন্য একটি দ্বিগুণ প্রাচীরের মধ্যে সংরক্ষিত, তা কেবলমাত্র গর্ভগৃহের সরলতার মৌলিক রহস্য এবং বহির্ভাগের জটিল সংগঠনের মধ্যে বৈপরীত্যকে প্রতীয়মান করে, এখানে প্রসাদ প্রাচীরের দ্বিগুণ বাহ্যিক স্তর।
প্রসাদকে পুরুষা হিসাবে দেখানো গ্রন্থগুলো মানব দেহের অংশের নাম স্থাপত্যগত গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে যুক্ত করার বাইরে যায় না, যা সম্পূর্ণভাবে কেবল বাহ্যিক দিক থেকে দেখা যায়। উচ্চতম সুপারস্ট্রাকচারের কোনো অভ্যন্তর নেই, কারণ এটি দেখা হওয়ার জন্য নয়। এটি সাধারণত সমতল ছাদের মাধ্যমে গর্ভগৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন।
তবু, প্রসাদা হিসাবে পুরুষার মোট ধারণা স্থপতির দ্বারা স্থাপত্যের মাধ্যমে আকার পায়। স্থাপত্যিক বিষয় ও নকশার ক্রম ও সংহতি এমনভাবে গঠিত হয় যেন তা মানুষের দেহের ত্বকের মতো ঘনবদ্ধ আবরণ গঠন করে। স্থাপত্যিক বিষয় ও নকশার যুক্তি বা প্যাটার্ন একাধিক উপাদানের দ্বারা বজায় রাখা হয়, যেখানে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত উৎস বিভিন্ন নিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যা অনুপাত ও ছন্দের সংবেদন অনুযায়ী স্থল ও সময় অনুসারে পরিবর্তিত হয়।
কিছু সর্বব্যাপী, সমগ্র ভারতীয় নকশা হলো বক্রাকার গবাক্ষ বা জানালা, ফুলদানি বা কুম্ভ, ছাদের প্রান্ত বা ছদ্য; অন্যান্য, যেমন ডমলক, যার বৃত্তাকার আকৃতিতে ইখারার ভর সংরক্ষিত, এবং সিখর, শুধুমাত্র নাগরা শৈলীর জন্য স্বতন্ত্র, যা প্রধান মন্দির রূপ এবং কেবল দক্ষিণ ভারতকে বাদ দিয়ে সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত।
এই সমস্ত আকার মূলত একটি কাঠামোর কার্যকর অংশ ছিল। মন্দিরে এবং এর প্রাচীরে এগুলো প্রতিফলিত হলেও, যদিও মূল কার্য সম্পাদন না করলেও, কিছু কার্যকরী অর্থ ধরে রাখে: উদাহরণস্বরূপ, গবাক্ষ এখানে সর্বদা একটি কঠিন আকার হিসেবে থাকে, প্রসাদের যে কোনো স্থানে খোদাই করা হতে পারে, তার অর্থ শুধুমাত্র তখনই বজায় থাকে যখন মানুষের বা প্রাণীর মাথা এর বক্রাকার ফ্রেমের মধ্যে খোদাই করা হয় এবং এই জানালা থেকে বাইরে তাকায়।
মন্দির প্রাচীরের জীবন্ত, অর্থাৎ স্থাপত্যগতভাবে জীবন্ত আবরণের অংশ হিসেবে এই এবং অন্যান্য নকশার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলো হলো:
(১) মূল আকারের হ্রাস, স্মৃতিস্তম্ভের আকারের অনুপাতে এবং একই মন্দিরে একই নকশার আকারের আরও অনুপাতে হ্রাস;
(২) সমান আকারের পুনরাবৃত্তি উল্লম্বভাবে বা অনুভূমিকভাবে, অথবা উভয়ভাবে;
(৩) একটি সম্পূর্ণ নকশাকে অংশে ভাগ করা;
(৪) তৃতীয় মাত্রায় একটি আকারের উপর অন্য আকার স্থাপন;
(৫) একটি নকশা বা থিমকে অন্য ধরনের থিম বা নকশার মধ্যে খোদাই করা; এবং
(৬) একাধিক থিমকে উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে সন্নিবেশ বা একত্রিত করে একটি জটিল নতুন সত্তা তৈরি করা।
মূল আকারের হ্রাস, তা সম্পূর্ণ ভবনের হোক বা এর অংশের, দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যে সবচেয়ে প্রাধান্যপুষ্ট স্মৃতিস্তম্ভে প্রতিফলিত হয়, যেখানে বিমানার সুপারস্ট্রাকচার বা এর বিভিন্ন তলা (ভিত্মি) ছোট মন্দির (বা ঘর) আকারে সাজানো থাকে। এই এডিকিউলগুলি, যেগুলোর আকার অনুসারে কিতা, কোষ্ঠা ইত্যাদি নামে পরিচিত, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে, যেমন মহাবলিপুরমে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে সারিবদ্ধ হয়, যেখানে তাদের বর্গাকার এবং আয়তাকার আকার পরিবর্তিত হয়, প্রতিটি স্তরে এডিকিউলের মালা গঠন করে (প্লেট ১)।
উপরের স্তরে স্তূপিত এডিকিউলগুলির অনুভূমিক সারিবিন্যাস জটিল ত্রিমাত্রিক প্যাটার্ন তৈরি করে, যা আলো এবং ছায়ার অন্তরালে আরও ফুটে ওঠে, এবং দিনের বিভিন্ন সময় ও ঋতুর সঙ্গে এর গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়, সূর্যের আলোকে তাদের সমতলগুলিতে প্রয়োগ করে। এডিকিউলগুলোর ধারাবাহিক ক্রম এবং এর বাতাসের ফাঁকসমূহ একটি খাঁজযুক্ত প্রান্তরূপ গঠন করে, যা প্রাথমিক ড্রাবিড় মন্দিরের সুপারস্ট্রাকচারের আকারের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন গাছের ছাল। ছাল এবং ত্বকের মতো স্থাপত্যিক আবরণও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এর বার্ধক্যের চিহ্ন এডিকিউলগুলোর আকারের সংকোচন বা শিথিলতার ফলে উদ্ভূত হয়। এদের আপেক্ষিক আকারও পরিবর্তিত হয়; তারা কেবল অপেক্ষাকৃত ছোট হয় না, বরং সপ্তম শতাব্দীর পল্লব মন্দিরের তুলনায় আরও সমতল হয়ে যায়। তারা তাদের ত্রিমাত্রিক সম্পূর্ণতা, কঠিন প্রান্তের সূক্ষ্মতা এবং সরলতা হারায়। কখনো আর দেবীয় বাসস্থানের বাড়িগুলোর সেই কাল্পনিক পর্বতমালা এত স্পষ্টভাবে প্রসাদকে ঈশ্বরের অভয়ারণ্য ও দেহ হিসেবে ঘোষণা করতে দেখা যায়নি।
যেখানে নির্দিষ্ট আকারের বিভিন্ন পর্যায়ের হ্রাস বুদ্ধিবৃত্তিক স্বভাবের—যাতে মাপযোগ্য রূপে একটি শ্রেণিবিন্যাস বা মূল্যায়ন প্রকাশ পায়—সেখানে একই আকারের ছোট আকারের পুনরাবৃত্তি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার আরও জীবন্ত উৎস থেকে উদ্ভূত হয়, যা বারবার নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকে আসে, নির্বাচিত আকার ও তার অর্থের মাধ্যমে মাপযোগ্য অন্তরালে। ছন্দের পরিমাপযোগ্য, পরিমাণগত প্রকৃতি দিক নির্ধারণ করে, তবে তাতে তীব্রতার পরিবর্তনও অন্তর্নিহিত থাকে, যেমন স্রোত ও জোয়ারের ক্ষেত্রে, যেখানে একটিও অপরের থেকে আলাদা নয় এবং প্রতিটি পরবর্তীটিকে পূর্বাভাস দেয়।
হ্রাস এবং পুনরাবৃত্তির নীতি বা নিয়মগুলো একত্রে এবং প্রায় অনন্ত পর্যন্ত কাজ করে, যেমন সুপারস্ট্রাকচারের নিম্নতম তলায় সাজানো অপেক্ষাকৃত বড় এডিকিউলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা এর সর্বোচ্চ স্তর গঠনের এডিকিউলগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়।
গবাক্ষের নকশা, যা এডিকিউল থেকে আলাদা কারণ এটি সাধারণত ঘনাকার আকারের নয়, বিভিন্ন আকারের ক্রমবিন্যাসে ব্যবহার করা হয়, সুকান্দসার স্মৃতিস্তম্ভমূলক চওড়া আর্ক থেকে—যা দীর্ঘকাল টিকে থাকা এবং এমন একটি হলের ফ্যাগেডের বড় জানালার রূপান্তর, যেমন বৌদ্ধ চ্যাট্যাহল—প্রসাদের সুপারস্ট্রাকচারে প্রসাদের প্রবেশদ্বারের ওপর, সর্বনিম্ন ‘ডরমার জানালা’ নকশা পর্যন্ত, যেটি সিখর, প্রাচীর, প্লিন্থের ছাঁচ বা এন্টাবলেচারে খোদাই করা হয়, সংক্ষেপে, প্রায় প্রতিটি অংশে। মূলত জানালা হওয়ায়, অর্থাৎ ফ্যাগেডের অংশ হওয়ায়, গবাক্ষের বক্রাকার আকার এডিকিউলের ত্রিমাত্রিক প্রভাব রাখে না। এটি সাধারণত, একক বা সারিতে, যে পৃষ্ঠাকে এটি দখল করে তার অংশ। যখন বিভিন্ন আকার ও জটিলতার গবাক্ষ উপরে স্তূপিত হয়, সারিগুলি অনুভূমিকভাবে চলে, অথবা—and এটি গবাক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত কার্য—অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় সারিতে গবাক্ষ ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়, সম্পূর্ণ প্যানেল তৈরি করে গবাক্ষের মাঠে।
সপ্তম শতাব্দী থেকে, যেমন এলোরার গুহা X-এর ফ্যাগেডে দেখা যায়, গবাক্ষ অক্ষুণ্ণ থাকে না (প্লেট ২)। এর বক্ররেখা বিভক্ত হয়, ফলে তৈরি অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং একটি স্পষ্ট ব্যবধান রেখে পুনরায় মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। মূল কার্য থেকে মুক্ত নকশাটি অন্যান্য উদাহরণে স্তম্ভের আকারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যার উল্লম্ব আকৃতি ঘনভাবে সংযুক্ত গবাক্ষের মাঠে উল্লম্ব মাত্রা যোগ করে। অথবা, ছোট গবাক্ষগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। একটি আবরণ ছায়ার মতো, প্রসাদের দেয়ালগুলো তাদের ধারাবাহিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আবৃত হয় (প্লেট ৩)। ক্রমবর্ধমান বড় প্যানেলে এর প্যাটার্ন একটি দৃশ্যমানভাবে শ্বাস নেওয়া আবরণ হিসাবে গঠন করে, যেখানে তাদের জালিকায় স্থান আটকানো হয়।
বিশেষত কর্ণাটক অঞ্চলে চালুক্য স্থপতিরা সত্যিকারের সৃষ্টিশীল যুক্তিতে গবাক্ষ নকশার সম্ভাবনাকে তার একটি রূপান্তমুলক উপসংহারে অনুসরণ করেছেন। তারা জটিল লিনিয়ার প্যাটার্নে গবাক্ষের জালে খেলানো আলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রতিটি গবাক্ষের খোলায় স্থানকে ধরে অন্ধকারে প্রবাহিত করেছেন। তারা “জানালার” খোলা স্থানগুলো ধাপে ধাপে গ্রেড করেছেন, উল্লম্ব পৃষ্ঠের একটি বিমূর্ত ক্রমে, প্রতিটি খোলা বা চোখের মতো অংশে অন্ধকারের একটি কূপের মতো পিছিয়ে।
মূল থিম বা নকশার ক্রমবর্ধমান অনুপাতের আকারে হ্রাস, এই হ্রাসকৃত আকারগুলোর এক বা দুই মাত্রায় পুনরাবৃত্তি—অর্থাৎ এককভাবে, সারিবদ্ধভাবে সংযুক্ত বা সম্পূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করা—যেখানে পুরো নকশা বা বিভক্ত নকশা ডিজাইনের ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এবং তৃতীয় মাত্রায় সমতল নকশার গভীরতা, অর্থাৎ স্থানদেখার জন্য নয় বরং ধাপে ধাপে প্রসাদের তন্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত হওয়া: এই সমস্ত নীতিকে বিভিন্ন স্তর এবং সংমিশ্রণে আকার দেওয়া হয়েছে এবং গবাক্ষ নকশাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিশীল ডিজাইনের বিস্ফোরণে প্রকাশিত হয়েছে।
এই নকশা আরও স্তূপিত হতে উপযুক্ত ছিল এবং মোল্ডিং-এর উপর সর্বোচ্চ ভাস্কর্যগত জোর হিসেবে দেখা যায়, যার বক্ররেখা তাদের মূল ছাদের কার্য প্রকাশ করে। যখন এটি স্তূপিত হয়, কেবল এককভাবে নয়, বরং পুরো গবাক্ষ ক্ষেত্র হিসেবে, এটি একটি লেইস পর্দার মতো উপরের খোদাই করা ছাদের পুনরাবৃত্তি ও সংযুক্ত আকারের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। এগুলো গবাক্ষ ক্ষেত্রকে বহন করে, যার প্রান্ত ধরে চলে, মোল্ডিং হিসেবে অনুভূমিকভাবে সমান্তরাল, উল্লম্বভাবে staggered ক্ষুদ্র ছাদ প্রান্তের নকল করে, যার রেখা এবং তাদের মধ্যে থাকা স্থান মাছের শ্বাস নেওয়ার গিলের কাঠামোর কথা মনে করায়।
যেখানে পূর্বোক্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত সমতল এবং ত্রিমাত্রিক প্যাটার্ন ও টেক্সচারের নীতি ক্রমাগত বিভিন্ন সংমিশ্রণে জড়িয়ে নতুন ইউনিটে একীভূত হয়, যেমন গবাক্ষ নেট দিয়ে আচ্ছাদিত ছাদের রেখাযুক্ত ক্ষেত্র, সেখানে অন্য একটি—বিশেষত ওড়িশার—নকশা উল্লেখযোগ্য, যা অনুরূপ নীতি অনুসরণ করে। এটি প্রসাদের প্লিন্থ দখল করে, যেখানে পাত্রাকৃতির (কুম্ভ) এবং অন্যান্য মোল্ডিং উপরের বক্ররেখার মাধ্যমে সংযুক্ত, যা স্থাপত্যিক “রিলিফ”-এর সর্বোচ্চ সমতলে সূক্ষ্মভাবে লতাপাতার মতো খোদাই করা।
একটি থিমকে অন্য থিম বা নকশার অধীনস্থ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বা খোঁচানো নীতির প্রচলন দীর্ঘস্থায়ী বা বিস্তৃত নয়, যদিও ইতিহাসে এটি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে পিতলখোরা বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলিতে (প্লেট ৪) থেকেই। সেখানে একটি ভল্টযুক্ত মন্দিরের ফ্যাগেড একটি স্টূপার ট্র্যাবিয়েট, সরলরেখাযুক্ত হরমিকার মধ্যে খোদাই করা হয়েছে। সমানভাবে স্পষ্ট হলো মহাবলিপুরমের কিছু মন্দিরে (ভীম রথ, নকুল ও সহদেব রথ) ভল্টের প্রোফাইল দ্বারা আবৃত এবং রিলিফে খোদাই করা গম্বুজাকৃতির মন্দিরগুলি (প্লেট ১)। এই উদাহরণগুলিতে, একটি থিমের অন্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি বা অধীনতা একটি দিকে অন্য থিমের মধ্যে, অন্যদিকে একটি হ্রাসকৃত আকারের থিমকে মূল স্মৃতিস্তম্ভের পূর্ণ আকারের অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি প্রধান থিম বা নকশার দ্বারা বেষ্টিত।
এই নীতি তিন-মাত্রিকভাবে প্রয়োগ করে, কয়েক শতাব্দী পর নাগরা সিখরের বক্ররেখাযুক্ত উত্থানে, এই উঁচু টাওয়ার নিজস্ব আকারের ক্ষুদ্র বহুগুণ তৈরি করে উচ্চ রিলিফে বা প্রায় ত্রিমাত্রিকভাবে তিন-চতুর্থাংশে, প্রতিটি এবং সমস্তই বৃহত্তর আকারের অধীনস্থ এবং সম্পূর্ণ সিখরের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত (প্লেট ৫)। অংশ-সিখরাগুলি (যাকে চেস্ট সিখরা বা উরোসর্ঙ্গা বলা হয়), প্রতিটি অর্ধেক সিখরা এবং সম্পূর্ণ আকারের একটি উপ-বহুগুণ, পুরুষার “চেস্ট”-এর সাথে সংযুক্ত, যার সঙ্গে প্রসাদের সুপারস্ট্রাকচারের অংশ হোমোলজাইজড। এই উপ-সিখরাগুলি, সম্পূর্ণ সিখরের নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত উচ্চতায় পৌঁছায়, এবং ক্ষুদ্র সিখরাগুলিতে গ্রেড করা হয় (প্লেট ৩), যার উচ্চতা আসল উচ্চতার একটি ছোট অংশ মাত্র, এবং এগুলো অনুভূমিক সারিতে সাজানো যায়, প্রতিটি পুরো সিখরার আকারের ক্ষুদ্র মডেল, গবাক্ষ নেটওয়ার্ক, অ্যামালাকা এবং অন্যান্য থিম ও নকশাসহ, উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সংযুক্ত, যা প্রসাদের সব অংশে প্রয়োগ করে এবং এর বহির্ভাগকে পুরুষার সৃষ্টিশীল আবরণে রূপান্তরিত করে। এই নীতির নিখুঁত আকারগত সংহতি দেখায় প্রসাদের জীব, জিভা, স্থাপত্যের প্রতিটি কণিকায়, প্রতিটি সুনির্দিষ্ট ইউনিটে অবস্থিত।
প্রসাদা হিসাবে পুরুষা শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং বিরাজ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধিমত্তা দ্বারা আচ্ছন্ন, যা গর্ভগৃহের কেন্দ্রে থেকে চারদিকে প্রসারিত হয়। এর প্রভাব দৃশ্যমান হয় বাট্রেসে, তাদের কেন্দ্রবাহ্য ক্রমায়ন এবং কেন্দ্রমুখী অবকাশে (প্লেট ৬)। প্রতিটি সমতলপর্যায় পরপর স্থাপত্যিক জীবন্ততা দ্বারা পরিচালিত, যা দেয়ালের ত্রিমাত্রিক টেক্সচারের প্যাটার্ন থেকে, পুরুষার দেহের রূপে প্রকাশ পায়।
প্রভাষঙ্কর ও. সোমপুরা
বিশ্বকর্মার বাস্তুবিদ্যা
১। ভূমিকা
পশ্চিম ভারতীয় বাস্তুভিদ্যা গ্রন্থটি, যার রচয়িতা, মধ্যযুগীয় পশ্চিম ভারতীয় বেশিরভাগ গ্রন্থের মতো, দেব স্থপতি বিশ্বকর্মাকে ধরা হয়, মারু-গুজরাতা স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্পের ঐতিহ্যের একটি হারানো গ্রন্থ। আজকের আলোচনায় আমি সেই অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্তসার দেব যা মন্দিরের নির্মাণসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
বর্তমান সহস্রাব্দের প্রথম তিন শতকে, যখন অনহিলাপাতক ও অন্যান্য রাজবংশের সোলাঙ্কি রাজারা পশ্চিম ভারত শাসন করতেন, তখন মধ্যযুগীয় মারু-গুজরাতা স্থাপত্যের শৈলী গুজরাট ও রাজস্থানে সম্পূর্ণ আধিপত্য রাখত। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানরা পশ্চিম ভারত দখল করলে এই ঐতিহ্য কিছুটা হ্রাস পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং পুনরায় সতেরো শতাব্দীর প্রারম্ভে এটি পুনর্জীবিত হয়। এগারো শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক থেকে অলংকারশিল্পে ধীরে ধীরে পতন শুরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতেই ফর্মাল সৌন্দর্য এবং মাপের সঠিকতায় অবনতি দেখা দেয়। তবু এই বিপর্যয় সত্ত্বেও ঐতিহ্যটি এখনও টিকে আছে। আমি এই ঐতিহ্যের একজন উত্তরাধিকারী প্রচারক। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের বিশেষজ্ঞদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আনন্দিত।
পশ্চিম ভারতের মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য টিকে রয়েছে মূলত সিলপিনদের নির্মাণবিধি সংরক্ষিত থাকার কারণে এবং জৈন সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। এই নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য নির্মাতাদের অতীত দিনের শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারলেও, এটি অন্তত মাপ নির্ধারণে সহায়ক হয় এবং মোল্ডিং খোদাই করার সময় নির্দেশিকা দেয়, যার ফলে নির্মাণকৌশলের আকারগুলো ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে মূল স্থাপত্যরূপের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য বহন করে।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ঐতিহ্যবাহী শৈলীতে মন্দির নির্মাণ কিছুটা কালবৈষম্যমূলক মনে হয়। প্রাচীন নির্মাণবিধির কোডগুলো আজকের দিনে মন্দির নির্মাণে যতটা ব্যবহার হয় না, তার চেয়ে বেশি সহায়ক হয় মন্দিরের আকার ও নকশা বোঝার ক্ষেত্রে—সেই যুগের নির্মাণশিল্পের ভাষায়, যা মধ্যযুগীয় সময়ে মহৎভাবে নির্মিত হত। স্থাপত্যসংক্রান্ত সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া নতুন গ্রন্থসমূহ দর্শন প্রসারিত করার জন্য একটি স্বাগতযোগ্য উৎস প্রমাণিত হবে এবং এর মাধ্যমে মারু-গুজরাতা মন্দিরের কারিগরি ও রূপগত দিকগুলোর সূক্ষ্মতর মূল্যায়ন সম্ভব হবে।
ভাস্তুভিদ্যার অস্তিত্ব আমার কাছে সন্দেহজনক হয়ে ওঠে যখন আমি অন্য একটি মারু-গুজরাতা গ্রন্থ দীপর্ণাভা নিয়ে কাজ করছিলাম। কিছু অধ্যায়ের শেষে কিছু পাণ্ডুলিপিতে সংক্ষিপ্ত কলোফন দেখা যায়, যা জানায় যে এগুলো বিশ্বকর্মার ভাস্তুভিদ্যা নামক একটি কাজের অংশ বা এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এম. এ. ধাকি দ্বারা এর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে দীপর্ণাভা সম্ভবত ষোড়শ শতকে গঠিত একটি সংকলন; এটি অনেকাংশে ভাস্তুভিদ্যা এবং অপরাজিতপ্রচা থেকে ধার করেছে, এবং কম পরিমাণে আরও দুটি গ্রন্থ, ক্ষীরার্ণব এবং বৃক্ষর্ণব থেকেও উপাদান গ্রহণ করেছে। পরে দেখা গেছে, দীপর্ণাভা-তে ভাস্তুভিদ্যার অংশগুলি প্রায়শই মূলের সংক্ষিপ্ত সারাংশ বা কিছু ক্ষেত্রে আনুমানিক অনুলিপি হিসেবে উপস্থিত, পূর্ণাঙ্গ এবং অপ্রচলিত পাঠের সংখ্যা খুব কম।
দীপর্ণাভা-র ভাস্তুভিদ্যার অংশ ভাষা, বিশ্লেষণ এবং বিষয়বস্তু পরিচালনার ক্ষেত্রে, মোটামুটি কারিগরি শব্দভাণ্ডার ও বিষয়বস্তু বাদ দিলে, মারু-গুজরাতা ঐতিহ্যের সুপরিচিত কর্তৃত্বপূর্ণ গ্রন্থ অপরাজিতপ্রচা-র থেকে ভিন্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি পশ্চিম ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদ্যমান উদাহরণ এবং অন্যান্য পশ্চিম ভারতীয় স্থাপত্যগ্রন্থের সাদৃশ্য অনুসারে, বিশেষ করে অপরাজিতপ্রচা-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল, এবং ধাকি ও আমি ভাস্তুভিদ্যার মূল গ্রন্থ অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
যে কোনও একক, প্রামাণিক পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় হতাশা এখনও আছে, যা ওই কাজের সংযুক্ত অধ্যায়গুলো প্রদান করতে পারত। তবে এই ব্যর্থতা আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে সৃজনরত্নকোষ নামের একটি সম্মিলিত সংকলন থেকে ভাস্তুভিদ্যার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ বলে মনে হওয়া অধ্যায় আবিষ্কারের মাধ্যমে। আরও সহায়তা এসেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে, যার মধ্যে আমার নিজের সংগ্রহও রয়েছে, যেগুলো যথাযথভাবে ভাস্তুভিদ্যার সত্যিকারের অংশ হিসেবে শনাক্ত করা গেছে।
ভাস্তুভিদ্যা সম্ভবত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়েছে।
প্রকাশিত হয়েছে, পালিতানা, ১৯৬০।
বিশেষত অধ্যায় ৪–৯।
দেখুন, তাঁর “Introduction to Prasadamafijari,” The Vastusastras of Western India, আমার সম্পাদনায় এবং বর্তমানে মুদ্রণাধীন।
তথ্যবিস্তারিত আলোচনার জন্য একই উৎস।
বাস্তুবিদ্যা সম্ভবত খুব প্রাথমিক সময়ে বিভক্ত হয়েছে, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের পর খুব বেশি সময় নয়। বাকি এই গ্রন্থের রচনার সবচেয়ে সম্ভাব্য সময় হিসেবে একাদশ শতকের শেষাংশ বা দ্বাদশ শতকের প্রথমাংশ নির্দেশ করেছেন।
যখন থেকে আমরা এই গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছি, আমরা মূল কাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যতটা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে চলেছি। গ্রন্থটির একক, প্রামাণিক পাণ্ডুলিপি অনুপস্থিত থাকায়, পাঠের মূল অধ্যায়ের ক্রম এখনও অনিশ্চিত। আমরা এও জানি যে, মূল গ্রন্থের অন্তত একটি অংশ, যদিও খুব বড় নয়, এখনও অনুপস্থিত; তাই ভবিষ্যতে যদি কোনও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তা আমাদের অনুমানকে ব্যাহত করতে পারে, এজন্য আমরা অধ্যায়ের ক্রম নিয়ে অনুমান করতে চাই না।
আমি গ্রন্থের সমালোচনামূলক উপকরণে বা এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে বিস্তারিতভাবে থামব না। এটি প্রকাশিত চিত্রিত সংস্করণের ভূমিকায় উপস্থাপিত হবে, যা ধাকি ও আমি শীঘ্রই প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছি।
গ্রন্থটি প্রচলিত সংলাপ রূপে রচিত। এই ক্ষেত্রে, জয়া—বিশ্বকর্মার চারটি মনোজন্ম সন্তানের প্রথম—প্রশ্ন উত্থাপন করে, এবং বিশ্বকর্মা উত্তর প্রদান করেন। পাঠ্যের ভাষা সরল সংস্কৃত; শৈলী সুস্পষ্ট, অপরাজিতপ্রচা-র চেয়ে বেশি সুরময়, কিন্তু সমরঙ্গণসাস্ত্রধারার সূক্ষ্ম, প্রতিধ্বনিমূলক, গতিশীল শৈলীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। পাঠ্যের প্রাথমিক অধ্যায়গুলো সাধারণত অনুষ্ঠান, জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং নাগরিক স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করে থাকে। আমাদের অনুসন্ধানের সময় এই কয়েকটি অধ্যায় উদ্ধার হয়েছে; তবে আমি এখানে তা আলোচনা করব না, কারণ আমি শুরুতে যেমন উল্লেখ করেছি, আমার তাত্ক্ষণিক আগ্রহ মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো উপস্থাপন করা।
II. স্থাপত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার—জগতিলক্ষণাধ্যায়
মন্দিরকে সমর্থনকারী জগতি, অর্থাৎ ছাদ বা প্ল্যাটফর্ম, নির্মাণ সংক্রান্ত বিবেচনায় মন্দিরের নিজস্ব স্থাপনার চেয়ে প্রাধান্য পায়। ভাস্তুভিদ্যা-তে, সাতত্রিশ শ্লোকের মধ্যে, জগতির পরিকল্পনা, ক্রম এবং অনুপাতমূলক মাত্রাসহ বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে, এবং জগতির নিসে স্থাপনযোগ্য প্রতিমার বিবরণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি অন্যান্য মারু-গুজরাতা গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্যমান মন্দিরগুলিতে তা পরিচিত। এছাড়াও জগতির সিঁড়িতে স্থাপনীয় প্রতিধ্রা (প্রতিমা) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোট রয়েছে। জগতির প্রাথমিক বর্ণনা একটি শৈব মন্দিরের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু তার পরপরই একটি বিষ্ণু মন্দিরের জগতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে জগতির সাথে সম্পর্কিত দেবতাগুলো বৈষ্ণব প্যানথিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এরপর চণ্ডিকা এবং জীনা মন্দিরের জগতির বিবরণ আসে।
জীনা জগতি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়, কারণ এটি মধ্যযুগীয় জীনা মন্দিরের জগতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনা প্রদান করে। এতে ভল্ডনকা (প্রবেশদ্বার হল), চব্বিশ দেবকুলিকা (চ্যাপেল) এবং তাদের জগতির ওপর বিন্যাসের ক্রম, ত্রিকা (ভেস্টিবিউল), মণ্ডপ (হল) এবং প্রসাদ (মূল মন্দির) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পিঠলক্ষণাধ্যায়
পিঠলক্ষণ (প্ল্যাটফর্ম বা ভিত্তির চরিত্র) সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ত্রিশ দুইটি শ্লোকে বিস্তৃত। এটি যথেষ্ট বিস্তারিত এবং অপরাজিতপ্রচা-র সমজাতীয় এবং অধিক পরিচিত অংশের সঙ্গে তুলনীয়। অপরাজিতপ্রচা-র মতো নয়, প্রধান ধরনের পিঠার বিস্তারিত বর্ণনা ভাজিপিঠা বা অশ্বপিঠা (ঘোড়া-বন্ধনী) মোডুলিংকে বাদ দেয়। এরপর তিন ধরনের অন্যান্য পিঠার বর্ণনা আসে, যার মধ্যে একটি ভাজিপিঠাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরে, বিভিন্ন দেবতার মন্দিরের জন্য যে পিঠা নির্মাণ করা যেতে পারে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। শেষাংশে, পিঠার নির্মাণে ত্রুটি থাকলে যে ফলাফল হতে পারে তার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
বাস্তুবিদ্যা অবাক করার মতোভাবে মন্দিরের প্রাচীরের জন্য প্রচলিত মধ্যযুগীয় শব্দ মন্দোবর এর পরিবর্তে প্রাচীন শব্দ কাটি ব্যবহার করেছে। এই অধ্যায়ে মন্দিরের প্রাচীরের উচ্চতা মন্দিরের প্রস্থের সাথে সম্পর্কিত অনুপাত, সালিলন্তর (মধ্যবর্তী ফাঁক), ফলান্দস (প্রধান বৃদ্ধির ছোট প্রক্ষেপণ), এবং খুরা (খুর), কুম্ভ (মাটকা), কলস (পিচার), অন্তরপত্র (গভীর ফিলেট), এবং কপোতিকা (সাইমা-কর্নিস) এর অনুপাত ও অলংকারমূলক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এরপর আসে মাসিরাকা (পেডেস্টাল) এবং জঙ্গা (ফ্রিজ) এর বিস্তারিত বিবরণ। মাসিরাকা শব্দটি, যা অপরাজিতপ্রচা-তে পাওয়া মাফিসিকা এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে, তা লক্ষণীয়। জঙ্গা-তে প্রতিটি ভদ্র (মধ্যবর্তী অফসেট) এ একটি খট্টক (প্রক্ষেপিত নিস) থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খট্টক শব্দটি দিলওরা এবং কুম্ভারিয়ার জীনা মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায়, তবে এ পর্যন্ত পরিচিত ভাস্তু গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়নি।
ভদ্রদেব (প্রধান নিসে থাকা প্রতিমা) এর মধ্যে, দক্ষিণের নিসে শিব-অন্ধকবধ, পশ্চিমে নটেশ্বর এবং উত্তরে চণ্ডী প্রতিস্থাপনের প্রচলিত সূত্রও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, যদিও বাক্যরীতি অপরাজিতপ্রচা থেকে পৃথক। কিন্তু এখানে একটি বিকল্পও দেওয়া হয়েছে (যা অপরাজিতপ্রচা-তে নেই), যা তিনটি প্রধান নিসে যথাক্রমে পুরুষত্রয় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব) এর প্রতিমা স্থাপনের বিধান দেয়; এটি কিছু মারু-গুজরাতা মন্দিরে দেখা যায়।
পাঠে আরও উল্লেখ আছে রাঠকা (ফ্রেমযুক্ত প্যানেল), দিকপাল এর প্রতিমা যা জঙ্গা-র কর্ণ অংশে স্থাপন করতে হবে, এবং মুনি (ঋষি) প্রতিমা যা সাম্প্রদলকোণা (ফাঁকা কোণা) তে রাখা হবে। মনে রাখা যায় যে অপরাজিতপ্রচা-ও এই বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করেছে। প্রায় একাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে পশ্চিমী ভারতীয় মন্দিরে সালিলন্তর-এর পরিবর্তে মুনি প্রতিমা প্রদর্শন শুরু হয়।
ভদ্র অংশগুলিতে, নিসের শীর্ষে, ভাস্তুভিদ্যা পরবর্তী সুপারিশ দেয় সিংহকর্ণ (পেডিমেন্ট) স্থাপনের। মনে রাখা যায় যে অপরাজিতপ্রচা একই অংশের জন্য উদগম শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। এরপর আসে সুর-পর্যায়ের বিবরণ: যথাক্রমে ভারনা (ক্যাপিটাল), (উপরের) গ্রাসপাত্তিকা, কপোতালি (ছাদ-কর্ণিস) এবং কিতাচ্ছাদ্য (রিবযুক্ত ছাউনি)। পাঠটি সংক্ষিপ্ত ভাষায় কাটি এর বিকল্প অনুপাতও প্রস্তাব করে। অধ্যায়টি শেষ হয় নিয়মিত সতর্কবার্তার মাধ্যমে, যা নির্দেশিত অনুপাত অবহেলার ফলাফল সম্পর্কে জানায়।
সিখরালাক্ষণাধ্যায়
এই অধ্যায়টি একত্রে ঊনত্রিশ (২৯) শ্লোকে মারু-গুজরাতা সিখরা এর আকারগত দিক সম্পর্কে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। প্রথমে সিখরার পরিকল্পনা, এর বিভাজন—ভদ্র, কোণা (কোণ), এবং অনুগ (প্রতীরথ)—এর অনুপাত, রেখা (কোণ বাঁক) এর সূক্ষ্ম বিবরণ, স্কন্ধ (কাঁধ) এর অনুপাতিক প্রস্থ, এবং রেখা-চিত্রের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা বিবেচনা করা হয়। এখানে একটি খুব স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে: ভিমি সংখ্যা অবশ্যই বিসম (বেজোড়), তিন থেকে পনেরো পর্যন্ত হতে হবে। এরপর আসে গ্রিভা (গলা), ডমলাসারক, চন্দ্রিকা (শীর্ষ-পাথর), ডমলাসারিকা (ছোট ডমলাসারক) এবং কালগা (পিচার-ফিনিয়াল) এর বিবরণ। এর পরে সংক্ষিপ্তভাবে প্রসাদ পুরুষ—ব্যক্তিত্ববদ্ধ মন্দির—এর এবং সিখরা-দেহে তার সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাঠটি এরপর পঁচিশ ধরনের রেখা তালিকাভুক্ত করে। তবে, সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি।
[৭] দেখুন M.A. Dhaky, “The Chronology of the Solanki Temples of Gujarat,” Journal of the Madhya Pradesh Itihas Parishad, No. 3 (1963), পৃ. 26।
ধ্বজালাক্ষণাধ্যায়
অধ্যায়টি পতাকা ও তার দণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে; সিখরার অনুগ স্তরের উচ্চতায় এবং মন্দিরের অভিমুখের সাথে সম্পর্কিত অবস্থানে পতাকা স্থাপনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাঠে বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন চতুর্মুখ প্রাসাদ (চারমুখী মন্দির) এ পতাকা দণ্ডের অবস্থান সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এরপর পতাকার জন্য অন্যান্য শুভ স্থানগুলির নামোল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ফোরানা, সুকনাসা (সিখরার ফ্রন্টনের অ্যান্টেফিক্স), এবং ভাল্ডনাকা।
পাঠে পতাকা দণ্ডের পাঁচটি ভিন্ন প্রমাদানা (অনুপাত) উল্লেখ করা হয়েছে: জয়া (ত্রিপার্ব, ‘‘ত্রিনোডাল’’), শক্তীরিপা (পেন্টাপার্ব, ‘‘পেন্টানোডাল’’), সুপ্রভা (সপ্তপার্ব, ‘‘সেপ্টানোডাল’’), জয়বাহা (নবপার্ব, ‘‘এনিয়ানোডাল’’), এবং বিশ্বরূপা (বহুপার্বসামান্যবিত, ‘‘মাল্টিনোডাল’’)।
পাঠ সতর্ক করে যে, পতাকা বিহীন মন্দিরে রাক্ষসরা বাস করতে প্রলুব্ধ হয়।
দ্বারালাক্ষণাধ্যায়
দরজার কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি যথেষ্ট বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে উনত্রিশ (২৯) শ্লোক অন্তর্ভুক্ত। অপরাজিতপ্রচা এর তুলনায় এখানে ভাস্তুভিদ্যা সংক্ষিপ্ত হলেও, কিছু নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে পাওয়া গেছে যা অপরাজিতপ্রচা তে নেই।
দরজার সখাস (ফেসিয়া) এর মধ্যে রয়েছে রূপ (চিত্রবাহী), পাত্র (পাতার মতো ভাঁজবাহক), এবং খালভা (গহ্বরযুক্ত) প্রকার। এই নামগুলো অপরাজিতপ্রচা তেও পাওয়া যায়। তবে, পরের পাঠে মধ্যবর্তী রিপাস্তম্ভ (চিত্রবাহী কলাম) কে ভদ্রসখা (কেন্দ্রীয় জাম্ব) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি দরজার সখাসগুলির অনুপাত বিশটি অংশ হয়, পাঠ নির্দেশ করে যে আটটি অংশ নিগারা (ফ্রেমযুক্ত, উঁচু প্যানেল) এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে; নিগারার ডান পাশে থাকবে নন্দি এবং বাম পাশে মহাকালা, শিবের দুই সহচর। এটি সাইভ মন্দিরের নিয়ম। নিগারার উপরে তিন বা চারটি স্তরযুক্ত রথিকা (ফ্রেমযুক্ত প্যানেল) তে শিবের আকার খোদাই করতে হবে। এই প্যানেলগুলোর উপরে থাকবে ভারনা (ক্যাপিটাল) যা পল্লব (পাতা) দ্বারা সজ্জিত। দরজার উত্তরঙ্গ (আর্কিট্রেভ) এ খোদাই করা থাকবে মল্লাধারাস (ফুলের মালা বহনকারী) এবং কেন্দ্রস্থানে বিনায়ক।
[১] এখানে ব্যবহৃত নামগুলো অপরাজিতপ্রচা তে পাওয়া নামের থেকে ভিন্ন (তুলনা, অধ্যায় ১৪৪, প্রকাশিত: গয়েকওয়াড ওরিয়েন্টাল সিরিজ XV, বারোদা, ১৯৫০)। [২] তুলনা দেখুন অধ্যায় ১৩০-১৩১ এবং ১৩২।
গ্রহদের সঙ্গে প্যানেলে যেভাবে পাঠ নির্দেশ করে, তেমনভাবেই অধিষ্ঠায়ক রূপ (উপাস্য দেবমূর্তির প্রতিরূপ) খোদিত হওয়া উচিত। এই বিবরণগুলি বাস্তব উদাহরণেও বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
এরপর পাঠে উদুম্বর (দোরসিল)-এর রূপগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উদুম্বরকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে—মধ্যবর্তী অংশে থাকবে পদ্মডাঁটা এবং তার উপরে পদ্ম। এর দুই পাশে খোদিত থাকবে (উন্নত) গ্রাসমুখ এবং এদের বাইরের দিকে থাকবে ধনদা ও বিনায়কের মূর্তি। পরবর্তী অংশে পাঠ শিল্পীদের কঠোরভাবে ফাঁকাগুলোর (শাখা) সন্নিবেশের নিয়ম মানতে নির্দেশ দেয়; এতে ব্যর্থতা নির্মাতার মৃত্যু এবং স্থপতির নিঃসন্তান হওয়ার কারণ হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। শেষে অর্ধচন্দ্র, অর্থাৎ দোরসিলের নিকটস্থিত চন্দ্রাকার পাথরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে; এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর মধ্যবর্তী অর্ধবৃত্তাকার প্রধান অংশের দুই পাশে উদ্ভাসিত খোদাইয়ে পদ্ম ও শঙ্খের রূপ অঙ্কিত থাকবে।
কোলিকালক্ষণাধ্যায়
কোলিকা, যাকে কপিলিও বলা হয়, হল সেই প্রাচীর যা মূল প্রাসাদকে (মন্দিরের গর্ভগৃহসহ প্রধান স্থাপনা) মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত করে। উভয় শব্দই অপরাজিতপ্রচ্ছা-তেও পাওয়া যায়। বাস্তুবিদ্যা এখানে নির্দিষ্ট বিবরণ প্রদান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মূল প্রাসাদের সঙ্গে তুলনামূলক বিভিন্ন অনুপাত।
কোলিকে কর্ণে (প্রান্তীয় কোণে) সজ্জিত করতে হবে। এটি যেন কর্ণের মাত্রার অর্ধেক অতিক্রম না করে বা তার মধ্যভাগে প্রবেশ না করে। কোলির উপরে স্থাপন করতে হবে সুকনাসা। নাসা-বিহীন মন্দিরের কোনো গুরুত্ব নেই।
এরপর পাঠে মূল প্রাসাদের তুলনায় কোলিকার পরিমিতির অনুপাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদি এটি মূল প্রাসাদের অর্ধেক মাপের হয় তবে সেটি শ্রেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ); যদি এক-চতুর্থাংশ হয় তবে মধ্যম (মধ্য্যম); আর যদি এক-তৃতীয়াংশ হয় তবে সাধারণ (কনিয়স)। যেখানে জ্যেষ্ঠ অনুপাতের কপিলি থাকে সেখানে মণ্ডপের উপস্থিতি অনিবার্য। এর নির্গম (প্রক্ষেপণ) ভাবনার ক্ষেত্রে কোনামার্যাদা, অর্থাৎ কোণের সন্নিবেশরেখা, অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। জলান্তর (অন্তঃরেখা/রিসেস) প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রেও কোনামার্যাদা অনুসরণ করতে হবে। যারা কোলির মধ্যভাগে জলান্তর পরিকল্পনা করতে চায় তারা অল্পবুদ্ধি—পাঠে এ-রূপ মন্তব্য করা হয়েছে।
১০ — অপরাজিতপ্রচ্ছা-এ উক্ত অংশের জন্য ব্যবহৃত মন্দারক শব্দটি এখানে উল্লিখিত হয়নি।
আমি মনে করি মোধেরা সূর্যমন্দিরের (খ্রিস্টাব্দ ১০২৭) গর্ভগৃহের দোরসিলে কুবের ও বিনায়কের মূর্তি দেখা যায়।
মণ্ডপ-লক্ষণাধ্যায়
এই অধ্যায়ে রতি (নৃত্য) বা নৃত্য-প্রকারের মারু-গুর্জর মণ্ডপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যদি মণ্ডপের পরিমাপ প্রসাদ (মন্দিরগৃহ)-এর সমান হয় তবে তা ‘কণিয়স’; যদি তা এক-চতুর্থাংশ বেশি হয় তবে তা ‘মধ্যম’; যদি তা অর্ধেক বেশি হয় তবে তা ‘উত্তম’। Vastuvıdya বলে যে, যদি মণ্ডপের শীর্ষাংশ যুক্তিসংগতভাবে শুকনাসার চূড়ার নিচে রাখা যায়, তবে মণ্ডপ প্রসাদ থেকে দ্বিগুণ বড় করা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। মণ্ডপের পীঠ মন্দিরগৃহের পীঠের সমান উচ্চতার হতে পারে, অথবা কিছুটা কমও হতে পারে। মণ্ডপের উচ্চতার অলঙ্করণসমূহ ক্রমানুসারে হলো— রাজসেনক (গভীর ফিলেট, উচ্চতায় এক অংশ), বেদিকা (রেলিং, এক-ও-তিন-চতুর্থাংশ), কাটাকার (অর্ধাংশ), এবং মাত্তাবরণ (আসনের পিঠ, এক-ও-দেড় অংশের)। কাটাকার ফলকের উপর, অর্থাৎ আসনপট্টকার উপর, [বামন] স্তম্ভটি তিন-ও-দেড় অংশ উচ্চতায় নির্মিত হওয়া উচিত। এর ভরণ (মূলাধার/ক্যাপিটাল) হবে অর্ধাংশ এবং শীর্ষ (ব্র্যাকেট) হবে এক-ও-তিন-চতুর্থাংশ অংশ উচ্চতায়। এর প্রস্থ পট্ট (বিম)-এর অধিবিমের প্রস্থের সমান হওয়া উচিত।
দণ্ডচ্ছদ্য (পাঁজর-আঁটা ছাউনি), যা লintel-এর উপরে থাকে, তার উচ্চতা হবে অর্ধাংশ এবং প্রস্থ দুই অংশ। এর ঢালু অপরপ্রান্ত পট্টোদর (লেন্টেলের অধিবিম)-এর উপরে এক-বারো ভাগ অংশ থাকবে। দণ্ডচ্ছদ্যের উপরে তিন অংশে কাপোটালি (কার্নিস-ছাউনি) নির্মিত হওয়া উচিত। বর্তমান গ্রন্থে মণ্ডপের উচ্চতা-রূপায়ণে মাত্র চৌদ্দটি শ্লোক উৎসর্গিত হয়েছে। অপরাজিতপ্রচ্ছা এই বিষয়ের আলোচনায় তুলনামূলকভাবে আরও নির্দিষ্ট।
কারোটক-লক্ষণাধ্যায়
ক্যারোটকার (মণ্ডপের বিশাল উল্টো-বাটি-আকৃতির, খাঁজকাটা ও কোফারযুক্ত কেন্দ্রীয় ছাদ) আলোচনা আরও সম্প্রসারিত। এটি মোট বিয়াল্লিশটি শ্লোক জুড়ে বিস্তৃত। ছাদের পরিকল্পনা, ছাদের অলঙ্করণ যেমন দারদরী (উল্টো সাইমা), ঋজুপকণ্ঠ (মূর্তি-ধারক বেল্ট),
১২ এমন কোনো মধ্যযুগীয় মণ্ডপের উদাহরণ জানা যায় না যা মন্দিরের দ্বিগুণ বড়, গুজরাতে। ধাক্য আমাকে জানান যে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় উন-এ (চৌবাড়েদারা মন্দির নং ২, একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ) মালবায়, খাজুরাহোর চিত্রগুপ্ত মন্দিরে (একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ), এবং কীড়াড়ুর সোমেশ্বর মন্দিরে।
এমনটাই দেখা যায় কোটাইয়ের শিব মন্দিরের গূঢ়মণ্ডপে এবং মোধেরার সূর্য মন্দিরের রাজগৃহমণ্ডপে।
এটি আসনপট্টকার বহির্মুখী অংশ।
অপরাজিতপ্রচ্ছা ও অন্যান্য কিছু গ্রন্থেও এই সদস্যকে ‘কক্সাসন’ বলা হয়েছে।
১৬ দেখুন অধ্যায় ১৮৪।
নিচের অংশে উল্লেখিত কোলাস (শূকরের-দাঁতের আকৃতির কর্স) এবং কেন্দ্রীয় পদ্মকেশর (পরাগনালার নালি)–এগুলোর খোদাইরীতি, প্রতিটি মোল্ডিং-এর উপবিভাগ এবং তাদের আনুপাতিক পরিমাপ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—বাস্তবে সামরাঙ্গণসূত্রধার বা অপরাজিতপৃচ্ছার তুলনায় আরও বেশি মাত্রায়।¹⁷
মারু-গুর্জর মন্দিরের সভামণ্ডপে যে সম্বরণ বা ঘণ্টার আকৃতির ছাদ দেখা যায়, তা দশম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ নাগাদ রাজস্থান এবং গুজরাট—দুই জায়গাতেই প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হয়।¹⁸ অল্প কিছু পরে মালবা, জেজাকভুক্তি এবং গোপগিরীতেও নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্বরণ-রীতি বিকশিত হয়।
বাস্তুবিদ্যা প্রথমে সম্বরণের প্রস্থের অনুপাত অনুসারে তার উচ্চতা নির্ধারণ করে। যদি উচ্চতা প্রস্থের অর্ধেক হয়, তাকে বলে বামন; যদি নয় ভাগে ভাগ করা সেই উচ্চতা থেকে দুই ভাগ কম হয়, তবে অনন্ত; আর যদি তিন ভাগ কম হয়, তবে বরাহ। এগুলো নির্মাতার জন্য শান্তি, মঙ্গল এবং স্বাস্থ্য নিয়ে আসে। সম্বরণের উচ্চতা নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়।
পাঠ্যটি এরপর ভিত্তি-পরিকল্পনার রেখাগত পরিমাপ অনুসারে ঘণ্টাসংখ্যা নির্ধারণ করে এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আকারের নির্দিষ্ট নিয়ম দেয়। তারপর সম্বরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়—যেমন ভদ্রার উপরে স্থাপিত রথিকা এবং তিলক (সভামণ্ডপের মডেল), কূটর (ক্ষুদ্র ঘণ্টা) এবং ঘণ্টিকার (বৃহৎ ঘণ্টা)-এর ক্রমবিন্যাস, মূলকূট বা মূলঘণ্টা (শীর্ষের ঘণ্টা), এবং অলংকরণগত অন্যান্য উপাদান—যেমন সিংহ, হাতি, গরুড় (দিকচক্রে) ও কলশ (যার উপস্থিতি পাঠ্যে নিহিত)—যেগুলো প্রত্যেক ঘণ্টার উপর স্থাপিত হয়। এরপর বিভিন্ন ধরনের সম্বরণের নাম এবং তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। অপরাজিতপৃচ্ছায় যে অংশটুকু আছে, তার তুলনায় এখানে আলোচনা আরও বিস্তারিত।¹⁹
কেশর্যাদি-প্রকার-লক্ষণাধ্যায়
মারু-গুর্জর রীতির মন্দিরে প্রধান যে ধরনের সুপারস্ট্রাকচার দেখা যায়, তা হলো—কেন্দ্রীয় মূলশৃঙ্গ (মূল শিখর) ঘিরে বহু ক্ষুদ্রতর কন্টকাকৃতি কুঞ্জিকা বা শিখরের সমষ্টি। বাস্তুবিদ্যায় এই বিভিন্ন ধরনের সুপারস্ট্রাকচারের উপর একাধিক অধ্যায় ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ধাখি এবং আমি শনাক্ত করতে পেরেছি। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি খুঁজে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই ধারাবাহিকতা, যা পঞ্চান্দক কেশরি ধরনের মাধ্যমে শুরু হয়। বাস্তুবিদ্যা এই পরিকল্পনা এবং নির্মাণ-বিধানের জন্য প্রায় দুই শত পদ সংরক্ষিত রেখেছে।
¹⁷ দেখুন সামরাঙ্গণসূত্রধার, অধ্যায় ৬৭, এবং অপরাজিতপৃচ্ছা, অধ্যায় ১৮৪।
¹⁸ ধাখি, “ক্রোনোলজি,” পৃ. ২৭।
¹⁹ দেখুন অধ্যায় ১৯৩।
এই ধারার শিখরগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এটিকে সামরাঙ্গণসূত্রধারায় পাওয়া একই ধারার সঙ্গে তুলনা করলে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে। পরবর্তী অধিকাংশ মারু-গুর্জর গ্রন্থসমূহ, এমনকি অপরাজিতপৃচ্ছাও, কেশরী প্রসাদ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য সম্ভবত বাস্তুবিদ্যার ওপরই নির্ভর করেছে।
সর্বাঙ্গসুন্দর প্রসাদ এবং শ্রীবৎস প্রসাদ–এর বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি, যা মূলত বাস্তুবিদ্যার একটি স্বাধীন অধ্যায়ের অংশ ছিল, বর্তমানে হারিয়ে গেছে।
শ্রীনন্দ প্রাসাদ-লক্ষণাধ্যায়
প্রাক-মধ্যযুগীয় ও মধ্যযুগীয় পশ্চিমভারতীয় স্থাপত্যকলায় জৈনদের অবদান অপরিমেয়। পশ্চিমভারতীয় বাস্তুগ্রন্থগুলোতে নিয়মিতভাবে জৈন মন্দিরের স্থাপত্য, জৈন প্রতিমার আইকনোগ্রাফি ও পরিমাপতত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।²⁰ বাস্তুবিদ্যা পঞ্চান্ন প্রকারের জৈন মন্দির, সমবসর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিতে ১৩৬টি পদ উৎসর্গ করেছে।
সাতাশ প্রকারের মণ্ডপ, প্রাকার (প্রাচীর), প্রাতোলী (দ্বারমণ্ডপ), এবং কীর্তিস্তম্ভ–সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিও উদ্ধার করা গেছে। বর্তমানে এগুলো অধ্যয়নের অধীনে আছে, এবং যাই হোক, শেষোক্ত তিনটি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে না।
²⁰ এই বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তুবিদ্যার অংশগুলি উদ্ধার হওয়া অংশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
অ্যালিস বোনার
শিল্পসারিণী থেকে উদ্ধৃতি
শিল্পসারিণী একটি অপুস্তকভুক্ত ওড়িশার গ্রন্থ, যা সম্পূর্ণরূপে মন্দির-স্থাপত্যের কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করে—এক অর্থে স্থপতিদের জন্য একটি নির্দেশিকা। প্রকৃতপক্ষে, পুরীর ঐতিহ্যবাহী স্থপতি, যার কাছ থেকে আমার সহকর্মী পণ্ডিত সদাশিব রথ শর্মা প্রথম প্রতিলিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন, দাবি করেন যে এটি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত, এবং তাঁর কোনো এক পূর্বপুরুষই সেই সংকলন করেছিলেন। তবে সম্প্রতি ওড়িশার দক্ষিণাংশে আর-একটি প্রতিলিপি পাওয়া গেছে, যাতে অতিরিক্ত কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। সেই কারণে এই দুই প্রতিলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও তুলনা না করা পর্যন্ত এর রচয়িতা বা প্রকৃত রচনাকাল সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।
এই একই কারণে, আজ যে কয়েকটি অংশ আমি আপনাদের দেখাতে পারব, সেগুলিও গ্রন্থের চূড়ান্ত রূপ বলে দাবি করতে পারে না; এখানে উত্থাপিত বহু সমস্যাই এখনো সমাধানের অপেক্ষায়। আজ আমি যা দিতে পারি, তা কেবল শিল্পসারিণীর কর্মশালার এক ঝলক—যাতে বোঝানো যায়, কী পদ্ধতিতে এটি মন্দির-স্থাপত্যকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে। এই পদ্ধতি ভারতের অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর থেকে আলাদা বলে মনে হয়, যেখানে মন্দিরের উপাদানগুলোর উচ্চতা ও প্রস্থের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক সম্পর্কই যেন প্রধান মানদণ্ড। এখানে তার পরিবর্তে মন্দির ও মুখশালা নির্মাণের ভিত্তি রাখা হয়েছে একটি মৌলিক পরিমাপের ওপর, যাকে মূলসূত্র বা মালভাগ বলা হয়, এবং যার অনুসারে গঠনের সমস্ত অংশ অঙ্কিত হতে হবে।
গ্রন্থটি শুরুতেই “শিল্পবিদ্যার রহস্য”-এর একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে—
“শুধুমাত্র বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের স্থাপককেই এই অতল ও গুপ্ত শিল্পজ্ঞান প্রদান করতে হবে; অন্য কাউকে নয়।
“শুধুমাত্র সেই স্থাপকদেরই, যারা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাদের অনুগত ও প্রিয় শিষ্যদের কাছেই এই বিদ্যার অষ্টাঙ্গ প্রদান করা উচিত।”
ওড়িশি পরম্পরায় স্মরণ রাখা উচিত যে বিশ্বকর্মা ও শুক্রাচার্য প্রতীকী শব্দ—যা শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতাকে নির্দেশ করে; প্রথমটি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের নিয়মের প্রকাশক, দ্বিতীয়টি প্রসার ও বিচ্ছুরণের শক্তির প্রকাশক। একটিকে “ধ্রুপদি” বা “অ্যাপোলোনীয়” বলা যায়, অপরটিকে “বৈচিত্র্যময়” বা “ডায়োনিসীয়”।
বিভাগসমূহ, মাপ এবং ভাস্কর্যকর্ম যথাযথ ক্রমে প্রদত্ত হওয়া উচিত; সুত্রজ্ঞান (মূল মাপের এককের জ্ঞান) স্থপতি বা প্রিয় শিষ্যদেরকে দেওয়া যাবে না।
"মন্দিরের মাপগুলো আয়ত্ত করার পূর্বে সুত্রজ্ঞান দেওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র তখনই সেই সেরা শিষ্যকে স্নেহভরে সুত্রজ্ঞান প্রদান করা যেতে পারে।
যখন সে কোথাও সঠিক মাপ অনুযায়ী একটি মন্দির নির্মাণ করে ফেলেছে, তখন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করার পর তাকে রেখাজ্ঞান প্রদান করতে পারে।
যখন মন্দির নির্মাণের পরে রেখাজ্ঞান দেওয়া হয়, তখন তা শুধুমাত্র পুত্র এবং নাতি-নাতনির ধারায় থাকা লোকদেরই দেওয়া উচিত, আর অন্য কোনো ব্যক্তিকে নয়।
এই শাস্ত্র [শিল্পসারিনী] স্থপতির জন্য সেরা এবং সবসময় তাকে আনন্দ দেয়। এতে প্রধানত মাপ (অনুপাত) প্রকাশ করা হয়েছে, এবং অন্য বিষয়গুলো কম উল্লেখিত।
সারিনী মানে হলো মাপ, যা সমস্ত শিল্পকলার জন্য প্রয়োজন। যেহেতু এটি মাপ (অনুপাত) নিয়ে কাজ করে, তাই এই গ্রন্থকে শিল্পসারিনী বলা হয়েছে।"
এই কয়েকটি শ্লোকেই এই পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিল্পশাস্ত্রের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য যথাযথভাবে নির্দেশিত হয়েছে।
শিল্পসারিনী একটি অধ্যায় দিয়েছে মুলসুত্র সম্পর্কিত নিয়মাবলীর জন্য।
মুলসুত্রের তিন প্রকার আছে:
১. উচ্চতম, যা মন্দিরের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে;
২. মধ্যম, যা সুত্রধার বা যাজমানের মুষ্টি অনুযায়ী;
৩. সর্বনিম্ন, যা মন্দিরের প্লিন্থ বা মঞ্চের উপর ভিত্তি করে।
উচ্চতম মুলসুত্র নির্ণয় করতে প্রথমে মন্দিরের নির্ধারিত উচ্চতাকে দশ ভাগে ভাগ করতে হবে, এবং এগুলিকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে। এই অংশ, অর্থাৎ মোট উচ্চতার এক পঞ্চাশতম অংশ, হলো মুলসুত্র। বিশ্বকর্মা অনুসারে এটি সেরা মুলসুত্র।
মধ্যম মুলসুত্র নির্দেশ করে নির্মাতা—স্থপতি হোক বা যাজমান—এবং মন্দিরের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কারণ মুলসুত্র তার মুষ্টি অনুযায়ী নেওয়া হয়। সর্বনিম্ন মুলসুত্র নেওয়া হয় মন্দিরের প্লিন্থ ভিতিপীঠ অনুযায়ী, সেই মঞ্চের উপর মন্দির দাঁড়িয়ে আছে।
এভাবে, প্রথমটি নির্দিষ্ট উচ্চতার ভাগ করে বের করা হয়, আর শেষটি মূল অংশকে গুণ করে বের করা হয়; এই দুটি ক্রিয়াই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রভাব বহন করে।
আমার মতে, এই পাঠ্যপুস্তকের মহৎ দিক হলো—মুলসুত্রকে মন্দির নির্মাণে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে, এটি চোখকে অনুপাতের নিয়মাবলীর উপর পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়।
যা যাই হোক, এগুলোই এই প্রাচীন স্মৃতিসৌধের অমর সৌন্দর্যের গোপন রহস্য, বড় হোক বা ছোট, সম্পূর্ণ হোক বা ধ্বংসাবশেষে থাকা।
নিজের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, শিল্পসারিনী সবসময় মন্দিরের বর্ণনা শুরু করে একটি গ্রিড স্থাপন করে, যার বর্গক্ষেত্রগুলি নির্বাচিত মিলাসূত্র অনুযায়ী মাপা হয়। এ গ্রিডের উপর ভিত্তি করে মাটির পরিকল্পনা (ground plan) অঙ্কিত হয়। উল্লম্ব নির্মাণের জন্য আরেকটি গ্রিড দেওয়া হয়, যা একই ভাগে হতে বা না-ও হতে পারে।
উচ্চতার বর্ণনা দেওয়ার সময়, অনুভূমিক এবং উল্লম্ব বিভাজন আলাদাভাবে প্রদত্ত হয়। তবে এর মানে এই নয় যে এই দুটি বিভাগ সবসময় নিখুঁতভাবে আলাদা রাখা যায়। যেহেতু এই দুই বিভাগ একে অপরের সঙ্গে ওভারল্যাপ করে, তাই পুনরাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে। মাত্র তখনই যখন উচ্চতা এবং প্রস্থে মাপ এবং অনুপাত নির্ধারিত হয়, তখন পাঠ্যটি বিভিন্ন স্থাপত্য উপাদান, তাদের মোল্ডিং, ভাস্কর্য এবং অলঙ্করণের বিস্তারিত বর্ণনায় এগোয়।
মন্দিরগুলোকে সেই দেবতার নামে উল্লেখ করা হয় না যাদের উদ্দেশ্যে এগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে। বরং এগুলো সর্বদা স্থাপত্যিক ধরণ হিসেবে বর্ণিত হয়, যেমন: সমভদ্রপীঠ (Samabhadrapitha) সাদি দেউল ধরণের জন্য; সমসর্বতোভদ্রপীঠ (Samasarvatobhadrapitha) রাজারাণী ধরণের জন্য; সমদ্বিপীরপীঠ (Samadvipirapitha) প্যারাফুরমেশ্বর মন্দিরের জন্য। যেহেতু এই বর্ণনাগুলো মূলত সুপরিচিত স্মৃতিসৌধের জন্য, সেগুলো চিহ্নিত করা কঠিন নয়।
উপরন্তু, বর্ণনাগুলো এত বিস্তৃত এবং নির্ভুল যে এগুলোর একটিমাত্র শক্তির উপর ভর করে একজন মন্দিরকে চিনতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মন্দিরগুলোর যথাযথ চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়।
মহাপ্রসস্ত পঞ্চরথ প্রাসাদ ও মুখশালার ভিত্তি পরিকল্পনা
সংক্ষিপ্ত সময়ে আমাদের পক্ষে, আমি শুধুমাত্র মহাপ্রসস্ত পঞ্চরথ প্রাসাদ এবং তার মুখশালার বর্ণনার কয়েকটি বিষয়ই দেখাতে পারব। এই মন্দিরকে সেই একই শ্রেণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে কাইলাস ভদ্রপীঠের সৌম্যভদ্র মুখশালা রয়েছে, যার মধ্যে লিংগরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। মহাপ্রসস্তকে কাইলাসভদ্রের সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি স্পষ্টতই কোনার্কের সির্যা মন্দিরকে নির্দেশ করে।
চিত্র ক হল মাটির পরিকল্পনার অঙ্কন, যা পাঠ্যের বর্ণনার সঠিক অনুসারে করা হয়েছে। যেই গ্রিডে এটি অঙ্কিত হয়েছে, সেটির প্রস্থে ২২টি ভাগ রয়েছে, যাকে ভীমিভাগ বলা হয়। দৈর্ঘ্যে কত ভাগ রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি।
এই বিভাজনগুলো মিলাসূত্র, অর্থাৎ মাপের মৌলিক একককে উপস্থাপন করে, যা অনুভূমিক সম্প্রসারণের সব অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে। মুখশালা, পাশাপাশি প্রবেশপথের পাশে অবস্থানরত প্রক্ষেপিত দেয়ালসমূহ (আলাসবদ্দাস) সহ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২২ মিলাসূত্র। কেবল হলের বাহ্যিক দেয়ালই ১৮ মিলাসূত্রকে আচ্ছাদিত করে, এবং হলের অভ্যন্তরীণ স্থান কভার করে…
চিত্র ক: মহাপ্রসস্ত পঞ্চরথ প্রাসাদের মাটির পরিকল্পনা, শিল্পসারিনী অনুযায়ী।
মিলাসিত্রার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী ১২ মিলাসিত্র। এতে দেয়ালের পুরুত্বের জন্য ৩ মিলাসিত্র অবশিষ্ট থাকে, যা অছিদ্রভিত্তি (অকাটা ভেড়া দেয়াল) এবং শিল্পিত বাইরের দেয়াল উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। দেয়ালের মধ্যভাগ, যা রাহা নামে পরিচিত, এবং পার্শ্বের দেয়াল (আলাসবদ) ৩ অংসার প্রক্ষেপণ রয়েছে। এখানে অংসা মনে হয় অর্ধেক মিলাসিত্র সমান। এই দেয়ালগুলোর সামনে বড় স্তম্ভের জন্য একটি অতিরিক্ত অংশ এক মিলাসিত্র রয়েছে, যা বঙ্কাপতি, পোর্টালের উপরে বিস্তৃত চওড়া ধনুককে সমর্থন করে। এই দুটি প্রক্ষেপিত দেয়ালের মধ্যে থাকা পোর্টালের প্রস্থ ৪ মিলাসিত্র। এই প্রস্থ ৩ ভাগে ভাগ করলে, মধ্যভাগটি দরজার পথ এবং পার্শ্বের অংশগুলি দরজার ফ্রেমের জন্য থাকে।
এরপর দেয়াল অংশের বিভাজন শুরু হয় কোণকা থেকে, অর্থাৎ কোণ অংশ থেকে। এই বিভাজনগুলি মাটির রেখা বরাবর কঠোরভাবে নেওয়া হয়নি, বরং প্রধানত পঞ্চকর্মার উপরের একটি রেখায়। কোণকা একটি সিত্র দখল করে এবং এটি তিনটি কোণমংসায় (উল্লম্ব ফাঁকা) ভাগ করা হয়েছে, যা সোজা স্তম্ভের আকারে। এর ভিত্তিতে একটি পঞ্চকর্ম রয়েছে। এরপর দুটি প্রতিরথ আসে, ছোট পিলাস্টারের আকারে, একসাথে এক সিত্র দখল করে, এবং তারপরে একটি অনর্থা রয়েছে এক সিত্রের, যা একটি ছোট রথকা এবং মূর্তির জন্য নীচযুক্ত। এটি আবার দুইটি প্রতিরথ দ্বারা ঘেরা, একসাথে এক সিত্র প্রস্থে। তারপর আসে এক গভীর ফাঁকা অংশ এক অংশের, যা অকাটা দেয়ালের সাথে সংযুক্ত, এবং এর দুই পাশে দুইটি উঁচু, সমতল অর্ধেক অংশ রয়েছে। সবচেয়ে গভীর অংশটি কন্যা, মিথুনা এবং বীরদলের মূর্তিগুলিকে ধারণ করার জন্য তৈরি।
মিলাসিত্রা বা তার বিভাজনগুলিকে ক্ষুদ্রতম বিবরণ পর্যন্ত সম্মান করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়ার পর, পাঠ্যটি একটি কৌতূহলজনক মন্তব্য করে, অর্থাৎ এখান থেকে (প্রক্ষেপিত দেয়াল পর্যন্ত) মিলাসিত্রা কিছুটা সংকীর্ণ হওয়া উচিত। (বাস্তবিক ভবনে এমন হ্রাস লক্ষণীয় নয়, তবে পরিমাপ করার পর এটি সত্য প্রমাণিত হয়)।
ফাঁকা অংশের পরে একটি অনর্থা রয়েছে, যা পূর্বের মতো দুইটি প্রতিরথ দ্বারা ঘেরা, তবে এই দলটি পূর্বেরটির চেয়ে অর্ধেক অংসা বেশি প্রক্ষেপিত হওয়া উচিত। শেষাংশে আরেকটি এক সিত্র গভীর ফাঁকা অংশ রয়েছে যা আলাসবদ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং পূর্বে উল্লেখিত মূর্তিগুলির মতো মূর্তিগুলি ধারণ করে। প্রক্ষেপিত দেয়ালের বাইরের অংশ দুটি সংকীর্ণ অনার্থা দ্বারা সজ্জিত, যেগুলি রাহার ওপর অবস্থানের কারণে অনুরাহা নামে পরিচিত। এদের কোনো প্রতিরথ নেই, তবে অন্যান্যভাবে এগুলির বৈশিষ্ট্য মূল দেয়ালের সঙ্গে একই রকম।
পাঠ্যটি বারবার উল্লেখ করে যে, এই দেয়ালকর্মে অনার্থার দুটি দল একে অপর থেকে খুব স্পষ্টভাবে আলাদা করা উচিত (সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় গভীর ফাঁকা অংশ এবং ভারিলা ও মিথুনার মূর্তির মাধ্যমে)। সব তিনটি বাহ্যিক পাশে পোর্টাল তৈরি করা উচিত, এবং এগুলি গর্ভগৃহের দিকে তৈরি করতে হবে। প্রতিটি পোর্টালের সামনে দুইটি গোলাকার ধাপ (নন্দাবর্ত) থাকবে।
গর্ভগৃহ, একই গ্রিডে স্থাপিত, কোণকা থেকে কোণকা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১২ মিলাসিত্র। মুখশালা এবং গর্ভগৃহের মধ্যে দূরত্ব নির্দেশিত নয়। এটি কেবলমাত্র রাহার দুই পাশে প্রক্ষেপণ এবং বিমানের সামনের গান্দি-স্থখরার অনুযায়ী হিসাব করা যায়। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ স্থান ছয় মিলাসিত্র। রাহার প্রস্থ চার ভাগে বিভক্ত। দুইটি মধ্যবর্তী ভাগে পার্শ্বদেবতার নীচ রাখা হয়, যাকে মধ্যভাগ, অর্থাৎ মধ্যসিত্রে স্থাপন করতে হবে। তাদের পার্শ্বের দেয়াল কোনো অলঙ্কারযুক্ত খোদাই ছাড়া থাকবে।
রাহার সামনে নীশে মন্দিরগুলি রয়েছে, যা চার ভাগের (ছয় মিলাসিত্রের) এবং কোনার চারটি স্তম্ভ রয়েছে (উপরের তলায়)। নিচের তলায় রয়েছে দ্বিদ্রবন্দ, অনার্থা এবং কোণকাস্থম্ভ। এই উপাদানগুলো চারপাশের সব দিকেই তৈরি করতে হবে একটি মিলাসিত্র অনুযায়ী, যা মন্দিরের মিলাসিত্রের অর্ধেক।
ভূমি পরিকল্পনার বিশ্লেষণ
এই ভূমি পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে সমস্ত অংশের মধ্যে জ্যামিতিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জটিল নির্মাণে এমন কোনো অংশ নেই যা সমস্ত অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ বা মিল রাখে না। এটি একদম স্পষ্ট একটি বক্তব্য মনে হতে পারে, কিন্তু এর পূর্ণ প্রভাব কেবল তখনই বোঝা যায় যখন এগুলোকে একটি চিত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় (চিত্র খ).
এখানে চিত্রটি পাঠ্য অনুযায়ী তৈরি করা ডিজাইনের উপর স্থাপন করা হয়েছে (চিত্র ক)। প্রথমে আসুন মাত্রাগুলো বিবেচনা করি।
ভিমানের চারপাশের বাহ্যিক বর্গাকার, কোণকা থেকে কোণকা পর্যন্ত, মুখশালার অভ্যন্তরীণ বর্গাকার সমান। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ বর্গাকার সমান মুখশালার চারটি স্তম্ভের অভ্যন্তরীণ কোণগুলির মধ্যে কক্ষের সমান; এটি তিনটি নীশে মন্দিরের বাহ্যিক বর্গাকার সমানও। সুতরাং, নীশে মন্দিরগুলি গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ কক্ষে স্থান পাবে, গর্ভগৃহ মুখশালার স্তম্ভগুলির মধ্যে অবস্থান করবে, এবং গর্ভগৃহের বাহ্যিক মাপ মুখশালার অভ্যন্তরীণ স্থানে ফিট হবে।
এটি আরেকভাবে প্রদর্শন করা যায়, প্রতিটি অংশকে একটি বৃত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে (চিত্র খ)। গর্ভগৃহের চারটি অভ্যন্তরীণ কোণের স্পর্শকারী বৃত্তটি সমান মুখশালার স্তম্ভগুলির চারটি অভ্যন্তরীণ কোণের স্পর্শকারী বৃত্ত এবং নীশে মন্দিরের বাহ্যিক কোণগুলোর চারপাশের বৃত্তের সমান। গর্ভগৃহের বাহ্যিক কোণের স্পর্শকারী বড় বৃত্তটি মুখশালার অভ্যন্তরীণ কোণ স্পর্শকারী বৃত্তের সমান। এই দুটি বৃত্ত একে অপরকে মধ্যভাগে স্পর্শ করে, দুইটি কাঠামোর মধ্যে। এগুলো হচ্ছে …
পরিমাপ ও আকারের সম্পর্ক, যা কাঠামোর বিভিন্ন অংশকে এক স্থির জ্যামিতিক সমন্বয়ে একত্রিত করে।
কিন্তু এখানে আরেকটি, গতিশীল সম্পর্কও রয়েছে বিভিন্ন অংশের মধ্যে, যা পাওয়া যায় বিভিন্ন মন্দিরের কেন্দ্র দিয়ে তির্যক রেখা টেনে এবং তাদের কোণ বরাবর সমান্তরাল রেখা যুক্ত করে।
মুখশালার তির্যক রেখাগুলি, যখন গর্ভগৃহের দিকে সম্প্রসারিত হয়, তখন দুটি পার্শ্ব নীশে মন্দিরের বাহ্যিক কোণ স্পর্শ করে এবং সেগুলোকে তাদের ক্ষেত্রের মধ্যে ধরে রাখে। ভিমানের তির্যক রেখাগুলি, যখন সম্প্রসারিত হয়, মুখশালা-কোণকাগুলির বাহ্যিক প্রান্তকে ছেদ করে এবং সেগুলোকে ভিমানের সঙ্গে সংযুক্ত করে। পার্শ্বের দুই নীশে মন্দিরের তির্যক রেখাগুলি, তাদের অভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণসহ, ভিমানের বাহ্যিক প্রান্তকে ছেদ করে এবং তারপর মুখশালার গ্যান্ডিলার সাথে সংযোগস্থল থেকে অন্য পাশে আলাসাবদার সঙ্গে মুখশালার সংযোগস্থলে চলে যায়, অভ্যন্তরীণ দরজার কেন্দ্র এবং স্তম্ভের অভ্যন্তরীণ প্রান্ত বরাবর। পার্শ্বের নীশে মন্দিরের অন্যান্য তির্যক রেখা, পেছনের দিকে সম্প্রসারিত হলে, তৃতীয় নীশে মন্দিরের তির্যক তৈরি করে। এভাবে সমস্ত নীশে মন্দির তাদের তির্যক রেখার মাধ্যমে সংযুক্ত।
এখন, যদি গর্ভগৃহের চারটি অভ্যন্তরীণ কোণে স্পর্শক হিসেবে তির্যক রেখা আঁকা হয়, তাহলে এগুলো সম্প্রসারিত হলে সমস্ত নীশে মন্দিরের বাহ্যিক কোণ ছেদ করবে, এবং সম্প্রসারিত কেন্দ্ররেখা থেকে সোজা কোণে ভাঁজ করলে, এই রেখাগুলি নিয়মিত তির্যক বর্গ তৈরি করবে যা এই মন্দিরগুলিকে আচ্ছাদিত করবে। মুখশালার দিকে সম্প্রসারিত হলে, এগুলো হলের অভ্যন্তরীণ কোণ ছেদ করবে এবং ভূমি পরিকল্পনার বাহ্যিক সীমায় পার্শ্ব-পোার্টালের সামনে শেষ হবে। সেখান থেকে সোজা কোণে ভাঁজ করলে, এই রেখাগুলো হলের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ কোণ ছেদ করবে এবং প্রধান প্রবেশপথের সামনে কেন্দ্রে মিলিত হবে। এভাবে, এগুলো নীশে মন্দিরের মতো মুখশালার অভ্যন্তরীণ স্থানকেও তির্যক বর্গে আবদ্ধ করে।
এই সমস্ত তির্যক রেখার ব্যবস্থা, যা এই স্থাপত্যগুলোকে সংযুক্ত করে, গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ স্থান থেকে বিকীরণ করে। এই গর্ভগৃহকে আবদ্ধ করা তির্যক বর্গ চার দিকের স্থানমাপ অনুযায়ী আরও তির্যক বর্গ বিস্তৃত করে। এই রেখাগুলোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভবনের অন্যান্য সমস্ত অংশের অবস্থান নির্ধারিত হয়। পুরো জটিল কাঠামো একটি জীবন্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, যেখানে কেন্দ্রবিন্দু বা নিউক্লিয়াস থেকে অংশগুলো সঙ্গতিপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। এই নিউক্লিয়াস, একটি মন্দিরে, স্পষ্টতই অভ্যন্তরীণ কক্ষ, অর্থাৎ গর্ভগৃহ, যেখানে দেবতার আবাস। এটি সমস্ত জীবের গর্ভের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, সৃষ্টির মেট্রিক্সের মতো, যেখানে বিভিন্ন রূপ এবং ছন্দে এই বিশ্বের প্রকাশ ঘটে।
কোণার্কে সূর্য মন্দিরের (পরম সির্যা মন্দির) ভূমি পরিকল্পনা (Fig. c) দেখলে বোঝা যায় যে, সিল্পসারিনীর দ্বারা উল্লিখিত তাত্ত্বিক পরিকল্পনাই মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন এই জ্যামিতিক পরিকল্পনাটি প্রকৃত নির্মাণের উপর স্থাপন করা হয়, তখন মূল পরিকল্পনার সঙ্গে নির্মাণ কতটা মিলেছে তা সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায়।
আমি আগেও উল্লেখ করেছি যে, সিল্পসারিনী মুখশালার এবং গর্ভের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্দিষ্ট করে না। প্রথম অঙ্কনে এই দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিল দুই মিলাসিত্রা। কিন্তু যখন একটি বড় চিত্র অঙ্কন করা হয় এবং এই পরিকল্পনার উপর স্থাপন করা হয়, দেখা যায় যে প্রকৃত দূরত্ব এক মিলাসিত্রার বেশি নয়। এটি ডায়াগ্রামের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আনে না। কেবল দুটি বড় বৃত্ত পরস্পরের সংস্পর্শে না এসে কিছুটা ছেদ করছে এবং নিসা মন্দির থেকে মুখশালার দিকে যাওয়া তির্যক রেখাগুলো কিছুটা স্থানান্তরিত হয়েছে। যেগুলো নিসা মন্দিরের কোণ দিয়ে যায়, তা এখন মুখশালার কেন্দ্রের দিকে মিলিত হচ্ছে। এর ফলে তিনটি নিসা মন্দিরকে আচ্ছাদিত করা বড় তির্যক বর্গ, যার কেন্দ্রে গর্ভগৃহ রয়েছে, মুখশালার কেন্দ্রে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এর ন্যূনতম বিন্দু, যা আগের মতো ভাসমান ছিল, এখন মুখশালার কেন্দ্রীয় বিন্দু কন্দ্র-গর্ভে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে হলের উচ্চতা পরিকল্পনা ও হিসাব করা হয়।
যন্ত্র রাশ
কোনো মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন এর ভিত্তির নিচে অবস্থানরত যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই দিক থেকে, সিল্পসারিনী কোনো সহায়তা দেয় না।
কোণার্কে সূর্য মন্দিরের নির্মাণ সংক্রান্ত একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে এই যন্ত্রগুলো দেখানো হয়েছে। তবে এগুলো সঠিকভাবে অঙ্কিত নয় এবং বিশেষ অর্থের ব্যাখ্যা পাঠে নেই। গর্ভগৃহের জন্য একটি যন্ত্র, মুখশালার জন্য আরেকটি যন্ত্র, এবং প্রতিমার পৃষ্ঠভূমির জন্য (পিণ্ডি) তৃতীয় একটি যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রগুলোর সঠিক রূপ এবং সম্পর্কিত মন্ত্র এখন “মন্ডলসর্বস্যে” নামে একটি সূর্য যন্ত্র সংগ্রহে পাওয়া গেছে। তাদের অঙ্কন থেকে দেখা যায়, এই যন্ত্রগুলো মন্দিরের স্থাপত্যিক বিন্যাসের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।
গর্ভগৃহের ভিত্তিতে থাকা যন্ত্রকে সৌরভদ্র মণ্ডল বলা হয়। এটি ৬×৬ = ৩৬ ভাগে বিভক্ত একটি বর্গাকার ক্ষেত্রে অঙ্কিত হতে হবে। সিল্পসারিনীর পরিকল্পনায় গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ কক্ষও ৩৬ মিলাসিত্রায় বিভক্ত। এই বর্গাকার ক্ষেতের বহির্মুখী অংশগুলো দৈর্ঘ্য-wise দুই ভাগে ভাগ করা হয় যাতে একটি সীমানা তৈরি হয়। এই সীমান্তে ভীপুর-এর মাথা সীমান্তের বহির্মুখী অর্ধাংশে অঙ্কিত হবে এবং ঘাড় অভ্যন্তরীণ অর্ধাংশে অঙ্কিত হবে। যন্ত্র নিজে কেবল ১৬ বর্গের চার অভ্যন্তরীণ ভাগের মধ্যে অঙ্কিত হবে, তবে এর বহির্মুখী কোণে বড় কান যোগ করতে হবে। কেন্দ্রে সৌরবিন্দু একটি ত্রিভুজের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। এই বিন্দুর উপর মহাভাস্কর পূজা করা হবে। ত্রিভুজের চারপাশে একটি ষড়বিভুজ থাকবে এবং এটি তিনটি বৃত্ত দ্বারা ঘেরা থাকবে, যা তিনটি গুণকে নির্দেশ করে। বৃত্তগুলোর চারপাশে আট পাপড়ির একটি কমল থাকবে, যাতে আদিত্যদের অভিশাপ করা হয়, এবং বহির্মুখী বৃত্তে বারো পাপড়ির একটি কমল থাকবে, যা বারো মাসের দেবতাদের জন্য।
সুর্যায়নাধিপতি (দক্ষিণ ও উত্তরের পথের অধিপতি) এর পার্শ্বদেবতা হলো: পূর্বে অরুণ, পশ্চিমে পীশান, দক্ষিণে মিত্র, এবং উত্তরে হরিতপতি। এটি ঠিক সেই অবস্থান যেখানে কোণার্ক মন্দিরের বহির্মুখী নীচে মহান পার্শ্বদেবতাগণ অবস্থান করছে।
আরও বলা যায়, মন্ডলসর্বস্যা অনুযায়ী, মুখশালার ভিত্তিতে থাকা যন্ত্রকে সৌরপঞ্চভজ মণ্ডল বলা হয়। এখানে বর্গাকার ক্ষেতকে ৫×৫ = ২৫ বর্গে ভাগ করতে হবে। দুইটি তির্যক অঙ্কন করা হয় এবং কেন্দ্র নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রের চারপাশে আট পাপড়ির একটি কমল অঙ্কিত হবে, যা কেন্দ্রীয় ভাগের আকার অতিক্রম করবে না। এরপর তির্যকের উপর একটি ভাগ খালি রেখে চার কোণে অর্ধ ভাগ জুড়ে বারো পাপড়ির ছোট মণ্ডল অঙ্কিত হবে।
কেন্দ্রের কমলে, যা ষড়বিভুজের মধ্যে বিন্দু ধারণ করে, সেখানে সার্য ও তার শক্তি ছায়া এবং মায়া পূজা করা হবে। চারপাশের চারটি কমলে দক্ষিণ দিকে গণেশ ও রুদ্র, এবং উত্তর দিকে অম্বিকা ও বিষ্ণু অভিশাপিত হবে।
বহির্মুখী ভাগের অর্ধ অংশ রেখে আরেকটি বর্গ অঙ্কিত হবে এবং এর সব কোণে কান স্থাপন করা হবে। প্রতিটি কানে তিনটি বিন্দু থাকবে, একটি কেন্দ্র এবং দুটি পাশে। এই বিন্দুগুলিতে বারো ক্ষুদ্র সুর্য শক্তি অভিশাপিত হবে, যাদের নাম এবং মন্ত্র প্রদান করা হয়েছে। বহির্মুখী বর্গে দিকপালদের স্থান থাকবে, যা মন্দিরের বহির্মুখী প্রাচীরের দিক অনুযায়ী। বর্গের বাইরে ভীপুরগুলো যোগ করা হবে।
এই যন্ত্রের মুখশালার বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্ট, যদিও বর্গক্ষেতকে ১২×১২ ভাগের পরিবর্তে ২৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেন্দ্রে থাকা সির্য-কমল গ্রাউন্ড প্ল্যানের কেন্দ্র-গর্ভ-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। চারপাশের চারটি কমল হলো ছাদের ভরকে ধরে রাখার স্তম্ভ। কোণের শক্তিগুলি সম্ভবত ছোট মণ্ডপ বা চত্বরে অর্পিত ছিল, যেমন পাণ্ডুলিপিতে দেখানো হয়েছে, এবং যেমনটি লিঙ্গরাজ মন্দিরে সত্যিই দেখা যায়। বহির্মুখী বর্গে থাকা দিকপালরা বহির্মুখী প্রাচীরের দিকে নির্দেশ করে এবং ভীপুরা মন্দিরের চারটি প্রাসাদের দিকে নির্দেশ করে।
মহাপ্রসস্ত মুখশালার উচ্চতা (চিত্র d, e)
প্রসস্ত মুখশালার উচ্চতাও সিল্পসারিনীর অনুযায়ী একটি গ্রিডে অঙ্কিত হয়েছে, তবে এর বিভাজন আলাদা। এটি মন্দিরের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে, যা ১৩ ভাগে বিভক্ত: ৬ ভাগ প্রাচীরের জন্য এবং ৭ ভাগ ছাদের জন্য। প্রস্থ ১১ ভাগ বলা হয়েছে। এই সমস্ত মিলাভাগকে তিন দ্বারা ভাগ করা হয়েছে, ফলে প্রাচীরের জন্য ১৮ উপভাগ, ছাদের জন্য ২১ এবং ভিত্তির জন্য ৩৩ উপভাগ পাওয়া যায়। মাঝখানে একটি উপভাগ যোগ করলে এটি ৩৪ ভাগে পৌঁছে। এই বিভাজনগুলি গ্রাউন্ড প্ল্যানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়, তা এখনো উন্মুক্ত প্রশ্ন। ৩৩ উপভাগকে প্রস্থের জন্য সহজেই গ্রাউন্ড প্ল্যানের ১১ ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে এতে উচ্চতার উপভাগ গ্রাউন্ড প্ল্যানের উপভাগ থেকে আলাদা হবে। বর্তমানে আমাদের উচিত প্রতিটি স্কিমকে তার নিজের উপভাগ অনুযায়ী বিচার করা।
পোস্ট স্ক্রিপ্টাম: এই প্রবন্ধ লেখা থেকে পরবর্তীতে, গ্রাউন্ড প্ল্যানের মিলাসিত্র এবং উচ্চতার মিলাসিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়েছে। সমস্যাটি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল একটি ভুলের কারণে, যেখানে উচ্চতার মূল ভাগ (মুলাভাগ) গ্রাউন্ড প্ল্যানের সমান ধরা হয়েছিল, তবে দুই ভাগের পরিবর্তে তিন ভাগে বিভক্ত। তবে যদি উচ্চতার মিলাসিত্রকে এমন ধরা হয় যে এতে গ্রাউন্ড প্ল্যানের সমান তিনটি উপভাগ থাকে, এবং ফলে এটি গ্রাউন্ড প্ল্যানের মিলাসিত্রের ১৪ গুণ বড় হয়, তাহলে সমীকরণ সহজ হয়ে যায়। এভাবে গ্রাউন্ড প্ল্যান এবং উচ্চতার বিভাজন উভয়ই উপভাগের সাধারণ হর-এ নামানো যায়। এর ফলে গ্রাউন্ড প্ল্যানের ৩৬ উপভাগ উচ্চতার ৪৮ উপভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, গ্রাউন্ড প্ল্যানের ১৮ মিলাসিত্র উচ্চতার ২৪ ভাগের সঙ্গে এবং উচ্চতার ১৬ মিলাসিত্র গ্রাউন্ড প্ল্যানের ১২ ভাগের সঙ্গে সমন্বয় হবে—এটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক ফলাফল দেয়, যা ডিজাইন থেকে যাচাই করা যায়।
ভিন্ন ভিন্ন মন্দির অংশের জন্য ভিন্ন মিলাসিত্র নেওয়ার পদ্ধতি অস্বাভাবিক কিছু নয়। সিল্পসারিনীতে, বিমানার মিলাসিত্র সাধারণত মুখশালার মিলাসিত্রের ১৪ গুণ বড় ছিল। সুতরাং এটি একই মন্দিরের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। indian architecture
 |
| Encyclopaedia of Indian temple architecture |
পশ্চিমা ধারণায় ভারতীয় ভাস্কর্য
কেটাগরি নং ৭১. গণেশভারতে প্রাচীন ভাস্কর্যের একটি ঐতিহ্য ছিল, এ কথা পশ্চিমা জগত অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে জানত। তবে স্বয়ং শিল্পকর্মের প্রকৃতি বা তা বোঝার কোনো যথাযথ উপলব্ধি এবং প্রশংসা দেখা দেয়নি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। তখনকার সময়ে সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, ভারতীয় ভাস্কর্য মূলত এক ভয়ানক রাক্ষসতত্ত্বকে চিত্রায়িত করে, যেখানে এমন অদ্ভুত এবং অদ্ভুত রূপের দৈত্যরা বসবাস করে, যেগুলি তাদের প্রতিনিধিত্ব করা ধর্মগুলির মতোই অদ্ভুত।
এই ভুল ধারণার প্রমাণ মূলত কয়েকটি বিভ্রান্তিকর ভ্রমণকারীর বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়, এবং তা আরও শক্তিশালী হয় পৃথিবীর বিস্ময়গুলি প্রদর্শনকারী কল্পনাপ্রসূত বইয়ের মাধ্যমে, যতক্ষণ না এই ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজস্ব জীবন লাভ করে। এই সাঁচ শতাব্দী ধরে টিকে থাকে, এবং পশ্চিমা কল্পনায় ভারতীয় শিল্পের ধারণার ওপর সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, যার বিকাশ সহজেই নথিভুক্ত করা যায়।
অতএব ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রতি তাত্ত্বিক এবং পূর্বধারণাভিত্তিক অপছন্দ বুদ্ধিজীবী বৃত্তে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যায়, যারা বিষয়টির প্রতি আগ্রহী ছিলেন (এই ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা দেখতে Mitter 1977)। ১৮২০-এর দশকে, জার্মান দার্শনিক জর্জ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), যিনি সম্ভবত ভারতীয় ভাস্কর্য খুব কম দেখেছেন, তার “Aesthetik” বক্তৃতাগুলিতে এটিকে অযৌক্তিক কল্পনার আকার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গ্রিক শিল্পের বিপরীতে, যেখানে রূপ এবং অর্থের নিখুঁত ভারসাম্য সর্বদা প্রকাশিত থাকে (Osmaston 1920)।
যখন হেগেল ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিক ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখনই ভারতের মাটিতে একেবারে ভিন্ন ধরনের বাস্তব কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল। ইউরোপীয়, বিশেষত ব্রিটিশরা, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ধার করা বস্তুসমূহের মাধ্যমে ভারতীয় প্রাচীনকালের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন চালাচ্ছিল, যা ধীরে ধীরে আমাদের ভারতীয় শিল্পের বোঝাপড়ার ভিত্তি পরিবর্তন করতে শুরু করল। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে, পক্ষপাতহীন নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পথে একটি শত্রুভাবাপন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ বাধা সৃষ্টি করেছিল।


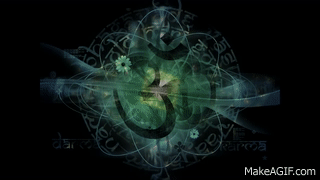




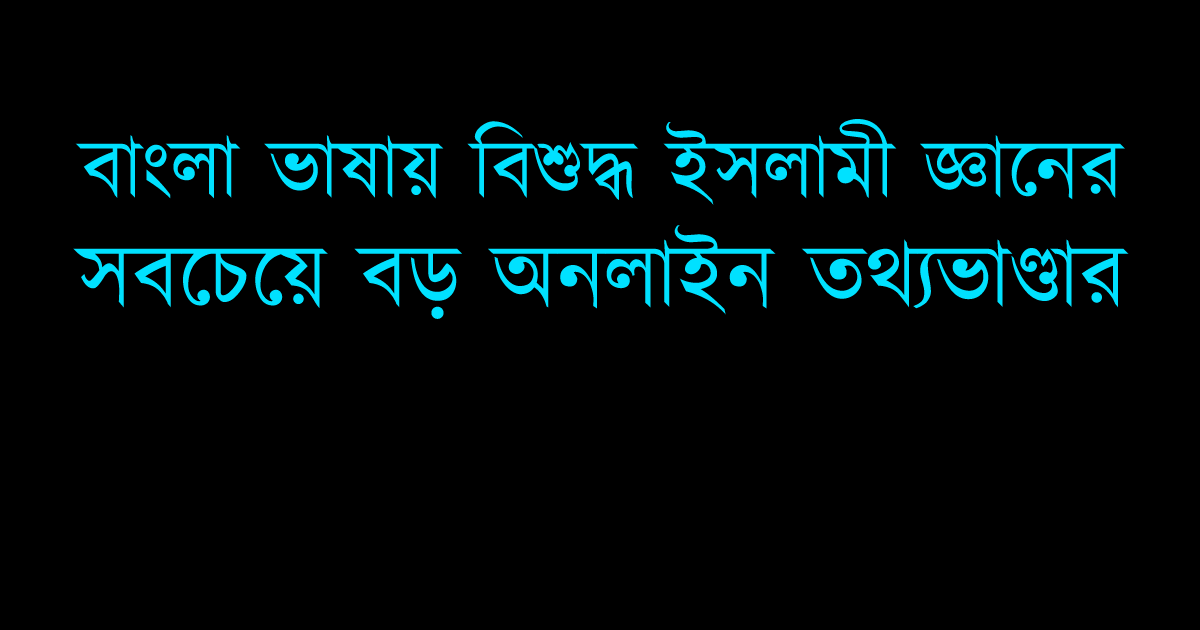
























No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ