আমার ধর্মপালজির বিস্ময়কর ঐতিহাসিক কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ১৯৭৬ সালে, একেবারে অপ্রত্যাশিত জায়গায়—হল্যান্ডের এক লাইব্রেরিতে। তখন আমি পিএইচ.ডি. থিসিসের জন্য উপাদান খুঁজছিলাম, যার এক অংশে ভারত ও চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল।
চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদান এবং গবেষণামূলক বইয়ের অভাব ছিল না—মূলত ড. জোসেফ নিডহ্যামের বহু খণ্ডে প্রকাশিত Science and Civilisation in China-এর জন্য। কিন্তু তার বিপরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ কার্যত অনুপস্থিত মনে হচ্ছিল। যা পাওয়া যাচ্ছিল, তা ছিল খুবই প্রাথমিক, দুর্বল, কল্পনাহীন, কাঠখোট্টা—দর্শন আর কিংবদন্তিতে ভরা, কিন্তু বাস্তব তথ্য কম।
হতাশ ও মনখারাপ অবস্থায় আমি হল্যান্ডের সম্ভাব্য প্রতিটি লাইব্রেরিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে যেকোনো কিছু খুঁজে পাওয়ার আশায়। ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপাদান খুঁজতে হল্যান্ডে ঘুরে বেড়ানো নিজেই এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু আমি যেহেতু সেখানেই পিএইচ.ডি. করছিলাম, তাই খুব বেশি বিকল্প ছিল না।
তারপর এক সকালে, আমস্টারডামের এক রাস্তায় অবস্থিত সাউথ ইস্ট এশিয়া ইনস্টিটিউটে ঢুকে তাকের উপর দেখতে পেলাম Indian Science and Technology in the Eighteenth Century নামের একটি বই। আগ্রহবশত নামালাম। লেখক—ধর্মপাল নামে এক ব্যক্তি, যার নাম আগে কখনো শুনিনি। বইটি বাড়িতে নিয়ে এসে একই দিনে পড়া শেষ করলাম। সেটি আমার ভারত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে দিল।
আজ, বিশ বছরেরও বেশি পরে, জানি যে বইটি হাজার হাজার পাঠকের উপর একই রকম গভীর প্রভাব ফেলেছিল। একটি নতুন প্রজন্মের ভারতীয়র জন্ম হয়েছিল, যারা স্কুলে শেখা ভারতচিত্রের বদলে একেবারে নতুন চোখে নিজেদের দেশকে দেখতে শুরু করেছিল, বিশেষত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শেখা চিত্রের বাইরে। আমার থিসিসের ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অংশেও বইটি এক দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিল। থিসিসটি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় Homo Faber: Technology and Culture in India, China and the West: 1500 to the Present Day নামে (পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে Decolonizing History: Technology and Culture in India, China and the West: 1500 to the Present Day, Other India Press থেকে পুনঃপ্রকাশিত)।
সেই একই বছর (১৯৭৬), ওড়িশার এক বন্ধু আমাদের আমস্টারডামের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। আমি তাকে ধর্মপালের কথা বললাম। অবাক হয়ে তিনি জানালেন, ধর্মপাল তার বন্ধু এবং তিনি লন্ডনে থাকেন। এমনকি তার টেলিফোন নম্বরও দিলেন। পরের সপ্তাহে আমরা লন্ডনে উড়ে গেলাম এবং প্রথমবারের মতো ধর্মপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তখন তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ফিলিস, দুই কন্যা গীতা ও রোসভিটা, এবং পুত্র ডেভিড।
সেই সাক্ষাৎ থেকে যে সম্পর্কের শুরু হয়েছিল, তা আজও অটুট। আজ আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যারা তার Collected Writings প্রকাশ করছে।
আমি নিজে ১৯৭৭ সালে ভারতে ফিরে এলাম। তারপর ঘটল আরও অদ্ভুত কিছু ঘটনা।
১৯৮০ সালে আমাকে চেন্নাই ডাকা হলো একটি সিভিল লিবার্টিজ টিমে যোগ দেওয়ার জন্য, যারা তামিলনাড়ুর নর্থ আর্কট জেলায় ভুয়া পুলিশ মুকাবিলায় রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যার তদন্ত করছিল। পূর্বানুমিতভাবেই আমাদের দলকে পুলিশের প্ররোচনায় গঠিত একটি ভিড় আক্রমণ করল। চেন্নাই ফিরে এসে, যেখানে আমরা প্রেস কনফারেন্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাদের এমএলএ হোস্টেলে রাখা হলো। হোস্টেলের এক ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখলাম, সেখানে বসে আছেন স্বয়ং ধর্মপাল! আমাকে তৎক্ষণাৎ প্রেস মিটিং-এ ছুটতে হলো।
কিন্তু প্রেস আসার আগেই দু’তিনজন তরুণ অচেনা লোক আমাকে দেখতে এলো। তারা জানাল, তারা Patriotic and People-Oriented Science and Technology (PPST) গ্রুপের সদস্য, যার সমর্থক ছিল কানপুর ও মাদ্রাজ আইআইটিতে। তারা আমার বই Homo Faber নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিল (ভারতীয় সংস্করণ তখন সদ্য Allied Publishers প্রকাশ করেছে)। তারা ধর্মপাল সম্পর্কেও আরও জানতে চাইল, যাকে তারা প্রথমবারের মতো Homo Faber পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করেছে।
আমি তাদের বললাম—“আমার সঙ্গে কেন কথা বলতে চাইছেন, যখন আপনারা সরাসরি ধর্মপালের সঙ্গেই দেখা করতে পারেন?” তারা বিস্মিত হয়ে বলল—“ধর্মপাল? এখানে মাদ্রাজে?” আমি বললাম কোথায় তাকে পেয়েছি। মুহূর্তেই তারা ছুটল এমএলএ হোস্টেলের দিকে।
নিশ্চিত। আমি আগের সব অংশ মিলিয়ে সম্পূর্ণ অনুবাদটি “ধর্মপাল” বানান সহ একত্রে বাংলায় দিচ্ছি।
ওই সাক্ষাৎকারটি ধর্মপাল ও পিপিএসটি (PPST)-র মধ্যে এক দীর্ঘ, ফলপ্রসূ এবং সৃজনশীল সম্পর্কের সূচনা ঘটায়, যা কিছু উত্থান-পতন সত্ত্বেও আজও টিকে আছে। কয়েক বছর ধরে পিপিএসটি একটি সাময়িকী প্রকাশ করেছিল, যার নাম ছিল পিপিএসটি বুলেটিন। সেখানে ধর্মপাল ও তাঁর কাজ সবসময়ই বিশেষ গুরুত্বের স্থান দখল করেছিল। আসলে ওই সময়েই পিপিএসটি দলের সদস্যরা ভারতীয় বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, এবং ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। পিপিএসটির কিছু সদস্য পরে ধর্মপালের রচনায় বারবার উল্লেখিত চেঙ্গালপট্টু তথ্যভাণ্ডার (Chengalpattu data) নিয়ে গভীরভাবে কাজ করেন।
আজ ধর্মপালের কাজ কেবল পিপিএসটি গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সুদূর বিস্তৃত—শুধু বুদ্ধিজীবী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যেই নয়, ধর্মীয় নেতা, স্বামী ও জৈন সন্ন্যাসী, রাজনীতিবিদ ও কর্মীদের মধ্যেও। তাঁর গবেষণার অন্যতম ফলশ্রুতি হল প্রাচীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দ্বিবার্ষিক কংগ্রেস আয়োজন, যা পিপিএসটি এবং এনআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় তিনবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কংগ্রেস প্রচুর প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছে। ধর্মপাল নিজেও দেশ-বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। (এই বক্তৃতাগুলির কিছু পাওয়া যাবে তাঁর সংগ্রহীত রচনা-র পঞ্চম খণ্ডে।)
ধর্মপালের কাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর মুক্তির অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। তবে প্রচলিত ভারতীয় ইতিহাসবিদরা—বিশেষত অক্সব্রিজে পড়াশোনা করা শ্রেণি—তাঁর কাজকে তাদের বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছেন। ধর্মপাল কখনো ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রশিক্ষিত হননি। যদি হতেন, তবে হয়তো তিনিও অন্যদের মতো গাছের আড়ালে বন দেখতে পেতেন না। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেও তিনি রয়ে গেছেন মূলত সাধারণ অনুসন্ধানী, যিনি নিজের সন্ধান নিয়ে সবসময় দ্বিধান্বিত থেকেছেন, লেখায় কখনো অতিরিক্ত অলংকার ব্যবহার করেননি। নিশ্চিত ভঙ্গিমা তাঁর ছিল না, যা পাওয়া যায় সেইসব মানুষদের মধ্যে যারা ইংরেজ ইতিহাসবিদদের ধারণা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদদের সামনে এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, যার উত্তর তাদের পক্ষে দেওয়া কঠিন ছিল—যেমন, সামান্য প্রমাণের ভিত্তিতে কীভাবে তাঁরা এত সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে ভারতীয়রা প্রযুক্তিগতভাবে আদিম ছিল, বা কীভাবে তাঁরা সেই নথিগুলি খুঁজে পেলেন না, যা তিনি কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই সহজে খুঁজে পেয়েছিলেন।
ধর্মপালের ইংরেজদের তৈরি ভারতীয় সমাজের ইতিহাসকে ভেঙে দিয়ে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করেছেন। ইংরেজ বা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাত এখন মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ, কিন্তু দেশীয় এক সুসংগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়নি। তাঁর অগ্রণী কাজের ফলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বাস্তব ইতিহাস লেখার উপকরণ এখন পাওয়া গেলেও, সেটিকে একত্রে উপস্থাপন করার মতো যোগ্য পণ্ডিত এখনও আসেননি। এর মধ্যে একটি সাম্প্রতিক কাজ অবশ্য উল্লেখযোগ্য—হেলেইন সেলিনের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ নন-ওয়েস্টার্ন সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড মেডিসিন—যেখানে ধর্মপালের গবেষণার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিই অনুকরণ করে যাব। আর যে সমাজ নিজের সম্পর্কে ধার করা ছবি নিয়ে বেঁচে থাকে, সে সমাজ টিকে থাকবে কীভাবে, সৃষ্টির শক্তি জোগাড় করবে কীভাবে?
ধর্মপালের তাঁর ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় প্রবেশের অভিজ্ঞতা নিজেই বর্ণনা করেছেন, যা এতটাই আকর্ষণীয় যে তা কিছুটা বিশদে বলা দরকার। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই গ্রামসমাজের ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হন। সম্ভবত এর পেছনে কারণ ছিল ১৯৪৪ সাল থেকে মীরা বেনের সঙ্গে রূর্কি-হরিদ্বার অঞ্চলের একটি ছোট আশ্রমে তাঁর অবস্থান। ১৯৪৮ সালে যখন তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদি কিব্বুটজ সম্বন্ধে শুনলেন, তখন তাঁর আগ্রহ আবার জাগল এবং ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে তিনি সেখানকার কিব্বুটজ পরিদর্শনে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে বুঝলেন যে কিব্বুটজ মডেল ভারতে কার্যকর হবে না। পরে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে তিনি ঋষিকেশের কাছে একটি গ্রাম গড়ার চেষ্টা করেন, যেখানে প্রতিটি পরিবার সমান পরিমাণ জমি পায়। কিন্তু সেই গ্রাম কোনো সম্প্রদায় হয়ে উঠতে পারেনি—সেখানে মিল ছিল না, আর শুরুতেই কোনো সম্পদও ছিল না। পরে ১৯৬০ সালে তিনি রাজস্থানের বিশ বিসওয়া গ্রামপঞ্চায়েত এবং ওড়িশার জগন্নাথ পুরীর কাছে ৭০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সাসন গ্রামসমাজ সম্পর্কে জানলেন, যেগুলো তখনও সমৃদ্ধ ও সক্রিয় ছিল।
এই প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতা ধর্মপালকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, যা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা শ্রেয়: প্রায় ১৯৬০ সালে তিনি গ্বালিয়র থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন, তৃতীয় শ্রেণির কামরায় ৬-৭ ঘণ্টার দিনের ট্রেনযাত্রা। সেখানে বারোজন যাত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়—কিছু মহিলা ও পুরুষ। তাঁরা রামেশ্বরমসহ বহু জায়গায় তিন মাসব্যাপী তীর্থযাত্রা করে ফিরছিলেন। তাঁরা বললেন, তাঁরা খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন—আটা, ঘি, চিনি—এবং কিছু অবশিষ্টও ছিল। মহিলারা ঠাসা কামরায় চাপা পড়লেও কিছু মনে করছিলেন না, কিন্তু কেউ তাঁদের খাবারের হাঁড়ি-বোঝায় পা লাগালে অস্বস্তি বোধ করতেন।
তখন ধর্মপাল জানতে চাইলেন, তাঁরা নিশ্চয় একই জাতির মানুষ। তাঁরা বললেন, না—তাঁরা বিভিন্ন জাতি থেকে এসেছেন। কিন্তু যাত্রায় জাতির ভেদাভেদ নেই। এই তথ্য ধর্মপালের অজানা ছিল—৩৮ বছর বয়সেও তিনি ভারতের সাধারণ কৃষক, কারিগর, গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতেন না।
তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা মাদ্রাজ বা বোম্বাই ঘুরেছেন কি না। তাঁরা বললেন, শুধু ট্রেন থেকে পেরিয়ে গেছেন, কোথাও থামেননি। এমনকি দিল্লিতেও তাঁরা থামবেন না, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হরিদ্বার। ধর্মপাল তখন ভাবলেন—এই ভারত কাদের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যানিকেতন, আধুনিক প্রতিষ্ঠান—এসব যাত্রীদের জন্য নয়। আর তাঁর কাছে এরা-ই ছিল আসল ভারত—পণ্ডিত নেহরুর থেকেও বেশি প্রতিনিধিত্বশীল। এই অভিজ্ঞতা ধর্মপালকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, এবং তিনি অনুসন্ধান শুরু করেন কেন ভারতের নতুন নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং এই বিচ্ছিন্নতা আগে থেকেই ছিল কি না।
একইভাবে, বিশ বিসওয়া ও সাসন গ্রামসমাজ দেখে তিনি জানতে চাইলেন কী কারণে এগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে গেছে, যেখানে অন্য অনেক সমাজ ভেঙে পড়েছে। তিনি ধারণা করলেন, যদি এর ভিত্তি বোঝা যায়, তবে ভারতীয় সমাজ—বিশেষত তার বুদ্ধিজীবী ও নেতারা—নিজেদের হতাশা কাটিয়ে নতুন করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি খুঁজতে শুরু করলেন উপনিবেশ-পূর্ব ভারতের কার্যপ্রণালী। প্রথমে তাঁর কাছে কোনো স্পষ্ট দিশা ছিল না। এমনকি প্রাপ্ত তথ্যের গভীর তাৎপর্যও পরে তাঁর কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়।
পাঠকের জানা জরুরি যে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ধর্মপালের আর্কাইভ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল কেবল সাধারণ পর্যায়ের। তাঁর প্রথম আর্কাইভ-পরিচয় ঘটে মাদ্রাজে ১৯৬৪-৬৫ সালে, এবং পরে তা বিস্তৃত হয়। তিনি আবিষ্কার করেন যে অধিকাংশ উপাদান ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পরের, এবং এগুলি প্রধানত ব্রিটিশদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি হয়েছিল। যদিও এর মধ্যে কিছু ভারতীয় ভাষার নথি ও তালপাতার পুঁথিও ছিল। (পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের ভারত-সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করেছিল, তবে সেগুলি ছোট আকারের ছিল।)
এই ব্রিটিশ আর্কাইভাল উপাদানগুলির (যার কিছু তাঁর সংগ্রহীত রচনায় পাওয়া যায়) বিষয় এই পর্যায়ে জানা গুরুত্বপূর্ণ যে এত বিশাল এবং বিস্তারিত আর্কাইভাল রেকর্ডটি আসলে কিভাবে তৈরি হয়েছিল। এর জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু প্রেক্ষাপট জানা অত্যাবশ্যক।
পরম্পরাগত ধারণা (যা অধিকাংশ ইতিহাসপুস্তকে শেখানো হয়) অনুযায়ী ১৬০০ থেকে প্রায় ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (E.I. Co.) প্রধানত ভারতের উপকূলীয় শহর ও নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই স্থানগুলোকে দুর্গনগরী ঘোষণা করা হয় এবং এগুলোকে “ফ্যাক্টরি” বলা হতো, অর্থাৎ ব্যবসার জন্য গুদাম, যেখানে প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থাও ছিল। ১৭৪৮ থেকে বলা হয় কোম্পানি ধীরে ধীরে ভারতের বিজয়ে নিজেকে যুক্ত করতে শুরু করে এবং ১৮৫৮ পর্যন্ত অন্তত: বিজয় ও লুটপাটের জন্য একমাত্র দায়ী ছিল। আমাদের বলা হয় যে ১৮৫৭-৫৮ সালের মহা ভারত বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা কোম্পানির অশাসন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সরাসরি শাসন প্রবর্তন করেন এবং ভারতের শাসনভার একটি ব্রিটিশ কেবিনেট মন্ত্রীর কাছে (ভারত সচিব) অর্পিত হয়, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে।
সত্যি, ১৬০০ সালে ব্রিটেনে একটি E.I. Co. চাটার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এর মধ্যে অভিযানকারী ও লুটপাটকারীরা ছিলেন। কিন্তু ধর্মপালের মতে, এটি কখনো একা কার্যকর হয়নি। শুরু থেকেই কোম্পানির সম্প্রসারণে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর পূর্ণ সমর্থন ছিল, প্রায়শই ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীরও। এছাড়াও কোম্পানি শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারের কোষাগারে বিশাল অর্থ (মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিংয়ে) দিত এবং কম সুদে অর্থ প্রদান করত। মাঝে মধ্যে কোম্পানি ব্রিটিশ রাষ্ট্রের নির্দেশ পেত, এবং কিছু সময়ে কোম্পানির কার্যক্রম ব্রিটিশ নৌসেনাদের তত্ত্বাবধানে চলে যেত, যারা সরাসরি ব্রিটিশ রাজা বা অ্যাডমিরালটির কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতেন। এই সমস্ত নির্দেশ ও যোগাযোগই প্রাথমিক আর্কাইভাল রেকর্ডের অংশ।
একটি বড় উদাহরণ হল ১৭৫৪ সালের আশেপাশে মহারাষ্ট্রের অ্যাডমিরাল কানোহজি অ্যাংগ্রের সঙ্গে ব্রিটিশদের শেষ সম্মুখসংযোগ। ব্রিটিশরা মনে করেছিল তিনি তাদের সম্প্রসারণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এবং তাঁকে somehow নির্মূল করতে হবে। ১৬০০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত এই ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছিল, যখন কোম্পানি বিজয়ী এবং সার্বভৌমের ভূমিকা গ্রহণ করছিল।
১৭৫০ থেকে ব্রিটিশদের আরও বেশি নির্দেশ বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে E.I. Co.-কে পৌঁছে দেওয়া হতো। ১৭৫৭ সালের পর বাংলা দখলের পর, রবার্ট ক্লাইভ—লর্ড চাথামের মতে “স্বর্গজন্মের জেনারেল”, তখনকার ভারতে প্রায় শাসক—ব্রিটেনে লিখলেন, ভারত কেবল ব্রিটিশ রাষ্ট্র দ্বারা সরাসরি শাসিত হতে পারে, কোনো কোম্পানির মাধ্যমে নয়। এই পরামর্শ এবং অনুরূপ অন্যান্য পরামর্শ কয়েক বছর আলোচিত হয়, যা ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এ রূপ নেয়, যেখানে ব্রিটিশ রাষ্ট্র গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর কাউন্সিল নিয়োগ করে, এবং ১১ বছর পরে ১৭৮৪ সালের অ্যাক্টে ভারত বিষয়ক কমিশনার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বোর্ডে এক প্রেসিডেন্ট ও ৬ জন সদস্য থাকতেন, যাদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। কমিশনাররাই ভারতের শাসক হন। ভারতের রাষ্ট্রের যে কোনো বিভাগের জন্য বা তিনটি প্রেসিডেন্সিতে যে কোনো নির্দেশ বিস্তারিতভাবে (শব্দে শব্দে, কমায় কমায়) অনুমোদিত হতো। একবার অনুমোদিত হলে, E.I. Co.-র কোর্ট এই নির্দেশগুলি ভারতের উদ্দেশ্যে তাদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের স্বাক্ষরে প্রেরণ করতো।
পাশাপাশি, কমিশনার বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের মধ্যে একটি পৃথক যোগাযোগ চ্যানেল খোলা হয়েছিল, যা কখনও কোম্পানির মাধ্যমে প্রেরিত আনুষ্ঠানিক নির্দেশকেও অগ্রাহ্য করতে পারত। কিছু বিভাগের নির্দেশ বোর্ড নিজেই প্রস্তুত করতো, কোম্পানির চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নিয়ে তা ভারতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হতো। এই ব্যবস্থা ১৮৫৮ পর্যন্ত বজায় থাকে। ১৮৫৮ সালে শুধু পদবীর পরিবর্তন হয়: বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নাম পরিবর্তন হয়ে ভারত সচিব হয়। (এইভাবে, ১৮১৩ সাল থেকে E.I. Co. ভারতের শাসনে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। ধর্মপালের মতে, এটি কেবল ভারতীয় মনে নয়, বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও গভীরভাবে উপলব্ধি হওয়া দরকার।)
এই কারণে, ১৮৫৮ পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে কোনো ঘটনার খবর পেত, তা লন্ডনে পৌঁছে দিতে হতো, যাতে লন্ডনের অনুমোদন বা নির্দেশ পাওয়া যায়। ফলে ব্রিটিশ আর্কাইভাল রেকর্ড প্রতিটি ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ করেছে।
যদি কেউ ব্রিটিশ আধিপত্যের আগে ভারতের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে বিশদে জানতে চায়, একমাত্র উপায় ছিল এই ব্রিটিশ-তৈরী আর্কাইভগুলির যত্নসহকারে অধ্যয়ন। ধর্মপাল এটিই করেছিলেন। তাঁর আয় তেমন বেশি ছিল না এবং পরিবারকেও দেখাশোনা করতে হতো। তবুও, তিনি নিয়মিতভাবে ইন্ডিয়া অফিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যেতেন। ফটোকপি করতে অর্থ লাগত। অনেক সময় পুরনো পাণ্ডুলিপি ফটোকপি করা যেত না। তাই তিনি হাতে হাতে লিখতেন, পৃষ্ঠা পর পৃষ্ঠা, কোটি কোটি শব্দ, দিনান্তে দিনান্তে। পরে সেই নোটগুলি টাইপ করতেন। এর ফলে তিনি আর্কাইভ থেকে হাজার হাজার পৃষ্ঠা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন। ভারত ফিরলে তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান ধন ছিল এই নোট, যা অনেক বড় ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেস ভর্তি ছিল।
অন্যান্যরা আগে এই রেকর্ড পরামর্শ করেছেন, তবে তারা সামগ্রিক চিত্রটি ধরতে পারেননি। তারা তথ্যকে টুকরো টুকরো দেখতেন, কয়েক মাস বা দুই বছরের জন্য। কিন্তু ধর্মপাল যুগের সুবিধা দিয়েছেন—তিনি দশকের পর দশকের ধৈর্য ধরেছেন। তাঁর মন প্রতিটি বিস্তারিত ধারন করত আশ্চর্যজনক তীক্ষ্ণতায়। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ চিত্র পেয়েছিলেন।
সেই চিত্র যা আর্কাইভ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তা বিস্ময়কর। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে যা শেখানো হয়েছিল তার বিপরীতে, এটি একটি কার্যকর সমাজের অস্তিত্ব নির্দেশ করেছিল, যা সেই সময়ের বিজ্ঞান ও কলায় অত্যন্ত দক্ষ। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এর আন্তঃক্রিয়াশীল দক্ষতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং প্রশংসার দাবিদার। এটি কৃষি ও শিল্প উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়। আমরা জানি, প্রায় ১৭৫০ সাল পর্যন্ত, চীনের সঙ্গে মিলিয়ে, আমাদের অঞ্চল বিশ্ব শিল্প উৎপাদনের প্রায় ৭৩% উৎপাদন করত, এবং ১৮৩০ পর্যন্ত দুই অর্থনীতি বিশ্ব শিল্প উৎপাদনের ৬০% পর্যন্ত অবদান রেখেছিল। এমনকি মধ্যম উর্বর চেঙ্গালপট্টুর (তামিলনাডু) অঞ্চলে ১৭৬০-৭০ সালের প্রায় ৫-৬ টন ধান হেক্টর প্রতি জমিতে উৎপাদন হত, যা বর্তমান জাপানের হেক্টর প্রতি উৎপাদনের সমান। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি বিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থা যুবকদের শিক্ষার চাহিদা পূরণ করত।
সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুসংগঠিত আর্থিক ব্যবস্থা। মোট উৎপাদনের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হতো—সেচের ট্যাংক ও নর্দমা দেখভাল করা ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে পুলিশ ও শিক্ষক পর্যন্ত। প্রযুক্তিতে, আমরা শেফিল্ড স্টিলের চেয়ে উন্নত স্টিল উৎপাদন করতাম। আমরা রঞ্জক, জাহাজ এবং শত শত অন্যান্য পণ্য তৈরি করতাম।
ধর্মপাল যখন সবকিছু নথিভুক্ত করতেন, তিনি দেখতেন কিভাবে ব্রিটিশরা ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ ধ্বংসে ব্যস্ত।
তিনি প্রতিদিন প্রায় নথি অধ্যয়ন করতেন, যা তাকে মানে যাদুবিদ্যা মতো আকৃষ্ট করত। তিনি দেখলেন ব্রিটিশরা কীভাবে জটিল নিয়ন্ত্রণ ও জোরপূর্বক সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করেছিল, অধিকাংশ উৎপাদিত শস্য ও পণ্য কর আকারে বাজেয়াপ্ত করা হতো। তিনি ভয় পান যখন দেখেন, এটি প্রায়ই খোঁপায় ব্যাজেটের আঘাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হত।
ধর্মপালের মতে, ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ভারতের জন্য, সম্ভবত ১৭শ শতাব্দীতে দীর্ঘ আলোচনা করার পরও, কখনোই ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন করার চেষ্টা করা ছিল না। মনে করা হয়েছিল, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে, জলবায়ু, তাপমাত্রার সীমা, দক্ষ, পরিশ্রমী ও ঘনবসতি জনসংখ্যার কারণে, ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন করার খুবই সীমিত উদ্দেশ্য থাকবে।
সুতরাং, ব্রিটিশদের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল—ভারতের জনগণের বৈচিত্র্যময় শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদন এবং এই শিল্পে আরোপিত করকে ব্রিটেন ও ইউরোপে পৌঁছে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রস্তাবটি ১৭৮০ সালের আশেপাশে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দর্শনের অধ্যাপক অ্যাডাম ফেরগুসন স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। (রোমাঞ্চকরভাবে, তাঁকে ব্রিটিশ সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।)
ভারত শাসনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার সময়, ফেরগুসন এই শাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, লক্ষ্য ছিল ভারতের সম্পদ যতটা সম্ভব ইউরোপে স্থানান্তর করা। এবং এই কাজ সরাসরি ব্রিটিশ রাষ্ট্রের সেবক ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হতে পারত না। তারা নিয়ম এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলায় এতটাই আবদ্ধ থাকবে যে তারা এই কাজ যথাযথভাবে করতে পারবে না। সম্পদ ইউরোপে স্থানান্তর করার জন্য সাধারণত নিয়ম ভঙ্গ এবং উপেক্ষা প্রয়োজন হবে, কারণ শাসিতদের কাছ থেকে বড় ধরনের আহরণ বা লুটপাট রাষ্ট্রের যন্ত্রের মাধ্যমে কার্যকরভাবে করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মনে করেছিলেন, ভারতের সরাসরি শাসন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সেবকদের হাতে থাকা উচিত, যেমন E.I. Co., যেখানে প্রয়োজনে তারা নির্দেশ বা নিয়ম উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু কোম্পানিটি রাষ্ট্র দ্বারা গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। এই যুক্তি ও বিশ্লেষণই শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ সালে ভারত বিষয়ক কমিশনার বোর্ড প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়।
ধর্মপাল দেখেছেন যে ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং ১৯শ শতাব্দীতে অনেক অঞ্চলে জমির কর উর্বর জমির মোট কৃষি উৎপাদনকেও ছাড়িয়ে যেত। বিশেষ করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির (বর্তমান তামিলনাড়ু, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু জেলা, কর্ণাটক ও মালবারের কিছু জেলা) ক্ষেত্রে। এই নীতির ফলাফল সহজেই অনুমেয়: মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১৮০০–১৮৫০ সালের মধ্যে সবচেয়ে উর্বর জমির এক-তৃতীয়াংশ অচাষে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, ১৮০৪ সালের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর লন্ডনে বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে লিখেছিলেন:
“আমরা এই দেশে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছি… আমার সাধারণ মত হলো, আমরা দেশটিকে অত্যন্ত চাপ দিয়ে নিয়েছি, ফলস্বরূপ এটি অত্যন্ত দুঃখজনক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে আমি ভয় পাচ্ছি যে সাধারণভাবে অত্যাচার অত্যধিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।”
অবশ্য, ধর্মপাল একই আর্কাইভে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সিভিল প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্যও খুঁজে পান, যেমন ১৮১০–১১ সালে বারাণসী অঞ্চলে এবং ১৮৩০ সালে কনারায়, এবং কীভাবে সেগুলি দমন করা হয়েছিল। তবে এসব ঘটনা সরকারিভাবে নীতিমূলক নথিতে ধরা হতো না। যদিও অভিযোগ পত্র গ্রহণ করা হতো, তা অফিসিয়ালি নথিভুক্ত হতো না যদি না অভিযোগে আবেদনকারীর নম্রতা এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত।
একটি বাতিল করা অভিযোগপত্রের অংশ যা বারাণসীতে ঘরের করের বিরুদ্ধে ছিল, তা হাইলাইট করা হলো:
“…সাবেক সুলতানরা কখনো সরকারী অধিকার (সাধারণত মালগুজারি বলা হয়) তাদের অধীনস্থ বসতি অঞ্চলে সম্প্রসারিত করেননি। এ কারণে, সম্পত্তি বিক্রির সময় মালিকের বসতি অঞ্চল বিক্রয় থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাই এই করের প্রয়োগ সমগ্র সম্প্রদায়ের অধিকার লঙ্ঘন করে, যা ন্যায়বিচারের মূল নীতির বিপরীত।”
“…জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে পাওয়া কঠিন, স্ট্যাম্প ডিউটি, আদালতের ফি, ট্রানজিট ও শহরের শুল্ক যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ধনী ও দরিদ্র সবাইকে প্রভাবিত করছে এবং এই কর, যেন ক্ষতের উপর লবণ ছড়ানো হয়, সকলের জন্য দুঃখ ও বিষণ্ণতার কারণ; বিবেচনা করা হোক যে এই করের ফলে দশ বছরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম ষোলগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, আমরা যারা উপার্জনের উপায় নেই, আমরা কীভাবে টিকে থাকব?”
ব্রিটিশরা এই ধরনের উপায় ও অন্যান্য সমান কৌশল ব্যবহার করে প্রায় ১৮২০–১৮৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় গ্রামীণ জীবন ও সমাজকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। একই সময়ে, বিস্তৃত ভারতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রও একই ভাগ্য ভোগ করে। ব্রিটিশ নীতির কারণে, থমাস মেটকালফ ১৮৩০ সালের আশেপাশে এবং কার্ল মার্কস ১৮৫০ সালের মধ্যে বর্ণনা করা বিখ্যাত ভারতীয় গ্রামীণ সম্প্রদায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমান মন্তব্য ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শুরুতে তা তাদের সমসাময়িক প্রয়োজন ও ব্রিটিশ counterparts-এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর, ভারতীয় জ্ঞান ও প্রথার ধারাবাহিকতা তাদের জন্য হুমকি মনে হয়। তাই এটি অব্যবহার্য বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য পাশ কাটানো হয়। ধর্মপাল দেখেছেন, এই ‘বিলুপ্তি’ প্রক্রিয়া প্রায় সকল মানবিক কার্যকলাপে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যেমন কটন বস্ত্র, ভারতীয় স্টিলের উৎপাদন, এমনকি ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে মুরগির ক্ষুদ্রপক্সের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিষেধক প্রথা।
একই ভাগ্য বিস্তৃত ভারতীয় স্কুল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অপেক্ষা করছিল, যখন ১৮২০–১৮৩০ সালের মধ্যে সেগুলি সমীক্ষা করা হয়। রোমাঞ্চকরভাবে, প্রধানত ব্রিটিশ আর্কাইভাল রেকর্ডের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা নেটওয়ার্কের বিস্তৃত প্রকৃতি এবং মাদ্রাজ ও বাংলা প্রেসিডেন্সিতে দ্রুত হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হই। পরে বোম্বে ও পাঞ্জাব প্রেসিডেন্সিতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এই আর্কাইভাল তথ্য থেকে পাওয়া চিত্র বিচ্ছিন্ন, একত্রিত নয়। তবে এসব সূচকই মূল্যবান। এছাড়াও এটি আমাদের প্রাচীন ভারতের জীবন ও সমাজের কিছু দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা ১৮৫০ সালের পর ব্রিটিশ শাসনের ফলে আমরা হারিয়েছি।
ধর্মপাল ইতিহাসের ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন:
“যদি আমরা এই রেকর্ডগুলি আরও গভীরে অনুসন্ধান করি, আমাদের প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক, শিলালিপি ও অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র এবং মানুষের স্মৃতি ও চেতনা ব্যবহার করে, আমরা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অতীত পুনর্গঠন করতে সক্ষম হওয়া উচিত, এবং আশা করা যায়, আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজকে সেই অনুযায়ী গঠন করতে পারব।”
স্বাধীনতার পর, ১৯৪৭ সাল থেকে, আমাদের অগ্রাধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আত্মপরিচয় ও সমাজ পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে আমাদের পণ্ডিত, প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের পক্ষে হারিয়ে গেছে। আমরা মনে হয় ভুলে গিয়েছি যে আমরা আমাদের অতীত থেকে শিখতে পারি এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে পারি। আমরা কী চাই—নিজস্বভাবে, অন্যের ধারণা ও সামগ্রিক সাহায্য ছাড়া? আমাদের কি উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে? আমরা কি নিজেদের মতামত রাখতে পারি— অন্যদের অনুসরণ না করে? ভারতীয় হিসেবে আমাদের কি বক্তব্য আছে?
ধর্মপাল যখন ১৯৬৫–৬৬ সালের আশেপাশে এই বৃহৎ কাজ শুরু করেছিলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন, ব্রিটিশ হিসাব যতই অসম্পূর্ণ হোক, এগুলি আমাদের সাহায্য করবে যদি আমরা ভারতের বিদ্যমান উপাদানগুলি আরও বিস্তারিত ও গভীরভাবে অনুসন্ধান করি। আমাদের নিজের মানুষের অংশগ্রহণও জরুরি— অধিকাংশ বিষয় এখনও তাদের অতীতের সাথে যুক্ত এবং জীবন্ত স্মৃতি বজায় রয়েছে। এক প্রজন্মের মধ্যে আমরা আমাদের প্রাচীন জীবন ও সমাজ পুনর্গঠন শুরু করতে পারি, যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে সংযুক্ত হবে।
যাইহোক, এটি উদ্বেগজনক যে আমরা এখনও এই কাজ শুরু করি নি। ধর্মপাল আরও লিখেছেন:
“আজ আমরা শত্রুতায় ঘেরা মনে করি— অনেকটা আমাদের নিজস্ব অদক্ষতা ও কাজের কারণে। ১৯৪৭ সালের পর আমরা নিজেদের পশ্চিমের সাথে আত্মীয় মনে করেছি। পশ্চিমের আধিপত্যের কারণে, কিছু সময়ের জন্য পশ্চিমের জ্ঞান ও পণ্য ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এটি কেবল অল্পকালীন। খুব শীঘ্রই, আমাদের যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে হয়, আমরা আমাদের নিজস্ব উপকরণ, পরিবর্তন ও সংস্করণ ব্যবহার করে তা তৈরি শিখতে হবে।
এদিকে, আমাদের সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে হবে; তাদের স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে, এবং তাদের প্রতিভা ব্যবহার করে নিজেদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জগত পুনর্গঠন করতে উৎসাহিত করতে হবে। (প্রয়োজন হলে এমন আইন ও নিয়ম প্রত্যাহার করা যা তাদের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয় এবং আমাদের পরামর্শ ও সমালোচনা নিজের মধ্যে রাখা উচিত)। তখনই স্থানীয় সম্পর্ক ও সংযোগ পুনরুজ্জীবিত হবে; সামাজিক আচরণ ও স্মৃতি নির্দিষ্ট কার্যকলাপে জাগ্রত হবে; এবং পুনর্গঠন শুধু অতীতের অনুকরণ থাকবে না। পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে ভারতীয় সমাজ সেই সব পশ্চিমী বা অন্যান্য প্রযুক্তি গ্রহণ করবে যা নিজেদের ভিত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক ও উদ্দীপক মনে হয়।”


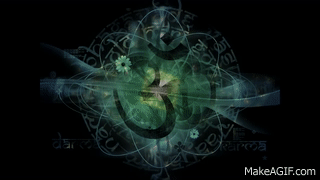




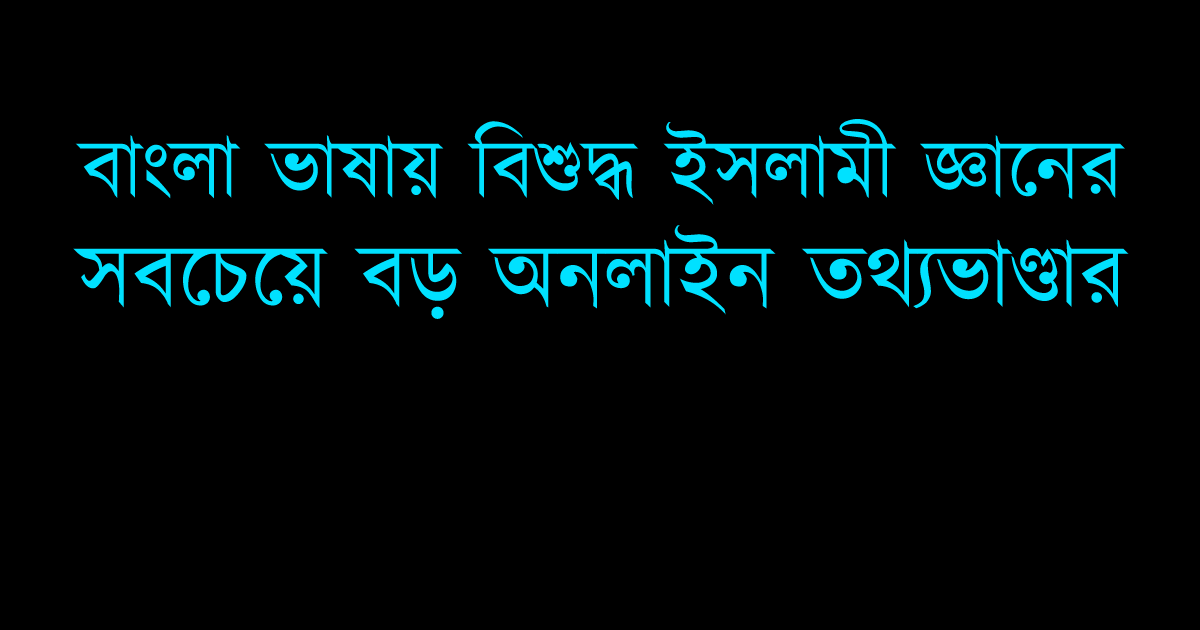
















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ